উপ-সম্পাদকীয়
রোকেয়া চেতনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা
আলমগীর খান

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি মুসলমান নারীর সমাজ জীবনে আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিলেন। সমাজের জগদ্দল পাথরটিকে নাড়া দিয়েছিলেন প্রচন্ড শক্তিতে। তার সাহসী ভূমিকা বাঙালি নারী জীবনের সর্বত্র। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন শিক্ষায় নারীর অগ্রগতিতে। আর তা শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, কর্মক্ষেত্রেও। রোকেয়া সাহিত্যচর্চা করেছেন সাহিত্যের খাতিরে নয়, নারীমুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে। আর রোকেয়ার নারীভাবনা সমাজভাবনা থেকে আলাদা নয়, সমাজের সার্বিক বিকাশের অংশ।
বেগম রোকেয়া খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারীকে পশ্চাৎপদ রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু নারী কোথায় পিছিয়ে আছে বা সমাজ কাঠামোর বন্ধনে তাকে কোথায় কিভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে রোকেয়া তা নিজে নারী হওয়ার কারণে এবং এসব কোনো কোনো বৈষম্যের প্রত্যক্ষ শিকার হওয়ার কারণে সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অন্যরা কি উপলব্ধি করেননি? রোকেয়ার মতো অন্য নারীরা যারা সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্য তারা প্রচলিত পুরুষাধিপত্যের সংস্কৃতিকে শুধু মেনেই নেননি, বরং ওই নারীবিদ্বেষী সংস্কৃতির ধারক-বাহকে পরিণত হয়েছেন। রোকেয়ার মন সেখানে শুধু প্রতিবাদ করেই থেমে থাকেনি, বরং কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি কাজ করেছেন। এভাবে রোকেয়া নিজে যেমন শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছেন, বাংলার সকল নারীকেও শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সে অভিযানে তাদের সাধ্যমতো সহায়তা করেছেন।
রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনার একটি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। তিনি শুধু নারী হিসেবে উপলব্ধিকেই তার লেখায় প্রকাশ করেননি। একটি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সমাজ ও নারীকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার বিজ্ঞানমনস্কতা এক্ষেত্রে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বিজ্ঞানমনস্কতার কারণেই রোকেয়া প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন ও অন্যদেরও মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের বস্তুবাদী কার্যকারণ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই কোনো কিছুকেই ভাববাদী ঘোলাটে দৃষ্টিতে দেখেননি। মানবমনের অন্যতম শক্তিশালী আবেগ ধর্মকেও দেখেছেন বিজ্ঞানের দূরদর্শনযন্ত্রে-দেখেছেন তার উৎপত্তির ঐতিহাসিক পটভূমি ও তাতে পুরুষাধিপত্যের রূপ-এমনকি ধর্মের জালে আবদ্ধ চিন্তাচেতনায় একটি পশ্চাৎপদ সমাজের বাসিন্দা হয়েও তা দেখতে, বুঝতে ও অকপটে বলতে দ্বিধা করেননি।
তাই ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।’
রোকেয়া এখানে তার যুক্তি উপস্থাপনের জন্য সমাজবিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছেন, যদিও কিছুটা অনিশ্চিতভাবে। স্পষ্টভাবেই তিনি প্রচলিত ব্যাখ্যার ওপর ভরসা করেননি। রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে Sultanas Dream । রোকেয়ার ২৪ বছর বয়সে লেখা ‘সুলতানাস ড্রিম’ ১৯০৫ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত। পরে ১৯২২ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিজেই একে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী ও লেখক আশরাফ আহমেদের বক্তব্য-
‘গল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলো হচ্ছে সূর্যের আলো ও তাপ, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, বিমানে আকাশ ভ্রমণ এবং বৈদ্যুতিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আবিষ্কারগুলোকে ভিত্তি করে কাল্পনিক মহিলা বিজ্ঞানীরা পুরুষকে গৃহবন্দি করার মত সামাজিক-প্রযুক্তি (সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) ছাড়াও বৈদ্যুতিক-প্রযুক্তি, উড়োজাহাজ-প্রযুক্তি, আবহাওয়া-প্রযুক্তি, যুদ্ধ-প্রযুক্তি, গৃহস্থালি-প্রযুক্তি এবং কৃষি-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেন। এর বাইরে আরো রয়েছে ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধ করে মহামারি নিয়ন্ত্রণ, যদিও এর বৈজ্ঞানিক কোনো উপাদান বইটিতে নেই। তিনি যেসব বৈজ্ঞানিক উপাদান ব্যবহার করেছেন সেগুলোর প্রায় সবই ছিল প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তত্ত্ব ও তথ্যের ওপর নির্মিত।’ (বেগম রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ একটি আদর্শ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, মে ২০২২)
রোকেয়ার এ উপন্যাস একটি নারীবাদী ইউটোপিয়া। যেখানে পুরুষরা অন্তঃপুরবাসী ও নারীরা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের কর্ণধার। সেইসঙ্গে সেখানকার নারীরা কেবল বিজ্ঞানমনস্ক তাই নয়, নতুন নতুন বিস্ময়কর সব জিনিসের আবিষ্কারক। অতএব সংক্ষিপ্ত এ উপন্যাসটির আরেকটি পরিচয় হলো এটি রোকেয়ার একটি সফল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। বিজ্ঞান-লেখক Thomas Lewton 2019G Feminist Visions of Science and Utopia in Rokeya Sakhawat Hossains Sultanas Dream প্রবন্ধে একে বলেছেন ‘বিশ্বে প্রথম দিককার নারীরচিত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলোর একটি।’ তার মতে, রোকেয়া তার সমকালের চেয়ে কয়েক দশক এগিয়ে ছিলেন। এ নারীবাদী বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীটিতে তিনি শুধু বিজ্ঞান ও পুরুষতান্ত্রিকতার যোগসাজশের সমালোচনা করেননি, সমালোচনা করেছেন বিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী শক্তির যোগসাজশেরও; যা তখন ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। নারী-অধিকারের জন্য রোকেয়ার জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও লেখালেখি বাংলার রাজনৈতিক অগ্রগতি ও ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তির বার্তা বহন করেছে বলেও মনে করেন লিউটন।
থমাস লিউটন আরও লিখেছেন- বিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘকালীন সুসম্পর্কের সমালোচনা রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন। রোকেয়া লিখেছেন, ‘আমরা অপরের জমি-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা এক খন্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না-যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞান-সাগরে ডুবিয়া রতœ আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভান্ডারে যে অমূল্য রতœরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাই ভোগ করি।’
বৈশি^ক প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে, কার্বন দূষণজনিত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবসভ্যতাই আজ যখন হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তখন রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্নই শুধু আমাদের বাঁচাতে পারে। আবার ‘সুলতানার স্বপ্নে’ আছে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। ‘নারীস্থান’ একটি আগ্রাসী বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে দেশের আপামর জনসাধারণ সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নারীস্থানের স্বাধীনতা রক্ষা হয় সেখানকার নারীদের বুদ্ধিমত্তার ফলে। পুরুষসৈন্যদের পরাজয়ের পরে নারীদের ডাক পড়ে দেশ রক্ষার জন্য। তারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন সৌরশক্তির মতো অগ্রসর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি যা তখন ছিল কল্পনাতীত তার ব্যবহার দ্বারা। নারীস্থানের সৈনিকেরা পরাজিত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে গুদামজাত করেননি, পুড়িয়ে ফেলেছেন। নারীস্থানের এই স্বাধীনতাযুদ্ধ একেকটি অনন্য যুদ্ধবিরোধী গল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।
রোকেয়াকে শুধু বাঙালি মুসলমান সমাজের মুক্তির বার্তবাহক মনে করলে তাকে খন্ডিত করে দেখা হবে। কারণ বাঙালি মুসলমান নারীর যে সংকট তা প্রতিবেশী অঞ্চলেও আছে। তার সুলতানার স্বপ্নের ‘নারীস্থান’ এমন এক নারীবাদী ইউটোপিয়া যা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সীমান্ত অতিক্রমকারী যেহেতু নারীর পরাজয়ও ব্যতিক্রম বাদ দিলে বৈশি^ক।
বেগম রোকেয়া নারীর মুক্তিকে সমাজের সার্বিক মুক্তি থেকে আলাদা করে দেখেননি। নারীমুক্তির অস্ত্র হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাদের মাঝে শিক্ষাবিস্তারকে। লেখালেখিতে প্রতিষ্ঠা লাভের চেয়ে তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এবং রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারের মেয়েদের উদার আধুনিক জীবনযাপন ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় করানোয়।
শিক্ষা বলতে বেগম রোকেয়া শুধু সনদপ্রাপ্তি বুঝতেন না, প্রকৃত শিক্ষা বলতে বুঝতেন যা মানুষের মনকে বিকশিত করে। সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তার শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তার লেখালেখিতে জীবনযাপনের সবক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিদ্যমান। শিক্ষাক্ষেত্রে এখন চারদিকে যে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, নোংরামি, লজ্জাজনক সব ঘটনা ঘটছে তখন আমাদের শিক্ষাজীবনের কর্ণধারদের রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।
নারীস্থানের ভগিনী সারা সুলতানারূপী রোকেয়াকে বলেছেন, ‘আমাদের ধর্ম প্রেম ও সত্য।’ আজ যখন ধর্ম ক্রমান্বয়ে উগ্র রূপধারণ করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা লুটার উপায়ে পরিণত হচ্ছে, তখন নারীস্থানের সুলতানার ধর্মচিন্তার সঙ্গে আমাদের আরও বেশি পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।
ক্রমবর্ধমান নারী-শিশু নির্যাতন, শিক্ষক নির্যাতন, ধর্মীয় উগ্রতা, বিজ্ঞান-বিদ্বেষের এ নেতিবাচক কালে রোকেয়া অনেক জরুরি। বেগম রোকেয়াকে তাই কেবল ‘বিশ^বিদ্যালয়’ ‘দিবস’ (৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস; তার জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর ও মৃত্যু ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর) ও ‘পদকের’ মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে শ্রমজীবীসহ সব শ্রেণী ও পেশার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।
তার অগ্রসর রাষ্ট্রীয় চিন্তার প্রমাণ হিসেবে আরও উল্লেখ করা যায়- সুলতানার এ স্বপ্নের রাজ্যে কোনো অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড নেই, মহামারি নেই, কর্মসময় দৈনিক দুই ঘণ্টা, শিশুমৃত্যু ও অকালমৃত্যু দুর্ঘটনা ছাড়া নাই বললেই চলে, মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স একুশ, অধিবাসীদের প্রধান খাবার ‘ফল’ (প্রাণীজ আমিষ নয়, যার ফলে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক) এরকম অনেক সামাজিক-রাষ্ট্রিক অর্জন যার কিছু কিছু এখনকারই অনেক উন্নত রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের পথে।
ওই রাজ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতি মানবিক, প্রকৃতিবান্ধব ও সুখকেন্দ্রিক। তারা মোট জাতীয় উৎপদনের বা জিডিপির হিসাব কষে রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ণয় করে না, বরং মোট সুখ পরিমাপ করে হয়ত। ভগিনী সারাকে তাই সুলতানা উচ্ছ্বসিত হয়ে নারীস্থান সম্পর্কে বলছেন- ‘আহা মরি! ইহার নাম সুখস্থান হয় নাই কেন?’ পৃথিবীর অনেক দেশ এখন মোট আয় বা অর্থ বা টাকা নির্দেশক জিডিপির শিকল ছিঁড়ে প্রত্যেক মানুষের সুখ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনীতি ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছে।
ভবিষ্যতের মানবিক রাষ্ট্রগুলোয় এসব আর কেবল সুলতানার স্বপ্ন হয়ে থাকবে না, দৈনন্দিন বাস্তবতা হয়ে উঠবে। তবে নিশ্চয়ই ওই স্বপ্নের রাজ্যে যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পথ পাড়ি দিতে হবে।
[লেখক : সম্পাদক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি]
-
টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি
-
রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা
-
রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...
-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক
-
জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা
-
টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং
-
ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়
-
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট
-
আসামি এখন নির্বাচন কমিশন
-
কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?
-
এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?
-
মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
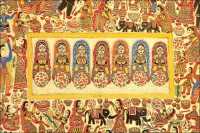
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?
-
সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব
-
প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক








