উপ-সম্পাদকীয়
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত শক্তি
শেখর ভট্টাচার্য

বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরের, আবার কেউ কেউ বলে থাকেন প্রায় দেড় হাজার বছরের কথা
সময়ের আবর্তে ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানুষ আহোরিত জ্ঞানের দ্বারা যতই পরিশুদ্ধ হয় ততই তার সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তন নদীর স্রোত, কিংবা প্রকৃতিতে বাতাস বয়ে চলার মতো স্বাভাবিক বিষয়। এক সময় সতীদাহ প্রথা আমাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল। জীবন্ত স্ত্রীকে আনন্দ উৎসব করে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হতো। স্ত্রীর বেঁচে থাকার আকুল মিনতিকে ঢাক, ঢোল, কাঁসার ঘণ্টার উচ্চ ধ্বনির দ্বারা ঢেকে দেয়া হতো। এই অমানবিক রীতি সমাজ তৈরি করেছিল এবং এই রীতিকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল সে প্রশ্নটি ভিন্ন কিন্তু সমাজ এই রীতি পালন করত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে।
উনবিংশ শতাব্দীতে অখন্ড বাংলায় কিছু মানুষের জ্ঞানচোখ উন্মিলিত হয়েছিল- পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে। এই মহান মানুষগুলো সমাজের অমানবিক রীতিনীতিগুলো পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজা রামোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ আরও শুভ শক্তি সম্পন্ন মানবিক মানুষ এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছিলেন যদিও সমগ্র বাংলায় তাদের এসব যুগান্তকারী উদ্যোগের প্রভাব ঘটেনি তবুও তারা চিন্তা ক্ষেত্রে একধরনের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা রোধ করতে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের নেতৃত্বেই উনবিংশ শতাব্দীতে একটি নীরব নবজাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণটিকে অনেকেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঘটা ইউরোপীয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রভাব বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল। ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয় দুটি অবিচ্ছেন্দ্য। ভাষার প্রশ্নে বায়ান্ন সালে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল তা মূলত সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে এ কথাটি খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।
বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরের আবার কেউ কেউ বলে থাকেন প্রায় দেড় হাজার বছরের কথা। তবে এই দীর্ঘ ইতিহাসের প্রায় চারটি কাল বা যুগের বিষয়ে সবাই ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন। আদি বা প্রাচীন যুগ, অন্ধকার বা অনুর্বর যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। বাংলা ভাষার গতিপথকে যদি চর্যাপদ রচনাকাল থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে বাংলা ভাষার পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি আমাদের বিস্মিত করে তোলে। চর্যার পদগুলো খ্রিস্টীয় অস্টম মতান্তরে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বলে অনুমিত হয়। চর্যার রচনার সময়কাল নিয়েও ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যার পদগুলো খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই সময়কালকে আরও ২০০ বছর পিছিয়ে দিয়ে চর্যার রচনাকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বলে মতপ্রকাশ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দী ধরে নিলেও এখন থেকে হাজারেরো বেশি বছর আগের এই ভাষার রূপ এবং গঠনের পরিবর্তন বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ বলে মনে হয়।
আদি যুগ থেকে বাংলা ভাষার এই পথ পরিক্রমায় ভাষা হিসেবে বাংলা নানারকম চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজকের এই আধুনিক অবস্থার রূপ নিয়েছে। চড়াই-উৎরাইয়ের কথা যা বলা হলো- তা দুরকমের; একটি হলো শাসকদের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া না পাওয়া এবং অন্যটি হলো ভাষার বিবর্তনের পথে নানারকম প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে করা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। আরবি হরফে বাংলা লেখার এক অদ্ভুত চিন্তা করেছিল পাকিস্তান সরকার। এই অদ্ভুত চিন্তার জনক ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। এই চিন্তাটি করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক চিন্তায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পূর্ববাংলার মানুষের মন থেকে চিরতরে নির্বাসিত করার হীন উদ্দেশ্যে নিয়ে।
পাকিস্তান সরকারের মধ্যে আগাগোড়াই বাংলা ভাষাবিরোধী মনোভাব ছিল। বাংলাদেশি ইতিহাসবিদদের মতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এর অংশ হিসেবে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়, যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান যুক্তি তুলে ধরেন যে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের গুরুত্ব রয়েছে। পাকিস্তানের সব ভাষার অক্ষর এক হওয়া উচিত বলে তিনি প্রচার করতে থাকেন। তার যুক্তি ছিল, পশতু, সিন্ধি এবং পাঞ্জাবি ভাষার হরফ আরবির মতো। সুতরাং বাংলা হরফ সে রকম হতে পারে। একপর্যায়ে বাংলায় আরবি হরফ প্রবর্তনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বলে মত দেন সৈয়দ আলী আহসান। পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, শিক্ষা উপদেষ্টা মাহমুদ হাসানকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠান ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কাছে। বদরুদ্দীন উমর তার ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ বইতে সে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।
বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, ‘সেই চিঠিতে মাহমুদ হাসান ডক্টর শহীদুল্লাহ কে লিখেন যে- সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তানকে ইসলামি মতে গঠন করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা বাংলা ভাষায় আরবি অক্ষর প্রবর্তন করতে চান। এবং এজন্য তার সাহায্য পেলে উপকৃত হবেন।’ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সে চিঠির কোন জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। উল্টো তিনি এই চিঠির বিষয়বস্তু সংবাদপত্রে জানিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে তিরষ্কার করা হয় পরবর্তীতে।
আরবি হরফে বাংলা চালুর জন্য পাকিস্তান সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে ধীরে-ধীরে প্রতিবাদ গড়ে উঠতে থাকে।
পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিদ এবং ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা।
আরবি হরফ প্রবর্তনের নিন্দা জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছে একটি চিঠি দেয়।
বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষার্থীরা যুক্তি তুলে ধরেন যে আরবি হরফ চালু হলে পূর্ব পাকিস্তানে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ একজন নতুন শিক্ষার্থীর জন্য আরবির চেয়ে বাংলা অক্ষর শেখা বেশি সহজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জগন্নাথ কলেজ এবং ইডেন কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং সচেতন মহলে এই প্রতিবাদ জোরালো হয়। এমন প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলা সরকার একটি প্রেস নোট জারি করে বলতে বাধ্য হয় যে বাংলা ভাষা বাংলা হরফে লেখা হবে, না আরবি হরফে লেখা হবে সেটি পূর্ব বাংলার জনসাধারণ নির্ধারণ করবে। এভাবেই আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্ভট চিন্তা বাতিল করতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়।
বাংলা ভাষার বিবর্তনের পথে আরবি হরফ, রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। মূলত ভাষা এবং সংস্কৃতি হলো স্রোতস্বীনি নদীর মতো। ভাষাভাষী সব মানুষের ইচ্ছায় ভাষা তার প্রয়োজনীয় শব্দকে কোলে তুলে নেয় আবার সবার কাছে গ্রহণীয় না হলে ভাষার নদী থেকে কিছু কিছু শব্দ হারিয়ে যায়। ভাষার মূল স্থান একটি দেশের মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জীবন আচরণের মধ্যে। এসব কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে ভাষাকে জোর করে পরিবর্তন করা যায় না। ভাষা বড় গণতান্ত্রিক। বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলনের পূর্বে যখন দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হরণ করা হচ্ছে তখন সব মানুষ জেগে উঠেছিল। মানুষের মনে শাসকের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। সেই যে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি অবিশ্বাস সে অবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীর অভাবিত এক মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন। কে জানতো এই অবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে মহীরুহ হবে এবং সাতচল্লিশে অর্জিত মানচিত্রকে ভেঙেচুরে নতুন একটি স্বাধীন ভূখন্ড উপহার দেবে। ওই যে বলেছিলাম মানুষের ভাষার বিবর্তন প্রকৃতির নিয়মের মতো বড়ই স্বতঃস্ফূর্ত এর গতি রোধ করা যায় না। গতি রোধের চেষ্টা সূর্যের উত্তাপকে প্রতিহত করার মতো অপচেষ্টা যা মূর্খ, অজ্ঞ মানুষেরাই করে থাকে। ভাষার বহমানতা, ভাষার অধিকার হরণের যারা চেষ্টা করেছিল, তারা আজ দেখছে তাদের চোখের সামনে লাল সবুজ পতাকা পত পত করে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশ আছে বাঙালিদের, যে দেশের সংবিধানে রক্ত দিয়ে লেখা আছে দেশটির রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। এরকম দেশের উদাহরণ গোটা বিশ্বে আর নেই। যারা এখনও নানা ভাবে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করছে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত বাংলাদেশের হৃৎপিন্ডের ভেতর থেকে ভেসে আসা ধ্বনি, প্রতিধ্বনি থেকে।
[লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক]
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
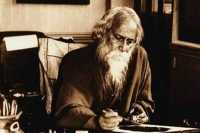
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম
-
রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়
-
মে দিবসের চেতনা বনাম বাস্তবতা
-
শ্রম আইন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই আন্তরিকতা
-
বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা কেন এত পিছিয়ে
-
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল : নিরাপদ যাত্রার প্রত্যাশা
-
কর ফাঁকি : অর্থনীতির জন্য এক অশনি সংকেত
-
১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় : উপকূলীয় সুরক্ষার শিক্ষা
-
যখন নদীগুলো অস্ত্র হয়ে ওঠে
-
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবন
-
বজ্রপাত ও তালগাছ : প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা
-
কুষ্ঠ ও বৈষম্য : মানবাধিকারের প্রশ্নে একটি অবহেলিত অধ্যায়
-

প্রান্তজনের বাংলাদেশ
-
অতীতের ছায়ায় নতুন বাংলাদেশ : দুর্নীতি, উগ্রপন্থা ও সরকারের দায়
-
সাইবার নিরাপত্তা : অদৃশ্য যুদ্ধের সামনে আমাদের প্রস্তুতি








