উপ-সম্পাদকীয়
‘সেপা’ চুক্তি নিয়ে কিছু কথা
এস এম জাহাঙ্গীর আলম
২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। তখন বিশ্ববাজারের অনেক সুবিধা আর থাকবে না। সে বিষয়টি সামনে রেখে এখনই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তির দিকে নজর দিতে হবে। তারই আলোকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি ‘সেপা’ নামে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ব্যাপারে যৌথ সমীক্ষাও হয়েছে।
সেপা চুক্তির মধ্যে পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব ও ই-কমার্সের মতো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকছে। সেপা চুক্তি হলে উভয় দেশের বাণিজ্য আরও বাড়বে এবং বিনিয়োগের নতুন দরজা উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে। সেপা চুক্তির কারণে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তার চেয়েও বড় বিষয়, এ চুক্তির আওতায় আমদানি শুল্কের প্রতিবন্ধকতা কমাতে হবে, যাতে বাংলাদেশ যথাযথভাবে এর সুফল পেতে পারে। এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আসিয়ান কিংবা চীনের সঙ্গেও হতে পারে।
ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে রেল ও নৌপথে যোগাযোগ আরও সহজ ও সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে সাতটি সমঝোতার মধ্যে দুটি রেলসংক্রান্ত। একটির আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মীরা ভারতীয় রেলওয়ের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নেবে। আরেকটি হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের রেলওয়ের মধ্যে আইটিবিষয়ক সহযোগিতা।
রেলওয়ের মাধ্যেও মালপত্র আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে রেল যোগাযোগ বাড়ানোর রয়েছে। ট্রাকে পণ্য আনা-নেয়ার খরচ অনেক বেশি; ঝামেলাও কম নয়। সেদিক থেকে ট্রেন ভালো বিকল্প নিঃসন্দেহে। সে লক্ষ্যে রেলওয়ের অবকাঠামো ও অন্যান্য সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সে ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রাইভেট সেক্টরকে কাজে লাগানোর কথা ভাবতে হবে। এখন পদ্মা সেতু নির্মিত হয়ে গেছে এবং সেখানে রেলওয়ে সংযোজনের কাজও হচ্ছে। ফলে ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও সহজ হবে। রেলওয়ের পাশাপাশি নদীপথে যোগাযোগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।
নদীপথে জাহাজে চাল, গম সহজেই আসতে পারে। ভারতীয় পাথর বা ভারী নির্মাণসামগ্রী আনা-নেয়ার জন্য নদীপথ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কলকাতা নদীবন্দরের সঙ্গে সরাসরি এবং ব্যাপক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি করা সম্ভব। ভারতীয় বিনিয়োগ আমাদের দেশে কীভাবে বাড়ানো যায়, সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে চলমান লাইন অব ক্রেডিটগুলোর (এলওসি) আওতাধীন প্রকল্পগুলোর গতিশীলতা বাড়াতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনও গঠন করা যেতে পারে।
এলওসির বাইরেও ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়াতে সে দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও আমাদের ব্যবসায়ী নেতারা আলোচনায় বসতে পারেন। ভারতের টাটা, বিড়লা, রিলায়েন্স বা আদানির মতো বড় বড় কোম্পানির বিনিয়োগের প্রসার বাংলাদেশে ঘটলে অর্থনৈতিক দিক থেকে উভয় দেশ লাভবান হবে। গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্নিষ্ট, সেটি হলো রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আমরা দেখেছি, ভারত মাঝেমধ্যেই রপ্তানি পণ্যে বিধিনিষেধ জারি করে। যেমন- পেঁয়াজ, চাল ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় পণ্য।
বস্তুত ভারত যখনই পেঁয়াজ বা চাল রপ্তানি করবে না বলে, তখনই আমাদের এখানে পেঁয়াজ বা চালের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে যায়। এভাবে যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা ভারতের ওপর নির্ভরশীল, সেসব পণ্যে ভারত যেন হঠাৎ বিধিনিষেধ না দেয়, সেজন্য তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। যেহেতু আমরা ভারতের ওপর নির্ভরশীল এবং আস্থাবান বাণিজ্যিক অংশীদার, সেহেতু ভারত অন্যদের সঙ্গে যে আচরণ করে, সেটা আমাদের সঙ্গে করা উচিত হবে না।
রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দিক থেকে অন্যান্য বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। এবার প্রধানমন্ত্রীর সফরে যেমন রহিমপুর খাল দিয়ে কুশিয়ারা নদী থেকে ১৫৩ কিউসেক পানি বণ্টনে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য নদীর ব্যাপারেও আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। কাউকে পেছনে ফেলে না রাখতে মানবসম্পদে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অথচ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) যথাক্রমে ১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ বিনিয়োগ করছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। দুই, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যাপক ব্যবহার। বাংলাদেশ এসব খাতে গুত্ব দেওয়া শুরু করেছে, তবে সক্ষমতার অভাব রয়েছে। তিন, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে অর্থনীতির রূপান্তর। বাংলাদেশে কৃষি থেকে ‘খালাস’ পাওয়া শ্রমকে নতুন ধারার শিল্পে নিয়োজন দিতে হবে। চার, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ। রপ্তানিযোগ্য পণ্য এবং রপ্তানির বাজার দুটোর বিস্তৃতি ঘটাতে হবে বাংলাদেশকে। পাঁচ, জলবায়ুর অভিঘাতের থেকে সুরক্ষায় ঝুঁকি সচেতন টেকসই উন্নয়ন। এ এলাকায় সচেতনতা বেড়েছে, কিন্তু এখনো কাক্সিক্ষত মাত্রায় অগ্রগতি নেই। ছয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধি করা। পুরোনো প্রতিশ্রুতির বাইরে এলডিসি-উত্তর পরিস্থিতিতে সহযোগিতার নতুন অঙ্গীকার নিতে হবে।
[লেখক: সাবেক কর কমিশনার; পরিচালক, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কো. লি.]
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
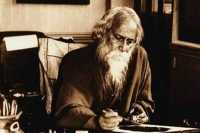
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম
-
রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়
-
মে দিবসের চেতনা বনাম বাস্তবতা







