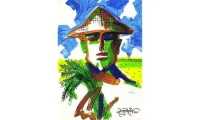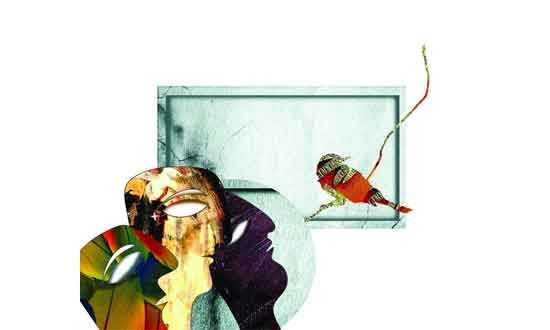
আলো, মাটি ও মানুষের বৈশাখ
রওশন রুবী
বৈশাখ বাংলার ঘরে ঘরে সাম্য নিয়ে আসে। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ, জাতপাতের দূরত্ব-সব যেন একদিনের জন্য হলেও লুপ্ত হয়। সবাই খায় এক থালায়, হাঁটে একসাথে, গলায় গলায় গান করে। এই সমানতা-এই মানবিক সংহতিই বৈশাখের সবচেয়ে বড় অর্জন।
গ্রামবাংলায় বৈশাখ একটি দিন বা সময়েরবাঁক বদল নয়, এটি একটি ঋতুচক্রের ভেতরে রচিত জীবনদর্শনের প্রতীক। তাই বৈশাখ তাদের কাছে জীবনের নবজন্ম, আত্মস্মরণ ও নবজাগরণ।বৈশাখ গ্রামে আসে কোনো বড় ব্যানার, মাইক কিংবা শহুরে সাজসজ্জার মোড়কে নয়; সে আসে বাতাসের গন্ধ হয়ে, মাটির ভিতর নরম স্পন্দন হয়ে, মানুষের মধ্যে সহজাত আনন্দের বন্যা হয়ে।
ধানক্ষেতে তরঙ্গে খেলে যায় বাতাস। আমের মুকুল, কচি আম, কাঁঠাল ফুলের মৌ মৌ গন্ধ, গাছে গাছে কনকচূড়া, বেলি, গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুল জানান দেয় বৈশাখ এসে গেছে। কৃষকের হাতে তখন কাস্তে নেই, আছে অপেক্ষা। ফসল ঘরে তুলে নিঃশ্বাস নিতে না নিতেই সে দেখে বৈশাখ দাঁড়িয়েছে তার উঠোনে-নতুন বছর, নতুন স্বপ্ন, নতুন হিসেব। ঘরের কোণে পুরোনো খাতা সরিয়ে জায়গা করে নেয় নতুন হালখাতা।এই নবজাগরণ কেবল প্রতীকি নয়-এটি বাস্তবিক। বৈশাখ বদলে দেয় কৃষির ছন্দ, উৎসবের রঙ, প্রেমের ভাষা এবং গানের সুর। মাঠে ধান কাটা শেষে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় নতুনভাবে। বৈশাখ সেই মুহূর্তে এসে বলে-এখন একটু থামো, একটু গান গাও, একটু নিজের দিকে ফিরে চাও।
গ্রামে বৈশাখ মানে একটা পূর্ণ মৌসুম। এখানে মেলা বসে, উৎসব হয় পাটখড়ির ছায়ায়, বটগাছের নিচে, নদীর ঘাটে, খালের ধার ঘেঁষা মাঠে, ছোট ছোট হাটে। মেলায় কাঠের ঘোড়া, কাঁচের চুড়ি, মাটির খেলনা, রঙিন পুতুল, রঙিন হাঁড়ি, মুড়ি-মুরকি, বাতাসা, জিলেপি, ফল, বেত বাঁশের জিনিসপত্র আরও কত কী উঠে। মেলায় যেমন লোকজ ঐতিহ্যের নানান স্টল বসে তেমনি নানান লোকজ খেলা পরিবেশিত হয়। নাগরদোলা, চরকি, ট্রেন, পুতুল নাচ ইত্যাদি অয়োজন। পোশাকেও দেখা যায় রঙ আর নকশিকাজের বৈচিত্রময়তা। বাঙালিয়ানায় লাল সাদা রঙের বাহারি সুতি শাড়ি, সালোয়ার কামিজ পরে মেয়েরা। পুরুষেরা সাদা, লাল কিংবা হালকা মেঘলা নীল নকশিকাজের পাঞ্জাবি, ফতুয়া পরে। মেলায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসে বাবা মা কিংবা ভাই বোনের সাথে। তারা ফড়িংয়ের মতো নেচে, গেয়ে বেড়ায় এধারে ওধারে। যুবক, যুবতী, কিশোর, কিশেরী নানা বয়সের মানুষের সমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে। বেলফুলের গন্ধে জড়ানো দুপুর যেন নিঃশব্দে প্রেম নিয়ে আসে বৈশাখের জীবনে।
কখনও কখনও উৎসবে তীব্র শব্দ ছাড়িয়ে কানে বাজে বাউলের কণ্ঠ, পালাগান, ঝাঁপান খেলার হাঁকডাক। কেউ একজন গেয়ে ওঠে, “মন রে, কৃষ্ণকলি আমি তাহারি নাম ধরি”- আর বটতলায় বসে শোনা-অদেখা শ্রোতারা হঠাৎ থেমে যায়। কণ্ঠ, মাটি, বাতাস-সবকিছু যেন তখন একযোগে গেয়ে ওঠে। গ্রামের বৈশাখ হয়তো তেমন জাঁকজমক পূর্ণ নয়, সোজাসাপটা তবুও তাতে যা থাকে তা একটি জাতির প্রাণের অমূল্য ইতিহাস।
খাবারেও সেই ইতিহাস লেখা থাকে। সেই ইতিহাসে বৈশাখ মানে পান্তা, উলিশ, নানা পদের ভর্তা, খিচুড়ি নয়-ধানভাজা, গুড়, নারকেল দিয়ে বানানো পিঠে। রান্নাঘরে ছড়ায় ঢেঁকিতে ভাঙা চালের গন্ধ, আগুনে পুড়তে থাকা খড়ের ধোঁয়া। ঘরের মেয়েরা আসে বাপের বাড়ি, রান্না হয় খড়ের চুলায়, খাওয়া হয় একসাথে-নতুন পাটপাটির উপর বসে। পুঁইশাকের ঝোল, মিঠা আলু ভাজি আর পাটালি গুড় মিশিয়ে বানানো মুড়ি-সব মিলিয়ে এক পরিপূর্ণ গ্রামীণ বৈশাখের ছায়া। এখনও স্বপ্ন ছড়িয়ে যায় দাদি-নানিদের মুখে শুনে। তবে সব বৈশাখ কি এতই কোমল? না, কখনো কালবৈশাখী এসে আঘাত হানে। মাঠের ধান পড়ে যায়, নদী, ঘরের ভিতখেয়ে নেয়। বৈশাখ তখন যেন বলে, “নতুন শুরু শুধু আনন্দ নয়, তা পরীক্ষা, তা শোধনের আগুনও।” গ্রামীণ মানুষ সেই আগুনে পুড়েও আবার গড়ে নেয়। এখনও গ্রামীণ নারীদের কাছে বৈশাখ মানে শুধু সাজ নয়-এটি তাদের নীরব ইতিহাসের এক উন্মোচন। এই সময়টাতে অনেক মেয়েই বাবার বাড়ি বেড়াতে আসে- যেখানে তারা তাদের শৈশবের আকাশ, গাছপালা, পুরোনো নুড়িপাথরের উঠোন খুঁজে পায়। বৈশাখ যেন তাদের কাছে সময়ের গর্ভে একবার ঢুকে, আবার বেরিয়ে আসার উৎসব। সেখানে থাকে সম্পর্কের পুনর্গঠন, স্মৃতির চুম্বক, আত্মার সংলাপ।
এই যে বৈশাখের মাঝে জীবনকে ছুঁয়ে দেখার এত আয়োজন, তার গভীরে আছে এক অলিখিত আধ্যাত্মিকতা। গ্রামীণ বৈশাখের প্রতিটি রীতি, প্রতিটি অভ্যাস যেন প্রকৃতির সাথে মানুষের আত্মীয়তার একটি জ্যামিতিক বিন্যাস। যখন খড়ের ঘরে বাতাস ঢুকে পড়ে, আকাশের রং বদলায়, বৃষ্টির গন্ধ পুকুরে পড়ে-তখন কৃষক জানে, প্রকৃতি তার সঙ্গে কথা বলছে। সব ছাড়িয়ে যখন ডেকে যায় ঘনকালো মেঘে, বজ্রবিদ্যুৎ খেলাকরে, প্রবাহিত হয় মৌসুমী বায়ু, সৃষ্টি হয় কালবৈশখী ঝড়। তখন সে বুঝে এ তা-বে প্রকৃতি ও মানবজীবনে নেমে আসবে বিপর্যয়।
পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ পালন করা হয় বাংলা মাসের প্রথম দিন, ১৪ এপ্রিলে। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল স¤্রাট জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর সিংহাসনে বসার পর থেকে বাংলা সন প্রবর্তিত হলেও বাংলা পঞ্জিকার উদ্ভাবক ধরা হয় ৭ম শতকের রাজা শশাঙ্ককে। খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে স¤্রাট আকবর পঞ্জিকাটি পরিবর্তিত করেন। প্রথম আকবরের পঞ্জিকার নাম ছিল “তারিখ-এ-এলাহী”। এর নামগুলো ছিল আর্বদিন, কার্দিন, বিসুয়া এমন। পরে বাংলা বারো মাসের নাম রাখা হয় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে এই সময়টিই ছিল নববর্ষ ও নতুন ঋতুচক্রের সূচনা। অষ্টকালের প্রভাতে ভক্তরা নদীতে স্নান করত, বোধিবৃক্ষের নিচে ধূপ জ্বালাত, আর ধানদেওয়া হতো দেবতাকে। সেই আচার আজ মেলা, নাচ গান আর আনন্দ দিয়ে গ্রামীণ হৃদয়ে বেঁচে আছে-অতীত ও বর্তমানের সংলাপের মতো।
বৈশাখ আমাদের সাহিত্যেও ছায়া ফেলেছে। বিশ^ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, “এসো হে বৈশাখ”-যেখানে তাঁর কামনার বৈশাখ আসে অগ্নিবাতাসে, পুরনোকে পুড়িয়ে নতুনকে ডেকে আনে। কবি জসীম উদ্দীনের ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কিংবা ‘নকশী কাঁথার মাঠ’-এ আমরা পাই গ্রামীণ আবেগ, প্রেম ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য গন্ধমাখা বৈশাখকে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভিতরে যেমন বাংলার প্রকৃতি, নিঃসঙ্গতা আর সৌন্দর্যের জ্যোতি, তেমনি গ্রামীণ বৈশাখের মাঝেও সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে।
আমাদের লোকসংস্কৃতিতেও বৈশাখের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ঢাকার “মঙ্গল শোভাযাত্রা” একদিকে আধুনিক নাগরিক আচার, অন্যদিকে তার মূল নিহিত আছে গ্রামীণ মঙ্গল কামনায়-যেখানে গরুর গাড়িতে আঁকা হতো আল্পনা। বাঁশের তৈরি মুখোশে উঠে আসে গাছ, নদী, প্রাণী, মানুষ-সব অদ্ভুত দৃশ্যপট।
এই নবজাগরণ মানে সমাজ চক্রের পূর্ণতা ও নতুন শুরুর ঘন্টা। বৈশাখে মহাজনের কাছে হালখাতা মেটানো মানে কেবল আর্থিক নয়-এটি আত্মিক মুক্তি, মন থেকে হিসেব মুছে দিয়ে নতুন করে জীবন রচনা। আবার কৃষিজীবী মানুষ কৃষিপঞ্জিকা অনুযায়ী বৈশাখ থেকেই পরবর্তী ফসলের প্রস্তুতি নেয় গোবর ছিটিয়ে জমি প্রস্তুত করা, জৈব সার তৈরি, নতুন বীজ বোনা। অর্থাৎ বৈশাখ কেবল উৎসব নয়, এটি উৎপাদনের একটি প্রধান পর্ব।
শেষ পর্যন্ত বৈশাখ আমাদের বলে-তুমি যতবারই ভাঙো, আবার গড়ো। গ্রামীণ মানুষ তাই বৈশাখকে কেবল উৎসব নয়, এক ধরনের আত্মজাগরণ হিসেবে দেখে। বৈশাখ তাদের কাছে ক্যালেন্ডারে পাতা নয়, খেজুর গাছের মাথায়, বাঁশঝাড়ের হাওয়ায়, পুকুরপাড়ের আলোছায়ায় লেখা থাকা দিনলিপি।
শহরের বৈশাখ হয়তো রঙিন হয়, কিন্তু গ্রামের বৈশাখ সরল-সমীকরণ।
তথ্যসূত্র:
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাত সংগীত, গীতাঞ্জলি
২. জসীম উদ্দীন, নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট
৩. জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলা, ধূসর পা-ুলিপি
৪. সৈয়দ মুজতবা আলী, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রম্যগল্প
৫. বাংলা একাডেমি প্রবন্ধ সংকলন, নববর্ষ ও বাংলার লোকঐতিহ্য
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, গ্রামীণ উৎসববিষয়ক গবেষণাপত্র