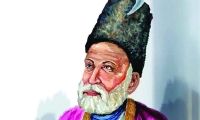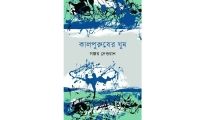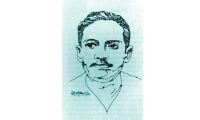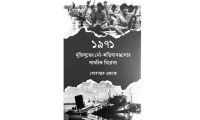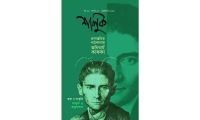নতুন কবিতার সন্ধানে
সরকার মাসুদ
‘কবিতার ভবিষ্যৎ’ শিরোনামের একটি গদ্যে আমি বলেছিলাম যে, বাংলা কবিতার নতুন সরণি তৈরিতে এখন আর ব্রিটিশ, মার্কিন, জার্মান কিংবা বেলজিয়ামের কবিতা সাহায্য করতে পারবে না। কিছুটা সাহায্য করতে পারে ফ্রান্স অথবা পূর্ব ইউরোপের কবিতা। আর পারে ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে রচিত নতুনতাপ্রয়াসী কবিতাসমূহ। ঢাকায় বসে সারা বাংলাদেশের কবিতা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কলকাতায় এমনকি দিল্লিতে থেকেও গোটা ভারতবর্ষের কবিতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া অসম্ভব। আশির দশকে ‘ভারতভবন’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে মধ্যপ্রদেশের শহর ভোপালে। তো ‘ভারতভবন’-এর লাইব্রেরিতে বসে জানা সম্ভব ভারতের দূর প্রান্তে কোন কোন লেখক কী কী উল্লেখ্য কাজ করেছেন। এমনকি জামশেদপুর বা কোচবিহার থেকে একটা মানসম্পন্ন বাংলা কাগজ বেরুলে তার খবরও জানা সম্ভব ওই ভবনে। সন্দ্বীপ দত্তের মতো কর্মযোগী মানুষ ছিলেন বলেই কলকাতায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। আর আমাদের এখানে পাঠবিমুখতা এবং মানসিক দীনতা এতই প্রকট যে, চোখের সামনে গড়ে ওঠা একটা সৃজনশীল বইয়ের বাজার দু’দশক যেতে না যেতেই পরিণত হলো তৈরি পোশাকের মার্কেটে।
সম্ভবত কবিতাই হচ্ছে সেই ব্যারোমিটার যার মাধ্যমে আমরা একটা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির চেহারা অবলোকন করতে পারি। যে দেশ লেখাপড়ায় অনেক পিছিয়ে তার সাহিত্যও পিছিয়েপড়া।
আবার অন্যভাবেও বিষয়টিকে দেখা সম্ভব। ধরুন, একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমানর মানুষ জাপানের সাহিত্য পড়েছেন কিন্তু তাদের ফুটবল খেলা দেখেননি। ইউকিয়ো মিশিমা বা হারুকি মুরাকামির সমকক্ষ না হলেও জাপানে অসংখ্য প্রথম শ্রেণির লেখক আছেন। আছেন ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা, কেনজাবুরো ওয়ের মতো বড় মাপের সাহিত্যিক যারা নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এখন ওই ব্যক্তি যদি ভাবেন, যে দেশের একাধিক লেখক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তার ফুটবল নিম্নমানের হতে পারে না; তার ওই ভাবনাকে আমরা অযৌক্তিক বলবো না। একটা উন্নত দেশের চিন্তা এমন- সে সবক্ষেত্রেই তার অগ্রসরতা কম-বেশি তুলে ধরতে সক্ষম। অন্যদিকে আমাদের অবস্থাটা দেখুন। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লেখক অল্প ক’জন, ঠিক যেমন অল্প কয়েকটি ছেলে/মেয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার বা ফুটবলার।
মোটাদাগে চিন্তা করলে দু’ভাবে পরিবর্তন সূচিত হয় কবিতায়। তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন (বাংলাদেশ) প্রভৃতির প্রভাবে এক ধরনের তীব্র কবিতা লেখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বাইরের প্রভাব। আর ভেতর থেকে আসা তাগিদের প্রভাবে নতুন ধরনের কবিতার দিকে এগিয়েছে কবিরা। বরঞ্চ ভেতরের তাগিদ থেকে যারা নতুনত্বসন্ধানী হয়েছেন তাদের মধ্যে সার্থক কবির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। হাংরি জেনারেশন, সহজ তকবিতা আন্দোলন (আশির দশক, বাংলাদেশ), অ্যান্টি পোয়েট্রিতে বিশ্বাসী কবিদের কর্মকা- যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়, পৃথিবীর কিছু কিছু কবি তীব্রভাবে প্রথার বাইরে যেতে চেয়েছেন, এখনও চান। অন্যদিকে অনেক সামর্থ্যবান কবি প্রথানুগ থেকেও তাদের প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়েছেন বাংলাভাষায় যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা আবুল হাসান। ইংরেজি ভাষার কবিদের মধ্য থেকে বলতে পারি ফিলিপ নারকিন, থম গান প্রমুখের কথা। শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলনগুলো এমনই যে, একবার যদি চাউর হয়ে যায় তাহলে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত তার খরব ছড়িয়ে পড়ে। এখন না- হয় ইন্টারনেটের জয়-জয়কার। কিন্তু পঞ্চাশের/ষাটের দশকে তো এই বাস্তবতা ছিল না। অথচ দেখুন পশ্চিমের অ্যান্ট্রি পোয়েট্রির ঢেউ ভারতবর্ষে এসে লাগার পর হিন্দি ভাষায় তা হয়ে গেল ‘অ-কবিতা’, বাংলাদেশে তারই নাম ‘বিকল্প কবিতা’। (এই নামেই একটি ক্ষণজীবী কবিতাপত্র বের করেছিলেন আশির প্রজন্মের শক্তিমন্ত কবি ও গল্পকার কাজল শাহনেওয়াজ।)
রবীন্দ্রনাথের সময় থেমে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতা খুঁটিয়ে পড়লে একটা বিষয় পরিষ্কার দেখতে পাওযা যায়। একজন জীবনানন্দ, খাকিটা অমিয় চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, বিনয় মজুমদার, আল মাহমুদ, তারাপদ রায়, অনেকখানি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুধেন্দু মল্লিক প্রমুখকে সসম্মানে এক পাশে রাখলে বাদবাকি কবিদের লেখা ধাঁধাময়, ফাঁপড়প্রদ, দমবন্ধকরা- এক কথায় অস্বস্তিকর।
দূরাতীতের রবার্ট ফ্রস্ট বা উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস এবং নিকট অতীতের ফিলিপ জাকোতে (ফ্রান্স), ভাস্কর চক্রবর্তী (ভারত) প্রমুখ কবির লেখায় সহজের ভেতর থেকে গভীর জীবনদৃষ্টি ব্যক্ত করার একান্ত ব্যক্তিক ভঙ্গি আমরা লক্ষ করেছি। ষাটের প্রজন্মেও দু’চারজন কবির হাত ধরে এবং প্রধানত সত্তরের কবিদের নিরন্তর তৎপরতায় বাংলা কবিতা আজ অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে। সুবোধ সরকার, নির্মল হালদার, আবিদ আজাদ, জাহাঙ্গীর ফিরোজ- এদের পরিণত বয়সের কবিতা বক্তব্যধর্মিতাকে সঙ্গে নিয়েই প্রয়োজনীয় আড়ালকে সঙ্গী করেছে। সাবলীলতা ও সহজতার জেল্লা এসেছে, এখনকার কবিতায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই যে চেহারার স্মার্ট দশা, ফুরফুরে ভাব, সহজভাবে সরাসরি কথা বলার প্রবণতা- এতে করে কবিতা কি তার গোপন ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলছে না? আমরা যাকে মানোত্তীর্ণতা বা শিল্পোত্তীর্ণতা বলি, কাব্যের বাচালতার বা অতিযোগাযোগ সক্ষমতার সঙ্গে তার বিরোধ কি অনিবার্য নয়? শিল্পের সঙ্গে রহস্যের সম্পর্ক আজও অবিভাজ্য বলেই মানি। সামান্য অলংকার বা একদম অলংকার ছাড়াই যে উৎকৃষ্ট কবিতা সম্ভব তা যেমন তারাপদ রায়, মুস্তফা আনোয়ারের মতো কবিরা করে দেখিয়েছেন; তেমনি রণজিৎ দাশ, নাসিমা সুলতানা, আহমেদ মুজিবদের লেখাতেও আমরা তা পেয়েছি।
ষাটের ও সত্তরের অজস্র কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে অথিকথনের পাল্লায় পড়ে। অস্বচ্ছ ভাবনা, উদ্ভট কবিকল্পনা, লক্ষ-ভেদ করতে না পারা বিদ্রƒপ বা কৌতুক, সর্বোপরি ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ স্থ’ূল কাব্যভাষা এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। আশির প্রজন্মেও নতুন কবিরা, তাই, কাব্যেও হারানো গৌরব উদ্ধারকল্পে সহজসরল ভাষার সঙ্গে মিশিয়েছেন শ্লেষ, অভিনতুন চিত্রকল্প, হৃদয়গ্রাহী ইশারা, অপ্রচল উপমা। বেশি কথার বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় কথা। এদের কবিতা, অতএব কাহিনিপ্রবণ নয়, কিন্তু উপস্থাপনার গুণে কোথাও কোথাও গল্পে স্বাদ থেকে যায়।
বিশ্বজুড়ে এখন যে কবিদেও বয়স ৫৮ থেকে ৬৭। এরকম ৬০/৭০ জন লেখকের কতিা পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। এরা সকলেই সরাসরি কথা বলার, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। লক্ষণীয়, সেই সোজাসাপ্টা কথার ভেতর আছে ইঙ্গিত, প্রতীকের আলোছায়া। আর এমন ভাষায়, এমন ভঙ্গিতে তারা কথা বলেন যে, আমরা মনোযোগী না হয়ে পারি না। কেরালার কবি বালচন্দন (১৯৫৬) তেমনই এক দৃষ্টিান্ত। ভাবাবেগ ও জীবনবাস্তবতার যৌক্তিকতার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকে তার কবিতা। তা না স্লোগান, না মন্ত্র। একই সঙ্গে স্পষ্ট ও রহস্যময়, সুগম ও সুষমাদীপ্ত এমন কবিতা শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতেই বিরল-‘সবচেয়ে তপ্ত হৃদয়? আমার মা/সবচেয়ে কভিন ব্যাকরণ? আমার বাবা/সবচেয়ে লবণাক্ত সমুদ্র? আমর স্ত্রী।/সবচেয়ে নিঃশব্দ কান্না? আমার বোন।/সবচেয়ে অনাথ জড়? আমার ভাই।/সবচেয়ে বিকৃত মুখ? তা আমারই।’ (অনুবাদ : দুর্গা দত্ত)
আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ইউরোপের কোনো দেশ থেকে এ মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় যে, কবিতা ফুটবল খেলার মতোই সহজ হয়ে উঠবে। এটা পড়ার পর রীতিমতো হতবাক হয়েছি। কেননা যেখানে কবিতার নন্দনতত্ত্ব নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে; সেখান থেকেই উঠলো এই কথা। অবশ্য এটাও ভেবেছি, আধুনিক ফুটবল আর সহজ নেই। নানা ধরনের কায়দা-কৌশল তাকে অনেকটাই কঠিন করে তুলেছে। অবশ্য একটা ব্যাপারে মিল আছে। ব্যক্তিগত নেপুণ্য একজন কৃতী ফুটবলারকে অনেকের থেকে আলাদা করে। নিজস্ব স্টাইল খুঁজে পাওয়া একজন প্রতিভাবান কবিও নিজেকে পৃথক করে নিতে পারেন।
বহুকাল আগেই কবিতা রাজদরবার থেকে সাধারণ মিলনায়তনে স্থান করে নিয়েছিল। এখন সে ওই হলরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তার মোড়ে কিংবা কারখানার গেটে। মনে পড়ছে, রবার্ট ব্লাই উত্থানের দিনগুলোয় আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের খোলা জায়গায় নিজের কবিতা পড়তেন ছাত্রদের উদ্দেশে। জীবনানন্দ দাশ এ যুগের মানুষ হলে এটা জেনে চমকে উঠতেন হয়তো। ক্যাম্পাসের খোলা স্থানে রেলস্টেশনে বা কারখানার গেটে কবিতা পড়ার কারণ তো একটাই। অনেক বেশি শ্রোতার কাছে পৌঁছানো। এখানে একটা জিনিস আমরা ভুলে যাই। রাজদরবারে কিংবা হলরুমে নির্বাচিত এলিট শ্রোতা-দর্শকদের সামনে কবিতাপাঠের যে রীতি চালু ছিল, সেটা কেন হয়েছে? হয়েছে এজন্য যে, কবিতার শ্রোতা বা পাঠক উন্নত রুচির অধিকারী সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আধুনিক কবিতা বুঝবার মতো শিল্পপ্রেমী মানুষদের জন্যই এই সাহিত্য। হ্যাঁ, জনসাধারণের মাঝখানে যাওয়া সাধ কবিতার হতেই পারে। সেই জনসাধারণ যারা প্রতীকের মূল্য কিংবা চিত্রকল্পের মর্যাদা বোঝে না। এ কালের কবিতা যতই সহজ হতে চাক না কেন তার ওই নিরলংকার সাদামাটা চেহারার পেছনে লুকিয়ে থাকে যেসব গূঢ় ভাব আর ইশারা-ইঙ্গিত, মামুলি পাঠক কিংবা শ্রোতা সেসবের অর্থ উদ্ধার করবে কী করে?
ধরে নেয়া যাক, দীক্ষিত-অদীক্ষিত নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষই কবিতার পাঠক। কবি যদি তার কাজে সত্যিকার দক্ষতা দেখাতে পারে, তাহলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকলেও পাঠক তার কাব্যেও রসাস্বাদন করতে পারবেন। একজন কবি যখন দেশবরেণ্য হয়ে ওঠেন তখন বুঝতে হবে, কেবল আঁতেল পাঠকরাই নয় বরং তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ওই অদীক্ষিত পাঠকদের ভালোবাসা তিনি অর্জন করেছেন।
এটা কীভাবে সম্ভব? কবিতার মতো সূক্ষ্ম শিল্প কীভাবে সাধারণ পাঠকদেরকে আনন্দ দিতে সক্ষম? সাদামাটা শব্দাবলি দিয়ে গড়ে তোলা এ যুগের নাতিসরল কবিতাসমূহে এমন এক মেজাজ, এমন আনন্দপ্রদ বাকভঙ্গি থাকে যদিও সবার বেলায় নয়, যে সেটাই হয়ে ওঠে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বক্তব্যবস্তুর অনন্যতা এখানে বিবেচ্য নয়। বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা গেলে কবিতার শিল্প ক্ষুণœ হতে পারে। আবার বিষয়বস্তু অস্পষ্ট হলেও কবিতা দরিদ্র হতে পারে যদি-না তাতে থাকে সঠিক পরিকল্পনা ও মনোহর বাকপ্রতিমা। নেরুদার কবিতায় বিষয়বস্তু প্রায়শই খুব স্পষ্ট; অথচ দেখুন তাঁর লেখা কতো চমৎকার। এটা সম্ভব হয়েছে তার অননুকরণীয় মজাদার ভাষার গুণেই। সহজ-সাবলীল, মজাপ্রদ বাক্যভাষার আরেকটা উদাহরণ দেবো অরুণ কোলাতকারের কবিতা থেকে। হিন্দি, মারাঠি ও ইংরেজির মিশেলে তৈরি এক মিশ্রভাষা প্রযুক্ত হয়ে অরুণের কাব্যে। সেখানে ঠেলাগাড়িওয়ালা বা সব্জিবিক্রেতার মতো অতি সাধারণ মানুষ যেন কথা বলে ওঠে। -‘আমার বুকটা মেপে দরজি বলবো/একত্রিশ ইঞ্চি মোটে একত্রিশ ইঞ্চি/ জুতোয় জোর করে পা ঢুকিয়ে দিয়ে মুচি বললো,/ব্যবহার করো, আর টাইট লাগবে না।’ এই কবিতাটিরই শেষ দিকে লেখক বলছেন- ‘বাড়াটা চেপে ধরে আমার ওয়াইফ বললো,/একদিন এটা কেটে ফেলবোই ঠিক কেটে ফেলবো।’(অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
এখন মানুষের দৈনন্দিন ব্যস্ততা আগের চেয়ে এত বেশি যে, সব ধরনের ‘প্রিন্টেড ম্যাটার’ পড়ার জন্য সে প্রতিদিন গড়ে কুড়ি থেকে পাঁচিশ মিনিট সময় পাচ্ছে। তার ওপর আছে টেলিভিশন, আছে ফেসবুকের হাতছানি। এইসব থেকে সময় বাঁচিয়ে একজন শিক্ষিত লোক যদি কবিতা পড়তেই চান, তাহলে কোন ধরনের কবিতা তিনি বেছে নেবেন? নিশ্চয়ই সে কবিতা তিনি চাইবেন যা একই সঙ্গে অনব্য ভাবুকতা ও ভাষাঘটিত বিনোদন জোগাতে পারে। সেই টেক্সট সরাসরি কথা বলছে নাকি আড়ালপ্রিয় সেটা তার প্রধান বিবেচ্য নয়। কিন্তু স্পষ্ট করে কথা বলার গুণ আছে আবার তা খানিকটা আলোচায়াও তুলে ধরে এক কথায় শিল্পসম্মত সুগমতা যেসব কবিতার মুখ্য চারিত্র, সেই দরনের রচনা খুব সুলভ নয়। তবে সেটাই আজ পৃথিবীর সকল ভাষার কবিদের কাম্য বলে মনে হয়।