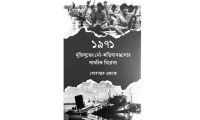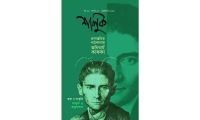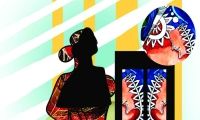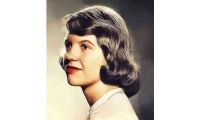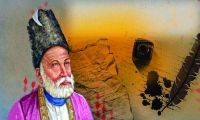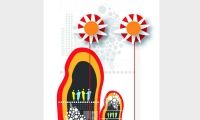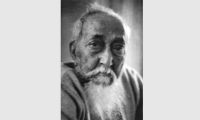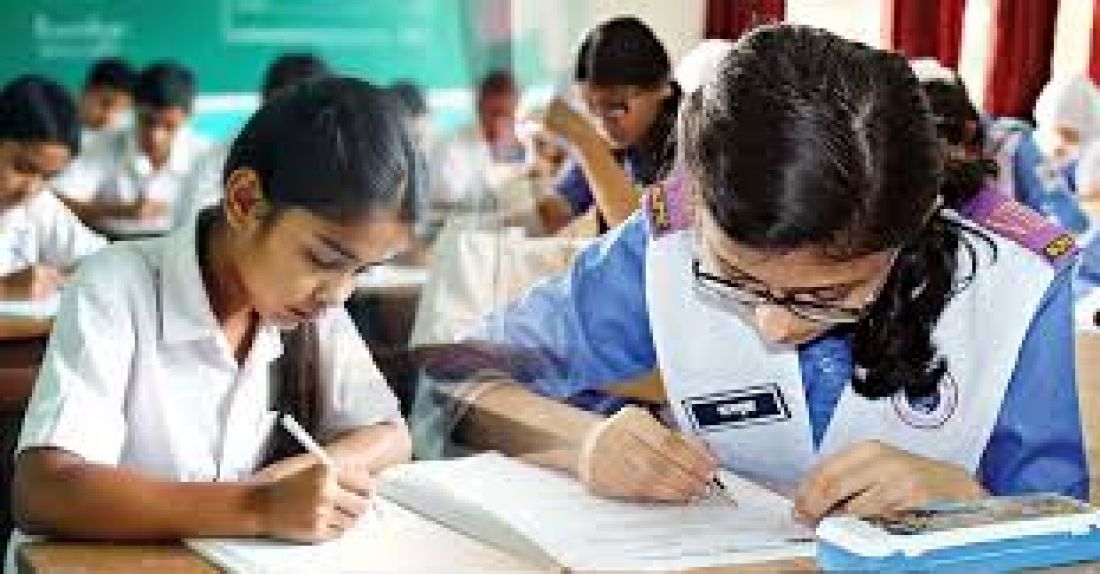??????? ?????
এক বিস্ময় প্রতিভা
গৌতম রায়
মানুষের জীবনে তার বোধকে পরিচালিত করবার ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিসরের মধ্যেই হোক বা পরিবারের বাইরে বৃহত্তর পরিসরের ভিতরেই হোক, একজন বা কয়েকজন মানুষের বিশেষ রকমের প্রভাব থাকে। জসীম উদ্দীনের ক্ষেত্রে সেই প্রভাব ছিল তাঁর অন্ধ দাদা দানুমোল্লার। সদ্য প্রয়াত সন্জীদা খাতুন তাঁর জসীম উদ্দীন মূল্যায়নে এই প্রেক্ষিতটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, খুব কমজসীম উদ্দীন গবেষকের কাছ থেকে এই ধরনের মূল্যায়ন আমরা পেয়েছি।
এই যে দানুমোল্লা,যাঁকে জসীম উদ্দীন উল্লেখ করেছিলেন, গ্রাম বাংলার কৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক হিসেবে, এমন ব্যক্তিত্বদের প্রতি সন্জীদা খাতুনের একটা স্বভাবজাত আকর্ষণ ছিল। সেই কারণেই তাঁর পিতার (মনীষী কাজী মোতাহার হোসেন) সূত্রে হারামণির ¯্রষ্টা মহম্মদ মনসুরুদ্দিনের সঙ্গে প্রথম জীবন থেকেই একটা সুন্দর যোগাযোগ ছিল সন্জীদার।
দানুমোল্লার জীবনে চিকিৎসা বিভ্রাটজনিত কারণে ছোটবেলায় চোখের দৃষ্টি হারানো,সেটি যে আক্ষরিক অর্থে কেবল চোখের দৃষ্টি হারানো,তা নয়। বৃহত্তর দুনিয়াকে চেনা-অচেনার এক সুনিপুণ সংযোগ থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দেওয়া- সেকথা সন্জীদার জসীম উদ্দীন মূল্যায়নের মধ্যে বারবার উঠে এসেছে।
এই মূল্যায়নের অভিনিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই, সন্জীদার সমাজবিজ্ঞানের প্রতি এক বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বাল্যকৈশোরে, তাঁকে একটা ভিন্ন ধারার চেতনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে শুরু করেছিল। সেই ক্ষেপণটি,তাঁর জীবনের বোধহয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষত ছিল। আর অক্ষত ছিল বলেই তিনি অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাইই বাঙালি সংস্কৃতির সম্যকবিকাশের মূলধারাটিকে, মূলসুর থেকে, বাঙালি সংস্কৃতির শিকড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে কখনো পারেন নি সন্জীদা।
এই জসীম উদ্দীনের প্রতি সন্জীদা খাতুনের অনবদ্য মূল্যায়ন ঘিরে আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের গান ঘিরে পরবর্তীকালে প্রায় কিংবদন্তি পর্যায়ে চলে যাওয়া সন্জীদা খাতুনের একদম কৈশোর কালে গানের দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে, পল্লীগীতির একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর বড় দিদিকে যিনি গান শেখাতে আসতেন, তিনি অনেক ধরনের পল্লীগীতি শেখাতেন। শিশু সন্জীদা সেগুলি খুব মনোযোগ সহকারে শুনতেন। একদিন বড় দিদির অনুপস্থিতিতে সেই শিক্ষকের কাছে সন্জীদা একটি ছোট্ট রাগ শিখেছিলেন। যেটির মধ্যেও লোকায়ত ধারার একটা বিশেষ সংযোগ ছিল।
তাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঘিরে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদির মধ্যেও জসীম উদ্দীনকে নিয়েতাঁর যে চিন্তা চেতনার দুনিয়ার প্রসারণ, সেটি কিন্তু তাঁর বহুমাত্রিক,বৌদ্ধিক অবস্থানের একটি বিশিষ্ট পরিচয়বাহী।
জসীম উদ্দীন তাঁর নিজের লেখায় দাদা দানুমল্লার কথা বললেও সেই মানুষটি নানান ধরনের কিসসা, শোলোক, গ্রাম্য গান আর তার সুর ঘিরে কি অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, বারবার তুলে এনে সন্জীদা তাঁর লেখায়। যেটাতিনি বারবার তুলে এনেছেন তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই যে,দানুমোল্লাকে নিয়ে সন্জীদার কলমের নিঃসরণে দানুমোল্লার একটা আবীল চরিত্রের প্রকাশ, এটা কিন্তু সাধারণ মামুলি কোনও বিষয় নয়।
একজন মানুষের চিন্তা চেতনার সামগ্রিক ধারা তৈরি হতে পারিপার্শ্বিকতার কি অনবদ্য ভূমিকা থাকে, সেটা জসীম উদ্দীনের জীবন ঘিরে,তাঁর দাদা দানুমোল্লার জীবনের যেএকটা বৈশিষ্ট্য, তার ভেতর দিয়ে বোঝানোর এই যে মুন্সিয়ানাটা, এটাই ছিল সন্জীদার সৃষ্টির ভুবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে মণি মুক্ত তুলে আনা,ঠিক যেভাবে জসীম উদ্দীনের সামগ্রিক বিকাশে তাঁর দাদার অবদানকে তুলে আনছেন সন্জীদা।ঠিক এভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নজরুল, মুজফফর আহমেদ, নিজের পিতা, মনীষীকাজী মোতাহার হোসেন কিংবা সমসাময়িক সাংস্কৃতিক জগতের নানা বৈশিষ্ট্য,তার ছোট ছোট উপাদানের ভেতর দিয়ে তুলে এনে দেখিয়েছেন, বিন্দু থেকে কিভাবে সিন্ধুর উৎপত্তি ঘটে।
এই যে দানুমোল্লার মতো মানুষ, আমাদের বাঙালি সমাজে একটা সময় প্রায় প্রতিটি গ্রামে এক একজন করেছিলেন, লোকায়ত জীবন উজ্জীপনের এই সমস্ত আকর ব্যক্তিত্বরা, বাঙালি সমাজকে কতখানি বৈচিত্র্যময়, পরমত সহিষ্ণু,পরধর্মসহিষ্ণু এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক বিমূর্ত চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছিল,তা বুঝতে বৌদ্ধিক চর্চার যে আবশ্যিকতা তা ওকিন্তু সন্জীদারচেতনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল।
এই দানুমোল্লা জীবনকে ঘিরে সেকালের গ্রাম বাংলার অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসারধরণারযে বিবরণ আমরা পাই,তা আমাদের বিজ্ঞান নির্ভর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি অনেক বেশি আকৃষ্ট করে।
দানুমোল্লারচোখের কোনো সমস্যা হয়েছিল। সেকালের ধারা অনুযায়ী এক গ্রামীণ কবিরাজের কাছে তাঁকে নিয়ে যায় তাঁর পরিবার। সেই কবিরাজ বিধান দিয়েছিলেন, তার দেওয়া ওষুধটি লঙ্কা বাটার সঙ্গে রোগীর চোখে দিতে হবে।
এভাবে প্রায় ৭-৮ দিন রোগীর চিকিৎসা চলে। রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনরা রোগী ভালো হয়ে উঠবে-এই প্রত্যাশায় দানবীয় চিকিৎসা পদ্ধতি চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রোগীর চোখের মনি গলে বেরিয়ে আসে এবং দানুমোল্লা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যান।
জসীম উদ্দীন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই দানু মোল্লা প্রসঙ্গে সঞ্জীতা লিখছেন; “শোনা যায় একটি ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়ে ওঠে। বোঝা যায়, দৃষ্টিহীন দানুমোল্লা যেসব গান বা কাহিনী কানে শুনতেন তাই অন্তরে ধারণ করে রাখতে পারতেন (শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সন্জীদা খাতুন, পৃ-১৯৬, কথাপ্রকাশ)।
পারিবারিক পরিম-লের মধ্যে জসীম উদ্দীন কীভাবে লোকায়ত ধারার নানা উপাদান পেয়েছিলেন সেই উত্তরাধিকারের কথা
সন্জীদাস্বপ্রশংসভাবে জসীম উদ্দীন মূল্যায়নে লিপিবদ্ধ করেছেন। লোকায়তধারার এই পারিবারিক উত্তরাধিকার, এখন ধীরে ধীরে বাঙালিসমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। বাঙালি সমাজের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির কনসেপশন, অন্য ধরনের সামাজিক আবর্তন-বিনোদনের নিত্যনতুন কৌশলের সমস্ত কিছু,কীভাবে মানুষের মননলোকের দুনিয়াটাকে একটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে, তা যে জসীম উদ্দীনের জীবন,বিশেষ করে শৈশবকাল-কৈশোর কাল, তাঁর বেড়ে ওঠা, এই প্রেক্ষিতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারি, তার দিশা যেন আমরা অনেকটা খুঁজে পাই সন্জীদার, জসিম উদ্দীন মূল্যায়নের ভেতরে।
পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির জীবনের এই সমস্ত পর্বগুলিকে সংগৃহীত করতে,সংযোজিত করতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যে অবদান রেখেছেন।সেই অবদানের ও ভিত্তিভূমি হল সেকালের পূর্ব বাংলা, আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই সুনন্দা শিকদারের ‘দয়াময়ীর কথা’ এই কালজয়ী আখ্যানের মধ্যে।
এই সময় এমন ধারার সৃষ্টিযে শিশু মনস্তত্ত্বে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝাতেসন্জীদা, তাঁর জসীম উদ্দীন মূল্যায়নে, জসীম উদ্দীনের অনেক মুখের কথা উদ্ধৃত করেছেন। ‘রুব্বানকেচ্ছা’, ‘মধুমালা’, ‘আবদুল বাদশা’-গুলো কীভাবে জসীম উদ্দীনের সৃষ্টির দিগন্তকে প্রসারিত করেছে,সেইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য কালজয়ী ধারা তৈরি করেছে, সে বিষয়ে সন্জীদার মূল্যায়নগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাতেঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় জসীম উদ্দীন নিজে লিখেছেন,কেচ্ছা বলবার কালে দাদা,অর্থাৎ, সেই দানুমোল্লা; “আঙুলে তুড়ি দিয়া,দুই হাত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া,কখনো কণ্ঠস্বর বিলম্বিত লয়ে টানিয়া, কখনও দ্রুতলয়েখাটো করিয়া,কখনো ধমকের সুরে, কখনওআবেগমিশ্রিত সুরে, কখনওজোরে জোরেদাপটের সঙ্গে,কখনওফিসফিস করিয়া মনে মনে কথা বলার মতো করিয়া কাহিনির বিষয়বস্তুটিকে শ্রোতাদের মধ্যে জীবন্ত করিয়া তুলিতেন” (জসীম উদ্দীনের স্মৃতিকথা, পং-৩৮, দে’জ সংস্করণ, কলকাতা) [বানান অপরিবর্তিত]।
মধুমালা গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৯৫১) জসীম উদ্দীন ভূমিকা অংশে লিখেছিলেন প্রথম সংস্করণে; ‘সকল গাছেসকল ফল ধরে না’।এই শব্দটির মধ্যে দিয়ে জসীম উদ্দীনের বাংলা ও বাঙালির মননশীলতার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে, শৈশব কৈশোরের যে অনবদ্য অবদান, তাকে সন্জীদা খাতুন যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন,তেমনটাস্বীকৃতি বহু বিশিষ্ট আলোচকই জসীম উদ্দীনকে ঘিরে দেননি।
এক্ষেত্রে বলতে হয়,খানিকটা নিজের পরিসরথেকে সরে এসে, জসীম উদ্দীনকেঘিরেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা ও বাঙালির প্রতি নিজের যে অকৃপণ ভালবাসা-সেটা এখানে উজার করে দিয়েছেনসন্জীদা খাতুন।
উনিশ শতকে বাংলার নাট্য ধরারপ্রসঙ্গে মৃদু সমালোচনাও সন্জীদাকরেছেন, এই নাট্যধারা বিদেশের অনুকরণে পরিচালিত হওয়ার দরুন। দেশজসংস্কৃতির অভাব বাংলা ও বাঙালির মন মানসিকতাকে যে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। তার আভাস খানিকটা এই আলোচনায় সন্জীদা দিয়েছেন। বাঙালির দেশীয় নাট্যধারাকে অগ্রাহ্য করা- এই বিষয়টি যে উনিশ শতকে বাংলা নাটকের ¯্রষ্টাদের মধ্যে ছিল, তাকে কোনো অবস্থাতেই তিনি সমর্থন করতে পারেন না। এ কথাটি খুব স্পষ্টভাবেই বলতে দ্বিধা করেননি সন্জীদা খাতুন। তিনি লিখছেন- ‘ওই যে কথকথার লক্ষণযুক্ত সুর আর বাণীর বিচিত্র ভঙ্গিতে নাট্য বর্ণনা, বাঙালির ঐতিহ্যমন্ডিত বৈশিষ্ট্য এইখানে(ঐ, পৃ-১৯৭)।
বাংলায় প্রসেরিয়ামথিয়েটারের যে গোরাপত্তন লিয়েবেদফকরেছিলেন, সেই ধারাটি দেষজ ভঙ্গিমার মধ্যে আত্মস্থ হওয়ার দিকটি বহু বহু পরে বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে।এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, মোহাম্মদজাকারিয়া,গঙ্গাপদ বসু,রামেন্দু মজুমদার,ফেরদৌসী মজুমদার,আসাদুজ্জামান নূর,রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শাঁওলী মিত্র প্রমুখকে।
প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে লোকায়তধারার সংযোগ ঘটানোর যে বিষয়টি জসীম উদ্দীনকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেছেন সন্জীদা, তার থেকে এ বিষয়টি খুব জোরে সঙ্গেই বলতে পারা যায় যে, সাহিত্য এবং সংগীতের দুনিয়ার এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বটি, নাট্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং আত্মস্থতার জায়গায় বহু প্রথম সারির নাট্যবিদের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না।
জসীম উদ্দীন লিখেছিলেন- ‘মেয়েলি গানে রাখালী গানে,ছেলে ভুলনো ছড়ায় কথোপকথনের ছলে’ (ঐ, পৃ-১৯৮)
বাংলা কথোকথায়, বাঙালি জীবনের কথোকথাতে এই যে আঙ্গিক টাকে অনুধাবন করেছিল বাঙালি সমাজ একটা সময়ে,তার মধ্যে দিয়েই যে বাঙালি জীবনের বারোমাস্যারএক অদ্ভুত অনুরণন তিনি (জসীম উদ্দীন)ফুটিয়ে তুলতেপেরেছিলেন- সেটা একজন রবীন্দ্র সাধিকার জীবনে সত্যিই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাঙালি জীবনের লুকোয়াতধারা ঘিরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রবীন্দ্রনাথ, নজরল, অন্নদাশঙ্কর রায়,মোহাম্মদমনসুরউদ্দিন, শামসুজ্জামান খানএবং সাম্প্রতিককালের আবুল আহসান চৌধুরী যেভাবে আলাপ আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, সেটা বাঙালি জীবনে বিশেষ ধরনের প্রাপ্তি।
বাঙালি জীবনে এমনপ্রাপ্তিবাঙালি সমাজে সাম্প্রতিক অতীতেএর আগে খুব একটা ঘটে নি। লোকায়ত বাংলা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সন্জীদা খাতুনের পিতা কাজী মোতাহার হোসেন,সঙ্গীতে বাঙালি মুসলমানের অবদান শীর্ষক যে আলোচনা করেছিলেন, সেটি সমকালে একাংশ ধর্মান্ধমানুষদের কাছে বহুসমালোচিত হলেও, বাংলা ও বাঙালির,বিশেষ করে,বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য অবদান।
সঙ্গীত ঘিরে মুসলমানের অবদান, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজের কাছে অজানা ছিল।এক্ষেত্রে বাঙালিকে মুসলমান সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ করে তোলার প্রথম দিশা দিয়েছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন।
একটা সময় পর্যন্ত বাঙালির কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল এইসব বিষয়গুলি। পরবর্তীকালে একটা সময় বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ঘিরে কিংবদন্তি তুল্য গবেষক আবুল হাসান চৌধুরী।কাজী মোতাহার হোসেনের রচনাবলীর পুনঃ সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ করে তাঁকে দিয়েছিলেন সন্জীদা খাতুন। এই কাজে তাঁর সহযোগিতার কথা অধ্যাপক চৌধুরী, সব সময়ে খুব সপ্রশংস ভাবে বলে থাকেন।
লোকায়ত ধরার প্রতি সন্জীদার যে আকর্ষণ ছিল,সেই আকর্ষণ প্রসারিত হয়েছিল রবীন্দ্র সৃষ্টির লোকায়তসঙ্গত ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ আদ্যপ্রান্ত ধ্রুপদী ঘরনার সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত ঘরানার সংস্কৃতির মেলবন্ধন রচনা করেছেন।এই মেল বন্ধনের ধারা রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারায় খুব একটা প্রচলিত ছিল না। এই যে ধ্রুপদীসংস্কৃতি ধারার সঙ্গে লোকায়ত ধারার সাংস্কৃতিক মিলনেরঅভিযাত্রার সংমিশ্রণ ঘটানো-রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য কৃতিত্ব ঘিরে সন্জীদা খাতুনের আগ্রহ, উৎসাহ এবং চর্চা ছিল অত্যন্ত নিবিড়।
যদিও এই চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর যে সোভিয়েত পন্থী রাজনৈতিক চেতনা এবং সেই চেতনার যাঁরা অংশীদার, তাঁদের প্রতি তাঁর ছিল একটা বিশেষ ধরনের পক্ষপতিত্ব। আর সেই পক্ষপাতিত্ব দেখাবার ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগতভাবে সোভিয়েতপন্থী হয়েও,যাঁরাসমস্ত ধরনের কমিউনিস্ট সংস্কৃতিগত সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন, তাঁদেরঘিরেও কখনো কখনো কিছু ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছিলেন।
জসীম উদ্দীন ঘিরে সন্জীদা খাতুনের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এক ধরনের অদ্ভুত নৈকট্য অনুভব করতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ঘিরে যে চিন্তা চেতনার প্রবাহমান ধারা, তার। রবীন্দ্র সাহিত্যের সৃষ্টি, তা গল্প, উপন্যাসইহোক, কবিতাই হোক- তার মধ্যে যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান ঘিরেএকটা অসামান্য ‘বস্তু রয়েছে, তার সঙ্গেমনের প্রাণের মিল অনুভব করতেন
সন্জীদা খাতুন। আর সেই মিল অনুভব করবার মধ্যে দিয়েই তিনি দেখিয়েছিলেন, জানালাগুলোকে কেটে দিলেই, একটা প্রশস্ত দরজা পথ অনুভূত হয়।যার মধ্যে দিয়েই সংস্কৃতি চিরন্তন ধারা-উপধারা এক অদ্ভুত ধরনের সংমিশ্রণ ঘটে।
এই সংস্থানের কথাইকিন্তু সন্জীদারচিন্তা চেতনার অন্যতম স্থাপক অন্নদাশঙ্কর রায়,তাঁর আত্মকথন মূলক আলেখ্য, ‘বিনুর বই’তেউল্লেখ করেছেন।
এদিক থেকে বলতে পারা যায়, অন্নদাশঙ্করের চিন্তা চেতনার এক অদ্ভুত ধরনের প্রবাহীনি ধারাসন্জীদাখাতুনের মধ্যে অনুভূত হতো। সেই অনুভূতির মধ্যে প্রবাহের যেমন সংমিশ্রণ ঘটতো। তেমনিইসমসাময়িক কালের আবর্তে নানা ধারা উপধারা এসে সংমিশ্রিত হতো। সংস্থানের মধ্যে কখনো কখনো কোনো কোনভাবে সেই সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়াশীল এবং মৌলবাদী ধ্যান ধারণাও যে সংমিশ্রিত হয়নি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারা যায় না।
সেই ধরনের চিন্তা চেতনার ধারার সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের মতো মুক্তবুদ্ধির মানুষের চিন্তা চেতনার কখনো কোনো রকম সংমিশ্রণ সাযুজ্যবা কোনো রকমেরসহানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়নি।
এমনকি সলজেনেৎসিন কে কেন্দ্র করে চিন্তা চেতনার প্রবাহ টিতেসোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির যে ভাবধারা, তার সঙ্গে হয়তো সন্জীদার পিতা, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঋত্ত্বিক কাজী মোতাহার হোসেনের মিল খুঁজে পাওয়া যেত না।যদিও এ সম্পর্কে কাজী মোতাহাল হোসেন কখনো প্রকাশ্যে কোনরকম অনুভূতির কথা জানেননি।
কিন্তু অন্নদাশঙ্করের মতো গান্ধীবাদী ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সমরেশ বসুর মত কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি দলের কোনো ধরনের নিগড়ে নিজেকে কোনোদিনের জন্য বাঁধেন নি। তেমন মানুষ,চিন্তা চেতনা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যে মুক্তবুদ্ধি জয়গান গেয়েছিলেন যে জয়গানের সঙ্গে গত শতকের বিশের দশকের মধ্যভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র করে মুসলিম সাহিত্য সমাজের যে আন্দোলন,শিখা গোষ্ঠীর যে আন্দোলন,তার অদ্ভুত ধরনের মিলছিল।
কিন্তু সেই ধরনের জায়গা ঘিরে সানজিদা খাতুনের কি অবস্থান ছিল সে সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মধ্যে একটা ধারা উপধারা আছে।সন্জীদা নিজে এ সম্পর্কে রেজিমেন্টেশনের বিষয়ে রণেশ দাশগুপ্ত কে উদ্ধৃত ও করেছেন।
এই বিতর্ককিন্তু সন্জীদা খাতুনের জীবনাবসনের পরও প্রশমিত হয়নি। কারণ এই সম্পর্কে সন্জীদা খাতুন, চিরদিনই একটা তাটর স্বভাব সুলভ কৌশলী অবস্থানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পরিচালিত করেছেন। যার জন্য কলিম শরাফিকে ঘিরেতাঁর বিরক্তি যেমন আমরা প্রকাশ্যে দেখেছি।সুপ্রিয়া কামাল ঘিরে তাঁর অমর্যাদাকর অবস্থান ওআমরা প্রকাশ্যে দেখেছি।ঠিক তেমনি সোভিয়েতপন্থী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদেররবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নজনিত অবস্থান ঘিরে তাঁর অবস্থান এবং চীনপন্থী কমিউনিস্ট,যারা বাংলাদেশে সেই সময় অবস্থান করেছিলেন বা পরবর্তীকালেও ছিলেন, তাঁদের যে চিন্তা চেতনা ধারা, সে সম্পর্কেসন্জীদা খাতুনের কি দৃষ্টিভঙ্গি-সে সম্পর্কে আমরা কার্যত অজ্ঞইথেকে গেলাম।
সুফিয়া কামাল,সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত,শহীদুল্লা কায়সার, আনিসুজ্জামান,শামসুর রাহমান, কবীরচৌধুরী, মুনীর চৌধুরী প্রমুখদের সার্বিক অবদান ছাড়া,অখ- বাঙালি জাতিসত্তা,অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনার বিকাশ যেমন অসম্ভব। ঠিক তেমনভাবেই সন্জীদাখাতুনকে ব্যতিরেকে অখ- বাঙালি জাতিসত্তার সার্বিক বিকাশ কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে পারা যায় না।
কিন্তু এখানে একটা যতিচিহ্ন থেকেই যায়। বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথের, অখ- বাঙালি জাতিসত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা,ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কখনোই এক এবং একমাত্র নাম সন্জীদাখাতুন নন। সন্জীদা খাতুন সমস্ত আত্মনিবেদিত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি চিন্তা চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী সমাজের এক অনন্য অনবদ্য প্রতিনিধি।যাঁর কাছে চিরদিন বাঙালি সমাজ, অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞ থেকে যাবে।