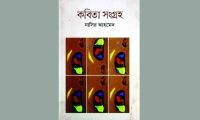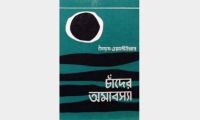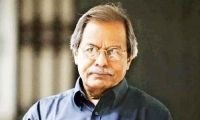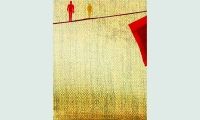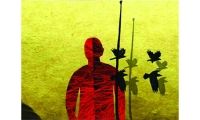নারী যখন পাঠক নারী যখন লেখক
রুমা আক্তার
একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করে। কিন্তু শিশুকাল থেকে নানাবিধ আরোপিত চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সন্তানকে শেখানো হয় নারী-পুরুষের প্রভেদ, তাই সমাজে নারীর পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে। ফলে নারী আবদ্ধ থাকে চিরাচরিত প্রথাগত নিয়মের আবরণে। যুগে যুগে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনার বলি নারী। পাশ্চাত্যের মেরি ওলেস্টোন ক্রাফট এবং প্রাচ্যের বেগম রোকেয়া পুরুষতান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে এসে নারী জাগরণের প্রচেষ্টা করেন। তাঁরা নারীকে আত্মসচেতন, মুক্তচিন্তার অধিকারী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, প্রজ্ঞা ও মননে শক্তিশালী হয়ে ওঠার আহ্বান জানান।
নারীবাদ বা ঋবসরহরংস শব্দটি ঋবসরহরহব ফরাসি শব্দ থেকে এসেছে এবং এর অর্থ নারী। নারী শব্দটির সাথে বাদ বা রংস প্রত্যয়যুক্ত করে ঋবসরহরংস। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই নারীবাদ। নারীবাদ সম্পর্কে জুডিথ অ্যাস্টেলারার মতবাদ স্মরণ করা যেতে পারে- “নারীবাদ হচ্ছে সমাজপরিবর্তন ও আন্দোলনের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা, যা নারী নিপীড়ন বন্ধ করা লক্ষ্যে চেষ্টা করে থাকে।” এ মতের সাথে ফ্রাইডেনের আলোচনায় আনা যেতে পারে- “যখন একজন মহিলা একজন পুরুষের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীন হবেন, পরিবার তখন তাঁর ওপর কোনো অত্যাচার করতে পারবে না।” নারীবাদী বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অবস্থান, তার পশ্চাৎপদতা এবং উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তার সফল উদাহরণ- বেগম রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, হেনরিক ইবসেনের, অ উড়ষষ’ং ঐড়ঁংব, সিমোন দ্যা বোভেয়ারেরঞযব ংবপড়হফ ংবী, ভার্জিনিয়া উলফের অ জড়ড়স ড়ভ ড়হব’ং ড়হি, হুমায়ন আজাদের নারী এবং তাসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম উল্লেখযোগ্য।
নারীবাদী ভাবনায় নারীরা প্রথাগত ছক ভেঙ্গে দেয়, নারীবাদী সমালোচকগণ দুইভাবে সমালোচনা করেন- প্রথমত নারী যখন পাঠক দ্বিতীয়ত নারী যখন লেখক। প্রথমত নারী যখন পাঠক তখন পুরুষরচিত সাহিত্যে পুরুষতান্ত্রিক একরোখা ভাব, লৈঙ্গিক রাজনীতি, সমাজ বাস্তবতা, নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা এ নানামাত্রিক অভিক্ষেপকে তাঁরা প্রশ্নবিদ্ধ করে। কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্যিকরা তাঁদের শিল্পকর্মে নারীকে তোলে ধরে কিংবা মূল্যায়ন করে তার রূপভেদ নারী পাঠকের কণ্ঠে ধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি (১৯০৪) উপন্যাসে নারীর অবস্থানকে নারীবাদী পাঠক উন্মোচন করেন। এ উপন্যাসে বিধবা নারী বিনোদিনী যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। তার ভিতরেও ঈর্ষা, প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনা বিদ্যমান। তার প্রমাণ মেলে- ‘ক্ষুধিত হৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ¦ালাময় মদের মত কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল, তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরে রক্ত জ¦লিয়া উঠিল।’ যুবতী বিধবা বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রক্তে-মাংসে গড়ে তুললেও তাকে শেষ পর্যন্ত সমাজ-সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে কাশিতে প্রেরণ করেন। নারীবাদী পাঠক এখানে প্রশ্ন করেন, কেনো তাকে কাশীতে পাঠনো হলো? বিহারী বাবুর সাথে কী তাকে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ করা যেত না? তার মানবীয় এবং জৈবিক প্রবৃত্তির সঠিক চর্চা কেনো করা হলো না? তাহলে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সবকিছুই কি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ফসল? এভাবেই একের পর এক প্রশ্ন করেন নারী সমালোচকবৃন্দ।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরবিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসটিতে বিধৃত বিধবা বিবাহের কুফল। ঈশ^রচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেখানে বিধবা বিবাহের পক্ষে আজন্ম লড়াই করেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিপক্ষে অবস্থান করেন। কুন্দনন্দিনী অনাথ বালিকা। গোবিন্দ্রপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথের সাথে কুন্দ দ্বিতীয়বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্মীয় সংস্কার থেকে বের হতে পারেননি। তাই বিধবা বিবাহের পাপ স্বরূপ তিনি কুন্দকে মৃত্যদ- দেন। কুন্দ যে মানবীয় প্রবৃত্তির দ¦ারা তাড়িত- ‘আমার সাধ মিটিল না, জীবন বড় সুন্দর, এমনকি বাঁচা না গেলেও।’
শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক (১৯৬৫) উপন্যাসে নারীর নিপীড়িত হওয়ার চিত্র স্পষ্ট। সমাজপতিদের দ¦ারা কীভাবে নি¤œবিত্ত শ্রেণির হুরমতিকে ব্যবহার করেন। এমনকি তার শাস্তিও হয় একপাক্ষিক স্বরূপ। হুরমতিকে জারজ সন্তান ধারণের জন্য কলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ ফেলু মিঞা, রমযান ও খতিব সাহেবের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ আমলের একটি কয়েন দিয়ে কপালে ছেঁকা দেয়। নারী যে যুগান্তরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার তার প্রমাণ এ উপন্যাসের পরতে পরতে পরিলক্ষিত। ‘চিমটের আগায় পোড়া পয়সাটা ধরে এক পা এগোয় কালু, ছ্যাঁৎ করে চেপে ধরে অনেকক্ষণ চেপে রাখে, মেয়েটির কপালের ঠিক মাঝখানে।’ নারীবাদী পাঠকগণ এখানেই প্রশ্ন করেন, সন্তান উৎপন্ন কী নারী একাই করে? পুরুষের কী কোনো ভূমিকা নেই? যদি থাকে তাহলে তার কেনো বিচার হলো না?
দ্বিতীয়ত নারী যখন লেখক তখন তিনি সমাজের নানা অসঙ্গতি, নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে যত আচার তা শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় তোলে ধরেন এবং নারীকে কীভাবে মুক্ত বুদ্ধির আলোকে সচেতন করে তোলা যায় তারই নান্দনিক প্রয়াস করেন। এ ভূখ-ের নারীবাদী সাহিত্যিক রোকেয়া খাতুন তাঁর স্ত্রীজাতির অবনতি (১৯০৮) গ্রন্থে তিনি স্ত্রীজাতির অবনতির পেছনে ত্রিমুখী কারণ চিহ্নিত করেন- পরিবার-সমাজ, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং নারীর সদিচ্ছা। একটি সমাজ তথা জাতির উন্নয়নে নারী-পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা। একই সাথে নারীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শক্তিকে সম্মান করা। তিনি নারীকে পুরুষতান্ত্রিক বর্বর সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। বেগম রোকেয়ার পাঠক সমাদৃত উপন্যাস সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫)। এ উপন্যাসে তিনি একটি নারীবাদী স্বপ্নরাজ্য গড়ে তোলেন, যেখানে নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকার যবনিকা পড়েছে। নারীরা সামাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজের প্রধান চালিকাশক্তি, পুরুষেরা সেখানে গৃহবন্দি। নারী পরিচালিত এ কল্পরাজ্যে কোনো অপরাধ নেই এবং সমাজের ধর্মই ভালোবাসা ও সত্যের। তাঁর অবরোধ-বাসিনী (১৯৩১) গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় নারীদের করুণ অবস্থাকে বাস্তবতার নিরিখে মূর্তায়ন করেন। বিশেষ করে মুসলিম নারীদের অবরোধ প্রথার জন্য যে বহুবিধ টানাপোড়েন সম্মুখীন হতে হয় তারই শৈল্পিক প্রয়াস এ গ্রন্থটি।
নারী সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলিত এবং এ শৃঙ্খলিত জীবনের নানামাত্রিক অভিজ্ঞতাকে যাপিত জীবনের সাথে টেনে তিনি এক মৌলিক অনুসন্ধান করেন। পর্দাপ্রথা, একরৈখিক সামাজিক বিধি-নিষেধ, লৈঙ্গিক রাজনীতি নারীকে করেছে গৃহবন্দি। পর্দার বিনাশ কিংবা ধর্মের নাশ এ উভয় প্রসঙ্গে নারীর নীরবতা- নারীকে করে অবরুদ্ধ। বহুকালের এ অভ্যস্ততা নারী অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। ফলে নারী তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন কিংবা পুরুষের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্ব বলে মেনে নেয়। দীর্ঘদিনের এ মেনে নেওয়া কিংবা মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম (১৯৯২) বইটিতে পুরুষসৃষ্ট ব্যাকরণের ব্যঙ্গ করেন। পুরুষের সমার্থক শব্দ- মনুষ্য, মানুষ, মহাপুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু নারীর সমার্থক শব্দ- রমণী, অবলা, জননী, বনিতা, পতœী, কামিনী। যার প্রত্যেকটি অর্থ অতি নগণ্য ও নিকৃষ্ট। ব্যাকরণের কোথাও নারীর সমার্থক শব্দ হিসেবে মানুষ ব্যবহৃত হয়নি। মানুষ হিসেবে নারীর মূল্যায়ন অকল্পনীয়, অপর, আকস্মিক কিংবা অপ্রয়োজনীয়।
ভার্জিনিয়া ওলফের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অ জড়ড়স ড়ভ ড়হব’ং ড়হি (১৯২৯), ঞযৎবব এঁরহবধং (১৯৩৮)। প্রথম বইতে তিনি নারীর সাহিত্যকর্মের সামাজিক ও ঐতিহাসিক সমালোচনা করেন। নারী কি তার কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারছে? কিংবা অতীত ও বর্তমানে নারী লেখকদের যে সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয় এমনি কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং তার নান্দনিক সমাধান বিধৃত এ বইটিতে। বইটির পরতে পরতে লক্ষণীয়- নারী স্বাধীনতার নিহিতার্থ। দ্বিতীয় বইটিতে বিধৃত কীভাবে বিভিন্ন জীবিকা পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি মূলত জীবনের নানাক্ষেত্রে নারীর নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার শৈল্পিক প্রয়াস করেন। নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা মেরি ওলেস্টোন ক্রাফট তাঁর ‘ভিন্ডেকেশন অব দ্য রাইটস অফ ওম্যান’ গ্রন্থে মহাপুরুষদের ও প্রশ্নবিদ্ধ করেন, সমান্তরালে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নারীকে মুক্তচিন্তার অধিকারী করার প্রচেষ্টা করেন। সিমোন দ্য বোভেয়ার তাঁর ঞযব ঝবপড়হফ ংবী (১৯৪৯) এ বইটিতে লৈঙ্গিক রাজনীতির নগ্নরূপকে উন্মোচন করেন। কেউ নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং সমাজ তাকে গড়ে তোলে নারী হিসেবে। একটি শিশু জন্মের পরে শুরু হয় লৈঙ্গিক রাজনীতি। পরিবার এবং সমাজ তাকে দ্বিতীয় লিঙ্গ বলে পরিচিত করে। শুধু তাই নয়, পুরুষ যদি সুন্দর বলে তবেই নারী সুন্দর। এর সফল উদাহরণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসী কবিতা- ‘শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী-/ পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/ পুরুষ নারীকে গড়ে তোলে চিরন্তন ‘অপর’ কিংবা ‘কর্ম’ হিসেবে কখনো তাকে কর্তা হয়ে উঠতে দেয়নি। তাই নারী তাদের কাছে প্রকৃতি, রহস্যময়ী, অ-মানুষ। মানুষ হিসেবে তার মূল্য অমূর্ত ধারণার প্রতিরূপ। এরূপ নানামাত্রিক প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত, মূর্ত কিংবা বিমূর্ত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার প্রতিফলন তাঁর এ বইটিতে সুস্পষ্ট। নারী লেখকদের গ্রন্থে এ ব্রাকেটবন্দি জীবন থেকে বের হয়ে আসার এক মানবীয় ও মৌলিক অভিঘাত লক্ষণীয়। কারণ নারী যতদিন নারী হয়ে থাকবে ততোদিন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। নিজেকে গুটিয়ে রাখা নয়, বরং আত্মশক্তিকে বলীয়ান হয়ে সকল সঙ্কোচ হেলায় তুচ্ছ করে নিজেকে বিকাশ করাই নারীর কর্ম এবং ধর্ম।
নারী সত্তার চিন্তা ও বিকাশে নারীর মৌলিক অবস্থান, সময়, সংস্কার, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির কাঠামো বিবর্তনশীল। তবে নারী লেখক হিসেবে পাঠক হিসেবে কিংবা ফিকশনের চরিত্র হিসেবে যে দ্বৈরথ তৈরি করে সেটাকে অগ্রগণ্য ও মৌলিক সত্তার দাবি করা যেতে পারে।