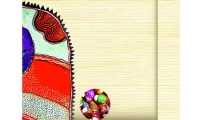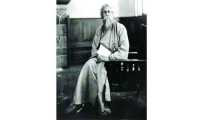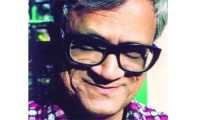টি এস এলিয়টের সংস্কৃতি চিন্তার অভিমুখ
শরীফ আতিক-উজ-জামান
টিএস এলিঅট / ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮; মৃত্যু : ৪ জানুয়ারি ১৯৬৫
সৃজনশীল সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে টি এস এলিয়টের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির পাশাপাশি মননশীল লেখক হিসেবে তাঁর পরিচিতি স্বল্পই বলা চলে। The Waste Land-এর অগণিত পাঠকের ক’জন তাঁকে Notes Towards The Definition of Culture-এর জন্য মনে করেন? পাঠকের চৈতন্যে এই বইটির কতটুকু প্রভাব রয়েছে? তবে স্বীকার করতেই হয় যে, এ গ্রন্থে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা উসকে দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে রচিত এই বইয়ের প্রসঙ্গসমূহ অনেক পাঠকের কাছেই অসহনীয় ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। আবার কেউ কেউ সহমতও পোষণ করতে পারেন। সংক্ষিপ্ত বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা একশোর কাছাকাছি। ৬টি অধ্যায়ে তিনি সংস্কৃতি ও তার অনুষঙ্গ নিয়ে নিজস্ব চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন।
The Three Sense of Culture এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ যেখানে তিনি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমগ্র সমাজের সংস্কৃতির আদল কেমন হতে পারে তা নিয়েমত প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তির সংস্কৃতি বলতে তিনি তার নিজস্ব চর্চা ও বুদ্ধির বিকাশকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তির জ্ঞান, শিল্প সম্পর্কে ধারণা, আচার-আচরণ ইত্যাদির মতো সাংস্কৃতিক উপাদান সম্পর্কে বোধগম্যতা তৈরির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব প্রচেষ্টা জড়িত। পক্ষান্তরে গোষ্ঠীর সংস্কৃতি শ্রেণি বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ ও অর্জনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিক্ষিত অভিজাত ও নির্দিষ্ট পেশাজীবীর সংস্কৃতি অন্যদের সংস্কৃতি থেকে আলাদা। আর একটি সমাজের সংস্কৃতি সবচেয়ে জটিল, কারণ তা একটি সামগ্রিক জীবনধারার প্রতিনিধিত্ব করে। সামাজিক মূল্যবোধ, শিল্পচেতনা, ধর্মীয় অনুভূতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক চর্চা এর অন্তর্ভুক্ত। এলিয়ট মনে করতেন যে একটি সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়ের বিকাশের জন্য অপরিহার্য।
The Class and the Elite প্রবন্ধে তিনি শ্রেণি ও অভিজাত গোষ্ঠীর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। Class বলতে এলিয়ট সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন যারা পরিবার ও স্থানের সাথে গভীর সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তারা সংস্কৃতির প্রবহমানতা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে যত্নবান। অন্যদিকে Elite বা অভিজাতরা হলেন ছোট দল বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যারা সমালোচনার মধ্য দিয়েসংস্কৃতির নানা অবয়ব দান করেন এবং সামনের দিকে চালিত করেন। শ্রেণিভুক্ত মানুষ সংস্কৃতির রক্ষণশীল জিম্মাদার হিসেবে কাজ করে আর অভিজাত শ্রেণি হলো সেই সংস্কৃতির সচেতন সমালোচক ও নবরূপ দানকারী যাদের একটি বিশেষায়িত সংস্কৃতি নির্মাণের সক্ষমতা রয়েছে। পূর্বপুরুষ ও সামাজিক অবস্থান দ্বারা শ্রেণি সংজ্ঞায়িত হয়। আর অভিজাতরা বিশেষায়িত জ্ঞান ও কৃতিত্ব দ্বারা চিহ্নিত হন। এলিয়টের ধারণা, শ্রেণি ও অভিজাত গোষ্ঠী দুটোই সমাজের জন্য প্রয়োজন। শ্রেণি সাংস্কৃতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখে আর অভিজাতরা তাকে পুনঃনির্মাণ করে ও অভিযোজনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করে।
তৃতীয় অধ্যায় Unity and Diversity: The Region-এ তিনি সংস্কৃতিকে ভৌগোলিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং একটি উন্নত সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রবহমানতার জন্য স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্থায়িত্বের অপরিহার্যতা অনুসন্ধান করেছেন। এলিয়টের যুক্তি হলো, একটি সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সংহতি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন। সংস্কৃতির জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের গুরুত্ব রয়েছে, কারণ তা সামাজিক শ্রেণির স্থায়িত্ব ও সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ঐতিহ্যের বিকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রবাহকে সচল রাখে। তাঁর মতে, স্থানীয় সংস্কৃতি তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও চর্চার মাধ্যমে একটি অতি প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মাণ করে।
চতুর্থ অধ্যায় Unity and Diversity: Sect and Cult-এ তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে ধর্মীয় সম্প্রদায় সংস্কৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে, আবার ভেঙেচুরে তার সর্বনাশও ঘটাতে পারে। অত্যাধিক বিভাজন সংস্কৃতির ধ্বংস ডেকে আনে। তিনি মনে করতেন, ইংল্যান্ডে একটি বিশাল খ্রিস্টীয়সংস্কৃতির মাঝে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ?সুনিয়ন্ত্রিত বৈচিত্র্য একটি গতিশীল উদ্দীপনা তৈরির মাধ্যমে অতিমাত্রায় সৃজনশীল হতে পারে। এলিয়ট গুরুত্ব দিয়েছেন কীভাবে প্রধান ধর্মীয়কাঠামো অতীতের সাংস্কৃতিক অর্জনগুলোকে বেশিমাত্রায় সংরক্ষণ করে এবং মূল ধর্মের ওপর নির্ভরশীল উপধারাগুলো আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপধারাগুলোর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। একটি ঐক্যবদ্ধ খ্রিস্টধর্মকে একটি সমগ্র সংস্কৃতির জন্য হিতকর বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি একটি সমাজের সামগ্রিক সুসংহত নির্মাণ, যা তার ধর্ম ও সামাজিক কাঠামোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা কেনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সরকারি নীতি দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়।
সংস্কৃতিকে একটি সর্বজনীন কল্যাণকর বিষয় হিসেবে তিনি দেখতে রাজি ছিলেন না এবং সাধারণভাবে সভ্যতার অগ্রগতি অনেক সময় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
A Notes on Culture and Politics I Notes on Education and Culture এই বইয়ের শেষ দুটি অধ্যায়। মূলত এলিয়ট সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছিলেন যা যুদ্ধের পর থেকেই অপব্যবহৃত হয়েআসছে। সভ্যতাকে একটি আবেগগত উদ্দীপনার উৎস হিসেবে ভেবে ভুল করা হয় বলে তাঁর ধারণা। তিনি মূলত যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতির সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে নিশানা করে এ কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি জনসাধারণের জন্য অবাধে বিতরণযোগ্য কোনো বিষয় নয়। সংস্কৃতি সমাজ থেকে পৃথক কোনো সত্তাও নয়। সংস্কৃতির মহৎ অনুষঙ্গগুলো সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভূত। সংস্কৃতির প্রাথমিক শিক্ষা আসে পরিবার থেকে, তারজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও প্রয়োজনীয়, তবে অপর্যাপ্ত এক বাহন। এলিয়ট আধুনিক সংস্কৃতিতে ধর্মীয়প্রভাবের ঘাটতি মেনে নিতে পারতেন না। শিক্ষার সমান সুযোগের বিষয়টি একটি ভ্রান্ত ধারণা বলে তিনি মনে করতেন। তিনি সর্বজনীন শিক্ষা প্রদানের বিপদ দেখেন, কারণ তা শিক্ষার মান নষ্ট করে এবং শিক্ষাকে সুলভ করে তুলতে পারে। শিক্ষা তাঁর মতে, ব্যক্তিগত, পেশাগত ও সামাজিক দিকগুলোর আন্তঃসম্পর্কের ওপর জোর দেয়। তিনি ধ্রুপদী শিক্ষাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।
এ থেকে বোঝা যায়এলিয়ট সংস্কৃতিকে কীভাবে দেখতে ও সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। যখন তিনি যুক্তি দেখান যে, একটি উচ্চমানের সংস্কৃতির জন্য শ্রেণিবিভক্ত সমাজ প্রয়োজনীয়এবং একইসাথে সাম্যের ধারণাকে অবজ্ঞা করেন তখন তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ঢাকা থাকেনা। আধুনিক সমাজের অবক্ষয়কে তিনি অভিজাত শ্রেণি কাঠামোর পতনের সাথে যুক্ত করেন। তাঁর মতে শ্রেণিহীন সমাজ তখনই সম্ভব যখন সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রতি সমর্থন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রক্ষণশীল ভূমিকার পক্ষে ওকালতি, সাংস্কৃতিক মান বজায় রাখার প্রশ্নে একটি সুসভ্য সমাজের শ্রেণি বিভাজনের ওপর নির্ভরশীলতা, সংস্কৃতিকে সর্বজনীন অধিকার হিসেবে বিবেচনা না করা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। যতই বলা হোক না কেন যে, তাঁর রচনা তাঁর সময়ের মৌলিক সমালোচনা, তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তিনি সংস্কৃতিকে ধর্মের সাথে যুক্ত করেন, কারণ তাঁর মতে তাদের শিকড় এক। গ্রীক, রোম বা ইজরায়েল থেকে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হলো ঐতিহ্য ও অনড় সাংস্কৃতিক ভিত্তির অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করা। তিনি সংস্কৃতির মানের অবক্ষয় ও মানবিক কর্মকা-ের অবনতি প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একটি সময়আসবে যখন সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এই হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়েরাখার পক্ষে মত দেয়, যা একটি প্রতিক্রিয়াশীল আকাক্সক্ষা। যখন ম্যাথ্যু আর্নল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে সংস্কৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করেন যে, সংস্কৃতি ধর্মের চেয়েও ব্যাপক কিছু তখন এলিয়টের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য মনে হয়এবং এটাই তিনি আর্নল্ডের মতামতের মৌলিক দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেন। অন্যের কাছে প্রথমে নিজের সংস্কৃতি ও পরে ধর্মকে উপস্থাপন করাকে তিনি মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। এলিয়ট যতই বলেন, সংস্কৃতি যেমন ধর্মজাত, ধর্মও সংস্কৃতিজাত, কিন্তু মূল্যায়নের সময় ধর্মকে প্রথমে ও সংস্কৃতিকে পরে বিবেচনা করতে বলেছেন। সংস্কৃতি তাঁর কাছে ধর্মেরপ্রতিরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো এমন একটি বিষয় যার প্রতি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা স্থির করতে পারি না, এবং শিল্প সম্ভবত একটি উপজাত পণ্য যার জন্য আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো অবস্থা তৈরি করতে পারি না।’ মজার ব্যাপার হলো, তিনি ঐতিহ্য সংরক্ষণের কথা বলেন, আবার বিলুপ্তপ্রায় কোনো সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার চান না।
যৌনতাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি, যৌনতা ও ধর্ম- এই তিন বৈশিষ্ট্য মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এই ৩টি বিষয়কে তাঁর অবিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে। আধুনিক সমাজের অসুস্থতা হলো এই তিনটি আবেগের বিচ্ছিন্নতা। সমসাময়িক পশ্চিমা সমাজের অধোগতির জন্য তিনি এই তিনটি বিষয়ের সংহতরূপে কাজ করতে না পারার ব্যর্থতাকে দায়ী করেন।
রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো, সাম্যবাদ, নাৎসিবাদ, উদারনীতিবাদ ও সা¤্রাজ্যবাদের মতো সকল মতবাদ একটি সুস্থ সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ। রাজনীতিতে সংস্কৃতির অপব্যবহার সম্পর্কে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংস্কৃতিকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন। উন্নত দেশগুলো সাংস্কৃতিক চেতনা দিয়েরাজনৈতিক প্রতারণা করায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাজনীতির জন্য রাজনীতি তাঁর পছন্দ নয়, বরং মানবজীবনের সাথে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েতিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন।
এলিয়টের ভাবনার মধ্যে কিছু যুক্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কথা বিভ্রান্তিকর মনে হয়। যেমন, সংস্কৃতির বিকাশে তিনি উদারবাদকেও অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়মনে করেন, কারণ তার মতে উদারবাদ ঐতিহ্যকেন্দ্রিক সামাজিক চর্চাগুলো ধ্বংস করে সংস্কৃতির একটি নেতিবাচক ধারণা তুলে করে। উদারনীতি এই সমাজে মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রগুলোর নামমাত্র সুরক্ষা দিয়ে থাকে, যা একসময় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। খ্রিস্ট আদর্শের মাঝে তিনি এর সমাধান খুঁজে পান। তবে এটাও স্বীকার করেন যে সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে খ্রিস্ট ধর্মমুখি করা জরুরি হলেও তা খুবই কঠিন। তিনি নিজেকে যখন রাজনীতিতে রাজতন্ত্রী, সাহিত্যে ধ্রুপদীবিদ্যার অনুরাগী ও ধর্ম বিশ্বাসে অ্যাংলো-ক্যাথোলিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন তাঁর চৈতন্যের আদলটি আরো পরিষ্কার হয়ে। তিনি বিশ্বাস করেন ধর্ম মানুষের জীবনকে আরো অর্থবহ ও জীবনযাপনের যোগ্য করে তোলে। ধর্মের আশ্রয় না নিয়েসমাজে কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বব্যাপী ধর্মযোদ্ধাদের বিষাক্ত দাঁত ও নখর দেখে দেখে এ কথার সাথে সহমত পোষণ করতে কুণ্ঠা হয় বৈকি। ধর্মই মানুষকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে। তাই সংহত জীবনের জন্য অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিনির্মাণ অতি জরুরি।
মূলত এই গ্রন্থে সংস্কৃতিকে একটি সজীব, সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক বিশ্বাস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরি করা যায়না, বরং পরিবার, ধর্ম, সামাজিক শ্রেণি এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সময়ের সাথে সাথে প্রজন্ম পরম্পরায় বিকশিত হয়। এলিয়ট বিশ্বাস করেন, সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম, যা একটি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। একটি সুস্থ সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজন বৈচিত্র্য ও ঐক্য, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। তবে একথা অতি সত্য যে, Notes Towards the Definition of Culture পড়বার পর কেউ কেউ স্বস্তি বোধ করতে পারেন আবার কেউ কেউ বিচ্ছিন্নতাবোধ ও পাল্টা যুক্তির মাঝে নিজেদের অবস্থান খুঁজে পেতে পারেন। তবু একথা বলতেই হয় যে এই রচনায় তিনি আমাদের সময়ের গভীর সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলোকে ব্যক্তি ও সমাজ, রূপরীতি ও বিষয়বস্তু এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রথার মাঝে দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখেছেন। এ গ্রন্থে অনেক কিছুই আছে যার সাথে দ্বিমত করার যথেষ্ট কারণ আছে। টিএস এলিয়ট আধুনিক সমাজের অসুস্থতা, ধর্মীয় বিশ্বাসহীনতা, সংস্কৃতির অশ্লীলতা, সুস্থচিন্তার অক্ষমতা ও বৈষম্যহীন আচরণের অনুপস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক বিশ্বের অস্পষ্টতার মাঝে যারা নানাবিধ দ্বিধাগ্রস্ততার সম্মুখীন হন, তারা সমসাময়িক সমাজের জরাগ্রস্ততার সমাধান দেখাতে পারেন।
-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার
-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন
-

কেন তিনি লালনকন্যা
-

আধুনিক বাংলা কবিতার একশ’ বছর
-

নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক বলয় অতিক্রমের ক্ষমতা
-

কেরাসিন বাত্তি ও লালচুলা মেয়েটি
-

তাঁর সমকালীনদের চোখে
-

নিজের মতো করেই সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে