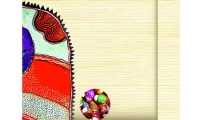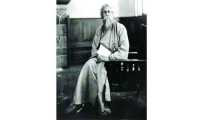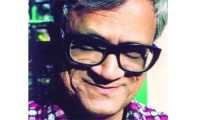ফরিদা পারভীন
কেন তিনি লালনকন্যা
গৌতম রায়
ফরিদা পারভীন / জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪; মৃত্যু : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি
কিংবদন্তি শিল্পী সদ্যপ্রয়াত ফরিদা পারভীনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আজ থেকে ৪০ বছর আগে লোকসংস্কৃতির কিংবদন্তী গবেষক অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর মাধ্যমে। ফরিদা পারভীন তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কণ্ঠে লালনকে নিবেদন করেন। আর আবুল আহসান চৌধুরী লালনকে ঘিরে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় তাঁকে আমাদের আরো নিকটজন করে দেন।
ফকির মকসেদ আলী শাহ, ছিলেন একজন আত্মনিবেদিত মহাত্মা লালনের গানের ভা-ারী। ফরিদা ছিলেন তাঁরই মুরিদ।স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির অল্প কিছুকাল পরে, ’৭২ সালে, গুরু মকসেদ আলী ফরিদাকে লালনের গান শেখার কথা প্রথম বলেন।তখন কিন্তু মহাত্মা লালন ঘিরে ফরিদার তেমন কোনও ধারণাই নেই।শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যেভাবে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে একটা উন্নাসিক ধারণা নিয়ে চলে, ফরিদার সেই বয়সে এই ধরনের গান সস্পর্কে ধারণাটা তার থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না।
তাই গুরু যখন লালনের গান ঘিরে তাঁকে প্রথম বলেন, কিশোরী ফরিদা একটু আলগা উত্তরই দিয়েছিলেন। কিন্তু ফরিদার গুরু মকসেদ আলী শাহ শেখালেন:‘সত্য বল, সুপথে চল, ওরে আমার মন।’
গানটা ছেঁউরেতে দোল উৎসবে গাইলেন ফরিদা।একটা গানের নিবেদনের মধ্যে একজন মানুষের কীভাবে রূপান্তর ঘটতে পারে তা একদিন লালনের গানকে, ‘ফকির ফাকরার গান’ বলে অবজ্ঞা করা মেয়েটির লালনের গানের স¤্রাজ্ঞীর মুকুট মাথায় নিয়ে ভবনাট্য মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়।
মহাত্মা লালনের আখড়ায় জীবন কাটানো করীম শাহ বা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র দুনিয়ার বিখ্যাত শিল্পী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভিন্টু, যাঁরা লালন তরিকার সঙ্গে নিজেদের জীবনকে আত্মমগ্ন করে দিয়েছেন, তাঁদের নিবেদনের ধারার সঙ্গে ফরিদার নিবেদন কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।ফরিদা লালন তরিকার দীক্ষিত মুরিদ ছিলেন না।কিন্তু মহাত্মা লালনকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘গোরা’ উপন্যাসের শুরু; ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’-র উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বা লালনের গানের খাতা ঘিরে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে অন্নদাশঙ্কর কিংবা একাধারে লালনের জীবন এবং সৃষ্টির বিশুদ্ধতা আর তত্ত্বের গভীরতার আখ্যান নির্মাণ করে আবুল আহসান চৌধুরীরা যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন, লালন পরিবেশনে ফরিদার আত্মমগ্নতার ভূমিকা তার থেকে কোনও অংশে কম নয়।
লালন তো কখনো এই মানুষে সেই মানুষের সন্ধানকে তাঁর নিজস্ব তরিকার মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখবার কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির গুরু পরম্পরায় যে ভাব এবং মূর্ছনা তাকেও তো তিনি অস্বীকার করেননি। কারণ, পরম্পরাগতভাবে নিজের সৃষ্টির ধারাবাহিকতা ঘিরে কখনো এতটুকু নিষেধাজ্ঞাও লালন বা তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের ছিল না।
কীর্তনের যেমন কোনও স্বরলিপি হয় না, ঠিক তেমনই বাউল-ফকিরদের গানেরও বিধিবদ্ধ স্বরলিপি হয় না।এটা গুরু পরম্পরাগত বিদ্যা। সেই বিদ্যার প্রসার লালন নিজে তাঁর মুরিদদের মধ্যে সঞ্চারিত করে গেছেন।প্রথাগতভাবে বেশরা তরিকায় দীক্ষিত না হয়েও গুরু পরম্পরাগতভাবে এই শিক্ষার ধারাকে হৃদয়ে ধারণ করে ফরিদা, লালনের মানুষ রতনের সন্ধানের খোঁজের আকাক্সক্ষাকে বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রবাহিত করে গেছেন সারাজীবন ধরে।ফরিদা ছিলেন পবিত্র ইসলামের রীতিনীতির একজন গভীর অনুরাগী, অনুসারী। রেওয়াজউদ্দিন আহমদের মতো লোক ১৩০৫ বঙ্গাব্দে বা তার পরে আরো অনেকে বাউল বিধ্বংসী ফতোয়া জারি করেছিল। সে সব ঘিরে এতটুকু বিচলিত নন লালন কন্যা ফরিদা।তাঁর কাছে পবিত্র ইসলামের ঔদার্য আর বেশরা লালনের ভাব ও বাণীর মধ্য কখনো এতটুকু সংশয় জাগেনি। দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়নি।ধন্ধও লাগেনি।
লালনের গান মূলত সাধন সঙ্গীত।প্রচলিত ধারায় দীক্ষা না নিলে সাধন হবে না- একথা নিজের দীর্ঘ জীবনে মহাত্মা লালন একবারও বলেননি।সংসারে থেকে, সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সাধন- মরমীয়া সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার এই ধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, যে সন্ন্যাসী সে তো সাধনা করবেই- এতে তো কোনও অভিনবত্ব নেই।কিন্তু সংসারে থেকে যে সংসার সামলে মনটা সাধনায় নিয়োজিত রাখতে পারে- সেও কোনও অংশে কম বড় সাধক নন।
এই ধারাতেই ফরিদা পারভীন ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লালন তরিকার সাধক।শততালির খিলকার বাহ্যিক আবরণ ফরিদার দরকার হয়নি তাই কখনোঅন্তরে যে সমন্বয়ী সাধনার মর্মবাণী, মানুষ রতনের সন্ধানের বেড়াকুড়াকে তিনি তাঁর জীবনের প্রধান উপলক্ষ করে তুলেছিলেন- সেই সাধনার ধারাতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম প্রধান লালন দুহিতা।
বিভিন্ন ধারা উপধারার লোকসঙ্গীত, বাউলাঙ্গের গান, ফকিরি- মারফতি গান- এসবের পরিবেশনার সঙ্গে লালন পরিবেশনের কিছু ফারাক আছে।লালনের জনপ্রিয়তার তালে তালে তাঁর পরম্পরাগত সুরে সাম্পানে বাণিজ্যিকীকরণের ঝোঁক বৃদ্ধি পেয়েছে।সাধনার ধারাকে বাণিজ্যিক ধারায় রূপান্তরিত করবার প্রবণতাও বেড়েছে।করিম শাহের গায়ন ধারা আমরা যারা ছেঁউড়িয়াত বসে শুনবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁদেরই আবার কলকতার মধুসূদন মঞ্চের সামনে তাঁরই কন্ঠে ‘জাত গেলো, জাত গেলো বলে’ শুনতে একটু অন্যরকম লেগেছে। সেই করিম শাহই আবার যখন কলেজ স্ট্রিট এলাকার সূর্য সেন স্ট্রিটের মিনি হোটেলে গানের সাধনায় আত্মমগ্ন হচ্ছেন- তখন তিনি এক অন্য মানুষ। এই আত্মমগ্নতাই ছিল লালন কন্যার শিল্পী সত্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুচিত্রা মিত্র যেমন তাঁর অনন্য সাধারণ গায়নভঙ্গী আর উচ্চারণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে গোটা বিশ্বের সামনে একটার পর একটা স্লাইডের মতো করে উন্মোচিত করেছিলেন, লালনের গানকেও ফরিদা তাঁর অনন্য সাধারণ উচ্চারণ এবং দ্যোতনার মাধ্যমে পরতের পর পরত উন্মোচিত করেছেন। বহিরাঙ্গে বাউল না হয়েও অন্তরঙ্গে বাওরা হয়ে, দুনিয়ার লোক সব বাওরা হো কর- ঘর ঘর বাঘিনী পালে- বাউল-ফকিরি-মারফতী গান ঘিরে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত এই প্রাচীন ধারণাকে সত্যিই ‘বাঘিনী’র মতো গোটা জীবন ধরে বহন করে গেছেন ফরিদা আপা।
গানে গ্রেস নোটের ব্যবহার, গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।রবীন্দ্রনাথের গানে এই গ্রেস নোটের ব্যবহার একমাত্র সফলভাবে করেছেন শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র এবং কলিম শরাফী। লালনের গানে এমনই এক সফল গ্রেস নোটেরপ্রয়োগকর্তী ফরিদা।তাঁর নিবেদনে মহাত্মা লালনের প্রতিটি কথাকে ছুঁতে পারা যায়।এই স্পর্শানুভূতি লালনের গানে কজন পেরেছেন- সেটা বিতর্কের বিষয়।আর কেউ পারুন বা না পারুন ফরিদা পারভীন পেরেছেন।
আত্মনিবেদনের এই গনঘোর লালনকে ঘিরে তাঁর তরিকায় দীক্ষিত বাউলেরা একটা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন বা ভবিষ্যতেও হবেন।কিন্তু সেই আত্মনিবেদনের যে আঙ্গিক তা সাধারণের দহলিজকে কতখানি কারবালার মাতমে মাতাতে পেরেছে, যতটা ফরিদার কাকুতির মূর্ছনা মাতিয়েছে আম বাঙালিকে? ‘সত্য পথে কেউ নয় রাজি,/ সবি দেখি তানা না না-/ জাত গেল জাত গেল বলে / একি আজব কারখানা’- লালনের এই আপ্ত বাক্যের চিত্রকল্প নির্মাণে সিদ্ধ সাধিকা ছিলেন ফরিদা পারভীন।
লতা মঙ্গেশকর একবার গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, তাঁর মতো পাতলা গলা দিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয় না। লতাজীর মতো সরু সুরেলা কণ্ঠ ছিল না ফরিদার।তাঁর ছিল বেগম আখতারের মতো কিছুটা খড়খড়ে শ্রুতিমধুর কণ্ঠ। আর এটাই ছিল তাঁর কণ্ঠের সব থেকে সেরা সম্পদ। এই সম্পদ ছিল বলেই তাঁকে আর দশজনের মত ‘বাবার মেয়ে’ বলে পরিচয় দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা পেতে হয়নি।প্রতিষ্ঠা তাঁর আঁচলে এসে ধরা দিয়েছিল।এমন সম্পদশালী ছিলেন বলেই হানাদারদের তুষ্ট করতে তাঁকে সেনা ছাউনীতে গিয়ে গান বিক্রিও করতে হয়নি।
বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতি যতদিন বেঁচে থাকবে, তাই ততদিন বাংলা লোকসঙ্গীতের সেরার সেরানারী শিল্পী হিশেবে প্রতিমা বড়–য়ার সঙ্গে ফরিদা পারভীন বেঁচে থাকবেন। লোকসঙ্গীতের মধ্যে কায়িক শ্রম এবং অর্থনীতির প্রচলিত ধারার যে ছাপ আছে তাকে চিরভাস্বর করে গিয়েছেন প্রতিমা বড়–য়া। আবার ‘দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে / রঙ্গীলা দালানের মাটি গো / সাঁই জী কোন রঙে’ এমন গান ও প্রতিমা রেখে গিয়েছেন। সেই ধারারই সাধিকা ছিলেন ফরিদা। খিলকাবিহীন এক ব্যতিক্রমী সাধিকা। নাটোরের রাণী ভবানী তাঁর মায়ের বাড়ি ছাতিনগাঁ হয়ে কুষ্টিয়া- নদিয়ার এক স্বর্ণ সন্তান।
লালন চর্চায় ভূগোল, কাঁটাতার অতিক্রম করে নদিয়া নামটিকে সর্বজনীন করে নেওয়া হয়েছে। সেই সর্বজনীনতাকে একটা প্রজ্ঞা আর দর্শনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে নিজের লালন পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শ্রোতার হৃদয়ে কারবালার মাতম তুলতে পারা সম্ভবত একমাত্র শিল্পী হলেন ফরিদা।তাঁর লালন নিবেদনে বুকের মধ্যে জমে থাকা কান্না দলা পাকিয়ে ওঠেনি- এমন শ্রোতা বোধহয় কমই আছেন। অনেক বিদেশি শ্রোতাকেও দেখেছি, বাংলা তাঁরা জানেন না। বোঝেন না। কিন্তু ফরিদা আপার নিবেদনের কাকুতি তাঁদের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে বার বার।
সাধন সঙ্গীতকে গৃহস্থের দহলিজে নিয়ে আসা- এটা অনেক জ্যাঠামশাই ধরনের লোক মেনে নিতে পারে না।কিন্তু বিশ্বায়নের কালে সাধন সঙ্গীতের বিরুদ্ধতা কেবল বাউল-ফকিরের আঁখড়াতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়।অদ্ভুত পোশাক পরে সুকণ্ঠের অধিকারীর পার্ফরমারেরা বাউলের অনুকরণে চুলে ‘ঝুঁটি’ বেঁধে বাউল-ফকিরি-মারফতীর বিপণন করে।ফরিদা কিন্তু এই বহিরঙ্গের বাউল সেজে লালনকে বাজারের পণ্য করেননি।
আসলে মাটির সুর, মানুষের কথা, মানুষ রতনের সন্ধান- এসবে কখনও আব্বাসউদ্দিনকে ভেকধারী পোশাক পরতে হয়নি।আবদুল আলিম, রণেন রায়চৌধুরী, অমর পাল, প্রতিমা বড়–য়াদেরও কখনো নিজেদের লোকগানের শিল্পী হিশেবে আলদা করে মেকআপ নিতে হয় নি।ঠিক তেমনটাই ছিল ফরিদা আপার গোটা জীবনের যাপনচিত্র।
-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার
-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন
-

টি এস এলিয়টের সংস্কৃতি চিন্তার অভিমুখ
-

আধুনিক বাংলা কবিতার একশ’ বছর
-

নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক বলয় অতিক্রমের ক্ষমতা
-

কেরাসিন বাত্তি ও লালচুলা মেয়েটি
-

তাঁর সমকালীনদের চোখে
-

নিজের মতো করেই সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে