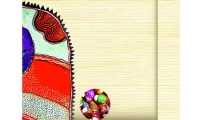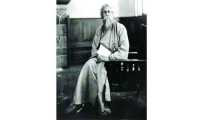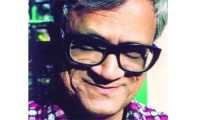নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন
আবদুর নূর রাজ্জাক
বাংলা লোকসংগীতের ভুবনে লালনগীতি এক অমর ঐতিহ্য। এটি কেবল গান নয়, বরং এক আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যম, মানুষের চেতনার মুক্তির আহ্বান এবং ভেদহীন মানবতার এক অব্যর্থ ভাষা। লালন শাহ তাঁর জীবদ্দশায় যেমন এই দর্শনকে সুর ও বাণীর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তী যুগে কিছু নিবেদিত সাধক শিল্পী এই গানকে তাঁদের কণ্ঠে ধারণ করে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেইসব শিল্পীদের মধ্যে একজন কিংবদন্তি কণ্ঠসাধক সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর প্রস্থান শুধু একজন শিল্পীর চলে যাওয়া নয়, বরং লালনগানের ধারাবাহিক যাত্রায় এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি। “পাখি কখন জানি উড়ে যায়”- এই লালনগীতির অমোঘ সত্য যেন তাঁর জীবনের সঙ্গেই মিলে গেছে।
লালনের গান বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির মাটি থেকে উৎসারিত হলেও এর বিস্তার বহুদূর। অষ্টাদশ শতকের বাংলার সাম্প্রদায়িক বিভাজন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লালনের গান ছিল প্রতিবাদের প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের বড় পরিচয় হলো মানুষ হওয়া; ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত এসবই মানুষের কৃত্রিম নির্মাণ। তাঁর গান তাই কেবল সংগীতের আনন্দ দেয় না, বরং মুক্তির দার্শনিক বার্তা বহন করে। এই গান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিণত হয় এক ঐতিহ্যে। তবে এ ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে ও প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন হয়েছিল কিছু বিশেষ কণ্ঠের, যারা সত্যিকার অর্থে সাধনার মাধুর্য দিয়ে লালনের গানকে মানুষের অন্তরে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমাদের সদ্যপ্রয়াত এই শিল্পী সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায়।
শিল্পীর জন্ম হয়েছিল গ্রামীণ পরিবেশে, যেখানে জীবনের সহজ সরল ¯্রােতধারা তাকে প্রথম লালনের গান শুনতে শেখায়। গ্রামের মেলা, আখড়া, বা স্থানীয় আসরে তিনি শৈশব থেকেই লালনের গান শুনতেন এবং ধীরে ধীরে সে গান হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের অংশ। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে তিনি গান গাওয়া শুরু করলে মানুষ প্রথম উপলব্ধি করে তাঁর কণ্ঠে লুকিয়ে থাকা সেই অদ্ভুত শক্তি। কেবল সুরেলা কণ্ঠই নয়, তাঁর পরিবেশনায় ছিল লালনের দর্শনের ব্যাখ্যা, ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি।তাঁর কণ্ঠে যখন উচ্চারিত হতো-
“মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি”
তখন শ্রোতারা যেন অনুভব করতেন, এটি কেবল গাওয়া নয়, বরং জীবনের এক মহামন্ত্র। তাঁর গান শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে তুলত আত্মোন্নতির আকাক্সক্ষা। একইভাবে যখন তিনি গাইতেন-
“খাঁচার ভিতর অচিন পাখিকমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়”
তখন তাঁর পরিবেশনা হয়ে উঠত ধ্যানমগ্ন। শ্রোতারা বুঝতে পারতেন, দেহের ভেতরে এক রহস্যময় আত্মা বসবাস করে, যাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না। তাঁর কণ্ঠের সুরেলা মায়া সেই দার্শনিক সত্যকে আরও সহজ করে তুলত।
তাঁর গানে লালনের প্রতিবাদী কণ্ঠও ধ্বনিত হতো। যখন তিনি গাইতেন-
“সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে”
তখন তিনি যেন সমাজের ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিতেন। এই গান তাঁর কণ্ঠে হয়ে উঠত নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর, যা ধর্ম-বর্ণের কৃত্রিম দেয়াল ভেঙে মানবতার বার্তা দিত।
শিল্পীর সৃজনশীলতা ছিল বহুমাত্রিক। তিনি লালনের গানকে শুধু আদি রূপে পরিবেশন করেননি, বরং এর ভেতরের দার্শনিক মর্মার্থ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন “শোন রে দুঃখী মানুষ, বান্দেরে আমায় দেখাইয়া যাবি” পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি কণ্ঠের ভাঁজে ভাঁজে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা এবং মমতা একসঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। ফলে গানটি কেবল এক সুরেলা আবেগ হয়ে থাকত না, বরং হয়ে উঠত অবহেলিত মানুষের প্রতি সমবেদনার প্রকাশ।
তাঁর পরিবেশনা ছিল আলাদা মাত্রার। শ্রোতারা বলতেন, তিনি গান গাওয়ার সময় কণ্ঠকে কেবল সুরের যন্ত্র বানাতেন না, বরং প্রতিটি গানের পেছনের দর্শনকে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে গান গাইতেন, যেন নিজেকে লালনের দর্শনে নিমগ্ন করে তুলতেন। সেই তন্ময়তা শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হতো।
বাংলাদেশের ভেতরে যেমন তিনি লালনগীতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তিনি এর পরিচয় বহন করেছেন। বিভিন্ন লোকসংগীত উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি লালনের গানকে বিদেশি শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে শ্রোতারা বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে যে, বাংলার গ্রামীণ মাটি থেকে উঠে আসা গান এত গভীর দার্শনিক তাৎপর্য বহন করতে পারে। ফলে লালনগীতি এক বহুজাতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, তাঁর কণ্ঠে লালনের গান শুনে অনেক বিদেশি গবেষক বাংলা সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং লালন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন।
গবেষকরা মনে করেন, লোকসংগীতের মূল প্রাণশক্তি টিকে থাকে তার ধারক ও বাহকদের মাধ্যমে। যদি প্রকৃত সাধকরা না থাকেন, তবে ঐতিহ্য হারিয়ে যায়। এই শিল্পী ছিলেন সেই ধারকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পরিবেশনা ছিল গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যার মতোই নিখুঁত। তিনি শুধু গাইতেন না, প্রতিটি গানের পেছনের দর্শনও শ্রোতাদের সামনে উন্মোচন করতেন। এর ফলে লালনের গান সাধারণ মানুষের কাছে কেবল বিনোদন হয়ে থাকেনি, বরং হয়ে উঠেছে চিন্তার খোরাক, জীবনের পথপ্রদর্শক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যখন লালনগীতি নিয়ে গবেষণা করা হয়, তখন এই শিল্পীর অবদান উল্লেখ করা হয় বারবার। তাঁর কণ্ঠে সংরক্ষিত অনেক গানই আজ গবেষণার মূল উপকরণ।
তাঁর প্রস্থান তাই নিছক ব্যক্তির মৃত্যু নয়, বরং এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সমাপ্তি। সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে, সামাজিক মাধ্যমে সর্বত্র মানুষ তাঁকে স্মরণ করছে। তাঁর গানের অগণিত শ্রোতা যেন অনুভব করছে, তাদের হৃদয়ের ভেতর থেকে একটি আলোর প্রদীপ নিভে গেছে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, প্রকৃত শিল্পীরা কখনো মরে না। তারা থেকে যান তাদের সৃষ্টিতে, তাদের সাধনায়। লালনের গানের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি সুরে আজও আমরা তাকে খুঁজে পাব।
রবীন্দ্রনাথ যেমন লালনকে সাহিত্যিক আলোচনায় এনেছিলেন এবং বিশ্ব দরবারে তাঁর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি এই শিল্পী কণ্ঠ ও পরিবেশনার শক্তিতে লালনকে মানুষের অন্তরে পুনঃস্থাপন করেছেন। তাঁর গান শোনার সময় শ্রোতারা বুঝতে পারতেন, লালনের দর্শন আজও কতটা প্রাসঙ্গিক। সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, রাজনৈতিক অস্থিরতা- এসবের ভিড়ে লালনের গান আজও মানুষের কাছে মুক্তির ডাক হয়ে আসে। আর সেই ডাককে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁর কণ্ঠের শক্তিতে।
আমরা বুঝতে পারি, তাঁর অবদান বহুমাত্রিক। প্রথমত, তিনি লালনের গানকে সংরক্ষণ করেছেন; দ্বিতীয়ত, সঠিক সুর ও অর্থে পরিবেশন করেছেন; তৃতীয়ত, আধুনিক প্রেক্ষাপটে নতুন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন; এবং চতুর্থত, আন্তর্জাতিক পরিম-লে লালনের গানকে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি বাংলা লোকসংগীতকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।
তাঁর মৃত্যুতে আমরা বেদনার্ত, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া সঙ্গীত ভা-ার আমাদের শক্তি জোগায়। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর গান আমাদের অন্তরে রয়ে গেছে। “পাখিকখন জানি উড়ে যায়”- হয়তো তিনি উড়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি চিরকাল আমাদের ভেতর বেঁচে থাকবে। এই প্রতিধ্বনি আমাদের মনে করিয়ে দেবে, সংগীত কখনো মৃত্যুবরণ করে না, প্রকৃত সাধকের সাধনা চিরকালীন।
অতএব বলা যায়, তিনি শুধু একজন শিল্পী নন, ছিলেন এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারক, লালনের দর্শনের জীবন্ত কণ্ঠস্বর। তাঁর প্রস্থান আমাদের গভীরভাবে শোকাহত করলেও তাঁর অবদান আমাদের সাংস্কৃতিক ভুবনকে অনন্তকাল সমৃদ্ধ করে যাবে। লালনের গান যেভাবে বাংলার আত্মাকে স্পর্শ করেছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও তেমনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রতিধ্বনিত হবে। এই কিংবদন্তি সাধক আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবেন, যেমন বেঁচে থাকে নদী, যেমন বেঁচে থাকে গান, যেমন বেঁচে থাকে মানুষের আত্মিক সত্য।
তথ্যসূত্র
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালন ফকিরের গান, বিশ্বভারতী প্রকাশনী।
২. সেলিম মুহিউদ্দীন, লালন ফকিরের দর্শন ও গান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০০৫।
৩. আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশের লোকসংগীত: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪।
৪. জেমস পিকার্ড, Shah: Mysticism in Bengal, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০।
৫. সৈয়দ জাকির হোসেন, লালনগীতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা জার্নাল, ২০১৮।
-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার
-

কেন তিনি লালনকন্যা
-

টি এস এলিয়টের সংস্কৃতি চিন্তার অভিমুখ
-

আধুনিক বাংলা কবিতার একশ’ বছর
-

নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক বলয় অতিক্রমের ক্ষমতা
-

কেরাসিন বাত্তি ও লালচুলা মেয়েটি
-

তাঁর সমকালীনদের চোখে
-

নিজের মতো করেই সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে