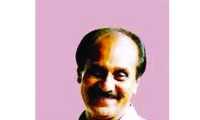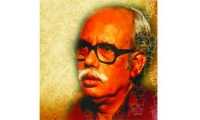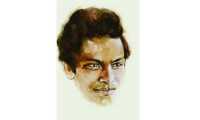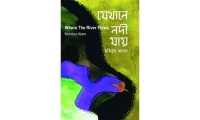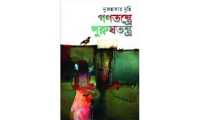বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকা
কয়েকটি নির্ঘণ্ট
নুরউল করিম খসরু
বুদ্ধদেব বসু / জন্ম: ৩০ নভেম্বর ১৯০৮; মৃত্যু: ১৮ মার্চ ১৯৭৪
ভাবা যায়? আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে ‘কবিতা’ নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রথম বেরিয়েছিলো তা পঁচিশ বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যার ঐকান্তিক শ্রম ও মেধায় এই অসম্ভব কীর্তি স্থাপিত হয়েছে তিনি কবি বুদ্ধদেব বসু। মূলত “কবিতা” একটি লিটল ম্যাগাজিন হিশেবেই বেরিয়েছিল। প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছিলো আশি^ন,১৩৪২ বাংলা সনে, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। লেখকসূচি এরকম : প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত,জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী। কল্লোল যুগের নবীন-তরুণ লেখকরাই ধৃত হয়েছে এখানে। আসলে,রবীন্দ্র-নজরুল পরবর্তী যে লেখক কবিকুলের আগমন- যারা সেই তিরিশে প্রতিশ্রুতিময় ও আধুনিকতার ধ্বজা উড্ডীনের সম্ভাবনায় প্রচুর-প্রতুল প্রতিভার অধিকারী, বলতে দ্বিধা নেই তাদের প্রায় সকলের উত্থান এই পত্রিকাকে আশ্রয় করে হয়েছে।
উল্লেখ্য যে, কবিতা এবং বুদ্ধদের বসু সম্পর্ক-লগ্নতার ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। কবিতায় তিনি নিনাদিত,কবিতায় তিনি নিমজ্জিত কবিতায় তিনি উন্মাদ-সম। কবিতা, কবিতা, কবিতা- যেন শুধু কবিতা নিয়েই নিমজ্জমান ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তার বসবাসেও কবিতা, বাড়ির নাম “কবিতা ভবন”। তার সম্পাদিত পত্রিকা- ‘‘কবিতা”, এই পত্রিকা তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর একনিষ্ঠভাবে সম্পাদনা করেছেন। অপিচ, তিনি জীবনভর কবিতা-মত্ত ছিলেন যা বলার অপেক্ষা রাখেনা।
দুই.
উল্লেখ্য যে বুদ্ধদেব বসুর জন্ম বাংলাদেশে, ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লা জেলায়। তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অধিক সময় কটেছে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ঢাকার পুরানা পল্টনে। তার শিক্ষাজীবন ও লেখকজীবিতার উন্মেষ এই ঢাকাতেই, এটি নিঃসন্দেহে আমাদেও জন্য গৌরবের বিষয়। আজি হতে শতবর্ষ আগে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯২৫), ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে আইএ ও ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। বস্তুত,বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যবোধ, লেখক-সত্তার বিকাশ ও বোধন,জাগরতা সবই এই বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সংস্পর্শে জ¦লমান হয়েছে, তথাক্রমপরিস্ফুট ও প্রোজ্জ্বল হয়েছে। তার সাহিত্য-অধ্যায়ন ও চর্চায় ঢাকাবাস যে সবিশেষ গুরুত্ববাহী অধ্যায় তা বুদ্ধদেব বসু নিজেওস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন:
‘আমি ধারাবাহিকভাবে ঢাকায় ছিলাম মাত্র সাড়ে নয় বছর, কিন্তু ছিলাম ঠিক সেই বয়সটায় যেটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে সগর্ভ ও প্রভাবশালী। ভাবলে মনে হয়- আমার মধ্য-তিরিশ থেকেই তা-ই মনে হচ্ছে- যেন কতকাল ছিলাম আমি সেখানে, ঢাকার বছরগুলি ভ’রে যেন অনেক-কিছু ঘটেছিলো, আমি অনেক-কিছ করেছিলাম - মনে হয় যেন দিন রাত্রি ঋতু বৎসর অমন বিচিত্রভাবে ও প্রগাঢ়ভাবে আমার চেতনায় আর প্রবিষ্ট হয়নি। এই অনুভূতি সবচেয়ে তীব্র হ’য়ে ওঠে ঢাকায় আমার প্রথম পাঁচ বছরের কথা ভাবলে- যখন পর্যন্ত আমি বিশ^বিদ্যালয়ে ঢুকিনি, ‘প্রগতি’ পত্রিকা প্রস্ফুট হয়নি ছাপার অক্ষরে।আমার এই মনে হওয়ার সঙ্গে তথ্যেও কোনো সংগতি নেই তা না-বললেও চলে; আসল কথা,আমি তখন উত্তীর্ণ হচ্ছি বাল্য থেকে কৈশোরে আর কৈশোর থেকে নবযৌবনে; আসল কথা আমি তখন আমি হয়ে উঠছি,আবিষ্কার করছি নিজেকে।’ [আমার ছেলেবেলা]
আসল কথা হচ্ছে, বুদ্ধদেব বসু প্রাথমিক- বুদ্ধদেব বসু হয়ে উঠেছেন এই ঢাকাতেই; তার মধ্যে কাব্যঅভিপ্সা ও অন্বেষা অঙ্কুরিত হয়েছে এখানে, তিনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছেন ক্রমাগতভাবে। এখানে আরো একটি তথ্য যুক্ত করতে চাই, বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৯২৭ সালে ঢাকা থেকে ‘প্রগতি’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বেরুতো, এই ‘প্রগতি’ পত্রিকাই হয়ে উঠেছিলো তিরিশের তরুণ সাহিত্যিকদের প্রথম কন্ঠস্বর; কেননা ‘প্রগতি’র মূল বিশিষ্টতা বা উদযাপন ছিলো আধুনিকতা।
তিন.
মূল প্রতিপাদ্য:আগেই বলেছি, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রকাশনার শুরু ১৯৩৫ সালে। সেই থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর একনাগাড়ে বেরিয়েছে; বিরতিহীন ভাবে- সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত হয়ে। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি অবলীলায় লক্ষ্যভেদ করলেন যেনো; তিনি জানান দিলেন- এটি নতুনদের কাগজ, তিরিশি লেখকদের পত্রিকা। এ পত্রিকায় লিখবেন শুধু তারাই যারা অধুনা-লেখক, যারা রবীন্দ্র-নজরুল বলয় ভেঙ্গে রচনা করতে চান নতুন-সাহিত্য। সেজন্য, দেখা যাচ্ছে যে ‘কবিতা’র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নেই, নেই নজরুল-মোহিত লাল-জসীম উদ্দীন- এঁরা কেউ; সেসময় যাদের পদচারণা ছাড়া মনে করা হতো বাংলা সাহিত্য যেন দ্যুতিহীন। বস্তুত বুদ্ধদেব বসু চেয়েছেন যারা প্রতিশ্রুতিময়, যাদের মধ্যে নতুন প্রতিভার অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা প্রবল তাদেরকেই তিনি তার এই পত্রিকায় নিয়তভাবে ধারণ করেছেন। এই ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন শেষাবধি।
কবিতা-অন্তঃপ্রাণ বুদ্ধদেব বসু- ‘কবিতা’ পত্রিকাকে প্রতিনিয়ত সুন্দরতর,উজ্জ্বলতর ও গৌরবদীপ্ত করেছেন তার মননশীলতা এবং মেধা পরিচর্চায়,- পরিচর্যায়। ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রকাশে যে যতœ, যে নিষ্ঠা বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তা অনন্য। তিনি তার সমসাময়িক প্রত্যেক কবিরউপর লিখেছেন, এতো মনোযোগ ও সময় দিয়েছেন উত্তসূরিদের, এতো নিরপেক্ষ হয়ে সমালোচনা করেছেন সমসাময়িককবিদের যার দৃষ্টান্ত বিরল।’ [কবিতা সংকলন ১/মীনাক্ষী দত্ত সম্পাদিত]
সমর সেন তার “বাবু বৃত্তান্ত” গ্রন্থে না-প্রশংসা না-তিরস্কার অভিপ্রায়ে একটি যুতসই বাক্য ব্যবহার করেছেন: ‘কোন পত্রিকা বিষয়ে আতিশয্য অনুচিত’। পরক্ষণে আবার লিখলেন ‘কিন্তু আশি^ন ১৩৪২ অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা ‘কবিতা’ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকদের ভালো লাগতে পারে’।আসলেই তাই, সেজন্য আমিও উক্ত ‘কয়েকটি উদ্ধৃতি’ বর্তমান পাঠকবর্গের জন্য সন্নিবেশ করলাম:
প্রেমেন্দ্র মিত্র : তামাশা“তামাশাটা রেখ মনে। ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাশা।... পথের ধারে / বেড়ায় ঘেরা বিদেশী গাছ / যেদিন চমকেদেবে হঠাৎ পুস্পিত আহ্বানে, আর সাধ হবে যেদিন/ তার কালো চুলে সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে/ ভুলোনা সেদিন ইলেকট্রনেরএই তামাশা।”
বুদ্ধদেব বসু : চিল্কায় সকাল
“কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়/ কেমন করে বলি /কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর, / যেনগুণীর কন্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান / দিগন্ত থেকে দিগন্তে ;/ কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;/ চারদিকে সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায ধোঁয়াটে,/ মাঝখানে চিল্কা উঠচে ঝিলকিয়ে।”
বিষ্ণু দে : পঞ্চমুখ
“... উত্তরে হাওয়া লাগেনি কখনো তোমার গায়ে।/ পাহাড়তলীর দাবদাহ আজো দেখনি চোখে।সাহারার বালি পোড়েনি তোআজো কোমল গায়ে/ প্রসাপিনার পরশ পাওনি এ মরলোকে। / হৃদয়বিহীন খর যৌবনে তোমার হিয়া /হাসি তব তাই বৃথাইছড়ালো তুষার, প্রিয়া।”
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জাগরণ
“তোমার চিকন দেহে বিজড়িত সে-দিব্য,কুহক,/ ভাস্কর অলজ্জ কটি, দৃপ্ত কুচ, নিঃসঙ্কোচ ঊরু,/অধরে সিতাব হাসি, মুক্তকেশে উথলে অগুরু,/সাবলীল আত্মদান ¯িœগ্ধ চোখে এনেছে ঝলক।”
জীবনানন্দ দাশ : মৃত্যুর আগে
“আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পৌষ-সন্ধ্যায়,/দেখেছি মাঠের পাওে নরম নদীর কোলে নিমগ্ন দেউল,/ দেখিয়াছিনদীটিরে; ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা চোখে দেখা যায় / যতদূর; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল / জোনাকীতে ভরেগেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে / চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ- কোনো সাধ নেই তার ফসলের তরে।”
অজিতকুমার দত্ত : ন খলু ন খলু বাণ
“সংহত করো, সংহত করো অয়ি,/ যৌবন-বাণ তীক্ষè ভয়ঙ্কর, এ নহে তন্দ্রা অরণ্য-ছায়াচারী ত্রস্ত হরিণ; সংহরো তব শর।তীক্ষèসায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে / ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,/শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,/মৃগয়ারো তরে ভিন্নসে-ঋতু আছে।”
সমর সেনের এই ভালো-লাগা উদ্বৃতি; আবার দুটি টুকরো মন্তব্যও যোগ করেছেন তিনি:“সুধীন দত্তের লেখা ঋজু ও স্পষ্ট, কাব্যিপনা নেই। কবিতাটির নায়িকা কি বিদেশিনী? কিন্তু ‘অগুরু’ কোথা থেকে এলো?প্রেমেনবাবু তখনি ইলেকট্রনের তামাশা ধরে ফেলে সংসার সীমান্তে থাকতেন ব’লে চেহারা ও স্বাস্থ্য অটুট রেখেছেন।”
তবে কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মদিরতা-প্রমত্ততা নিঃসন্দেহে ঋদ্ধ ও প্রাচুর্যময় করেছে সাহিত্যকে। ‘কবিতা’ পত্রিকার অনেক অগুনতি লেখাই বুদ্ধদেবের- স্বনামে, বেনামে অপিচ অ-নামেও। আগেই বলেছি,তিনি পূর্বজদের লেখাকে বিষয়বস্তু করেছেন, তার সমকালীন প্রায় সব কবি-লেখকের লেখার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, উত্তরসূরিদেরকেও স¯েœহ জায়গা দিয়েছেন এই ‘কাবিতা’ ভূমিতে।প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এ-সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন- ‘তার (বু. ব.) লক্ষ্য ছিল আধুনিক কবিতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ‘আধুনিক’ কবিতা লেখকদের পক্ষ সমর্থন করা।’ আবার তিনি এখানে অনেক সাহিত্যিক বিতর্কের অবতারণা করেছেন, উসকেদিয়েছেন,- চেয়েছেন সুরাহা হোক। যেমন, কবিতার দুর্বোধ্যতা। এ-বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন- বলেছেন- “দুর্ব্বোধ্যতা নিয়ে স্পষ্টভাবে জানালেন ‘‘কবিতা সম্বন্ধে ‘বোঝা’ কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা বুঝিনে; কবিতা আমরা অনুভব করি। কবিতা আমাদের কিছু ‘বোঝায়’ না; স্পর্শ করে, স্থাপন করে একটা সংযোগ ‘কবি অল্প একটু আভাস দিলেন,বাকি অনেকটা আমরা ধ’রে নিলাম; এই যোগাযোগ হলো কবিতার সার্থকতা।’ ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে, তা ‘বোঝা’ যাবে না, ‘বোঝানো’ যাবে না।’ অন্যত্র আবার “কবিতার পাঠক” শিরোনামে লিখেছেন, ‘কবি অল্প একটু আভাস দিলেন,বাকি অনেকটা আমরা ধ’রে নিলাম; এই যোগাযোগ হলো কবিতার সার্থকতা।’ ‘প্রকৃত কাব্যসম্ভোগ- অন্তত উচ্চতম কবিতার সম্ভোগ- বিশেষ শ্রেণির পাঠকের জন্যেই। পৃথিবীতে ভালো কবির সংখ্যা অল্প,ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়।... কবি বার বার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন,তা খানিকটা কল্পনা শক্তি থাকতেই হবে পাঠকের।’
বস্তুত ‘কবিতা’ ক্রমাগতভাবে যেন প্রণয়ন করেছে রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্যের নতুন ইশতেহার, দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক বাংলা কবিতা অভিধায় যাদের কবিতাকে ধারণ করেছেন [বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ,সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী] তার“আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ” গ্রন্থে; তাদের কবিতাই হয়ে উঠেছে আধুনিক বাংলা কবিতার ভবিতব্য, নতুন অন্বিষ্ঠ, নতুন কাব্যচেতনাশৈলী। এই ‘কবিতা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো তিরিশী কবি-প্রজন্ম।
চার.রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকী
সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কবিতা পত্রিকা যখন বেরিয়েছে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বাংলা সাহিত্যাকাশে সমুজ্জ্বল দীপশিখা-সম, উজ্জ্বল হীরকখ- যেন, আকাশ-শিখরী তিনি। তার বয়স তখন চুয়াত্তর বছর, কিন্তু লিখছেন দুহাতে তখনো; ফলে ‘কবিতা’ পত্রিকার প্রকাশকে তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করলেন যেন; ‘কবিতা’ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তার‘ ছুটি ’ কবিতা প্রকাশিত হলো; এ-ভাবেই তিনি ‘কবিতা’ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ছুটি কবিতার প্রথম পংক্তি ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি’, সবিশেষ তাৎপর্যময় বলে মনে হলো আমার কাছে। তিনি কি কবিতা পত্রিকার উদ্বোধনকে ‘বাদল গেছে টুটি’ বলে সম্ভাষণ করলেন?- হয়তো।
অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রণোদিতভাবেই বুদ্ধদেব বসুকে একটি পত্র লিখেছিলেন,৩ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে,যা কবিতা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। উক্ত পত্র তিনি অরম্ভ করেছেন এ-ভাবে: ‘তোমাদের ‘‘কবিতা’’ পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনায় মধ্যে বৈশিষ্ট আছে। সাত্যি-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকের সঙ্গে এরা নতুন পরিচয় স্থাপন করেছে।’‘কবিতা’ পত্রিকার অভীপ্সা তো তাই ছিলো- লেখকের ‘ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য’ ও পাঠকের সাথে ‘নতুন পরিচয় স্থাপন’।‘উত্তররৈবীক ক্যারাভান’ (আবদুল মান্নান সৈয়দ এই শব্দবন্ধ-টি ব্যবহার করেছেন তার “নির্বাচিত প্রবন্ধ” গ্রন্থে ) অর্থাৎ রবীন্দ্র-উত্তর কবি-সারথি যারা ‘কবিতার ’ প্রথম সংখ্যায় সূচিবদ্ধ হয়েছেন- উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাদের লেখা নিয়ে যে-মন্তব্য করেছেন, তার চুম্বক-অংশ ধৃত হলো এখানে:
‘প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘‘তামাসা’’ কবিতাটিতে পাহাড়তলীর বন্ধুর ভূমির গদ্যেও রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো।’‘তোমার (বুদ্ধদেব বসু) কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক।’‘বিষ্ণু দে’র কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, সেটা দুর্ব্বলতা।’‘সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে।’‘সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে।’‘জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে-’‘অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাদের কবিত্ব।’
এবার কবিতা পত্রিকায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত-তালিকা প্রণয়ন করা যাক:
দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘ছুটি’ কবিতা প্রকাশ
রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে
রবীন্দ্রনাথের কবিতা- ‘আফ্রিকা’ প্রকাশ
যামিনী রায়: রবীন্দ্রনাথের ছবি (আলোচনা)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ও সাহিত্যের উৎস (বু.ব.কে চিঠি)
রবীন্দ্রনাথের পত্র যামিনী রায়কে-
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আধুনিক বাংলা কবিতা (বু.ব.কে চিঠি)
প্রবোধচন্দ্র সেন : সমালোচনা- সঞ্চয়িতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমিয় চক্রবর্তী : ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য
বুদ্ধদেব বসু: ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য
পাঁচ.নজরুল প্রাসঙ্গিকী
‘কবিতা’ পত্রিকা প্রথম বেরিয়েছে ১৯৩৫ সালে, আর দশম বর্ষে এসে কবিতার একটি বিশেষ “নজরুল সংখ্যা” বেরিয়েছিলো। ইতিমধ্যে নজরুলের লেখক-সত্তার মৃত্যু হয়েছে, তিনি ১৯৪২ সাল থেকে বাক-রহিত নিস্তব্ধ ছিলেন। উক্ত সংখ্যায় নজরুল-উত্তর অনেক লেখকই লিখেছেন; তন্মধ্যে ক’জন বিশেষ উল্লেখযেগ্য- যেমন : বুদ্ধদেব বসু,জীবনানন্দ দাশ,লীলাময় রায়,শ্রীনলিনীকান্ত সরকার,সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,হিমাংশুকুমার দত্ত প্রমুখ। এছাড়া একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় আছে উক্ত সংখ্যায়।বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের শিরোনাম ‘নজরুল ইসলাম’; তিনি বলেছেন তখন তার বয়স দশ বছর, সে-সময়ে তিনি খোঁজ পেলেন নজরুলের কবিতার;তার ভাষায়- ‘‘এই সময় নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে এলো। ‘বিদ্রোহী’ পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে-মনে হ’লো এমন কখনো পড়িনি।অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করেছিলো, এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।” নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা কিরকম ইতিহাস-প্রাসঙ্গিক ছিলো তা বুদ্ধদেবের এই বিমুগ্ধ ভাষ্য থেকেই প্রতিয়মান হয়। নজরুলের সাথে বুদ্ধদেব বসুর কীভাবে, কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো তা’ও তিনি এখানে বিবৃত করেছেন। তিনি স্পষ্টত জানিয়েছেন, ‘বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে রড় কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের।’ তিনি মন্তব্য করেছেন যে, নজরুলের কাব্যে ‘স্বকীয়তা সুস্পষ্ট’ এবং তিনি যে ‘অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন’ ‘এ-টা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা’। জীবনানন্দ দাশ লিখলেন ‘নজরুলের কবিতা’ শিরোনামে প্রবন্ধ; তিনি তার স্বভাবসুলভ ভাষায় কাব্যের আদি-অন্ত, কবিতার ভেদ-প্রকরণ-শৈলী-কুশলতা বিষয়ে সম্যক আলোচনা করেছেন অধিক, তবে তিনি স্বীকার করেছেন,- ‘নজরুল ইসলামের আগ্রহ পুষ্ট হয়েছিল, তিনি অনেক সফল কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন।’ আবার বলেছেন ‘ কিন্তু যে বিশেষ সময়ধর্ম,ব্যক্তিক আগ্রহ ও একান্ততার জন্যে নজরুলের অনেক কবিতা সফল ও কোনো-কোনো কবিতা সার্থক হয়েছিল-’।
শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের লেখাটি সবিশেষ স্মৃতিকথন; তার সাথে নজরুলের পরিচয়-পর্ব থেকে আরম্ভ, তাদের বিবিধ আড্ডাপর্ব, নজরুলের বোহেমিয়ান জীবনযাপন,তার লেখালেখির খোঁজখবর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের পারস্পরিক সম্পর্কতা এসব তিনি অনেক অনুপংখভাবে বয়ান করেছেন। তিনি একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন এভাবে: ‘নজরুলের অভ্যুদয়ের যুগে যে-সব কবিতায় তার স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল, সেগুলির মধ্যে আমি প্রথম পড়ি “শাতিল আরব” কবিতাটি। বোধ হয় ঐ শ্রেণির কবিতার ঐটিই তাঁর সর্বপ্রথম রচনা।’তিনি আরো লিখেছেন, “প্রবাসী” পত্রিকার যেমন রবীন্দ্রনাথ, “মোসলেম ভারতে”র তেমনি ছিলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের তখনকার লেখা প্রধানত বেরুতো “মোসলেম ভারতে”।
তিনি এ-তথ্যটিও জানিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে:‘নজরুলের জেলে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসব করেন কোলকাতায় এবং তার “বসন্ত” নাটিকাটি উৎসর্গ করেন এই কথা লিখে-
“শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম
¯েœহভাজনেষু”
তার প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি বেশ প্রণিধানযোগ্য,- ‘বিংশ শতাব্দীর কোলে নজরুল যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদায়কালীন প্রীতি-উপহার।’
আসলেই তাই-।
ছয়.পরিশেষ
আগেই উল্লেখ করেছি যে ‘কবিতা’র প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে ১৯৩৫ সালে, আর পঁচিশ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে- শেষ সংখ্যাটি যখন বেরোয় তখন বুদ্ধদেব বসু দেশের বাইরে; ফলে ঐ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন জ্যোতির্ময় দত্ত। তবে এ-কথা মানতেই হবে যে রবীন্দ্র-পরবর্তী যতো উৎকৃষ্ট কবিতা বাংলা সাহিত্যে রচিত তার প্রায় সবই এই ‘কবিতা’ পত্রিকা থেকে আমরা পেয়ে যাই; তিরিশ চেতনার মূল সম্ভার হচ্ছে- ‘কবিতা’। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য যোগ করতে চাই, ‘কবিতা’র শেষ পর্যায়ের কয়েকটি সংখ্যায় বাংলাদেশের কয়েকজন কবিও তাদের কবিতার প্রবেশ ঘটিয়ে সৌভাগ্যের তিলক ধারণ করেছেন; তারা হচ্ছেন: আলাউদ্দিন আল আজাদ,শামসুর রাহমান,আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, সৈয়দ সামসুল হক, ইমামুর রশীদ প্রমুখ।
এ-ভাবেই বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ রবীন্দোত্তর বাংলা সাহিত্যে দুই যুগ পরাক্রমের মধ্য দিয়ে উদযাপন করলেন, উত্তীর্ণ করলেন সবিস্ময়ে,- যেন সুবর্ণখচিত ইতিহাস বাংলার কাব্যাকাশে।