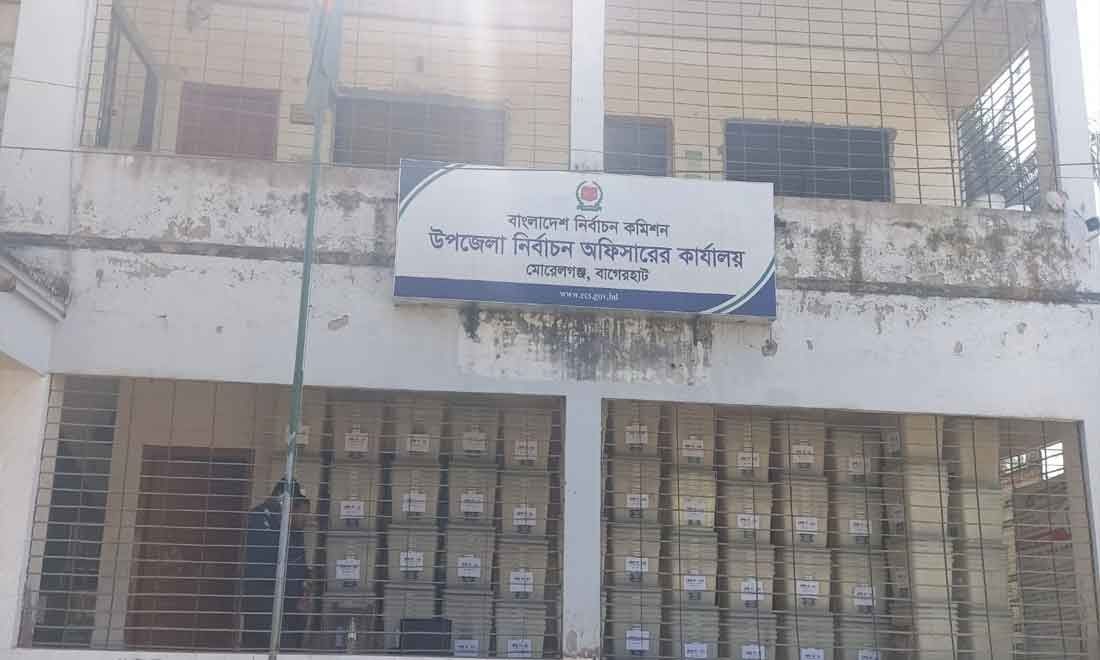শিক্ষার হাল-হাকিকত : পরীক্ষার ফলই কি মূল উদ্দেশ্য?
মাহরুফ চৌধুরী
সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দেশজুড়ে নানা আলোচনা, সমালোচনা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেউ একে শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহ বিপর্যয় হিসেবে দেখছেন, কেউ বলছেন এটি কেবল একটি গণপরীক্ষার ফলাফল নয়, আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থার অদৃশ্য অন্তর্দাহের বহিঃপ্রকাশ।
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে এখন ‘পরীক্ষা’ নামের এক অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই শিক্ষার মান, ছাত্রের যোগ্যতা, শিক্ষকতার সাফল্য, এমনকি একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাও নির্ধারিত হচ্ছে পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে
এই ফলাফল কোনো দুর্ভাগ্যজনিত ঘটনা নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা এক ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদর্শন, যান্ত্রিক রীক্ষানির্ভরতা ও গুণগত অবক্ষয়ের স্বাভাবিক ফলাফল। তাই জিজ্ঞাস্য কেবল এতটুকু নয় যে, এইচএসসি পরীক্ষায় কারা পাস করল, কারা ফেল করল। বরং এর চেয়েও গভীরভাবে ভাবনার বিষয় হলো: পরীক্ষার ফলাফলই কি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য? পরীক্ষার ফলাফলকেন্দ্রিক সকল প্রচেষ্টা আমাদের শিক্ষার সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত ও সাধারণ শিক্ষার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের মাঝেই এর শেকড় নিহিত আছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে এখন ‘পরীক্ষা’ নামের এক অতি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই শিক্ষার মান, ছাত্রের যোগ্যতা, শিক্ষকতার সাফল্য, এমনকি একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাও নির্ধারিত হচ্ছে পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পরীক্ষাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি কোথা থেকে ও কিভাবে এলো? ঊনিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতবর্ষে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল, তার উদ্দেশ্য কখনোই রাষ্ট্রের জন্য স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল নাগরিক তৈরি করা ছিল না; বরং সেটা ছিল ‘লিখতে-পড়তে জানা’ এমন এক তাবেদার শ্রেণির আমলা বা কেরানিদের তৈরি করা যারা শাসনযন্ত্রের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করবে। টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে তার বিখ্যাত ‘মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন’ (১৮৩৫), যা ম্যাকলের মিনিট হিসেবে পরিচিত, যাতে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য ‘এমন একটি শ্রেণি তৈরি করতে হবে যারা হবে রক্তেমাংসে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তাচেতনায় ও মূল্যবোধে ব্রিটিশ’। দুঃখজনকভাবে আমরা দু’বার স্বাধীনতা অর্জনের পরও শিক্ষাব্যবস্থার সেই উপনিবেশিক কাঠামো অক্ষুণ্য রেখেছি। এখনো আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবিক নাগরিক নয়, বরং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ‘চাকরিপ্রার্থী’ আমলা কিংবা কেরানি তৈরি করা আর পরীক্ষার ফলাফলই যাদের যোগ্যতার মাপকাঠি।
পরীক্ষার ফলাফলের জন্য উচ্ছ্বাসের আড়ালে ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রতি বছরই বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন দেশে যেন এক উৎসবের দিন হয়ে ওঠে। সংবাদমাধ্যমে বড় শিরোনাম ‘অমুক বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে’, ‘ফলাফল ভালো, পাসের হার ৯০ শতাংশের বেশি’। কিন্তু এ উচ্ছ্বাসের আড়ালে থেকে যায় তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যর্থতার গভীর এক বাস্তবতা। এই ফলাফল আসলে আমাদেরকে কী বলছে? এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ‘ফলাফল বিপর্যয়’ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, শুধু সংখ্যায় নয়, শিক্ষার গুণগত মানেও আমরা ভয়াবহভাবে পিছিয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো করলেও বাস্তবে তারা বিষয়বস্তুর গভীরতা বোঝে না। শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, ‘শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে পাস করে, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে না’। এই প্রবণতা কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটি এক সাংস্কৃতিক প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই নিজেদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে আত্মবিশ্বাসী নয়। অথচ টিউটরিং, কোচিং, গাইড বই ও মডেল টেস্টের দৌলতে তারা ভালো ফল করছে। ফলে পরীক্ষায় সফলতা এখন বাস্তব জ্ঞানের নয়, বরং কৌশলে নাম্বার অর্জনের বা মুখস্ত বিদ্যার দক্ষতার পরিমাপক।
মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শেখা আজ হারিয়ে যাচ্ছে নাম্বারের জন্য ‘পড়া’র চাপে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে যে, আমরা ‘পড়ালেখা’কে ‘শেখা’ ভেবে বসেছি। ‘পড়ালেখা’ মানে মুখস্থ করে তথ্য, উপাত্ত বা তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করা; আর ‘শেখা’ মানে সেই অর্জিত জ্ঞানকে নিজের জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা লাভ করা। আমরা আজ শিক্ষার্থীদের শেখাচ্ছি কেবল পরীক্ষার উত্তর দেওয়ার ও বেশি নম্বর পাওয়ার কৌশল, কিন্তু শেখাচ্ছি না কিভাবে জীবন, সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। ফলে তারা বইয়ের তথ্য, উপাত্ত কিংবা তত্ত্ব জানে, কিন্তু জীবনে সেসবের প্রয়োগ জানে না। ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’ (প্যাডাগোজি অব দ্য অপ্রেসড)-এ বলেছিলেন, ‘যে শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায় না, তা হলো দমনমূলক শিক্ষা’। আমাদের শিক্ষা এখন সেই দমনমূলক প্রথায় বন্দি যেখানে শিক্ষার্থী কেবল তথ্যগ্রহণকারী, চিন্তাশীল সত্তা নয়।
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোভিড-পরবর্তী শিক্ষার পটভূমি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতায় শিক্ষা ব্যবস্থার আশু সংস্কার ও রূপান্তর অত্যাবশ্যক। কোভিড মহামারি বিশ্বজুড়ে শিক্ষার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে শিক্ষার্থীরা বই থেকে নয়, ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে জ্ঞান আহরণ করছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারকরা এই পরিবর্তন এখনো উপলব্ধি করতে পারেননি বলে মনে হচ্ছে। ফলে পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষার কাঠামো এখনো সেই পুরোনো রূপেই চলছে, যেখানে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন ও প্রযুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা কিংবা অভ্যাসের কোনো প্রতিফলন নেই। অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন শিক্ষার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা উভয়ই। কিন্তু আমরা এখনো তার কোনো সুশৃঙ্খল ব্যবহার বা নৈতিক দিকনির্দেশনা তৈরি করতে পারিনি। শিক্ষার্থীরা চ্যাটজিপিটি বা অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুল ব্যবহার করে অ্যাসাইনমেন্ট করছে, অথচ শেখার প্রক্রিয়া বিশেষ করে বিচারবিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনা থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এই বিযুক্তিই এখন আমাদের শিক্ষার সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে।
আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, একটি দেশের শিক্ষার মান নির্ভর করে তার শিক্ষকের ওপর। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে একদিকে শিক্ষকরা যেমন নানা দিক থেকে উপেক্ষিত, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষকতা পেশা অশিক্ষকদের পদাচারণায় মুখর। সমাজের অন্য পেশার তুলনায় বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকেরা নানাভাবে বঞ্চিত। তাদের সামাজিক মর্যাদা, পেশাগত নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ সবক্ষেত্রেই ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার রাজনীতিকিকরণ ও দুর্নীতির ফলে অযোগ্যদের ভারে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। অনেক শিক্ষক মনে করেন, তাদের কাজ কেবল সিলেবাস শেষ করা; শিক্ষার্থীর চিন্তা বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাদের দায়িত্ব নয়। ফলে শ্রেণিকক্ষ এখন আলোচনার নয়, বরং বক্তৃতার জায়গা। শিক্ষক বলেন, শিক্ষার্থী শোনে এই একমুখী প্রথাগত পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষাকে নিস্তরঙ্গ ও প্রাণহীন করে তুলেছে। আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন ডিউইয়ের ভাষায়, ‘শিক্ষা হলো পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রক্রিয়া’, কিন্তু আমাদের শ্রেণিকক্ষে সেই পারস্পরিকতা অনুপস্থিত। নম্বর অর্জনের ও চাকুরির প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে শিক্ষার্থীদের ওপর আজ অভিভাবক ও সমাজের চাপও ভয়াবহ। একটি শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় ‘ভালো ফল করতে হবে’ নামের প্রত্যাশার এক বিশাল বোঝা। এর ফলে শিশুর মধ্যে শেখার আনন্দ হারিয়ে যায়, মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তীব্র প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার ভয়, উদ্বেগ ও তুলনামূলক হীনমন্যতা। অভিভাবকরা মনে করেন, জিপিএ-৫ মানেই সাফল্য। অথচ তারা ভাবেন না, সন্তান কীভাবে মানুষ হচ্ছে, তার মূল্যবোধ কীভাবে তৈরি হচ্ছে, সে সমাজের প্রতি কতটা সচেতন হচ্ছে। ফলে এই একপেশে সাফল্যচেতনা আমাদের নতুন প্রজন্মকে যান্ত্রিক, প্রতিযোগিতামুখী এবং আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে।
আমরা যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, সে কাক্সিক্ষত রাষ্ট্রের নাগরিকদের তৈরি করতে ফলাফল নয়, প্রয়োজন শিক্ষার পুনর্গঠন ও যুগোপযোগী রূপান্তর। সেই প্রেক্ষাপটে এবারের এইচএসসি ফলাফল আসলে এক প্রকার ‘সতর্কবার্তা’। যদি আমরা এখনই আমাদের শিক্ষার ভিত্তিকে পুনর্গঠন না করি, তবে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপর্যয় আসবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কেবল ‘পরীক্ষা পাস’ বা ‘চাকরি পাওয়া’র গণ্ডি থেকে বের করে এনে মানুষ গড়ার সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে পুনর্গঠন করতে হবে। এজন্য দরকার একটি নতুন শিক্ষাদর্শন, প্রাসঙ্গিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যেখানে জ্ঞান, নৈতিকতা ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এক সুতোয় গাঁথা থাকবে। শিক্ষাব্যবস্থার জীবনমুখী যুগোপযোগী রূপান্তরে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:
১. বস্তুগত শিক্ষার সাথে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার সংযোজন ঘটাতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা কেবল তথ্যের সঞ্চয় বৃদ্ধি নয়; এটি মানুষ হিসেবে আমাদের চরিত্র গঠন ও চেতনার বিকাশ সাধন করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে ‘আপনার সঙ্গে নিজের পরিচয় করায়’। তাই শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের পাঠ পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। এটি শিক্ষার্থীদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে এনে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। ২. শিক্ষার্থীদের শিখনফলের ক্রমাগত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাবর্ষের শেষে একটি মাত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর পুরো বছরের যোগ্যতা নির্ধারণ করা অন্যায্য ও অযৌক্তিক। শিক্ষার উদ্দেশ্য শেখার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশ, যা এককালীন পরীক্ষায় প্রতিফলিত হয় না। তাই শিক্ষাবর্ষের শেষে কেবল পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বছরজুড়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সৃজনশীলতা ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার নানা কার্যকলাপকে মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এতে শেখা হবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়াভিত্তিক আত্মোন্নয়ন প্রচেষ্টা, পরীক্ষার ফলাফলনির্ভর নয়।
৩. শিক্ষকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ ও তাদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক শুধু পাঠদানকারী নন, তিনি সমাজের আলোকবর্তিকাও বটে। অথচ আমাদের বাস্তবতায় শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার ঘাটতিতে ভোগেন। তাদেরকে প্রদত্ত বেতন-ভাতা অন্যান্য পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের গবেষণানির্ভর, প্রযুক্তি-বান্ধব ও সৃজনশীল শিক্ষাদানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষককে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়ে আনতে না পারলে কোনো সংস্কারই টেকসই হবে না।
৪. জীবনমুখী যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রনয়ন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের পাঠ্যক্রম এখনো পরীক্ষামুখী এবং বাস্তবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে যাতে শ্রেণিকক্ষের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য বা ইতিহাস সব ক্ষেত্রেই শেখার উদ্দেশ্য হবে আগামী প্রজন্মকে মানবিক করে গড়ে তোলা ও তাদেরকে সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা। শিক্ষা তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা জীবনের জন্য, কেবল পরীক্ষার জন্য নয়।
৫. প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল টুল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে ভয় নয়, সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তবে এ ব্যবহারের মধ্যে থাকতে হবে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ। শিক্ষার্থীরা যেন প্রযুক্তির দাস না হয়ে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানবিক জ্ঞান ও সৃজনশীলতা বাড়াতে পারে এমন কাঠামো তৈরি করা জরুরি।
৬. অভিভাবকদের ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা সংস্কারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের মানসিকতা। আমাদের অভিভাবকরা সন্তানদের শিক্ষা মানে বোঝেন ‘চাকরি পাওয়া’র উপায়। এই ধারণা বদলাতে হবে এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ‘মানুষ হওয়া’ এই উপলব্ধি তৈরি করতে হবে।। শিক্ষা আসলে মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়া, যেখানে সাফল্যের মাপকাঠি হলো নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও দায়িত্ববোধ। পরিবার ও সমাজ যদি এই মূল্যবোধের পুনর্গঠন না করে, তবে শিক্ষার যেকোনো সংস্কারই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষার দর্শনকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদরা তাই সর্বদাই বলে এসেছেন, শিক্ষা হলো জীবনবোধের অনুশীলন। কনফুসিয়াস বলেছিলেন, ‘শিক্ষা মানুষকে নিজের ভুল চিনতে শেখায়’। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা কোনো পাত্রে তথ্য ঢালা নয়; বরং মননের আগুন প্রজ্বলিত করা। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠার সেই আগুন এখন নিভে আসছে। আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবল তথ্য, উপাত্ত কিংবা তত্ত্ব ঢালছি, কিন্তু তাদের মধ্যে চিন্তার আগুন জ্বালাতে পারছি না।
বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে আমাদেরকে নতুন সম্ভাবনার ডাক দিতে হবে। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ হওয়াটা স্বাভাবিক; তবে এটিকে আমরা কেবল হতাশার প্রতীক হিসেবে দেখলে ভুল করব। আমাদের জন্য এটি এক গভীর আত্মসমালোচনার সুযোগও এনে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করার: আমরা কেমন শিক্ষার্থী চাই? কেবল পরীক্ষায় পাস করা মানুষ, নাকি মানবিক বোধসম্পন্ন নাগরিক? আমরা কেমন শিক্ষক চাই? কেবল সিলেবাস শেষ করা কর্মচারী, নাকি চিন্তা উসকে দেওয়া দার্শনিক? আমরা কেমন সমাজ চাই? কেবল ডিগ্রিধারী কর্মজীবী, নাকি ন্যায় ও সত্যের চর্চায় বিশ্বাসী মানুষ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষার দিকনির্দেশ। কারণ শিক্ষা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকরণ নয় এটি মানবমুক্তির প্রক্রিয়াও বটে।
এবারে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল হয়তো আপাতদৃষ্টিতে ‘বিপর্যয়’ মনে হচ্ছে, কিন্তু তা আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার এক সুযোগও বটে। এটা ‘সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দেব কোথা’ এই আক্ষেপ থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে জীবনমুখী যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ আহ্বান। এখন সময় এসেছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে নতুন করে ভাবার ও নতুন করে ঢেলে সাজাবার যেখানে শেখা মানে জীবন তথ্য, উপাত্ত বা তত্ত্বের বোঝা নয়, কেবল নাম্বারের জিপিএ নয়, সাথে সাথে জীবনের অর্থ খোঁজাও। আমাদের শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে শিক্ষাব্যবস্থার কাক্সিক্ষত রূপান্তরের মধ্যমে যেখানে শিক্ষক মানে অনুপ্রেরণা, আর শিক্ষার্থী মানে অনুসন্ধানী মন। পরীক্ষার ফলাফল নয়, জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানই হবে তখন আমাদের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। নতুন স্বপ্নের জাল বুনে আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।
(মতামত লেখকের নিজস্ব)
[লেখক: ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য]