উপ-সম্পাদকীয়
প্রবারণার ইতিবৃত্ত
বিপ্লব বড়ুয়া
প্রবারণা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মহামানব বুদ্ধের জীবনসংশ্লিষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যেসব ঘটনা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত সেগুলোর মধ্যে প্রবারণার গুরুত্ব অনেক বেশি। পালি সাহিত্যে প্রবারণার ব্যাপক অর্থ আমরা দেখতে পাই, যেমন- প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা, আশার তৃপ্তি, সন্তুষ্টি, নিমন্ত্রণ, শিষ্টাচার, অনুরোধ, ক্ষমা, সংযম, ত্যাগ। তিন মাস বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে অধিষ্টানকর্ম শেষ করে একজন অন্যজনকে ক্ষমা প্রদর্শনপূর্বক আপন করে নেয়াই হচ্ছে প্রবারণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এককথায় যদি বলি অন্যায় অকুশল কর্মকে বর্জন ও ন্যায় কুশল কর্মকে বরণ করার অর্থ হচ্ছে প্রবারণা।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশি^নী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাসকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় বর্ষবাস। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে বলে ছোট ‘ছাদাং’; আর আশি^নী পূর্ণিমাকে বলে বড় ‘ছাদাং’। এই বড় ‘ছাদাং’ হচ্ছে প্রবারণা পূর্ণিমা। ‘ছাদাং’ শব্দটি বার্মিজ শব্দ। বিভিন্ন প্রাপ্ত সূত্রের বরাতে জানা যায়, চট্টগ্রাম এলাকা প্রায় দেড় হাজার বছরের কিছু সময় আরকান শাসনের অধীনে ছিল। আরকানিদের আচার ব্যবহার ছিল বার্মিজ আদলের। সে কারণে তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রামের মানুষরা তাদের নিয়মনীতি পালনে অভ্যস্ত ছিল। আমাদের জীবন চলার পথে ‘ছাদাং’ শব্দের মতো এরকম বহু বার্মিজ ভাষা প্রচলিত ছিল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো আছে। এই ‘ছাদাং’ শব্দটিও ঠিক তাদের কাছ থেকে পাওয়া। সেই থেকে ‘ছাদাং’ নামটি বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত একটি প্রচলিত শব্দ বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য বছরের এই তিন মাস সবচেয়ে পুণ্যময় সময়। এই পূর্ণিমায় তথাগত গৌতম বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে মাতৃদেবীকে অভিধর্ম দেশনার পর সাংকাশ্য নগরে অবতরণ করেন এবং পুজনীয় ভিক্ষুসংঘকে নির্দেশ দিলেন আজ থেকে তোমরা বহুজন হিত, সুখ, কল্যাণে সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো। পরদিন থেকে শুরু হয় দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দান। ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নগর থেকে গ্রামে ছুটে যায়।
বর্ষবাসের এই তিন মাস বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ধর্মচর্চা, ধ্যানানুশীন, কৃচ্ছ্রসাধন, মানবিক কর্মসাধন, ত্যাগ, ধৈর্য, সহনশীল ও সংযমের মধ্যে দিনযাপন করে থাকে। যদিও বা ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধ এই নির্দেষ ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ করে প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন। তিন মাস সময় পর্যন্ত ভিক্ষুসংঘরা নিজ নিজ বিহারে অধিষ্টান করা ব্যতীত রাত্রে অন্যকোন বিহারে রাতযাপন করতে পারবে না। এর একটা ব্যাখ্যা আছে- তৎসময়ে এই তিন মাস ছিল ঘোর বর্ষাকাল, এখন অবশ্য বৈশি^ক ভূ-পরিবেশের পট পরিবর্তনের ফলে ঋতুর পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি।
যেহেতু বর্ষকাল ছিল তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে বললেন হে ভিক্ষুগণ, এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে নানা জাতের কীটপতঙ্গের বিচরণ ঘটে। বুদ্ধ আরো বলেন, আমাদের চলাচলের ফলে একটি কীটপতঙ্গও যাতে আঘাতপ্রাপ্ত বা বাধার সম্মুখীন না হয়, তাই যথাসম্ভব তোমরা বিহারে থেকে ধর্মচর্চায় রত থাকো এবং কল্যাণ সাধনে ব্রতী হও। ভিক্ষুদের দেখাদেখি এখন বহু বৌদ্ধ নর-নারীরাও এই তিন মাস সংযম-কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় জীবনযাপন অনুশীলনে রত থাকে। প্রতি অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল পালনের মধ্যে উপোসথ ব্রত পালন করে। এসময় বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকারা নিয়মিত বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, সূত্রপাঠ, ধ্যানানুশীলন, ধর্মশ্রবণ এবং কুশল কর্ম পালন এবং মঙ্গল চেতনার মধ্যে দিয়ে পরি¯œাত, পরিশীলিত দিন পালন করেন।
মহামানব গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথমেই সংঘ প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন। সংঘ মানে ভিক্ষু সংঘ। তিনি চিন্তা করলেন হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষকে কোনভাবে তার অর্জিত জ্ঞান প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদি সংঘের মধ্যে দিয়ে কথাগুলো প্রচার করা যায়, সে উদ্দেশ্যে ভিক্ষু সংঘকে প্রথমে একতাবদ্ধ করলেন এবং সর্বক্ষেত্রে ভিক্ষু সংঘকে প্রাধান্য দিয়ে ধর্ম প্রচারে এগিয়ে এসেছিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা আড়াই হাজার পরে এসেও ধর্মচর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে এটি ছিল যুগান্তকারী উপদেশ।
এবার আসি বৌদ্ধরা ফানুস বাতি বা আকাশ প্রদীপ কেন উড়ায়। কথিত আছে, বুদ্ধত্ব লাভ করার আগে সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করে অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে সংকল্প করলেন এবং এ সময় তার সঙ্গে থাকা সারথী ছন্নকে অশ্ব কন্থক ও শরীরের সমস্ত আবরাণাদী তার হাতে তুলে দিয়ে তাকে বিদায় দেন। অতঃপর তিনি ভাবলেন, ‘আমার মস্তকে সুবিন্যস্ত কেশকলাপ প্রব্রজিতের পক্ষে শোভনীয় নহে।’ তিনি দক্ষিণ হস্তে অসি এবং বাম হস্তে রাজমুকুটসহ কেশকলাপ ধারণ করে কেটে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করে সত্যক্রিয়া করেছিলেন, ‘যদি সত্যিই আমি ইহজন্মে মহাজ্ঞান (বুদ্ধত্ব) লাভে সমর্থ হই তাহলে এই মুকুটসহ কেশরাশি ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হবে।’
তার কেশরাশি আকাশে উত্থিত হলো। তাবতিংশ স্বর্গের দেবগণ কেশরাশি নিয়ে গিয়ে চুলমনি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে লাগলেন। এ খবর একান ওকান করতে করতে সমগ্র রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেই থেকে কুমার সিদ্ধার্থের কেশরাশিকে পূজা, শ্রদ্ধা, সম্মান করে প্রতি বছর প্রবারণার দিনে বাংলাদেশের মতো সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ফানুস উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রতি অযুত ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রণতি প্রদর্শন করে আসছে। ফানুস মানুষের অন্তর্জগৎকে আলোকিত করার মাধ্যমে সমস্ত রকমের পাপ, অন্ধ, কুসস্কার থেকে দূরীভূত হয়ে পবিত্রতা আনয়ন করে।
বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব হলেও পর প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উত্তোলনের ব্যাপক কর্মযজ্ঞের কারণে এই উৎসব জাতি ধর্ম-বর্ণ সব মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যায়। প্রবারণার পরদিন থেকে দীর্ঘ একমাস ধরে চলে কঠিন চীবর দানোৎসব। যে বিহারে তিন মাস ভিক্ষু অধিষ্টান বা বর্ষাবাস যাপন করে না সে বিহারে কঠিন চীবর দান করা হয় না। এই একমাস গ্রাম থেকে নগরে চলে কঠিন চীবর দানের আয়োজন। কঠিন চীবর উপলক্ষে প্রতিটি বিহারের উপাসক-উপাসিকামন্ডলী দুই তিন মাস আগে থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নেমে পড়ে। বিহারে বিহারে চলে উৎসবের আমেজ। সকালে পি-দান ও পূজাপর্বের কাজ শেষ করে বিকেলে চলে কঠিন চীবর দান, ত্রিপিটক থেকে বিশদ বর্ণনা এবং সমাজ-সদ্ধর্ম উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা।
কঠিন চীবর দানে অংশগ্রহণ করেতে ধর্মালোচক, ভিক্ষুসংঘ ও অতিথিরা দলেদলে ছুটে আসেন। কেউ ধর্মদান করে কেউ ধর্মশ্রবণ করে। কঠিন চীবর দানকে কেন্দ্র করে সামাজিক দায়িত্বও পালন করে থাকে। শিশু-কিশোরদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, এছাড়া বড়দের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা যেমন থাকে তেমনি থাকে যারা দীর্ঘ বছর ধরে সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে অবদান রাখে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জানানো হয় সম্মাননা-সংবর্ধনা এবং বিগত একবছরে যারা প্রয়াত হন তাদের বিশেষভাবে স্মরণ করে পুণ্যদান করাও কঠিন চীবর দানের অন্যতম অনুষঙ্গ। এ জাতীয় কাজগুলো যত বেশি করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ ভালো কাজের অনুপ্রাণিত করার চেয়ে মহৎ আর কিছু নেই।
[লেখক : প্রাবন্ধিক]
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
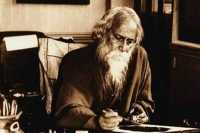
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম
-
রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়
-
মে দিবসের চেতনা বনাম বাস্তবতা
-
শ্রম আইন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই আন্তরিকতা
-
বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা কেন এত পিছিয়ে
-
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল : নিরাপদ যাত্রার প্রত্যাশা
-
কর ফাঁকি : অর্থনীতির জন্য এক অশনি সংকেত
-
১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় : উপকূলীয় সুরক্ষার শিক্ষা
-
যখন নদীগুলো অস্ত্র হয়ে ওঠে









