মতামত » উপ-সম্পাদকীয়
অগ্নিমূল্যের বাজার : সাধারণ মানুষের স্বস্তি মিলবে কি?
রেজাউল করিম খোকন
বাজেটে নতুন অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। অথচ গত মাসেও মূল্যস্ফীতির হার ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। তাই বাজেটে মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি কতটা বাস্তবভিত্তিক, সেটি যথেষ্ট প্রশ্নসাপেক্ষ। সারা বিশ্বে মূল্যস্ফীতি যেভাবে কমে আসছে, সেভাবে কমাতে পারছে না এখানে।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপই কাজ করেনি। মুদ্রানীতি, রাজস্ব নীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনার সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ চোখে পড়েনি। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ মূল্যস্ফীতির চাপে পিষ্ট। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ব্যাংকঋণের সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। এতে করে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যাংকঋণের সুদের হার সহনীয় পর্যায়ে আনতে জোর দেওয়া প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সব নীতি কাজে লাগছে না দেশে। তাই মূল্যস্ফীতি কমাতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
পাশাপাশি চাকরি-বাকরি দরকার। তার জন্য বিনিয়োগ লাগবে। টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে পুনর্ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। ভূরাজনৈতিকসহ বিভিন্ন কারণে চীন থেকে অনেক দেশের বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগ সরিয়ে নিচ্ছে। এসব বিনিয়োগ থেকে কোন কোন শিল্প আমাদের দেশে আনতে পারি, সে বিষয়ে পরিকল্পনা করা উচিত। পাশাপাশি রপ্তানি আয় বাড়াতেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
ধরা যাক, আগামী পাঁচ বছরে আমরা ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে চাই। কোন কোন খাত থেকে এই রপ্তানি আসবে, সেটি প্রথমে চূড়ান্ত করতে হবে। তারপর লক্ষ্য অর্জনে যা যা দরকার, সেসব করতে হবে। যখনই লক্ষ্য অর্জনে সময় দেওয়া হয় না, তখন তা ব্যর্থতায় পরিণত হয়ে থাকে।
প্রস্তাবিত বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় বাজেট-ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা বেশ কমানো হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সহায়ক। এটা সরাসরি মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়ক হবে। লক্ষ্যমাত্রা কমানোর পরেও প্রস্তাবিত বাজেটে-ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা বেশ বড়ই রয়ে গেছে। এজন্য ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়ার বড় লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে তা বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করবে। ফলে এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপরেও চাপ তৈরি করবে। নতুন বাজেটে আরও কিছু বিষয়, যেমন সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, উৎসে করকে ন্যূনতম কর পরিগণনা রহিতকরণ, আর্থিক খাতে বিকল্প উৎস তৈরি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত পরিস্থিতির উত্তরণ, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর কমানো ও সিএমএসএমই খাতের জন্য পৃথক ট্যাক্স কোড গঠনের মতো কিছু ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে।
প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি, স্থানীয় শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, করজাল সম্প্রসারণ, ঘাটতি মেটাতে আর্থিক খাত-নির্ভরতা কমানোর ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য বাজেট-ঘাটতি যেমন কমানো হয়েছে, তেমনি করহার না বাড়িয়ে করের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টাও আছে সেখানে।
সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, নতুন বাজেট অগ্নিমূল্যের বাজার থেকে স্বস্তি দেবে। মধ্যবিত্তের আশা, টিসিবির ট্রাকের পেছনে মুখ লুকিয়ে আর দাঁড়াতে হবে না। বেসরকারি খাতের প্রত্যাশা, ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় কমবে, বিনিয়োগ বাড়বে। প্রশ্ন হচ্ছে, সবার আশা কি পূরণ করতে পারবে এই বাজেট? টানা দুই বছর মানুষ কষ্ট করছে। তাই আশার আলোর সন্ধানে সবাই; কিন্তু টানেলের শেষে কি আশার আলো দেখা যাচ্ছে?
এদিকে সুদের হার বাড়ানোর কারণে ব্যবসার ব্যয় বেড়েছে। তাতে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ব্যবসার খরচ কমাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। নীতি ও বিধিবিধানের অনিশ্চয়তা, ধারাবাহিকতার অভাব এবং অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া হঠাৎ হঠাৎ নীতি পরিবর্তন করা- এসবই বিনিয়োগকারীদের বড় অভিযোগ। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই ধীরগতির ও উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন। ফলে তা ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে খুব বেশি সহায়তা করে না।
রাজস্ব বাড়াতে দেশে একটি প্রগতিশীল করকাঠামো থাকা দরকার, যেখানে প্রত্যক্ষ করের ওপর বেশি নির্ভরশীলতা এবং পরোক্ষ করের ওপর কম নির্ভরশীলতা থাকবে। এছাড়া করজাল সম্প্রসারণেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। যাঁরা কর ফাঁকি দেন বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের নিয়ন্ত্রণে কঠোর হতে হবে। অন্যদিকে আমদানি শুল্কের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো দরকার। বিভিন্ন খাতে যেসব কর অব্যাহতি সুবিধা রয়েছে, সেগুলোকে যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত ও যুক্তিযুক্ত করা কিংবা বাদ দেওয়া উচিত।
বর্তমান পটভূমিতে উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগ বাড়ানো আবশ্যক। কারণ আমরা যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলছি, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ছাড়া তা অর্জন করা ও টেকসই করা যাবে না। ফলে আসন্ন বাজেটে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এর মাধ্যমে দেশের তরুণেরা চাকরির বাজারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রায়ই নিয়োগকর্তারা চাকরির জন্য যোগ্য তরুণদের খুঁজে পান না। ফলে বাজেট হওয়া উচিত শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দও বাড়াতে হবে।
দেশের উন্নয়নের গল্পে নীতিনির্ধারকেরা সব সময় মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির কথা বলেন; কিন্তু শুধু জিডিপির প্রবৃদ্ধি দিয়ে চলমান অর্থনৈতিক সংকট কমবে না। তাই নতুন বাজেটে জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে মূল লক্ষ্য না করে বরং সংকট মোকাবিলায় বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপের মধ্যে রয়েছি। এছাড়া আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয় বা সম্পদের প্রাপ্যতার পরিমাণও কম। ফলে বাজেট কোনোভাবেই সম্প্রসারণমূলক করা উচিত হবে না। অন্যথায় বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে যে ধরনের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নিয়েছে, তা কাজ করবে না। যেসব প্রকল্পের কাজ শেষপর্যায়ে রয়েছে, সেগুলো দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থনীতির এ সংকটময় অবস্থায় সরকারের প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয় কমানো প্রয়োজন।
বিরূপ আবহাওয়ার কারণে কৃষি খাতের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা দীর্ঘ মেয়াদে বেড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। এই যে পরিবেশ পরিবর্তন হচ্ছে, মাছ মরে যাচ্ছে, শ্রমিকেরা ধান কাটতে যাচ্ছেন না- এমন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেসরকারি খাতের প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ফসল রোপণ ও তোলা সম্ভব। এসব খাতে বাজেটে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।
বিশ্বের চাষাবাদযোগ্য ভূমির মাত্র শূন্য দশমিক ১ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশে। এ অল্প পরিমাণ আবাদযোগ্য ভূমি নিয়ে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২ দশমিক ৭ শতাংশের খাদ্যের সংস্থান করতে হয় বাংলাদেশকে। এর মধ্যে ধান ও মাছসহ কৃষির নানা খাতে প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। বিদেশে রপ্তানির জন্য দেশের কৃষি খাত প্রস্তুত হয়নি, আমাদের কোনো অবকাঠামো নেই। কৃষিতে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির বিকল্প নেই। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৩৭ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১০০ কোটি ডলারে। তবে গত দুই দশকে দেশে ধান উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার অনেক কমেছে। লাভ কম হওয়ায় ধান উৎপাদনকারী কৃষকেরা বেশি দরিদ্র থাকছেন।
[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]
-
নতুন সরকারের কাছে পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা
-
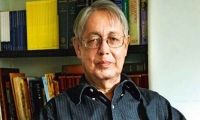
আন্দ্রে বেতেই : মানবিক সমাজবোধের অনন্য উত্তরাধিকারী
-
‘নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস’
-
মহাকাশ অর্থনীতি
-
কুষ্ঠ : নতুন সরকার ও একটি জাতীয় বিষয়ে প্রত্যাশা
-
বাংলাদেশের খাদ্যশিল্প
-
ভাষার রাজনীতি এবং রাজনীতির ভাষা
-

দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী
-

মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষায় সমতা নিশ্চিতের আহ্বান
-
কৃষিপণ্যের মূল্য শৃঙ্খলে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন
-

নির্বাচনে জোট, নাকি সরকারে
-
রমজান সামনে রেখে নিত্যপণ্যের বাজার
-
মানুষ কি বদলেছে, নাকি শুধু রং বদলিয়েছে?
-
সময় জীবনে চলার পথ দেখিয়ে দেয়
-
কালো ও সবুজ চা : জনস্বাস্থ্যগত গুরুত্ব
-
বাঙালিরা ধর্মভীরু কিন্তু ধর্মান্ধ নয়
-
অন্তর্বর্তী সরকার জাতিকে কী দিল
-
ভালোবাসা, সচেতনতা ও জনস্বাস্থ্য বাস্তবতা
-
ভালোবাসার দিনে সুন্দরবন: উদযাপনের আড়ালে অস্তিত্বের সংকট
-

তিরাশির সেই দিন
-
অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নতুন সরকারকে
-
সবুজ অর্থনীতির পথে বাংলাদেশ: সম্ভাবনা, সংকট ও করণীয়
-
গণতন্ত্র: একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা
-
‘ভোট দিছি ভাই, ছিল দিছি...’
-
নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ব্যবধান
-
ক্ষমতার অক্টোপাস: রাষ্ট্র দখল ও আমজনতার নাভিশ্বাস
-
কার হাতে উঠবে শাসনের রাজদণ্ড
-
নির্বাচন ও সাধারণ ভোটারের ‘অসাধারণ’ সামাজিক চাপ








