মতামত » উপ-সম্পাদকীয়
ব্যাংক খাতের সংস্কার
রেজাউল করিম খোকন
ব্যাংকিং খাত অর্থনীতির প্রাণ। দেশের আর্থিক খাত খুব একটা বড় নয়, পুঁজিবাজার দুর্বল, ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতও শক্তিশালী নয়; সে কারণে অর্থের ৯০ শতাংশই ব্যাংক খাত থেকে আসে। স্বাধীনতার পর দেশের উদ্যোক্তাশ্রেণী তৈরি করেছে এই ব্যাংক খাত। কিন্তু এই খাত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়েছে। ক্যামেলস রেটিং অনুসারে ব্যাংকের স্বাস্থ্য পরিমাপের যেসব সূচকÑ যেমন মূলধন পর্যাপ্ততা, তারল্য, খেলাপি ঋণ, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, এসব ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিপালিত হয় না। যদিও আলোচনা কেবল খেলাপি ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০০৮ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা; ২০২৪ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকায়। মূলধনের পর্যাপ্ততা আরেকটি বড় সমস্যা। আন্তর্জাতিক নীতিমালা বা ব্যাসেল অনুযায়ী যে পরিমাণ মূলধন থাকার কথা, তা কিন্তু সবাই মানতে পারে না। বিশেষ করে ১০-১২টি ব্যাংকের এই মূলধন অপর্যাপ্ততা আছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা।
আইনে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকলেও বাস্তবে তা অতটা পরিপালিত হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সেই স্বাধীনতা প্রয়োগ করা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব নয়। গভর্নর নীতিপরায়ণ হলে তার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োগ করা সম্ভব, তিনি ততটুকু করতে পারেন। কিন্তু সেটা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক আইনে বলা আছে, সরকারের কোনো কর্মকর্তা গভর্নর বা ডেপুটি গভর্নর হতে পারবেন না; কিন্তু পরপর দুজন গভর্নর আমলাতন্ত্র থেকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন টাস্কফোর্স করেছে, তারা এ লক্ষ্যে কাজ করবে বলে আশা করি। এছাড়া গত মে মাসে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করাসহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি দুই ধরনের হয়, এক ধরনের কোম্পানি দুর্বল ব্যাংকগুলোর সম্পদ অধিগ্রহণ করে এবং দুর্বল ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যায়। আরেকটি হলো, দুর্বল ব্যাংকের সম্পদ কিনে পরবর্তীতে ফেরত দেয়া হয়। তখন শঙ্কা থেকে যায়, আবারও সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য এই কাজে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নেয়া যেতে পারে।
ঋণ শ্রেণীকরণ, পুনঃতফসিল, অবলোপন এসব নিয়মকানুন বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২২ সালে এসব নিয়মকানুন শিথিল করা হয়েছে। এতে কী ফল হয়েছে, তা আমরা জানি না; কিন্তু যা হয়েছে, তা হলো সমস্যার স্তূপ তৈরি হওয়া। এসব খাতে আমাদের সংস্কার দরকার। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করি। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর একসময় অর্থনীতিবিদ হিসেবে যেসব কথা বলেছেন এখন সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে অনেক ধরনের উদারনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতেও বিশেষ কাজ হয়নি; বরং একধরনের দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। আমরা দুর্বৃত্তায়নমুক্ত, সচল ও টেকসই ব্যাংকিং খাত দেখতে চাই। এই খাতে দীর্ঘদিন ধরে যে জঞ্জাল তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংককে এখন তা দূর করতে হচ্ছে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ দরকার। ব্যাংকিং খাতকে অর্থনীতির মূল নিয়ামক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে টেকসই ব্যবস্থা নেয়ার বিকল্প নেই। সেজন্য কাঠামোগত দুর্বলতা আমলে নিতে হবে।
বিদায়ী সরকারের আমলে বাংলাদেশে অনেক ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও পর্ষদ সদস্য রাজনৈতিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে কেউ কেউ এমন সুবিধা পেতেন যে সবাই সেই প্রতিযোগিতায় সক্ষম থাকতেন না। রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাওয়া একটি পরিবার আট-নয়টি ব্যাংকের মালিকানা পেয়েছে। সেটি কীভাবে সম্ভব? অথচ বলা হচ্ছে, ব্যাংকে একটি পরিবারের শেয়ার ১০ শতাংশের বেশি হতে পারব না। রাজনৈতিক কারণে কিছু ভালো ব্যাংক দুর্বল হয়েছে। কিছু ব্যাংকের উদ্দেশ্য ভালো ছিল, কিন্তু নানা কারণে দুর্বল হয়েছে। এজন্য ব্যাংকের পূর্বাবস্থা যাচাই-বাছাই করে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। একটু সহায়তা দিলে কিছু ব্যাংক ঘুরে দাঁড়াবেই। তাই ব্যাংক খাত সংস্কারে সময়ক্ষেপণ করা উচিত হবে না।
ব্যাংক খাতের ক্ষতির প্রভাব পড়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে। ১৫ বছর আগে ব্যাংক খাত যে অবস্থায় ছিল, ১৫ বছর পর এসে সেই অবস্থায় নেই। ব্যাংক চলেছে মুদি দোকানের মতো। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই পর্যন্ত ১১টি ব্যাংকের পর্ষদ পরিবর্তন করা হয়েছে। এই যে এতগুলো ব্যাংকে লুটপাট হয়ে গেল, সেখানে এমডিরা কী করেছেন? তাদের সততা কোথায় ছিল? বর্তমানে ব্যাংক খাত যে অবস্থায় আছে, তাতে কিছু ব্যাংকের জন্য লভ্যাংশ বিতরণ কয়েক বছরের জন্য বন্ধ করে দেয়া দরকার। এছাড়া ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতেও বড় ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এ খাতের জন্য আলাদা কিছু নীতিও দরকার, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বন্ধ করে দেয়ার কথা হয়েছে। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে থাকতে হবে। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মতো আরেকটি বিভাগ থাকলে স্বার্থের গুরুতর সংঘাত সৃষ্টি হয়।
ব্যাংক খাত রুগ্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের মনে একধরনের ভীতি আছে। অনেকেই জানতে চান, কোন ব্যাংকে টাকা রাখা নিরাপদ? নতুন সরকার আসার পর মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি হলেও অনিশ্চয়তার বোধ এখনো আছে। সেজন্য বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। এছাড়া কোনো ব্যাংককে ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, সে রকম পরিকল্পনা নেই। যত রুগ্নই হোক, কোনো ব্যাংককে মরতে দেয়া হবে না। সেটা হলে পরিষ্কার বার্তা দেয়া দরকার; তা না থাকলেও পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত। সেই সঙ্গে শক্তিশালী ব্যাংক কোনগুলো, তা বলা উচিত। রুগ্ন ব্যাংক টিকিয়ে রাখা হলে ভালো ব্যাংকেও এর প্রভাব পড়ে। এ খাত মানুষের আস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১০০ থেকে ১ হাজার টাকা ঋণ তৈরি হয়, অর্থাৎ পুরো বিষয়টি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ভালো ব্যাংকও যে কোনো সময় ধসে যেতে পারে। সেজন্য সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে পরিষ্কার বার্তা থাকা উচিত, কোন ব্যাংকগুলো কী অবস্থায় আছে। ব্যাংক তদারকিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও দক্ষতা দেখাতে হবে। আইনকানুন পরিপালনে কাউকে ছাড় দিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রথা তুলে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিবেচনায় সব ব্যাংকের পরিচালকদের এক কাতারে রাখতে হবে। যখন যা সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, তা নিতে হবে। তাহলে এর সুফল পাবে দেশের অর্থনীতি।
[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]
-
প্রসঙ্গ: খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল
-
নতুন সরকারের কঠিন সমীকরণ
-
ভাষাপ্রকৌশল ও কালচারাল হেজিমনি: শব্দের আড়ালে ক্ষমতার রাজনীতি
-
মানবদেহে রোজার সুফল
-
নিরাপদ সড়কের দাবি
-
ভাষা, স্বাধীনতা ও সাহিত্য : ইতিহাস থেকে সমকাল
-
অপাহাড়ি প্রতিমন্ত্রী ও শান্তিচুক্তি
-

মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন!
-
চেকের মামলায় ভুল ঠিকানায় নোটিস
-
শান্তির স্বপ্ন বনাম বাস্তবের দোলাচল
-

ভাষা আন্দোলন বাঙালির বিপ্লব ও আন্দোলনের ভ্যানগার্ড
-
বিয়ে রেজিস্ট্রি কেন জরুরি
-
ভাষা নিয়ে ভাসাভাসা কথা
-
বিএনপি পাস, জামায়াতও পাস
-
ব্যালট থেকে বাস্তবতায় বিএনপি
-

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: একুশের ইতিহাস, বিশ্বস্বীকৃতি ও আমাদের দায়িত্ব
-
ফুলের নিচে চাপা পড়া ভাষার আর্তনাদ
-
নতুন সরকারের কাছে পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা
-
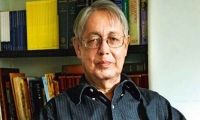
আন্দ্রে বেতেই : মানবিক সমাজবোধের অনন্য উত্তরাধিকারী
-
‘নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস’
-
মহাকাশ অর্থনীতি
-
কুষ্ঠ : নতুন সরকার ও একটি জাতীয় বিষয়ে প্রত্যাশা
-
বাংলাদেশের খাদ্যশিল্প
-
ভাষার রাজনীতি এবং রাজনীতির ভাষা
-

দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী
-

মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষায় সমতা নিশ্চিতের আহ্বান
-
কৃষিপণ্যের মূল্য শৃঙ্খলে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন
-

নির্বাচনে জোট, নাকি সরকারে







