উপ-সম্পাদকীয়
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ
বাংলাদেশে কারাগারব্যবস্থা চালু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত এবং প্রমাণের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার পন্থা হিসেবে উপমহাদেশে কারাগারব্যবস্থার উৎপত্তি করে ব্রিটিশরা। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যেগুলোকে আইনের মোড়কে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, সে কার্যকলাপগুলো সংঘটন করলে একজন ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং শাস্তি হিসেবে কারাগারে বন্দী রাখা হয় কিংবা অর্থ দ-সহ বিভিন্ন গুরু ও লঘু দ- দেয়া হয়। আবার, অনেকের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে কিন্তু অপরাধ শুনানি ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, তাদেরকেও কারাগারে বিচারকি হাজতি হিসেবে বিচারের জন্য অপেক্ষমাণ বন্দী রাখা হয়। যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়, তারা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থাকেন, তারপর মুক্তি পান। আর যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয় না তারাও কোর্টের নির্দেশে কারাগার থেকে মুক্তি পান। এক্ষেত্রে, আইনের প্রণিধানযোগ্য নীতি হলো-‘দোষী সাব্যস্ত বা প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিদোর্ষ’। কেননা অপরাধী নিজেও তার অপরাধকৃত কর্ম সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অধিকারী হয়ে ওঠে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধ প্রমাণিত হয়, একজন ব্যক্তিকে নিরপরাধ হিসেবেই ভাবা হয়। তবে বিচারিক হাজতি বা দ-প্রাপ্ত আসামি উভয়কেই কারাবরণ করতে হয়, যা সংস্কারের দাবি রাখে।
আজ থেকে ১৩০ বছর আগে ১৮৯৪ সালে অবহেলিত ভারতবাসীর জন্য ব্রিটিশরা যে আইন তৈরি করে গেছে, সেই আইনটি এখনও বলবৎ রয়েছে। বাংলাদেশের কারাগারে কয়েদিরা খুবই মানবেতর জীবনযাপন করে থাকেন। জেলখানা বা কারাগারে বসবাসের চিত্র খুবই ভয়াবহ। এখানে সুস্থ স্বাভাবিক বসবাসের কোন পরিবেশ নেই। অত্যন্ত ঘনত্বের মধ্যে গাদাগাদি করে থেকে আসামিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কারাগার কমবেশি প্রায় ৮০টি আছে। এর মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার, বাকিগুলো জেলা কারাগার। এসব কারাগারে বন্দী ধারণক্ষমতা ৫০ হাজার জন, কিন্তু আছে তার প্রায় দ্বিগুণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে তারও বেশি। কারা ফেরত বন্দীদের অভিযোগ রয়েছে এবং বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় কারাগারের নানা অনিয়ম নিয়ে অনেকবার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। বন্দীদের ভাষায়, কারাগারের ভিতরটা হলো একটি অবৈধ ব্যবসা কেন্দ্র। সেখানে কয়েদিদের রয়েছে নানা সিন্ডিকেট। আছে কারাগারের কিছু অসাধু কর্মকর্তা। কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্লক লিজ দেয়ার অভিযোগও রয়েছে। কারাগারে যারা বন্দী হিসেবে যান, তারা কোথায় থাকবেন, কতটা ভালো থাকবেনÑ তা নির্ভর করে তাদের ওপর অর্থাৎ তাদের টাকার ওপর কিংবা বাইরে থেকে প্রর্দশিত প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ প্রভাবের ওপর। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই অপরাধ মোকাবিলার জন্য বন্দী অধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারেÑ যেখানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি, মানবাধিকার কমিশনের সদস্য, দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য, সরকারের প্রতিনিধি, দেশের স্বনামধন্য মিডিয়া ব্যক্তিসহ এবং কমিশনের পর্যাপ্ত জনবল থাকবে যাতে দেশের সবগুলো কারাগার যে কোন সময় পরিদর্শন করার আইনগত অধিকার ও সক্ষমতা থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশ তদন্ত শেষ করতে না পারলে একজন অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে বিবেচনা করতে হবে। কেননা, চার্জশিট না আসা পর্যন্ত একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল প্রসিডিং আরম্ভ হয় না এবং তিনি তখন পর্যন্ত নির্দোষও বটে এবং সাজাপ্রাপ্ত নন। একজন অভিযুক্তকে তার মৌলিক অধিকার এবং তার পরিবারের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। অথচ অনেক কোর্টে শুনানিকালে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উক্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না। এর অর্থ হলো এটাই যে, আমরা একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং তার জীবনের স্বর্ণালী সময়গুলোকে সম্মান করতে ব্যর্থ হচ্ছি এবং অবহেলা করছি। এর ফলশ্রুতিতে মানবতা হচ্ছে ভূলুণ্ঠিত ও দলিত। রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে তাকে কোন অবস্থাতেই উন্নয়নশীল অথবা কল্যাণকামী রাষ্ট্র বলা যাবে না।
সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কিশোর-কিশোরীরা। কিন্তু নানা কারণে কিছু কিশোর অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বা ভবঘুরে অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এইসব কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে গঠিত হয় কিশোর অপরাধ সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রসমূহ। এসব প্রতিষ্ঠান কিশোরদের সংশোধন, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সংকট, মানবসম্পদ ঘাটতি ও কার্যকরী নীতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই এই নিবন্ধে এসব কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম এবং সেবার মান উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো। বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন কিশোর সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রের বেশির ভাগই সরকার পরিচালিত। কিছু বেসরকারি সংস্থাও এ ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ কেন্দ্রে দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত কর্মী এবং মানসম্মত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুরা এখানে নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়। চিকিৎসা, শিক্ষা ও মানসিক সহায়তা ব্যবস্থার অভাব এসব কেন্দ্রে সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি কিছু কেন্দ্রের পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবন পুনঃনির্মাণ অথবা সংস্কার করা হয়েছে। নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উন্নত ঘর, শোবার ঘর, শৌচাগার ও পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সিসিটিভি, নিরাপত্তা প্রাচীর ও গেট সিস্টেম চালু করে নিরাপত্তাব্যবস্থাও উন্নত করা হচ্ছে। কিশোরদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে কিছু কেন্দ্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, কারিগরি শিক্ষা যেমনÑ হস্তশিল্প, দর্জিবিদ্যা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কৃষিশিক্ষা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে যাতে সংশোধনের পর তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। অনেক কেন্দ্রে এখন নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা চালু হয়েছে। কিছু কেন্দ্রে মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করা হয়েছে যাতে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। কেন্দ্রগুলোতে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং দলগত কাজ শেখানো হচ্ছে। এসব কার্যক্রম শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিশোরদের সমাজে পুনরায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবারভিত্তিক পুনর্মিলনের কাজ শুরু হয়েছে।
এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের কারাগারব্যবস্থা ধীরে ধীরে একটি মানবিক ও পুনর্বাসনমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।
বর্তমানে দেশের কারাগারে বন্দীদের বড় অংশই বিচারাধীন। এই সংখ্যা কমাতে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, ভার্চুয়াল কোর্ট ব্যবস্থার প্রসার, এবং জামিনপ্রাপ্তদের দ্রুত মুক্তি দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। হালকা অপরাধে কারাদ- না দিয়ে বিকল্প শাস্তি যেমনÑ সমাজসেবা, প্রোবেশন, বা আর্থিক জরিমানা কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে করে কারাগারে অতিরিক্ত চাপ কমবে এবং অপরাধীদের পুনর্বাসন সহজ হবে। কারা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো এবং বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ শেখাতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রস্তাব বাস্তবায়ন আবশ্যক। একইসঙ্গে বন্দীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ বন্ধে কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অনেক পুরনো কারাগার ভবন সংস্কার, নতুন ভবন নির্মাণ, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নিশ্চিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন আবশ্যক। একইসঙ্গে সব কারাগারে সিসিটিভি, বায়োমেট্রিক সিস্টেম, ও ডিজিটাল নজরদারি চালুর উদ্যোগ নেয়া দরকার। নারী বন্দীদের নিরাপত্তা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভবতী বন্দীদের জন্য বিশেষ যতœ, এবং শিশুদের জন্য পৃথক খেলার ও শিক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে শাস্তি নয় বরং উদার ও নৈতিক সহযোগিতা ও আধুনিক সেবাকে অগ্রাধিকারের প্রস্তাবনা ও তার বাস্তবায়ন আবশ্যক।বন্দিদের জন্য টেকসই প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য আরও কার্যকর পরিকল্পনার সুপারিশ বাস্তবায়ন আবশ্যক। এতে করে তারা মুক্তির পর অপরাধজগতে না ফিরে সমাজে একটি সম্মানজনক জীবন শুরু করতে পারবেন। ১৮৯৪ সালের পুরনো কারা আইন এখনও ব্যবহার হচ্ছে। এই আইনের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী সংশোধনের মাধ্যমে বন্দিদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের দাবি উঠেছে।কারা সংস্কারে বেসরকারি সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার সুপারিশ রয়েছে, যাতে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় থাকে।
বাংলাদেশের কারা হাসপাতাল ও সেলবন্দী (বন্দীশালায় আটক) বন্দীদের উন্নত চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় বাংলাদেশের কারাগারগুলোর মধ্যে অনেক কারাগারেই নিজস্ব হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে, যেগুলোর দায়িত্ব সাধারণত কারা কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হয়। তবে বেশির ভাগ কারা হাসপাতাল এখনো পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাকর্মীর সংকটে ভুগছে। সাধারণ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কিছুটা সহজলভ্য হলেও গুরুতর অসুস্থতা দেখা দিলে উন্নত চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সেলবন্দী বন্দীদের ক্ষেত্রে (যাদের বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয় বা হাই-প্রোফাইল বন্দি হিসেবে গণ্য করা হয়), চিকিৎসার প্রাপ্তি আরও সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে কারা কর্তৃপক্ষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে যেমন কাশিমপুর, কেরানীগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নত চিকিৎসা সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট মেডিকেল ইউনিট, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, নার্স ও ফার্মেসি চালু করা হয়েছে। তবুও, যে সংখ্যক বন্দী রয়েছে, সেই তুলনায় চিকিৎসাসেবার পরিমাণ ও মান অনেক কম। সেলবন্দী বন্দীদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপ, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হাঁপানি, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগে ভুগে থাকেন। এদের জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হলে সাধারণত সরকারি অনুমতি নিয়ে বাহিরের হাসপাতালে প্রেরণ করতে হয়, যা প্রক্রিয়াগত জটিলতায় ধীর হয়ে পড়ে। অনেক সময় মানবিক বিবেচনায় উচ্চ আদালতের নির্দেশে গুরুতর অসুস্থ বন্দীদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), বা ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। কারা সংস্কারের অংশ হিসেবে বন্দীদের চিকিৎসা অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজন চিকিৎসাকেন্দ্রের আধুনিকায়ন, পর্যাপ্ত মেডিকেল অফিসার নিয়োগ, এবং জরুরি অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য একটি কার্যকর ও দ্রুত ব্যবস্থা। বন্দীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে চিকিৎসাসেবা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি একটি মৌলিক অধিকার, যা কারাগারের ভেতরেও পূরণ হওয়া উচিত।
ওপরের প্রস্তাবনা ও সংস্কার কার্যক্রমে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আছে। উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছেÑ প্রশিক্ষিত জনবল ও মনোবিজ্ঞানীর অভাব; বাজেট ঘাটতি ও সঠিক তদারকির অভাব; শিশুদের প্রতি কিছু কর্মীদের অবমাননাকর আচরণ; সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব; কিশোর অপরাধীদের অপরাধী হিসেবে দেখার প্রবণতা। এসব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে সেবার মান বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপনিতে হবে। পরিশেষে বলতে পারি যে, কারাগার কিশোর সংশোধাগার, ভবঘুরে কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্র, যাই বলি না কেন, বন্দী জীবনের গ্লানিতে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে যথার্থ মানবিক দৃষ্টিতে দেখা হলে এবং তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হলে আশ্রয় কেন্দ্র ও সংশোধনাগার পরিণত হবে নিরাময় কেন্দ্র হিসেবেÑ যার সুবাদে অনেকেই সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। অযতœ আর অবহেলার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি ওই সব প্রতিষ্ঠানে কোন সভ্য, সচেতন ও সুস্থ্য মানুষ সেবা দিতেও আগ্রহী হবে না। কাজেই এহেন অসুস্থ ধারার পরিবর্তনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নাগরিক সমাজÑ সবাই যদি মানবিকতা, মূল্যবোধ ও নিয়মের অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে সাম্যের, ভ্রাতৃত্বের, সৌহার্দ ও সহযোগিতার। অন্যথায় নিষ্ঠুরতার থাবায় মলিন হবে বাংলাদেশ। বৃদ্ধি পাবে পাশবিকতা। হারিয়ে যাবে মায়া-মমতা ও মানবিকতা। হিং¯্রতা ও নৈরাজ্যে টালমাটাল হবে সমাজ ও রাষ্ট্র। আসুন, সুন্দর কারা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কিশোর সংশোধাগার ভবঘুরে কেন্দ্রের অবকাঠামো নিশ্চিত করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবার দিকে নজর দিয়ে এবং সরকারি পরিকল্পনা ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানবিক বাংলাদেশ গঠনপূর্বক বিশ্বের কাছে আমাদের মহান করে তুলি।
[লেখক : সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি]
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
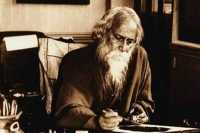
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম
-
রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়







