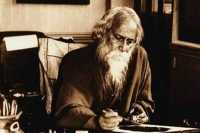উপ-সম্পাদকীয়
বরেন্দ্রর মাটিতে আমের বিপ্লব : সম্ভাবনা ও সতর্কবার্তা
সামসুল ইসলাম টুকূ
বহুদিন পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে পার্বতিপুর, আড্ডা ও পোরশা হয়ে সাপাহার যাচ্ছিলাম বাসে। আড্ডা থেকে সাপাহার পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথজুড়ে দুপাশে যতদূর চোখ যায়, কেবল ঘন আমবাগান। অধিকাংশই বামন আকৃতির হাইব্রিড আম্রপালি জাতের গাছ, কিছু বারি-৪ জাতেরও রয়েছে। ছোট ছোট গাছে গুটি আমে ভরপুরÑকোথাও যেন কোনো ফাঁক নেই। এই দৃশ্য দেখে মনে হতে পারে, যেন আমগাছগুলো প্রাকৃতিকভাবেই গজিয়ে উঠেছে। বাস্তবে, এটাই এখন এ অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। সবুজের এই বিস্তারে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাত্র এক সপ্তাহ পরেই পাকা আমের মৌসুম শুরু হবে।
মাত্র ত্রিশ বছর আগেও বরেন্দ্র অঞ্চলে এমন সবুজ দৃশ্য ছিল কল্পনার অতীত। বর্ষা মৌসুমের তিন মাস ছাড়া বাকি সময়জুড়ে খোলা প্রান্তর, কাটা ধানের শুকনো থোড় আর গাছহীন রুক্ষ ভূমি ছিল এখানকার চিত্র। সুপেয় পানির ছিল তীব্র সংকট। এই সংকট মোকাবিলায় তৎকালীন হিন্দু জমিদাররা ব্যাপক পুকুর খনন করেন, যা বরিন্দবাসীর জীবনযাত্রার একমাত্র ভরসা ছিল। দু-চার গ্রাম মিলিয়ে একটি নলকূপ থাকত, তা-ও গভীর পানির স্তর ও পাথরের কারণে অধিকাংশ সময় অচল থাকত। ফলে জনবসতি ছিল অল্প।
১৯৮০ সালে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা মত দেন, ভূপৃষ্ঠের নিচে পাথরের স্তর থাকায় পানি উত্তোলন সম্ভব নয়, ফলবান গাছ জন্মাবে না এবং বরেন্দ্র ভূমি দ্রুত মরুভূমিতে পরিণত হবে। এই আশঙ্কায় জাতীয় পত্রপত্রিকায় বিস্তর প্রতিবেদন প্রকাশ হয়, জনমনে তৈরি হয় উৎকণ্ঠা। কিন্তু বিএডিসির কিছু তরুণ প্রকৌশলী এই ধারণা আমলে না নিয়ে নিরবচর্চা চালিয়ে যান। তাদের বিশ্বাস ছিলÑপাথর কেটে হলেও পানি তোলা সম্ভব। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৮৫ সালে সেই মুহূর্ত এল, যখন মাটির নিচ থেকে ফল্গুধারার মতো পানি উঠে এল। এই সাফল্যের নেপথ্যে ছিলেন প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, রঞ্জন মিত্র প্রমুখ। বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প তখন অনুমোদন পায়। শুরু হয় গভীর নলকূপ স্থাপন ও বনজ বৃক্ষরোপণ।
প্রথমদিকে কেউ ভাবেনি, এই জমিতে আম চাষ হবে। বনজ গাছ দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও ধীরে ধীরে বন কেটে আমের বাগান গড়ে ওঠে। বর্তমানে পোরশা ও সাপাহার উপজেলায় প্রচুর ইউক্যালিপটাস গাছ থাকলেও তার স্থানে এখন আমগাছের চাষ হচ্ছে। মাত্র এক দশকে এ অঞ্চল দুই ফসলি হয়েছে; আম, ধান ও বনজ গাছ মিলিয়ে সবুজের সমারোহ তৈরি হয়েছে। মরুকরণের পূর্বাভাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে।
যদিও ধান উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু সেচ, সার ও কীটনাশকের খরচ এবং ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেননি। এর বিপরীতে পরীক্ষামূলকভাবে আম চাষে আগ্রহ বাড়ে। হাইব্রিড জাত আম উদ্ভাবন ও গবেষণা কেন্দ্রের ভূমিকা, সহজ পরিচর্যা এবং উচ্চ মূল্য কৃষকদের আম চাষে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে পোরশা ও সাপাহারে প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে আমবাগান রয়েছে, যা পুরো কৃষিজমির প্রায় ৪৫ শতাংশ। প্রতিটি বাগান ঘেরা বাঁশ, তারের জাল বা মাছ ধরার জালে। অন্য উপজেলাগুলোর তুলনায় এই দুই উপজেলায় আমচাষ সবচেয়ে বিস্তৃত।
তবে এখানে শতবর্ষী আমগাছের পরিবর্তে স্বল্পায়ু হাইব্রিড জাত চাষ হচ্ছে, যেগুলো ১০ বছরের বেশি ফলন দেয় না। ফলে পুরনো জাতের সংরক্ষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে এ নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৪ মেট্রিক টন আম উৎপন্ন হচ্ছে। এতে পোরশা ও সাপাহারে বার্ষিক উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে আম চাষে এক বিপ্লব ঘটেছে। কৃষকদের ভাষায়, ধানের তুলনায় আমের পরিচর্যা সহজ, লাভও বেশি। তবে এই সাফল্যের বিপরীতে খাদ্যনিরাপত্তার নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছেÑধানের জমি কমে যাচ্ছে। দুই উপজেলায় ধান উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।
অন্যদিকে আম উৎপাদন আগামী পাঁচ বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৫ লাখ টন ছাড়াতে পারে। সারাদেশেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ফলে জাতীয়ভাবে আম উৎপাদন ৩০ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। চাহিদার অতিরিক্ত এই আম যদি রপ্তানি করা না যায়, তাহলে বাজারে দাম পড়ে যাবে, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার আম রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বর্তমানে যা কিছু রপ্তানি হচ্ছে, তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমিত পরিসরে।
এখন সময় এসেছে আম উৎপাদন ও রপ্তানিকে বিশ্ববাজারের উপযোগী করে তোলার। সরকারি নীতিগত সহায়তা, রপ্তানিযোগ্য আমের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা জরুরি। বিদেশে বাংলাদেশের সুমিষ্ট আমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সঠিক উদ্যোগ নিলে এই খাত হতে পারে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। আমচাষিরা সেই দিনের অপেক্ষায়।
[লেখক : সাংবাদিক]
-
ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী আমূল সংস্কার জরুরি
-
অবশেষে ‘হাসিনা’ গ্রেফতার
-
স্ক্যাবিস সংক্রমণের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয়
-
বাস্তবমুখী বাজেটের প্রত্যাশা : বৈষম্যহীন অর্থনীতির পথে কতটা অগ্রগতি?
-
কৌশল নয়, এবার প্রযুক্তিতে সৌদি-মার্কিন জোট
-
সিউল : স্বর্গ নেমেছে ধরায়
-
নাচোল বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র সংগ্রহশালা : সাঁওতাল স্মৃতি কেন উপেক্ষিত?
-

অন্ধকার সত্য, শেষ সত্য নয়!
-
বিয়েতে মিতব্যয়িতা
-
এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বঞ্চনার কথা
-
রোহিঙ্গা সমস্যা : বাহবা, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়
-
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়
-
প্রযুক্তির ফাঁদে শৈশব : স্ক্রিন টাইম গিলে খাচ্ছে খেলার মাঠ
-
রমগদ্য : সিরাজগঞ্জে ‘ব্রিটিশ প্রেতাত্মা’
-
বামপন্থা : নীতির সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা
-
দাবি আদায়ে জনদুর্ভোগ : জনশিক্ষা ও সুশাসনের পথ
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা