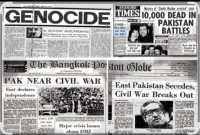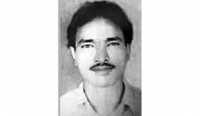opinion » post-editorial
ভারত-চীন সম্পর্কে কৌশলগত উষ্ণতার সূচনা
এম এ হোসাইন

তিয়ানজিন সম্মেলন কোনো নাটকীয় অগ্রগতি আনেনি, আর হয়তো সেটাই তার গুণ। বড় পদক্ষেপ প্রায়ই প্রত্যাশার চাপে ভেঙে পড়ে। ছোট, বাস্তবধর্মী পদক্ষেপই অনেক সময় টিকে থাকে
ইতিহাস কখনও কখনও এগিয়ে যায় বড়সড় ঘোষণা দিয়ে নয়, বরং নীরব পুনর্গঠনের মাধ্যমে। গত ৩১ আগস্ট ২০২৫, তিয়ানজিনে সেটাই ঘটল, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে মিলিত হলেন। এটি কেবল কোন আনুষ্ঠানিক করমর্দন ছিল না, এটি ছিল সচেতনভাবে নেওয়া এক কৌশলগত পদক্ষেপ। এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিনের সংকটপূর্ণ সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় খোলার চেষ্টা। ১৯৬২ সালের যুদ্ধ, সীমান্তসংঘর্ষ, এবং মাত্র চার বছর আগে গালওয়ান উপত্যকায় প্রাণঘাতী সংঘাতের পর আলোচনার টেবিলে মুখোমুখি বসা, যা এক ধরনের সাহসী কূটনৈতিক বার্তা।
২০১৮ সালের পর এই প্রথম মোদির চীন সফর কোনো বিজয়যাত্রা ছিল না; ছিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যুগান্তকারী পরিবর্তনের বার্তা। মাসের পর মাস নীরব কূটনৈতিক যোগাযোগ এই মঞ্চ তৈরি করেছে। গত বছর কাজানে ব্রিকস সম্মেলনে সংক্ষিপ্ত আলাপ একটি দরজা খুলেছিল, কিন্তু তিয়ানজিনে ওজন ছিল অন্যরকম। সীমান্ত, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সন্দেহÑশুধু অভিযোগ নয়, কাঠামোগত জটিলতা মোকাবিলার সুযোগ তৈরি হলো।
মোদি যখন “ইতিবাচক দিকনির্দেশনা”-র কথা বললেন, তা নিছক সৌজন্যমূলক বাক্য ছিল না। তিনি উল্লেখ করলেন স্পষ্ট পরিবর্তন: সামরিকীকৃত হিমালয় সীমান্তে শান্তি, কৈলাশ মানসরোবর যাত্রার পুনরায় চালু হওয়া (যা যেমন আধ্যাত্মিক, তেমনি রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রতীকী) এবং সরাসরি বাণিজ্যিক ফ্লাইট পুনর্বহালের পরিকল্পনা, যা সম্পর্কের এক নতুন মাত্রার সূচক।
শি’র বক্তব্যও ছিল অত্যন্ত পরিমার্জিত ও যুগান্তকারী। প্রায় ২.৮ বিলিয়ন মানুষের ভাগ্য যে আন্তঃসম্পর্কিত, তার স্বীকৃতি নিছক কূটনৈতিক সৌজন্য নয়। চীন জানে, ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শত্রুতা তার আঞ্চলিক অবস্থানকে দুর্বল করে, বিশেষত যখন বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যয়বহুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত এবং নিজস্ব অর্থনীতি চাপের মুখে।
তিয়ানজিনের অর্থ বোঝার জন্য ওয়াশিংটনকেও বুঝতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের রপ্তানি পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসিয়েছেন। যা ছিল বাণিজ্য নীতি ও রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির কারণে। এর প্রভাব শুধু রপ্তানিকারকদের চমকে দেওয়া নয়; বরং দেখিয়ে দিল, কত দ্রুত মার্কিন সুরক্ষা নীতি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে।
মার্কিন এই পদক্ষেপ চীনের জন্য এটি এক অপার সুযোগ তৈরি করেছে। বেইজিংয়ের নয়াদিল্লি দূত সু ফেইহং প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন, এবং সতর্ক করলেন যে “নীরবতা বা আপস শুধু দম্ভ বাড়ায়”। ভারতের পাশে থাকার এই ঘোষণা নিছক আবেগ নয়, বরং ছিল ভূ-রাজনৈতিক চাল। এর ফলশ্রুতিতে, দিল্লির সামনে উপস্থাপন করা হলো ওয়াশিংটন - মস্কো - বেইজিং এর মাঝে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের নতুন এক হাতিয়ার।
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়িয়েছে, কোয়াড জোটে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্ক আবেগনির্ভর নয়; বরং স্বার্থকেন্দ্রিক। যখন মার্কিন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ভারতের রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধিকে আঘাত করে, তখন দিল্লিকে বিকল্প খোঁজা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। চীনের সঙ্গে ভারতের এই সীমিত উষ্ণতা তার কূটনৈতিক দরকষাকষির শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিবে।
সম্প্রতি কূটনৈতিক তৎপরতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল সীমান্ত ইস্যুতে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের ২৪তম বৈঠক, যা এই মাসের শুরুতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় উন্নতির একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সীমান্ত বাণিজ্য পথ পুনরায় চালু করা এবং সামরিক আস্থা-বর্ধক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি।
এই পদক্ষেপগুলো চমকপ্রদ নয়, কিন্তু জরুরি। করোনা মহামারির পর বন্ধ থাকা ফ্লাইট চালু হওয়া স্বাভাবিকতা ফেরানোর সংকেত। সীমান্ত বাণিজ্য রুট খোলা স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রাণ ফেরাবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এটি সহযোগিতার অভ্যাস তৈরি করবে। সহজ সমস্যায় অগ্রগতি বৃহৎ জটিলতা সমাধানের পূর্বশর্ত।
একই সময়ে, ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের দীর্ঘ ছায়া এখনও বিরাজমান। যে সংঘর্ষে উভয় দেশের সৈন্যরা নির্মম হাতাহাতি লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। সেই ঘটনা কয়েক দশকের মধ্যে সম্পর্কের সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের ইঙ্গিত দেয়, আস্থা ভেঙে দেয় এবং দুই দেশেই জাতীয়তাবাদী আবেগ উসকে দেয়। বিচ্ছিন্নতা নতুন সংঘর্ষের ঝুঁকি কমালেও বাস্তব নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) এখনও সামরিকীকৃত রয়ে গেছে, আর কোনো পক্ষই তাদের ভূখ--সংক্রান্ত দাবি নিয়ে আপসের ইঙ্গিত দেয়নি।
তবু, ইতিহাস আমাদের শেখায় যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রায়ই সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়Ñতাৎক্ষণিক সমাধানের মাধ্যমে নয়। শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র–সোভিয়েত উত্তেজনা প্রশমণ পদক্ষেপ (যেমন: কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা আলোচনা চুক্তি, হেলসিঙ্কি চুক্তি) মতাদর্শগত শত্রুতা দূর করেনি, কিন্তু এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়ে এসেছিল পূর্বানুমানযোগ্যতা। ভারত ও চীনও হয়তো একই ধরনের এক পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছে যা সম্পূর্ণ মীমাংসা নয়, বরং স্থিতিশীলতা বয়ে আনবে।
তিয়ানজিন শুধু ভারত-চীন নয়, বড় কৌশলগত পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দিল। রাশিয়া-ভারত-চীন (আরআইসি) সংলাপ পুনরুজ্জীবন, যা ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে পশ্চিমা প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল। মস্কোর জন্য, ইউক্রেন যুদ্ধের পর আরআইসি হলো কূটনৈতিক অক্সিজেন। বেইজিংয়ের জন্য, এটি যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোটের বিপরীতে ভারসাম্য তৈরি করবে। দিল্লির জন্য, এটি বিকল্প যে তারা কোনো একক শক্তি-শিবিরের লেজ নয়।
ভারত ও চীন উভয়ই বহু-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান করে। তারা বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারের দাবি করে, এবং পশ্চিমাদের দ্বৈতমানদ-কেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু এই একতার আড়ালে রয়েছে ভিন্নতা: ভারতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এমন দেশগুলোর সঙ্গে, যারা চীনের উত্থান নিয়ে শঙ্কিত। যেমন: চীনের গভীর সম্পর্ক পাকিস্তানের সঙ্গে বা আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে প্রতিযোগিতা।
কূটনীতির সার্থকতা এখানেই: যেখানে স্বার্থ মেলে, সেখানে সহযোগিতা; যেখানে মেলে না, সেখানে প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রতিযোগিতাকে যেন বিপর্যয়ে না পরিণত করে।
তিয়ানজিন সম্মেলন কোনো নাটকীয় অগ্রগতি আনেনি, আর হয়তো সেটাই তার গুণ। বড় পদক্ষেপ প্রায়ই প্রত্যাশার চাপে ভেঙে পড়ে। ছোট, বাস্তবধর্মী পদক্ষেপই অনেক সময় টিকে থাকে।
মোদি জোর দিলেন “পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সংবেদনশীলতা”-র উপরÑভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগ চীন যেন স্বীকার করে, তার স্পষ্ট বার্তা। শি সরাসরি আবেগপ্রবণ না হলেও ইঙ্গিত দিলেন, বেইজিং নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করে, অযাচিত উত্তেজনা নয়।
আগামী মাসগুলোতে কাজ কথার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। সীমান্ত বাণিজ্য পোস্ট খুলবে? ফ্লাইট সময়মতো চালু হবে? তীর্থযাত্রা নির্বিঘেœ চলবে? এই ছোট ছোট পদক্ষেপই পরীক্ষা করবে নতুন উদ্যোগ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে কিনা। উভয় নেতা জাতীয় রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। মোদিকে ভারতের ভূখ-ের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে, কিন্তু যেন বেইজিংয়ের কাছে নরম না দেখায়; আবার প্রবৃদ্ধিও ধরে রাখতে হবে। শিকে ধীরগতির অর্থনীতি ও দৃঢ়তর মার্কিন জোটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে; তাকে দুর্বল দেখালে চলবে না। তাই দুজনেরই স্বার্থ উত্তাপ কমানো কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে।
তিয়ানজিন আমাদের স্মরণ করায় এক কঠিন বাস্তবতাকে। ভারত-চীন চিরস্থায়ী শত্রুতা হয়তোবা কৌশলগতভাবে অসহনীয় কিন্তু তারা প্রান্তিক শক্তি নয়। তারা সভ্যতার শক্তিÑপারমাণবিক, অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল, জনসংখ্যায় বিশাল। তারা একত্রে মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ও বিশ্ব অর্থনীতির বড় অংশ। পরিচালিত সহাবস্থানের বিকল্প হলো এমন এক এশিয়া, যা বারবার এমন সব সংকটে বিপর্যস্ত হতে পারে, যা মুহূর্তেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। যদি দিল্লি ও বেইজিং নিজেরা তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে না ওয়াশিংটন, না মস্কো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিতে পারবে।
ইতিহাস এখানে দিকনির্দেশনা দেয়। ১৯৭১ সালে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের তত্ত্বাবধানে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের দ্বারোদ্ঘাটন বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং পারস্পরিক কৌশলগত প্রয়োজনের স্বীকৃতির ফলে হয়েছিল। একইভাবে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতদের আফগানিস্তান ত্যাগও গভীর মতাদর্শগত শত্রুতার মাঝেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। যে সব জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়, তারা বোঝেÑআবেগ নয়, স্বার্থই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।
তিয়ানজিন হয়তো ভারত-চীন সম্পর্কের রূপরেখা বদলায়নি, কিন্তু নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে যেখানে নীতি নির্ধারিত হবে বাস্তবতা দিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত; এবং এশিয়ার দুই শক্তি মেনে নেবে, তাদের ভাগ্য একে অপরের সঙ্গে বাঁধা। পথ দীর্ঘ, অনিয়মিত, ভঙ্গুর হবে। কিন্তু ভূরাজনীতিতে, জীবনের মতোই অগ্রগতি প্রায়ই শুরু হয় সঠিক দিকে নেওয়া এক সচেতন পদক্ষেপ দিয়ে। তিয়ানজিন ছিল তেমনই একটি পদক্ষেপ।
[লেখক: প্রাবন্ধিক]
-
ভারত-চীন সম্পর্কে কৌশলগত উষ্ণতার সূচনা
-
একজন নাগরিকের অভিমানী বিদায় ও রাষ্ট্রের নৈতিক সংকট
-
নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য
-
আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে
-
জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে
-
পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা
-
সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত
-
অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স
-
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম
-
এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি
-
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ
-
ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে
-
রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”
-
কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা
-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’
-
স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য
-
ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি
-
ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য
-
তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
-
গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!
-
মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ
-
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি
-
হোক সবুজ বিপ্লব
-
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন
-
নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প
-
বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ
-
চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি