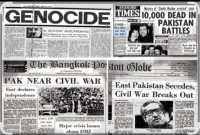opinion » post-editorial
সাইবার যুগে মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তা
মতিউর রহমান
একবিংশ শতাব্দীর এই ডিজিটাল বিপ্লব আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি একদিকে যেমন অশেষ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি অন্যদিকে তৈরি করেছে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ। ডিপফেক এবং সিনথেটিক মিডিয়া, যা একজন ব্যক্তির চেহারা, কণ্ঠস্বর, এবং অঙ্গভঙ্গি নকল করে বাস্তবসম্মত ছবি, অডিও বা ভিডিও তৈরি করতে পারে, এখন আর কেবল কল্পবিজ্ঞানের বিষয় নয়। রাজনৈতিক নেতাদের ভুয়া বক্তব্য, সামাজিক বিভাজন সৃষ্টিকারী মিথ্যা তথ্য, অথবা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য তৈরি ভুয়া অশ্লীল কনটেন্ট - এসব আমাদের সমাজের জন্য এক নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ডিজিটাল অধিকার রক্ষা করা এখন একটি বৈশ্বিক জরুরি প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, ডেনমার্ক সম্প্রতি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে, যা প্রতিটি মানুষের ডিজিটাল সত্তাকে একটি স্বতন্ত্র অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তারা এমন একটি আইন প্রস্তাব করেছে যা একজন ব্যক্তির চেহারা, শরীর এবং কণ্ঠস্বরের ওপর কপিরাইট-সদৃশ অধিকার প্রদান করবে। এই পদক্ষেপ শুধু ইউরোপের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, যারা দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং একইসাথে ডিপফেক ও গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।
ডেনমার্কের সংস্কৃতি মন্ত্রী জ্যাকব এঙ্গেল-শ্মিট এই আইনের প্রস্তাবনার মূল ভিত্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ‘প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে তাদের নিজস্ব শরীর, মুখ ও কণ্ঠের ওপর।’ এই বক্তব্যটি গভীর দার্শনিক এবং আইনগত তাৎপর্য বহন করে। এটি প্রমাণ করে যে মানুষের সত্তা শুধু শারীরিক জগতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ডিজিটাল জগতেও তার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে যা সুরক্ষার দাবিদার।
প্রচলিত কপিরাইট আইন সাধারণত সৃজনশীল কাজ, যেমন বই, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র বা চিত্রকলার মতো জিনিসের সুরক্ষায় ব্যবহৃত হয়। এই আইনগুলি স্রষ্টার শ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। কিন্তু মানুষের মুখ, কণ্ঠস্বর, এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি যা তার স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে, তা দীর্ঘকাল ধরে এই সুরক্ষার বাইরে ছিল। ডিপফেক প্রযুক্তির আবির্ভাব এই পরিস্থিতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। এখন একজন ব্যক্তির অজান্তে তার পরিচয়, বক্তব্য ও ভাবমূর্তি বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এটি তার খ্যাতি, সম্মান এবং এমনকি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে ফেলে। ডেনমার্কের এই প্রস্তাবিত আইনটি এই শূন্যতা পূরণ করে মানুষের এই ডিজিটাল সত্তাকে একটি স্বতন্ত্র অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায়।
যদি এই আইন কার্যকর হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার চেহারা বা কণ্ঠ ব্যবহার করে, তবে সেই ব্যক্তি আইনগতভাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে বা সেই কনটেন্ট অপসারণের জন্য চাপ দিতে পারবে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ কারণ এটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে নৈতিকতার মেলবন্ধন ঘটাচ্ছে। এর মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিগত অধিকারই সুরক্ষিত হবে না, বরং ডিপফেক প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহারকেও উৎসাহিত করা হবে।
বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে, যেখানে স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপক, সেখানে ডিপফেক ও ভুয়া তথ্যের বিপদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে, দেশে ভুয়া তথ্য ও হয়রানি রোধে সাইবার নিরাপত্তা আইন এবং ডেটা সুরক্ষা আইনের মতো কিছু আইন থাকলেও, সেগুলো ডিপফেক বা সিনথেটিক মিডিয়ার সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন:
রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা: বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিভাজন সৃষ্টিতে প্রায়শই ডিপফেক ভিডিও বা ভুয়া তথ্যের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষত নির্বাচনী সময় বা কোনো আন্দোলনের সময়, বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ভুয়া ভিডিও বা অডিও ছড়িয়ে দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়। ডেনমার্কের মতো একটি সুনির্দিষ্ট আইন থাকলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা দল দ্রুত সেই কনটেন্ট অপসারণ এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারত, যা রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ করবে।
ব্যক্তিগত মর্যাদা ও পারিবারিক সুনাম: বাংলাদেশের সমাজে একজন ব্যক্তির মর্যাদা এবং পারিবারিক সুনাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারীর ছবি বা কণ্ঠস্বর বিকৃত করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া তার সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে। এটি তার মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং তাকে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ডেনমার্কের আইনের মতো একটি কাঠামো নারীদের জন্য অনলাইন হয়রানি রোধে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে এবং তাদেরকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করবে। এটি সমাজে সাইবার বুলিং ও হয়রানির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।
অর্থনৈতিক ও উদ্ভাবনী দিক: এই ধরনের একটি আইন শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা দেবে না, বরং অর্থনৈতিক দিক থেকেও উপকারী হতে পারে। যদি বাংলাদেশ এমন একটি আইন প্রণয়ন করে, তবে তা দেশি-বিদেশি প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে নৈতিকভাবে ডেটা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তি খাতে একটি দায়িত্বশীল ও নৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এর ফলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির উন্নয়নে নৈতিকতার একটি নতুন মানদ- তৈরি হবে। এটি কনটেন্ট লাইসেন্সিং বা ডিজিটাল সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো নতুন আয়ের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারে।
ডেনমার্কের এই মডেলটি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা সহজ হবে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা মোকাবেলা করা প্রয়োজন।
আইনি ও কাঠামোগত পরিবর্তন: কপিরাইট আইন সাধারণত সৃজনশীল কাজের সুরক্ষায় ব্যবহৃত হয়। মানুষের স্বাভাবিক সত্তার ওপর এই ধরনের আইন প্রয়োগ করতে হলে বিদ্যমান আইনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে, একটি সুনির্দিষ্ট ‘পার্সোনাল রাইটস অ্যাক্ট’ বা ‘ব্যক্তিগত অধিকার আইন’ প্রণয়নের কথা ভাবা যেতে পারে, যা মানুষের ডিজিটাল সত্তার অধিকার নিশ্চিত করবে। এই আইনটি স্পষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করবে যে কোন ধরনের ব্যবহার অনুমোদিত এবং কোন ধরনের ব্যবহার অপরাধ।
ব্যতিক্রমী ধারা: একটি কার্যকর আইনের জন্য ব্যঙ্গচিত্র, সংবাদ প্রতিবেদন বা জনস্বার্থে ব্যবহৃত চিত্র ও কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ব্যতিক্রমী ধারা থাকা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সংবাদ সংস্থা কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য তার কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করে, তবে সেটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। এই ব্যতিক্রমী ধারাগুলো সাবধানে ও স্পষ্ট করে তৈরি করতে হবে যাতে বাকস্বাধীনতাকে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না করে। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে জনস্বার্থের বিষয়গুলো যেন এই আইনের আওতায় সীমাবদ্ধ না হয়।
প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি: ডিপফেক কনটেন্ট শনাক্ত করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ফরেনসিক সক্ষমতা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এই সক্ষমতা এখনো সীমিত। তাই সরকারকে এই খাতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সাইবার ট্রাইব্যুনালগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সেখানে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করাও জরুরি।
সচেতনতা বৃদ্ধি: আইনটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উচিত ডিপফেক ও সিনথেটিক মিডিয়ার বিপদ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
ডেনমার্কের মডেলের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্য একটি বিস্তারিত নীতি প্রস্তাবনা নিম্নরূপ হতে পারে:
ব্যক্তিগত সত্তাকে সম্পদ হিসেবে আইনি স্বীকৃতি: আইনটিতে একজন ব্যক্তির মুখম-ল, শরীর এবং কণ্ঠস্বরকে তার ‘ডিজিটাল সম্পদ’ হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। অননুমোদিত ব্যবহারকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এই সম্পদ ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে, এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হবে।
কনটেন্ট হোস্টিং প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা: গুগল, ফেসবুক, টিকটক-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন ২৪-৪৮ ঘণ্টা) অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে বাধ্য করতে হবে। যদি তারা ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাদের একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যা দ্রুত কাজ করে।
ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা: বৈধ অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। যদি কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি কোনো সেলিব্রিটির চেহারা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সেলিব্রিটির অনুমতি নিতে হবে এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একইসাথে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক বা আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান থাকবে।
পৃথক ট্রাইব্যুনাল বা শাখা: ডিপফেক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনালগুলোতে একটি বিশেষ শাখা গঠন করা যেতে পারে বা এই ধরনের অপরাধের জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে শুধুমাত্র এই ধরনের প্রযুক্তিগত অপরাধের বিচার করা হবে, যা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করবে।
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: ডিপফেক কনটেন্ট প্রায়শই আন্তঃসীমান্তীয় হয়। তাই এই ধরনের অপরাধ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা জরুরি।
ডেনমার্কের এই আইন শুধু একটি জাতীয় পদক্ষেপ নয়, বরং এটি একটি দৃষ্টান্ত যে ডিজিটাল যুগে মানুষের চেহারা, শরীর ও কণ্ঠস্বর আর অবাধে ব্যবহারের বস্তু নয়। বাংলাদেশ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তবে তা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। এটি কেবল ডিজিটাল অধিকার রক্ষা করবে না, বরং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের একটি নৈতিক কাঠামোও তৈরি করবে। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, মানব সত্তা যেন অবিকৃত থাকে, এটিই এই আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।
এই ধরনের একটি আইন বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। এটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা দেবে যে দেশটি নৈতিক ও দায়িত্বশীল প্রযুক্তি বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি প্রযুক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার এবং শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটি শক্তিশালী প্রতীক হবে। এটি আমাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে মানবিক মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত করবে।
[লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী]
-
ডাকসুৃ নির্বাচন : পেছনে ফেলে আসি
-
প্রসঙ্গ : এলডিসি তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ
-
“কোপা চাটিগাঁ...”
-
ই-কমার্স হতে পারে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন
-
ভারত-চীনের নতুন সমীকরণ
-

ভারত-চীন সম্পর্কে কৌশলগত উষ্ণতার সূচনা
-
ভারত-চীন সম্পর্কে কৌশলগত উষ্ণতার সূচনা
-
একজন নাগরিকের অভিমানী বিদায় ও রাষ্ট্রের নৈতিক সংকট
-
নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য
-
আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে
-
জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে
-
পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা
-
সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত
-
অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স
-
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম
-
এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি
-
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ
-
ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে
-
রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”
-
কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা
-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’
-
স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য
-
ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি
-
ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য
-
তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
-
গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!
-
মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ