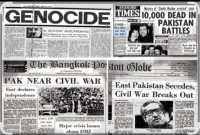opinion » post-editorial
ভারত-চীনের নতুন সমীকরণ
জাহাঙ্গীর আলম সরকার
দীর্ঘ কয়েক দশকের টানাপোড়েন, সীমান্তজুড়ে অবিশ্বাস, আর ভূরাজনীতির শীতল ছায়া যেন ভারত-চীনের সম্পর্ককে এক অন্তহীন অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। গ্যালওয়ানের রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর দু’দেশের সীমান্ত যেন হয়ে উঠেছিল স্থায়ী শীতল যুদ্ধের প্রতীক—এক অচেনা দূরত্ব, যেখানে প্রতিটি পাহাড়চূড়া যেন হয়ে উঠেছিল সন্দেহের প্রহরী। কিন্তু ইতিহাস সবসময়ই শেখায়, কূটনীতির ভাষা কখনো চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকে না।
আজ আবার সেই স্তব্ধতার দরজা খুলতে শুরু করেছে। দিল্লির মাটিতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই’র সফর তাই নিছক একটি আনুষ্ঠানিক প্রটোকল নয়; এটি যেন বরফে ঢাকা নদীতে প্রথম ফোঁটা জলের স্রোত, যা জানিয়ে দেয়—জমাট বাঁধা উত্তেজনাও একদিন গলবে। বহু বছরের বিচ্ছিন্নতার পর যখন দুই দেশের আকাশে আবারও সরাসরি উড়োজাহাজ চলাচলের প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন সেটি শুধু একটি পরিবহন-ঘটনা থাকে না; বরং হয়ে ওঠে আস্থার পুনর্জাগরণের প্রতিক। এ যেন সমিান্তের কাঁটাতারে আটকে থাকা বিশ্বাস আবার ডানা মেলতে চাইছে, অবিশ্বাসের কুয়াশা ভেদ করে উড়ে যাচ্ছে প্রথম পাখি।
এই সফরের তাৎপর্য আরও বিস্তৃত—এটি শুধু ভারত—চীন সম্পর্কের অন্দরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা বিশ্ব রাজনীতির হিসাব-নিকাশের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি ভূমিকম্পের ঢেউ পৌঁছে যায় ওয়াশিংটন, মস্কো কিংবা টোকিও পর্যন্ত। তাই ওয়াং ই’র দিল্লি সফর একদিকে যেমন প্রতিবেশী দুই পরাশক্তির মাঝে নতুন আস্থার সূচনা করছে, অন্যদিকে বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যে তৈরি করছে নতুন সমীকরণ।
এই মুহূর্তে ভারত—চীন যে টেবিলে মুখোমুখি বসছে, তা কেবল সীমান্ত বা বাণিজ্যের টেবিল নয়, বরং এক বিশাল ভূরাজনৈতিক দাবার বোর্ড, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে ইন্দো-প্যাসিফিক থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত। আর এই প্রেক্ষাপটে উড়োজাহাজের ডানা কিংবা কূটনীতিকদের করমর্দন হয়ে উঠছে এক ধরনের প্রতীক—শত্রুতার আঁধার ভেদ করে আলো খোঁজার প্রয়াস।
২০২০ সালের সীমান্ত সংঘর্ষে রক্তের যে দাগ লেগে ছিল গ্যালওয়ানের পাথরে, তার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। সেই রাতের হিমশীতল অন্ধকারে দুই সেনার মৃত্যু হয়েছিল, যেন হিমালয়ের তুষারও রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। সম্পর্কের দেয়ালে তখন যে শীতলতা জমাট বেঁধেছিল, তা অনেকদিন পর্যন্ত দুই দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঢেকে রেখেছিল অনাস্থার মেঘে।
কিন্তু ইতিহাস কখনো স্থির থাকে না। সময়ের প্রবাহে জমাট বরফও গলে যায়, আর কূটনীতির ভাষা একসময় আবার আলোচনার ছায়া ফিরিয়ে আনে। আজ যখন দিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে আবার কথোপকথনের সেতু গড়ে উঠছে, তখন সেই সেতুটি শুধু সীমান্তের পাহাড় ও নদীর ওপর দাঁড়িয়ে নেই; এটি দাঁড়িয়ে আছে বৈশ্বিক কূটনীতির অঙ্গনে, যেখানে প্রতিটি করমর্দন ভবিষ্যতের ভারসাম্য নির্ধারণ করে।
মোদি যখন চীন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এক ধরনের ইতিবাচক আবহ। মনে হচ্ছে যেন দুই দেশের দীর্ঘ নীরবতার পর আবারও সংলাপের শিখা প্রজ্বলিত হচ্ছে। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা কেবল সীমান্ত বিরোধের সমাধান বা উড়োজাহাজ চলাচল পুনরায় চালুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর আড়ালে লুকিয়ে আছে এক জটিল বৈশ্বিক হিসাব—যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েন, রাশিয়ার জ্বালানি বাজারে ভারতের ভূমিকা, আর ইন্দো—প্যাসিফিক কৌশলের ভবিষ্যৎ মিলেমিশে তৈরি করছে নতুন ভূরাজনৈতিক সমীকরণ।
অতএব, ভারত—চীন সংলাপ কেবল দু’দেশের সম্পর্ক মেরামতের প্রচেষ্টা নয়; বরং এটি হচ্ছে এক বৃহৎ দাবার চাল, যার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ওয়াশিংটন, মস্কো ও টোকিওর কূটনৈতিক করিডরে।
যুক্তরাষ্ট্র—ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক টানাপোড়েন যেন চীনের কূটনৈতিক অভিধানে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন যখন হঠাৎ করে ভারতের ওপর শুল্কের কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিল, তখন তা কেবল বাণিজ্যের অঙ্ক বদলালো না, বরং দিল্লির অভ্যন্তরে এক নতুন ধাক্কা সৃষ্টি করল। তারও বেশি আলোড়ন তোলে সেই অভিযোগ—ভারত নাকি রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কিনে শোধন করে বিশ্বের নানা প্রান্তে রপ্তানি করছে, আর এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত মস্কো পাচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় ডলার। হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা পিটার নাভারো তখন শীতল যুদ্ধের ধাঁচে হুঁশিয়ারি ছুড়ে দিলেন—‘ভারত যদি সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অংশীদার হতে চায়, তবে তাকে সঠিক পথে চলতে হবে।’
কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোনো দেশকে চাপ দিয়ে স্থায়ীভাবে নিজের শিবিরে বাঁধা যায় না। রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক টিকে থাকে পারস্পরিক স্বার্থ, আস্থা আর সমঝোতার ওপর। তাই যখন ট্রাম্প প্রকাশ্যেই ভারতের নেতৃত্বকে তিরস্কার করেন, তখন শুধু কূটনৈতিক মহলই নয়, সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের মনেও জন্ম নেয় এক ধরনের ক্ষোভ ও আঘাতবোধ। এর ফলেই দিল্লি—ওয়াশিংটন সম্পর্কের যে সেতুটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, তা আরও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। ফলে প্রশ্নের মুখে পড়ে ইন্দো—প্যাসিফিক নীতিমালা, এমনকি কোয়াড জোটের ভবিষ্যৎও, যা চীনকে ঠেকানোর জন্যই গড়ে উঠেছিল।
এমনই এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বেইজিং বুঝে নেয়—কূটনীতির দাবার ছকে চাল দেওয়ার এটাই সঠিক সময়। ভারত যখন পশ্চিমা চাপের ভারে ক্লান্ত, তখন চীন তার সামনে মেলে ধরে নতুন আস্থার হাত। সীমান্ত টহলব্যবস্থা নিয়ে চুক্তি, ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য তিব্বতের দরজা খোলা, চীনা পর্যটকদের জন্য ভিসা পুনরায় চালু করা—এসবই যেন আস্থার নতুন বীজ, যা দুই দেশের সম্পর্কের মাটিতে ধীরে ধীরে শেকড় গাড়তে শুরু করেছে।
ওয়াং ই’র সাম্প্রতিক সফর এই আস্থাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। সীমান্ত নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ও কার্যনির্বাহী দল গঠন, সীমান্ত বাণিজ্য পুনরুজ্জীবনের আলোচনা, এমনকি সার, বিরল খনিজ ও টানেল বোরিং মেশিন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি—সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভারত—চীন সম্পর্কের মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের আলো আবারও উঁকি দিতে শুরু করেছে।
তবে এটিকে কেবল ট্রাম্পের হঠকারী পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া বলে ক্ষুদ্রায়িত করা হবে ভুল। সত্যি বলতে, ভারত—চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তারও আগে, নিঃশব্দে ও ধীরলয়ে। ট্রাম্পের কণ্ঠস্বর হয়তো সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে, কিন্তু মূল বীজ রোপণ হয়েছিল সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর প্রয়াস থেকেই।
তবুও দিল্লি ভালো করেই জানে—চীনের সঙ্গে সম্পর্ক মানে কখনোই চিরস্থায়ী আস্থা নয়। এটি আসলে কূটনীতির সেই সূক্ষা¥ সুতো, যা একদিকে সহযোগিতার আলোয় ঝলমল করে, আবার অন্যদিকে অবিশ্বাসের ছায়ায় জড়িয়ে থাকে। অতীত বহুবার দেখিয়েছে—আজকের উষ্ণতা কালকে শীতলতায় রূপ নিতে সময় নেয় না। সীমান্তে সেনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা হিমালয়ের বরফগলা নদীর ধারে তাঁবু বসানোর প্রতিটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রতিবেশী দুই পরাশক্তির সম্পর্ক সবসময়ই টানটান সতর্কতার ওপর দাঁড়িয়ে।
এই বাস্তবতা থেকেই ভারত এখন চাইছে এমন এক প্রতিরোধ—কাঠামো নির্মাণ করতে, যাতে আর কোনোদিন ২০২০ সালের মতো রক্তাক্ত সংঘাতের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। দিল্লির দৃষ্টিতে সহযোগিতা জরুরি, কিন্তু তা হতে হবে সতর্কতা ও প্রতিরক্ষার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। কূটনীতির টেবিলে করমর্দন থাকলেও সীমান্ত পাহারায় থাকতে হবে প্রহরী; বাণিজ্যের করিডরে আলোচনার ফিসফিস থাকলেও আকাশে উড়তে হবে নজরদারির ড্রোন।
আজকের ভারত—চীন সম্পর্ক তাই দ্বিমুখী এক আখ্যানের মতো। একদিকে উন্মোচিত হচ্ছে সহযোগিতা ও সম্ভাবনার জানালা—সীমান্ত বাণিজ্যের পুনর্জাগরণ, আস্থার ছোট ছোট ইঙ্গিত, কিংবা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সেতু। অন্যদিকে অব্যাহত রয়েছে অবিশ্বাসের আঁধার—যেখানে প্রতিটি হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে সীমান্তের কাঁটা তারের স্মৃতি, প্রতিটি আলিঙ্গনের ভেতরেই টিকে থাকে প্রতিদ্বন্ধিতার শীতলতা।
এই সংঘাতময় বাস্তবতার মাঝেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এক নতুন ভূরাজনীতির সমীকরণ। ইন্দো—প্যাসিফিক থেকে মধ্য এশিয়া, ওয়াশিংটন থেকে বেইজিং—সবখানেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই সম্পর্কের টানাপোড়েন। ভারত ও চীন উভয়েই জানে, একে অপরকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়; আবার একে অপরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করাও বিপজ্জনক। ফলে সম্পর্কের প্রতিটি পদক্ষেপ এখন হয়ে উঠছে হিসাবি, সতর্ক এবং প্রতীকী—যেন দাবার বোর্ডে প্রতিটি চাল ভবিষ্যতের জন্য রেখে যায় গভীর ছাপ।
অতএব, আজকের ভারত—চীন সম্পর্ক হলো আলো ও আঁধারের মিলিত এক পথযাত্রা। এটি এমন এক যাত্রা, যেখানে প্রতিটি অগ্রগতি বহন করে আশা, আবার প্রতিটি বিরতি স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের ক্ষত। আর এই আলো—আঁধারের দ্বন্ধেই নির্ধারিত হবে আগামী দিনের এশীয় ভূরাজনীতির রূপরেখা।
[লেখক: আইনজীবী]
-
ডাকসুৃ নির্বাচন : পেছনে ফেলে আসি
-
প্রসঙ্গ : এলডিসি তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ
-
“কোপা চাটিগাঁ...”
-
ই-কমার্স হতে পারে প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন
-
সাইবার যুগে মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তা
-

ভারত-চীন সম্পর্কে কৌশলগত উষ্ণতার সূচনা
-
ভারত-চীন সম্পর্কে কৌশলগত উষ্ণতার সূচনা
-
একজন নাগরিকের অভিমানী বিদায় ও রাষ্ট্রের নৈতিক সংকট
-
নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য
-
আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে
-
জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে
-
পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা
-
সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত
-
অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স
-
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম
-
এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি
-
বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ
-
ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে
-
রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”
-
কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা
-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’
-
স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য
-
ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি
-
ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য
-
তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা
-
গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!
-
মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ