উপ-সম্পাদকীয়
বাল্যবিয়ের উদ্বেগজনক চিত্র
জিল্লুর রহমান
দেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে বাল্যবিয়ে একটি। একসময় বাল্যবিয়ে বাংলাদেশে মহামারী আকার ধারণ করেছিল। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও তদারকির কারণে বাল্যবিয়ে অনেকটা নিয়ন্ত্রণেও এসেছিল। কিন্তু করোনা অতিমারীর কারণে বাল্যবিয়ে আবারও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জন্য এই শব্দটা বিভীষিকাময় এক কালো অধ্যায়। অনেকে বলেন এটি একটি সামাজিক অভিশাপ কিন্তু সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা এটি সামাজিক বাস্তবতা বলে অভিহিত করে থাকেন।
বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যু, মানুষের গড় আয়ু ও মাতৃস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি দৃশ্যমান হলেও বাল্যবিয়ের হার কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না। বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাল্যবিয়ের হারে এখনো শীর্ষে। এটি মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও মারাত্মক হুমকি। সম্প্রতি জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) ‘৮০০ কোটি জীবন, অপরিসীম সম্ভাবনা’ শিরোনামের একটি প্রতিবেদন গত ১৯ এপ্রিল বৈশ্বিকভাবে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি-২০২৩ শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ১৮ বছরের আগেই ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যা খুবই উদ্বেগজনক চিত্র।
২০০৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাল্যবিয়ের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের (বিডিএইচএস) প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৫৯%। কিশোরী মায়ের গর্ভধারণের হার ছিল ২৮%; যা ২০১৪ সালে ছিল ৩১%। কিন্তু করোনাকালে এ সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করেছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের এক জরিপেও দেখা গিয়েছিল, ২০১৯ সালের প্রথম ১০ মাসের তুলনায় ২০২০ সালের প্রথম ১০ মাসে বাল্যবিয়ে বেড়েছিল ৬৮ শতাংশ। আসলে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও সেই আশঙ্কাজনক চিত্রটিই ভেসে উঠেছে।
করোনা অতিমারীর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা স্কুলবিমুখ হয়ে পড়েছিল। বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তখনই আশঙ্কা করেছিলেন বিদ্যালয় খুলতে দেরি হওয়ার কারণে বাল্যবিয়ের মতো সমস্যা আরও প্রকট হতে পারে। বৈশ্বিক পরিসংখ্যান বলছে, সংঘাত, দুর্যোগ কিংবা মহামারীর সময় বাল্যবিয়ের সংখ্যা বাড়ে। করোনা অতিমারীর আগে বাংলাদেশে ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো এবং করোনার কারণে আরও ২৩ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে গেছে বলে অর্থনীতিবিদরা বলছেন। তাই বাল্যবিয়ের ঝুঁঁকি এ সময়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকেও স্বীকার করা হয়েছে, করোনা অতিমারীর কারণে বাল্যবিয়ে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। ওই সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমও সীমিত ছিল। এখন সব কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে, এটার ফল পেতে আরেকটু সময় লাগবে। করোনা মহামারীর সময় দেশে বাল্যবিয়ের হার যে বেড়ে গিয়েছিল, তা বিভিন্ন জরিপেও ফুটে উঠেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাল্যবিয়ের ওপর ইউএনএফপিএর এক জরিপ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার ২০২১ সালে আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়েছিল। কোভিডের প্রাদুর্ভাবে ওই দুই বছর এই বয়সী প্রায় ২৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।
জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফের এক তথ্যে জানা যায়, বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই বাল্যবিয়ের প্রচলন এখনও সবচেয়ে বেশি, যা বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যেও রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের প্রবণতা ১৯৭০ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশেরও বেশি কমেছে, তা সত্ত্বেও এখনও এই হার অনেক বেশি। বর্তমানে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের ৫১ শতাংশের বিয়ে হয়েছে তারা শিশু থাকা অবস্থাতেই। এটি এই দেশকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ‘শিশু কনের’ দেশে পরিণত করেছে, যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের ১৮তম জন্মদিনের আগেই। আবার এদের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লাখ নারীর বিয়ে হয়েছে তাদের বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগেই।
ইউনিসেফের মতে, একসঙ্গে অবশ্যই ক্ষতিকর রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে এবং বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে হবে। মানবাধিকারের এই লঙ্ঘন ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনছে, যা শিশুদের কাছ থেকে তাদের শৈশব ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং নিজের পছন্দের জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে। মেয়েদের বেঁচে থাকা ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এবং তাদের সহিংসতা ও নিগ্রহের শিকার হওয়া কমাতে এখনই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বিনিয়োগ করতে হবে।
করোনা অতিমারীর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা স্কুলবিমুখ হয়ে পড়েছিল। বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তখনই আশঙ্কা করেছিলেন বিদ্যালয় খুলতে দেরি হওয়ার কারণে বাল্যবিয়ের মতো সমস্যা আরও প্রকট হতে পারে
ইউনিসেফ সামাজিক রীতিনীতির পাশাপাশি আইন ও নীতিমালার মতো লিঙ্গ বৈষম্যের কাঠামোগত কারণগুলোকে পরিবর্তন করতে সরকার, সুশীল সমাজ ও এনজিওসহ অংশীদারদের একটি বিস্তৃত জোটের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে। এটি মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন বিকল্প থেকে নিজের পছন্দের জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ করে দেয়। প্রথাগত এবং ডিজিটাল উভয় প্ল্যাটফর্মে কিশোরীদের প্রতিনিধিত্ব ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরার মাধ্যমে ইউনিসেফ তাদের ক্ষমতায়নেও কাজ করে।
বাল্যবিয়ের যে সমস্ত কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দরিদ্রতা, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কার, সামাজিক অস্থিরতা, যৌন নিপীড়ন, মেয়েশিশুর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তার অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিয়ে রোধসংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া। বাল্যবিয়ের কারণে অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি, তালাক, পতিতাবৃত্তি, অপরিপক্ব সন্তান প্রসবসহ নানাবিধ জটিলতার শিকার হচ্ছে। তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাল্যবিয়ের সঙ্গে মাতৃমৃত্যুর একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হলে প্রজননস্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে বাল্যবিয়ে পরিস্থিতি উন্নয়নে আশানুরূপ কোনো অর্জন নেই। এর পেছনে শুধু দারিদ্র্য নয়, সামাজিক আচার-আচরণও দায়ী। এখনো কম বয়সে বিয়ে দেয়াকে ভালো বলে মনে করা হয়। এ পরিস্থিতি রোধে মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে উপবৃত্তি দেয়া দরকার এবং সামাজিক মনোভাবেও পরিবর্তন আনতে হবে।
১৯২৯ সালের বাল্যবিয়ে আইন ২০১৭ সালে বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে রূপান্তরিত হয়। ২০১৭ সালে বাল্যবিয়ে আইন সংশোধন করা হলেও এখনো গ্রামগঞ্জে-মফস্বল এলাকাসহ সারাদেশে বাল্যবিয়ে হচ্ছে অহরহ। এ আইনে বাল্যবিবয়ের সংজ্ঞায় ছেলেমেয়ের বিয়ের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার সর্বশক্তি দিয়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারও করছে। বাল্যবিয়ে বন্ধের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিও সংগঠনের কার্যক্রমও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কার্যকরভাবে বাল্যবিবাহের ছোবল রোধ করা যাচ্ছে না।
অনেকে অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক ছেলে মেয়েদের বয়স বাড়িয়ে জন্ম নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করে বাল্যবিয়ে রেজিস্ট্রেশন করছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে দরিদ্র্যতা কিংবা যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে তারা বাস্তবতার নিরিখে এসব করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকে এটাকে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করছেন। ফলে বেড়ে যাচ্ছে বিয়ে বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, নারী-নির্যাতন, পরকীয়া, আত্মহত্যা, পুষ্টিহীন ও প্রতিবন্ধী শিশু প্রসব এবং গর্ভজনিত ও অপুষ্টিজনিত মৃত্যু। উদ্ভূত এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকারকে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। বাল্যবিয়ে রোধে সর্বপ্রথম দরকার পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অগ্রসর ভূমিকা। শুধু সরকারের একার পক্ষে নয়, সবার সম্মিলিত প্রয়াসই শুধু রুখে দিতে পারে বাল্যবিয়ের এই বিপজ্জনক ঊর্ধ্বমুখীনতা।
[লেখক: ব্যাংকার]
-
কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?
-
এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?
-
মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
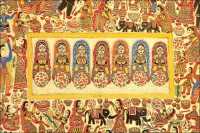
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?
-
সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব
-
প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক
-

বিকাশের পথকে পরিত্যাগ করা যাবে না
-
বর্ষা ও বৃক্ষরোপণ : সবুজ বিপ্লবের আহ্বান
-
প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষকের করণীয়
-
পারমাণবিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক ভণ্ডামির প্রতিচ্ছবি
-
পরিবেশের নীরব রক্ষক : শকুন সংরক্ষণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন
-
মশার উপদ্রব : জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা
-
ভুল স্বীকারে গ্লানি নেই
-
ভাঙনের বুকে টিকে থাকা স্বপ্ন
-
একটি সফর, একাধিক সংকেত : কে পেল কোন বার্তা?







