উপ-সম্পাদকীয়
নিয়ন্ত্রণহীন পণ্যের বাজার, লাগাম টানবে কে?
এসএম জাহাঙ্গীর আলম
ভোগ্যপণ্যের দাম আবার হু-হু করে বাড়ছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি, মাছ-মাংস, পেঁয়াজ, রসুন আদা থেকে শুরু করে যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েই চলছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণ্যিজ্যিক করপোরেশন (টিসিবি) গত ৮ অক্টোবর ঢাকা মহানগরীর ভোগ্যপণ্যের যে বাজার দর দেখিয়েছে, তাতে প্রতি কেজি সরু চাল (নাজির) ৬৬ টাকা, মাঝারি চাল ৫৬ টাকা আর মোটা চাল ৪৮ টাকা। অপরদিকে গণমাধ্যমগুলো বলছে, প্রতি কেজি সরু চাল ৭০ থেকে ৭২ টাকা, মাঝারি ৫৮ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টিসিবি বলেছে, প্রতি কেজি আটা ৩৫ টাকা, বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩৬ থেকে ৩৮ টাকায়। সয়াবিন তেল টিসিবি বলেছে প্রতি লিটার লুজ ১৩৬ টাকা, বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৩৮ টাকা, আর বোতল প্রতি লিটার ১৬২ থেকে ১৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
পেঁয়াজের কেজি ৭০ টাকা ছাড়িয়েছে আগেই। এক কেজি আদা বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকায়। বয়লার মুরগি একমাস আগেও ১৩০ থেকে ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল যা এখন ১৮০ টাকা ছাড়িয়েছে।
শাক-সবজি থেকে যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েই চলছে। কেন দাম বাড়ছে তার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। এখন দেশে লকডাউন নেই, নেই পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো অসুবিধা। লকডাউনের অজুহাতে গত প্রায় দুই মাস আগে পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছিল। এখন তো আর লকডাউন নেই।
চাল-আটার দামে কেন বাড়ছে? দেশে কী খাদ্যের ঘাটতি আছে? সরকারি ভাষ্যমতে, দেশে কোনো খাদ্য সংকট নেই। বরং চাহিদার তুলনায় বেশি খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য হচ্ছে যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালের উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৬৪ লাখ টন; যা সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। আর ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদন দাঁড়ায় ৩ কোটি ৮৭ লাখ টনে। আর গত ২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদন আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ৯৬ লাখ টনে। আর গমের উৎপাদন গত বছরে দাঁড়ায় প্রায় ২৮ লাখ টনে। গত অর্থবছরে ১১ লাখ টন ঘাটতি থাকলেও ৬৭ লাখ টন খাদ্য আমদানি করা হয়। কাজেই খাদ্য ঘাটতি থাকার কথা নয়।
দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ২৮ লাখ টন। এর মধ্যে গত অর্থবছর উৎপাদন হয় ২৫ লাখ টন, অপরদিকে আমদানি করা হয় (বেসরকারিভাবে) ৪ লাখ টনের বেশি। রসুনের উৎপাদন গত অর্থবছরে ছিল ৬০ হাজার টন। চাহিদার তুলনায় ঘাটতি থাকলেও আমদানি হয় চাহিদার চেয়ে বেশি। কৃষি সম্প্রসার অধিদফতর (ডিএই) সূত্রে জানা যায়, গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৮৫৪ হেক্টর জমিতে শাক-সবজির আবাদ হয়, আর উৎপাদন দাঁড়ায় ১ কোটি ৩০ লাখ ৬৫ হাজার ৭৪৩ টনে।
শাক-সবজির চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি। আর উৎপাদন বেশি হওয়ায় বিদেশে রফতানিও হচ্ছে। তারপরও দাম বেশি। কৃষক এক কেজি পটল বা বেগুন যে দামে পাইকারের কাছে বিক্রি করে, রাজধানীতে তার চার থেকে পাঁচগুণ বেশি দামে বিক্রি হয়। ঘাটতি বা সরবরাহ স্বাভাবিক থাকার পরও দাম হু হু করে বেড়ে যায় বা যাচ্ছে। ভোজ্যতেল নিয়ে তেলেসমাতি কান্ড নতুন কিছু নয়। এটা দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছে। হঠাৎ করে নানা অজুহাত দেখিয়ে দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে, আন্তর্জাতিক বাজার দর বেশি, জাহাজ ভাড়া বেশি, ডলারের দাম বেড়ে গেছে ইত্যাদি।
ভোজ্যতেলে চাহিদা সর্বোচ্চ ২০ লাখ টন। এর মধ্যে দেশেই তেল বীজ উৎপাদন হয় ১০ লাখ টন (২০১৯-২০ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী)। যা থেকে ৫ লাখ টন তেল পাওয়া যায়। তেল আমদানি হয় চাহিদার তুলনায় বেশি। অপরিশোধিত তেল ও বীজ প্রতিবছর ২২ থেকে সর্বোচ্চ ২৪ লাখ টন আমদানি হয়। বাজারে তেলে কোনো ঘাটতি নেই। অভ্যন্তরীণ মজুদ পর্যাপ্ত। তারপরও দাম বেড়েই চলছে।
একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ‘যেকোনো পণ্যের দাম একবার বাড়লে আর কমে না।’ এটাই সত্য। বাড়লে আর কমে না। বাংলাদেশের পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রক হলো ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়ায় বা বাড়িয়েই চলছে। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নীরব বা রহস্যজনক বলা যেতে পারে।
এটা সত্য যে, মিল মালিকরাই চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। কৃষক এক মণ ধান উৎপাদনে যত টাকা খরচ করেন, তার চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করতে হয়। শুধু ধান কেন, যেসব পণ্য কৃষক উৎপাদন করেন, সবগুলোতেই লোকসান দিতে হচ্ছে। কৃষক আর ভোক্তারা খেসারত দিচ্ছেন আর সুবিধা নিচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগীরা। বাজার সিন্ডিকেট ভাঙার দাবি বারবার উঠলে এক্ষেত্রে সরকার নীরব। অবশ্য মাঝে-মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা মেয়র সাহেবরা হুঙ্কার দিয়ে বলেন- ‘দাম বাড়লে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে’। এই বলেই শেষ। পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আছে, পাশাপাশি একই মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়েছে বেশ কয়েকটি সংস্থা বা দফতর। তারা দেখেও যেন দেখে না। সাধারণ ভোক্তার কথা চিন্তাও করে না।
সিংহভাগ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতির ফলে দিশেহারা। সরকার প্রতি জাতীয় বাজেটেই মূল্যস্ফীতির একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য আর ঠিক থাকে না। আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করেই নয়। তাহলো বাংলাদেশের বাজার এখন ভারত নির্ভর হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ পণ্যই ভারত থেকে আমদানি হয়ে থাকে। যেমন চাল, ডাল, পেঁয়াজ-রসুন, চিনি, মসলা ইত্যাদি। ভারত যদি কোনো পণ্যের রফতানি শুল্ক বাড়িয়ে দেয় বা রফতানি বন্ধের ঘোষণা দেয়, সাথে সাথেই বাংলাদেশে সেই পণ্যের বাজার অস্থির হয়ে উঠে। ধরা যাক চালের কথা। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল মজুদ থাকার পরও যদি ভারত রফতানির বন্ধের ঘোষণা দেয়, সাথে সাথেই চালের বাজার বেড়ে যায়। গত ২০১৯ সালের ঘটনা আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধের ঘোষণা দিলে বাংলাদেশের বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। তখন কিন্তু বাংলাদেশে পেঁয়াজের ঘাটতি ছিল না।
ভোগ্যপণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে কে? সরকার না ব্যবসায়ীরা? আর বাংলাদেশের বাজার ভারত নির্ভর হবেই বা কেন? ভারত ছাড়াও ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড থেকে চাল আমদানি হয়। ব্রাজিল থেকে আসে তেল ও চিনি। তুরস্ক থেকে ডাল ও পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। নেপাল ও ভুটান থেকে রসুন আমদানি করা যায়। আমরা কি শুধু ভারতমুখী হয়েই থাকবো?
পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারের। প্রয়োজন সার্বক্ষণিক পণ্যের বাজার মনিটরিং করা। কোন পণ্যের কত মজুদ আছে, বার্ষিক চাহিদা কত? বাজার মূল্য কোন পণ্যের কত এসবই তো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল আছে, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডিএইর মনিটরিং সেল আছে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ব্যুরো আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং সেল আছে। এছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়েছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ট্রেড এবং ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ইত্যাদি। এত সব থাকলে পণ্যের বাজার কেন সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই?
সরকার প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে মূল্যস্ফীতি নির্ধারিত করে। যেমন চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার নির্ধারণ করেছে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু নির্ধারিত হার আর ঠিক থাকে না। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও খাদ্যের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখীই থেকে যায়।
পণ্যের বাজার ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটনির্ভর হওয়ায় ভোক্তা সাধারণকে খেসারত দিয়েই যেতে হচ্ছে। এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে? ভোগ্যপণ্যের গতি ঊর্ধ্বমুখীতে নিম্ন ও স্বল্পআয়ের সিংহভাগ মানুষ এখন চোখে অন্ধকার দেখছেন। এক্ষেত্রে সরকারের কি কিছুই করার নেই? নিয়ন্ত্রণহীন পণ্যের বাজারের লাগাম টানবে কে?
[লেখক : সাবেক কর কমিশনার; পরিচালক, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কো. লি.]
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
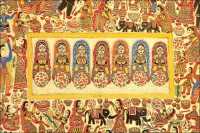
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?
-
সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব
-
প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক
-

বিকাশের পথকে পরিত্যাগ করা যাবে না
-
বর্ষা ও বৃক্ষরোপণ : সবুজ বিপ্লবের আহ্বান
-
প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষকের করণীয়
-
পারমাণবিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক ভণ্ডামির প্রতিচ্ছবি
-
পরিবেশের নীরব রক্ষক : শকুন সংরক্ষণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন
-
মশার উপদ্রব : জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা
-
ভুল স্বীকারে গ্লানি নেই
-
ভাঙনের বুকে টিকে থাকা স্বপ্ন
-
একটি সফর, একাধিক সংকেত : কে পেল কোন বার্তা?
-
দেশের কারা ব্যবস্থার বাস্তবতা
-
ইসলামী ব্যাংক একীভূতকরণ : আস্থা ফেরাতে সংস্কার, না দায়মুক্তির প্রহসন?
-
রম্যগদ্য : চাঁদাবাজি চলছে, চলবে







