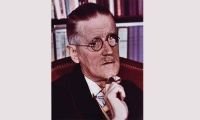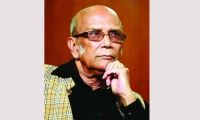সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব
রুহুল আমিন বাচ্চু
১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে শিল্পসাহিত্যের বহুযুগের সাধনার সম্পদ ধারণ করে কলকাতা আগেই উর্বর হয়ে উঠেছিল। এ বিভক্তির পর স্বাভাবিকভাবে বাংলা সাহিত্যের আরেকটি দিক উন্মোচিত হতে থাকে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকা কেন্দ্রিক।
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত মুদ্রণশিল্পের সহায়ক ভূমিকা। তখন ঢাকার মুদ্রণশিল্পের শৈশবকাল। কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য আসরে যারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে পূর্ববঙ্গীয় মুদ্রক প্রকাশক যারা কলকাতায় ব্যবসা করছিলেন তারাও ফিরে এলেন।
‘একজন শিল্পীর কাছে গোটা পৃথিবীটাই তার ঐতিহ্য’ এলিয়টের এ ধারণাকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে একজন লেখক তাঁর ভাষার পূর্ববর্তী সমস্ত সম্পদের ঐতিহ্যে লালিত; তা সে সম্পদ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে যেখানে এবং যখনই সৃষ্টি হোক না কেন।
বাংলাদেশের ছোটগল্পে গল্পকারদের দৃষ্টিপাত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এ দেশের ছোটগল্পের যে অবয়ব বিন্যাস ঘটেছে তা তার পূর্ববর্তী সমুদয় রচনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে রক্ষণশীলতা, প্রথাবদ্ধতা এবং গ্রাম্যতার বাহুপাশ থেকে বের হয়ে আধুনিকতার পরশ দিয়েছেন।
প্রথমদিকে তিনি ছিলেন রোমান্টিক অথচ সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল। তাঁর শেষদিকের রচনায় ব্যক্তি জীবনের ভিতর-জগত উন্মোচন করেছেন শৈল্পিকভাবে।
সমাজ থেকে ব্যক্তিতে অর্থাৎ সমষ্টি থেকে ব্যাষ্টিতে প্রত্যাবর্তন, বৃহত্তর পরিসর থেকে ছোট পরিসরে গুটিয়ে যাওয়া এবং সমাজের শরীরের যে সীমা আছে কিন্তু অন্তর্জগতের কোনো সীমারেখা বা অবয়ব নেই; সেই অন্তপুরের ছবি আঁকতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে।
পঞ্চাশের শুরুর পাকিস্তান ও বাঙালি মুসলমান ছিলো অনাধুনিক, অপসংস্কৃত, শিল্পহীন। পৃথিবীর চারদিকে জীবনে ও শিল্পে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন আধুনিক চেতনা, কিন্তু পাকিস্তানি সাহিত্য ছিলো মধ্যযুগ পরিক্রমায়। ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যের বিস্তার ক্রমান্বয়ে অনেকটা এগিয়ে যায়।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম, তাঁর ছোটগল্পের শুরুটাই ছিলো একজন শক্তিমান লেখকের অবয়বে। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বার্ষিকীতে ১৯৩৯ সালে কলেজের ছাত্র থাকাকলীন তার ‘সীমাহীন এক নিমিষে’ গল্পটি ছাপা হয়। তার সেই গল্পে রয়েছে অনেকটা পরিণত মনের স্থিরতা।
‘তার কোমল মুখে শ্রান্তির আর ব্যস্ততার ভাব দেখতে বেশ লাগে। ঠিক যেন তিন-চার বছরের ছোট্ট মেয়ের তার পুতুলের বিয়েতে চিন্তাযুক্ত ব্যস্ততার মতো।’
কিংবা
‘তার জলভরা চোখের ভেতর মধুর হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠলো, অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর ঝলমলানো রোদ ওঠার মতো’Ñ এ গল্পের শব্দের গাঁথুনী ও প্রবাহমানতায় তার বুদ্ধিবৃত্তির শিল্পবৃত্তির উচ্চতার পরিমাপ করা যায়। এ গল্প প্রকাশের চার পাঁচ বছরের মধ্যেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের একজন হয়ে ওঠেন।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম গল্প সংকলন ‘নয়নচারা’ কলকাতা থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়; এতে আটটি গল্প সংকলিত হয়Ñ নয়নচারা, জাহাজী, পরাজয়, মৃত্যুযাত্রা, খুনি, রক্ত, খ-চাদের বক্রতায় এবং সেই পৃথিবী। ‘দুই তীর’ তার দ্বিতীয় গল্প সংকলন। এর গল্পগুলো দুই তীর, একটি তুলসী গাছের কাহিনী, পাগড়ি, কেয়ারা, নিষ্ফল জীবন, নিষ্ফল যাত্রা, গ্রীষ্মের ছুটি, মালেকা, স্তন এবং মতিউদ্দিনের প্রেম।
প্রথম গল্পগ্রন্থের ‘নয়নচারা’ গল্পটি একটি গ্রামের নাম। যে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নদী। সেই গ্রামের দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত বহু লোক এসেছে কলকাতা মহানগরে দুটি ভাতের আশায়। এ গল্পটি বাংলা ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের বাস্তব চিত্রÑ দুর্ভিক্ষ ও দুঃখের গল্প। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উত্তাপ এ গল্পে উপস্থিত।
লেখকের ভাষায় :
‘ওধারে একটা দোকানে যে ককাড়ি কলা ঝুলচে সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলচে।’...
‘বহু অচেনা পথ ধরে ঘুরে আমু জানলে যে ও পথগুলো পরের জন্য, তার জন্যে নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষেরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থর থর কাঁপছে। কোন সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ উদ্রগ ব্যস্ততা।’...
মনোমুগ্ধকর বা বিচিত্র কোন কাহিনী নয়, ঘটনার পটভূমি মর্মান্তিকÑ কাহিনীটুকু উপলক্ষ মাত্র।
‘নয়নচারা শুধু’ ১৩৫০-এর কাহিনী মন্বন্তরকে উপজীব্য করে নয়। এ গল্পের মাঝে তিনি নিজেকে একজন কবি এবং চিত্রশিল্পীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেনÑ চিত্রময় ভাষায়।
নয়নচারার মতো ‘মৃত্যুযাত্রা’ গল্পটিও ধারণ করেছে ১৩৫০-এর মন্বন্তরকে। বাংলাদেশের অনাহারক্লিষ্ট জীবন্মৃত মানুষ যেন মিছিল করে মৃত্যুর পথে যাত্রা শুরু করেছে। এ গল্পে কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই, যেন লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের গল্প। অজানা গন্তব্যে চলার পথে হাজুর মা অনাহারে মারা যায়।
সেই মৃতদেহ নিয়ে সীমাহীন জাগতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে মানবিক বেদনার কথা বিধৃত হয়েছে এ গল্পে।
‘জীবন কি জীবন্ত-কবর, জীবন কি এতই ভয়াবহ?’
‘বহুদূরে একটা ঘূর্ণি উঠেছে দীর্ঘ হয়ে। হাওয়া যেন ধরণীর বুকে কী খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ ঊর্ধ্বে উঠে উন্মত্ত হয়ে চলছে; নেই নেই কিছু নেইগো কোথাও।’
অনাহার ক্লিষ্ট মানব সন্তানের মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেছেন লেখক বুভুক্ষুদের ভাষায় নয় নিজের ভাষায়।
‘হাত ভরে মুঠো মুঠো যখন কোপানো মাটি তুলে ফেলেছে, তখন করিম একবার আড়চোখে তাকালো তিনুর পানে। হাতভরা মাটি-হাতভরা ভাতের মতো মাটি; অথচ ভাত নয়...’
ক্ষুধায় কাতর মানুষগুলোর প্রয়োজন বাঁচার জন্য একমুঠো ভাত। ওদের ধারণা ওই গ্রামে এক চৌধুরী সাহেব আছেন তার পা ধরে অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই দুটি আহার মিলবে। গল্পকারের ভাষায়Ñ
‘ওদের মধ্যে আশাটা এরই মধ্যে এত দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, তা নির্ভুল সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। গায়ের চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে যেন দাওয়াত এসেছে।’
হাজুর মায়ের পর হাজুর বাবাও মরে গেল। সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। তারপরই ঘটলো অসহ্য বিরক্তির উদগিরণ। ক্ষুধার কাছে মৃতদেহ সৎকার গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।
‘থাক পরি বুড়োর লাশ। রেগে তোতা বললো’
‘তারপর সন্ধ্যা হলো, হাওয়া থামলো, ক্রমে ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইলো অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো’
১৩৫০ মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে শিল্পী জয়নুল আবেদিনের চিত্রাঙ্কন যেমন রেখার কবিতা, তেমনি বলা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্প ও শব্দে আঁকা ছবি ‘নয়নচারা’ ও ‘মৃত্যুযাত্রা’ গল্প দুটিও।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ‘জাহজী’ গল্পটি মানব মনের চিরকালীন পিতৃত্বের মায়াবী কাহিনী। সারেং সারাজীবন জাহাজে জাহাজে কাটিয়ে জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে গেছে। শুকনো ডেক ঘটঘট করে বুটের শব্দ। করীম সারেং নিঃশব্দে হাঁটছে তবু যেন জোরালো খট খটে শব্দগুলো তার পিছু তাড়া করছে। সাগর থেকে সাগরে ফেরা করীম সারেংয়ের মনটা মাঝে মাঝে ঘাসভরা মাটির টানে হাহাকার করে উঠতো। তেমনি এক নীরস জীবনে জাহাজে একটি ছোট্ট ছেলেকে দেখে নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতার গভীরতা, বেদনার বাঁধভাঙা স্রোতের মতো উত্তাল হয়ে উঠলো। কারণ তার সাগরে ভেসে থাকা নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গ থাকলে এমনি একটি ছেলে তারও হতে পারতো। দাঁড়াতো তার সামনে আপাত্য স্নেহের দাবিদার হয়ে।
ছাত্তারের মা-বাবা আছে আরো রয়েছে তার ভাই বোন; সারেং গোগ্রাসে তার কাহিনী শুনলো। যখন জানলো সাত্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে তখন সে ক্ষুব্ধ হলো অপ্রত্যাশিতভাবে। সাত্তার যখন চিফ অফিসারের লাথি খেয়েছে শুনলো তখন তার মনে চিরকালের আপাত্যস্নেহ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সারেং সাত্তারকে হুকুম করে জাহাজ বন্দরে ভেড়া মাত্র যেন সে নেমে পড়ে এবং বাড়িতে যেন ফিরে যায়। এ যেন তার পিতৃত্বের দাবির হুকুম। ‘গল্পের শেষটুকু’ এ রকম : ‘কয়েকজন লস্কর নাবছে মৃদু গুঞ্জন করে। সে দলে সাত্তারও রয়েছে। তার মুখে মুক্তির ঔজ্জ্বল্য। তবে সে যাত্রা নত করে নাবছে বলে ওপর থেকে তার মুখে দেখা যাচ্ছে না... করিম সারেং প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো আবছা হয়ে চোখ দুটো তার দীনতায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। ও তাকাল না।’
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ‘নয়নচারা’ ও ‘দুই তীর’ বিশ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত। নয়নচারা গল্পগ্রন্থে সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে প্রতিভূ মানুষদের এনে তাদের দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করিয়েছেন নিজ নিজ শ্রেণির। যুদ্ধ, মৃত্যু, দৈন্য, দুর্ভিক্ষের বাংলাদেশ এবং এর মধ্যযুগীয় প্রভাব তার এ সব গল্পের উপাদান।
‘দুই তীর’ গল্পে লেখক আলো ফেলেছেন সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শ্রেণির ভেতর আঙ্গিনায়। সেখানে আপাত উজ্জ্বলতার আড়ালে যে হতাশা বঞ্চনা, দীনতা, নিষ্প্রেম তারই চিত্রাংকন করেছেন তিনি। এখানে নায়ক-নায়িকার জীবন-মিলন অসম্ভব নদীর দুই তীরের মতো।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ দেশ বিভাগের পটভূমিতে লেখা একটি অসাধারণ গল্প। সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ বিভক্তির করুণ পটভূমিতে রচিত গল্পটি। তুলসীগাছটি শুধু গাছ নয়, প্রতীকী মানুষের বিভাজনের কাহিনী।
‘স্তন’ গল্পটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি অন্যতম গল্প। নিজ সন্তানের মৃত্যুর পর মানববৈকল্যে নির্বাসিত মা অপরের সন্তানকে দুধ দেয়ার জন্য অস্বাভাবিক মানসিকতায় ঘুরে দাঁড়ালেন। দুধহীন নারী কাঁটা দিয়ে নিজ স্তনের সুচাগ্রে ছেদন করে দুধ বের করে অন্যের সন্তানের মুখে অপত্যস্নেহে চেপে ধরেন। গল্পের শেষ বাক্য, ‘তার স্তন থেকে দুধ ঝরে অশ্রান্তভাবে, তবে সে দুধের বর্ণ সাদা নয় লাল।’
স্বল্প পরিসরে সার্বিকভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সমস্ত গল্পের আলোচনা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ছোটগল্পের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ নিঃসন্দেহে বলা যায়।
মূলত গল্পকার হলেও তিনি ‘লালসালু’র মতো উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন।
পঞ্চাশের দশকের আগেই পূর্ববঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রচিত হয়েছিল : শওকত ওসমানের ‘জননী’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ এবং আবু ইসহাকের ‘সূর্যদীঘল বাড়ি”।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের মধ্যে দুটি ধারা প্রবাহিত, একটি আবহমান বাংলার ছোটগল্পের ধারা; অন্যটি বাঙালি মুসলমান বাহিত ছোটগল্পের ধারা। তার ছোটগল্পের মধ্যে সাধারণ মানুষ অনেকটুকু জায়গা করে নিয়েছে। অনায়ক নায়ক হয়ে উঠেছে গল্পে, অন্যটি বহির্জীবনের পালা অনেকটুকু চুকিয়ে বাংলা গল্প হয়েছে অন্তর্মুখী। নয়নচারা গল্পগ্রন্থের আটটি গল্পের নায়কই উঠে এসেছে নিম্নবিত্তের জীবন থেকে ভিখিরি, চোর, সারেং, মাঝি, দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন মানুষ।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের সংখ্যা পঞ্চাশ-বাহান্নটি এবং উপন্যাস মাত্র তিনটি।
দুটি গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে সতেরোটি গল্প, বাকি গল্পগুলো তাঁর জীবদ্দশায় ছিল অগ্রন্থিত। তার গল্পের বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত নয়, কিন্তু কথাশিল্পী হিসেবে তিনি স্বকীয়তার উজ্জ্বল। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে নিজস্ব শৈলী ও ঢঙ রপ্ত করেছিলেনÑ যা তার সামসাময়িকদের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা ছোটগল্পের এক বড় স্তম্ভ নির্দ্বিধায় বলা যায়।