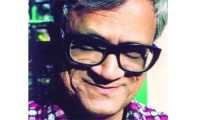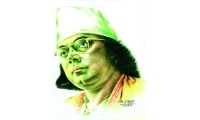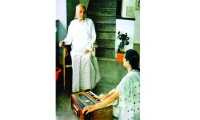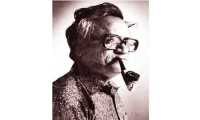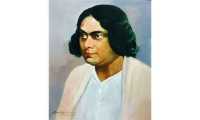literature » samoeky
খালেদ হামিদীর দৌত্যে ওরহান পামুক
মহীবুল আজিজ
ওরহান পামুক
‘আদার কালারস্’ গ্রন্থে ওরহান পামুক যাঁদের নিয়ে লিখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজস্ব ভাষায় অপিচ বিশ্বসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা রচয়িতা। খালেদ হামিদী তাঁর সীমাবদ্ধ কলেবরের ভাষান্তরে যাঁদের নিয়ে আসেন তাঁরাও একেকজন নবদিগন্ত উন্মোচনকারী হিসেবেই স্বীকৃত
ওরহান পামুক সেই সৎ ও সাহসী লেখক যিনি জন্মসূত্রে তুর্কি হয়েও তুরস্কের দ্বারা সংঘটিত আর্মেনিয় গণহত্যারসত্যকে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর সৃজনশীল প্রতিবাদী সত্তা দিয়ে সেই ভয়ংকর অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদকরেছেন। তাঁর যে-কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ করতে পেরেছি, পাঠ করে মনে হয়েছিল, আহা যদি তুর্কি ভাষাটাও শেখাযেতো! বিহারি আবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রানুরাগে নিমজ্জিত হয়ে বাংলা ভাষা শিখে এক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সাহিত্যেরসমালোচকই হয়ে গেলেন। আমি না হয় মূল ভাষায় পামুকই পড়ি। কিন্তু জীবন আমাকে এডওয়ার্ড লোবোর ধরনে বলে, ‘লাইফ ইজ আ ওয়ান ওয়ে রোড’ ম্যান! তাই তো, পেছনে তাকিয়ে দেখি সেই রাস্তার অনেকখানিই পেরিয়ে এসেছি। কাজেই ইংরেজিতে পামুক-পাঠেই আমাকে ঢেকুর না তুললেও থাকতে হবে পরিতৃপ্ত।
‘স্নো’, ‘ব্ল্যাক ক্যাসল’, ‘মাই নেম ইজ রেড’ এই তিনটি উপন্যাসের সমান্তরালে তাঁর অপূর্ব আত্মজীবনী ‘ইস্তানবুল’ পাঠ করে আমি এক অসাধারণ কথকের দেখা পাই যিনি তাঁর ভাষা ও বিষয়ের কুশলতায় নিজস্ব স্থানীয়তা থেকে ক্রমে হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক। এই স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুস্বাদু পাঠ আত্মস্থ করতে না করতেই হাতে আসে তাঁর বিচিত্র গদ্যের একখানা গ্রন্থ ২০০৭-এ প্রকাশিত ‘আদার কালারস্’। যদিও মূল তুর্কি ভাষায় এটি প্রকাশ পায় ১৯৯৯ সালে। বিশ্বসাহিত্যের পঠনপাঠন, জীবনাভিজ্ঞতার উপস্থাপনা, কথকতার মুন্সীয়ানা সবকিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এ-বইয়ে। আবার, বাড়তি পাওনা যদি বলি: রয়েছে ২০০৫-এর এপ্রিলে বিখ্যাত ‘প্যারিস রিভ্যু’কে দেওয়া একটি চমৎকার সাক্ষাৎকার, একখানা গল্প (‘টু লুক আউট দ্য উইনডো’) এবং তাঁর নোবেল-বক্তৃতা যেটির শিরোনাম‘আমার বাবার স্যুটকেস’। সাক্ষাৎকারটির এক জায়গায় পামুক তাঁর ‘ইস্তানবুল’ সম্পর্কে যে-কথাটা বলেছেন সেটা বেশ মজার:‘ইস্তানবুল’হলো অর্ধেক তাঁর আত্মজীবনী এবং বাকি অর্ধেক এই শহর নিয়ে তাঁর লেখা কিংবা আরও ভালোভাবে বললে এক বালকের চোখে সেই শহরটার চিত্রাবলি। তাঁর যে-লেখাই আমরা পড়ি না কেন পামুককেতাঁর জনপদ, প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই স্থিত হিসেবে পাওয়া যাবে। তাঁর দেখার চোখে একই সঙ্গে তিনি ও তাঁরপরিপার্শ্ব একটি অন্যটির পরিপূরক।
২০২৫-এর বইমেলা উপলক্ষে ‘দ্বিমত’-প্রকাশিত খালেদ হামিদী’র ‘ওরহান পামুকের নির্বাচিত গদ্য’ পড়ে বাংলা ভাষায় ওরহান পামুকের সাহিত্যিক উপস্থিতি অনুভব করা গেল এবং জেগে উঠলো ওরহানের আরও রচনা বাংলায়পাঠের ঔৎসুক্যও। হামিদী অনূদিত পামুকের সর্বমোট নয়টি প্রবন্ধ নেওয়া হয়েছে পামুকের ‘আদার কালারস্’ গ্রন্থ থেকে যেটি তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় বলা আছে। তুর্কি থেকে মরিন ফ্র্রিলিকৃত ইংরেজি গ্রন্থটি অবশ্য বিপুলকলেবর। ছয়টি বিভিন্ন শিরোনামে সর্বসাকল্যে ৭৩টি রচনা আমরা পাই পামুকের সে-গ্রন্থে। রচনাশ্রেণির উপশিরোনামগুলো চিত্তাকর্ষক: ‘জীবনযাপন এবং উদ্বেগ’, ‘গ্রন্থ এবং পাঠ’, ‘রাজনীতি, ইউরোপ ও সত্তার বিবিধসমস্যা’, ‘আমার গ্রন্থ আমার জীবন’, ‘চিত্র এবং উৎকীর্ণ পাঠ’, এবং ‘অন্য শহর অন্য সভ্যতা’। পামুকের মরিন ফ্রিলিকৃত ইংরেজি গ্রন্থের ৪৩৩ পৃষ্ঠার বিপরীতে খালেদ হামিদীকৃত বঙ্গানুবাদের ৮৮ পৃষ্ঠার এক-পঞ্চমাংশ পামুক উপস্থিতিকে অপ্রতুলতার দায়ে দায়ী করা যায় বটে কিন্তু ক্ষুদ্রে বৃহতের প্রতিফলনের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বিশেষ করে গল্প কিংবা উপন্যাস অনুবাদের চাইতেও প্রবন্ধ বা গদ্যানুবাদ যে খানিকটা দুরূহ সেটা বলাবাহুল্য। প্রবন্ধে নিহিত বক্তব্য, বিচার-বিশ্লেষণ, জীবনাভিজ্ঞতা, দার্শনিকতা এইসব জটিলতার মুখোমুখি হওয়া অনুবাদককে ফের বোধ্য এক প্রতিস্থাপনের কাজটিকে করতে হয় দারুণ কুশলতার সঙ্গে। কাজেই পামুকের গদ্যানুবাদের মতো কঠিন কাজটিকে বাংলায় বয়ে আনবার এমন উদ্যোগকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।
ওরহান পামুকের ‘গ্রন্থ এবং পাঠ’ পর্যায়ের লেখাগুলোর একটা সমান্তরাল দিক রয়েছে। একদিকে ভিন্ন ভাষা ওভিন্ন জাতির মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রচনাবলি এবং অন্যদিকে সেসব রচনা পাঠোত্তর পামুকের প্রতিক্রিয়া ওবিশ্লেষণ। যেমন ধরা যাক আরব্য রজনীর গল্প, সালমান রুশদি, দস্তয়েভস্কি, হুগো, কাম্যু, নবোকফ, মারিও ভার্গাস য়োসা, টোমাস বেয়ানহার্ট এসব লেখক এই বিশ্বের বিচিত্র গোলার্ধের বিচিত্র মানুষ সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে উপস্থিত তাঁদের রচনায়। পামুকের যে অন্যতম প্রিয় লেখক দস্তয়েভস্কি সেটা বোঝা যায় গ্রন্থে তাঁর ওপর তিনটি লেখা থেকে। তিনটি রচনারই বঙ্গানুবাদ করেছেন খালেদ হামিদী। জার্মানভাষী অস্ট্রিয় টোমাস বেয়ানহার্টকে (১৯৩১-১৯৮৯) নিয়েও রয়েছে পামুকের দু’টি লেখা। বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান ভাষার লেখকদের মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী লেখকদের একজন টোমাস। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বজুড়ে।গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা, পাঠক্রিয়ায় শব্দ, চিত্র, গ্রন্থপাঠের আনন্দ এমনকি বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পের নান্দনিকতা নিয়েও রয়েছে তাঁর ছোট্ট একটি রচনা। পামুক লিখেছেন, কখনও কখনও বইয়ের দোকানের দিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে পারে দোকানে সাজানো বইগুলোই নয় বরং ঐসব বইয়ের নান্দনিক প্রচ্ছদগুলো।
যাহোক যে-রচনাগুলো খালেদ হামিদীর অনুবাদ-গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে সেগুলোর খোঁজ নেওয়া যাক: ‘কারামাজভভাইয়েরা’, দস্তয়েভস্কির ‘পাতালবাসীর দিনলিপি’ : অধঃপতনের আনন্দ, দস্তয়েভস্কির ভীতিকর দানবেরা, আলব্যের কাম্যু, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য ও সময় : নবোকভের ‘অ্যাডা এবং লোলিটা’, মহত্ত্বের জন্যে ভিক্টর হুগোর আবেগী অনুভূতি, ‘এক হাজার এক রাত’ : পড়া বা না পড়া, মারিও ভার্গাস য়োসা এবং তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য এবং পড়ার আনন্দ। সবগুলো প্রবন্ধই ‘গ্রন্থ এবং পাঠ’ পর্যায়ের এবং কোনো না কোনো গ্রন্থ নিয়ে। কেবল সর্বশেষ লেখাটিতে (পড়ার আনন্দ) গ্রন্থপাঠে পামুকের মানসিক আনন্দক্রিয়ার এক সংক্ষিপ্ত অথচ সরস বর্ণনা পাওয়া যাবে। বইপড়া এবং পাঠের আনন্দ নিয়ে লেখা পৃথিবীর বহু লেখকের বহু রচনার কথা বলা যাবে। ছাত্রজীবনে আমরা পড়েছিলাম প্রমথ চৌধুরী কিংবা সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা কিংবা এল. এ. জি. স্ট্রং-এর ‘রিডিং ফর প্লেজার”।মনে পড়ে, মজার কথা লিখেছিলেন স্ট্রং। ছাত্রজীবনে সবাই বই পড়ে শিক্ষকদের খুশি করবার জন্য। খুব কম শিক্ষার্থীই সেই বইকে আনন্দসঙ্গী করে তুলতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে যারা সেই বইগুলোর পাঠে অনুপ্রাণিত করবার জন্য তাদের শ্রেণিশিক্ষকদের নিকটে ঋণী থেকে যায়। এমনকি শ্রেণিকক্ষে পড়তে বলা সেই বইগুলোই কারো কারো জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ওরহানের প্রবন্ধটি অবশ্য শুরু হয় স্তাঁদাল-এর ‘চার্টারহাউজ অব পার্মা’ পাঠের আনন্দের বর্ণনা দিয়ে। সে-অর্থে এটি আর পাঠানন্দের সার্বজনীনতার মধ্যে না থেকে চলে যায় স্তাঁদালের উপন্যাসেরই আলোচনায়। লেখাটাতে পামুক স্তাঁদালের সূত্রে একটি চমৎকার গ্রন্থপাঠের দিকগুলোতেও আলো ফেলতে সক্ষম হন। সর্বমোট এগারোটি পয়েন্টে পামুক তাঁর স্তাঁদালের উপর্যুক্ত গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। স্তাঁদালের বইখানা পামুক পড়েন তাঁর কুড়ি বছর বয়সে অর্থাৎ তরতাজা তারুণ্যের সুবর্ণখচিত কালে। কিন্তু তিনি কখনোই তাঁর সেই পাঠের স্মৃতি ভুলতে পারেন না। এমনকি নিজের জীবনের নানা অনুষঙ্গকে তিনি মিলিয়ে দেখেন তাঁর পঠিত গ্রন্থটির সঙ্গে। ক্ষীণকায় এ-লেখা সত্যিকার অর্থে এক অসাধারণ আত্মবীক্ষণ এবং গভীর দর্শনোন্মোচনের নমুনা যেখানে একটা বইকে জীবনের বিষয়বুদ্ধি নয় বরং মহত্তর উপাদানগুলোর সন্ধানে এক কার্যকর অনুঘটক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন পামুক। খালেদ হামিদীর অনুবাদ থেকেখানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:
“এভাবে, বইটি পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা একটি লক্ষ্য হিসেবে আমার আনন্দের সাথে মিশে গেছে। এ কারণেই আমি বইটিকে একটি তাবিজের মতো বহন করেছি যা আমাকে আনন্দ দিতে পারে। এমনকি আমি এমন জায়গায় যাওয়ার সময়ও একে সাথে রেখেছি যেখানে পড়ার সময়ই ছিল না। কোথাও থাকাকালে যখন আমি বিরক্ত বা মর্মাহত বোধ করতাম তখন এলোমেলোভাবে বইটি খুলতাম। একটি অনুচ্ছেদ পড়তাম এবং শান্ত হতাম। তখন বইয়ের পৃষ্ঠা এবং প্রচ্ছদ আমাকে এর শব্দগুলোর মতোই আনন্দ দিত। যত পড়েছি বইটি ততই আমাকে আনন্দদিয়েছে।”
মনে রাখতে হয়, তুর্কি ভাষায় লেখা পামুকের কথাগুলো ফ্রিলির ইংরেজি হয়ে তারপর এলো হামিদীর বাংলায় কিন্তু পড়বার পর সত্যিই বুঝতে পারা যাচ্ছে মানব-রচিত একটি গ্রন্থ যা ওরহান নামের কুড়ি বছর বয়স্ক এক তুর্কিযুবককে আমূল নাড়িয়ে দিচ্ছে যে কিনা কেবল পাঠ নয় সত্তায় বয়ে বেড়ায় সেই বইয়ের আরও নানা খুঁটিনাটি। অথচ বইটি ফরাসি ভাষায় (লা শাঘ্ৎঘুজ দ্য পাঘ্ম) লেখা হয়েছিল পামুকের জন্মেরও ১১৩ বছর আগে, দস্তয়েভস্কির‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্টের’ও ২৮ বছর আগে। আমার কেন জানি মনে হয়, বিশেষত ‘ইস্তাম্বুল’ পড়তে গিয়ে কোথাও যেন একটা ঘণ্টাধ্বনি বাজে, মনে পড়ে স্তাঁদালকে, তাঁর এই উপন্যাসের দিকে সমান্তরালে দৃকপাত করে।পরিণত বয়সে এসেও পামুক ভোলেন না তাঁর যৌবনের পাঠমগ্নতার সময়টাকে: “আমি এখনও সেই যুবকের প্রতি স্নেহ অনুভব করি যে তখন বইটি হাতে তুলে নেয়। এবং যে তার মনকে একটি নতুন জগতের দিকে উন্মুক্ত করতে এবং একজন ভালো মানুষ হতে অত আগ্রহের সাথে এটি পাঠ করে।” বালজাক অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়নকরেছিলেন স্তাঁদালের এ-উপন্যাসকে। মহত্ত্বের দিক থেকে এটিকে তিনি তুলনা করেছিলেন রাসিন-এর (১৬৩৯-১৬৯৯) পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডি ‘ফেড্রে’র সঙ্গে। লেখাটার শেষ দিকে এসে পামুক যে-কথা বলেন, সত্যিকার অর্থে তখনজীবন-জগতের কোলাহল-কর্মযজ্ঞ এসবকে মনে হয় তুচ্ছ, নগণ্য, জেগে থাকে শব্দাবলিতে উচ্চারিত প্রাচীন ভাবনা- ঘটনার দৃশ্যায়ন, কখনও তা হয় না ম্লান: “শেষ পর্যন্ত একটি বিস্ময়কর উপন্যাস আমাদের জীবন এবং চারপাশেরজগতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, যা আমাদের জীবনের অর্থের কাছাকাছি নিয়ে আসে।” কী অসাধারণ মূল্যায়ন পামুকের। মূক শব্দের কারিগর শক্তিমান মানুষ কীভাবে এক স্বতন্ত্র পৃথিবীর ¯্রষ্টা হয়ে ওঠে সেটা ছোট্ট অথচ ধন্বন্তরী একটি লেখায় ফুটিয়ে তোলেন পামুক।
ওরহান পামুকের মূল বইতে দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে লেখা আছে সর্বমোট তিনটি এবং খালেদ হামিদীও তিনটি প্রবন্ধেরই অনুবাদ করেন। মানে তাঁর বইয়ের এক-তৃৃতীয়াংশই মহান ফিওদর দস্তয়েভস্কির দখলে। নিঃসন্দেহে সেইদখলদারিত্বের বিষয়টি গৌরবময়। ‘আদার কালারস্’ পড়বার সময় ওরহান পামুকে দস্তয়েভস্কির নাক্ষত্রিক উপস্থিতি দেখে ভেবেছিলাম আমার অতি প্রিয় উপন্যাস ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো লেখা থাকবে। তানেই, তথাপি দস্তয়েভস্কির তিনটি উপন্যাস-পাঠের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই রুশ লেখকের অপরিমেয়গৌরবকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন ওরহান। দস্তয়েভস্কি হলেন সেই ঔপন্যাসিক যাঁর কোনো লেখাকেইগুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করা সম্ভব নয় এবং প্রয়াণের বহুকাল পরে এসেও তাঁরা বৈশ্বিক লেখকই রয়ে যান যদিও তাঁরা মূলত লিখেছিলেন তাঁদের স্থানীয় ভাষায়। দস্তয়েভস্কি, তলস্তোয়, গোগোল, পুশকিন, তুর্গেনিয়েফ এরকম আরও অনেক রচয়িতার কথা বলতে পারা যায় এবং পামুকও জানান সেইসব অমর লেখকদের পাঠের আনন্দ।
দস্তয়েভস্কির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস নিয়ে লিখেছেন পামুক: ‘নোটস্ ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড’, ‘ডেমোন্স’ এবং ‘দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ’। ‘নোটস্ ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড’-এর পাঠপ্রতিক্রিয়ার জন্য চমৎকার শিরোনাম দেন পামুক: ‘অধঃপতনের আনন্দ’। প্রথম পাঠের ত্রিশ বছর পরে দ্বিতীয় পাঠের নিরিখে উপন্যাসটি নিয়ে তাঁর লেখা। পাপ, হত্যা, অধঃপতন- মনুষ্যজগতের এইসব বিষয়কে এতোটা গুরুত্বের সঙ্গে উপন্যাসে তুলে আনেন যে মনে হয় একটা ভয়ংকর দুর্যোগের পৃথিবীকেই দস্তয়েভস্কি জীবনভর বর্ণনা করে গেছেন এবং তাঁর সেই বর্ণনায় উদ্ভাসিত হয় মানুষের টিকে থাকার বাস্তবতারই বৃত্তান্ত। অবশ্য ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’ও থাকে সমান্তরালে। এই উপন্যাসের নায়ক রাসকলনিকভকেই অন্য মাত্রায় পামুক দেখতে পান ‘নোটস্ ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড’-এ। এখানে মনে রাখা দরকার, ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ এই ধারণাটি দস্তয়েভস্কির উপন্যাস-মনন ভাবনার একটি মৌলিক দিক। যে-মানুষ মনের দিক থেকে সাধারণ সমাজে থেকেও বিচ্ছিন্নতার বোধে আক্রান্ত সে-ই ‘পাতালবাসী’, সেই পাতালই হলো ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’। আমাদের মনে পড়ে, ফরাসি কবি বোদল্যার উনিশ শতকের মধ্যভাগে কবিতা লিখেছিলেন ‘আউটসাইডার’ শিরোনামে। পরে ১৯০৮ সালে বেরোয় ফরাসি ঔপন্যাসিক অঁরি বারবুসের উপন্যাস ‘নরক’ যেখানে ‘আউটসাইডার’ বিষয়টাকে দার্শনিকভাবে তুলে ধরা হয়। তারও পরে. ১৯৪২ সালে প্রকাশ পায় আলব্যের কাম্যু’র ‘আউটসাইডার’ এবং আমরা পেলাম একটি ভিন্নতর ধারণা: আউটসাইডার-কমপ্লেক্স। বস্তুত দস্তয়েভস্কির ‘পাতালবাসী’ মানবেরউত্থানের কারণ সমাজের গর্ভেই নিহিত এবং সেই মানবেরা যুগে-যুগে উদ্ভূত হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। তাই ফরাসি লেখক আন্দ্রে জিদ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, দস্তয়েভস্কি যা-ই লিখে গেছেন তার সবইপাঠের জন্য প্রয়োজনীয়। এর কোনো কিছুকেই বাদ দেওয়ার উপায় নেই। তাঁকে একজন অসাধারণ মনোবিজ্ঞানী বলেও মনে করতেন জিদ।
আঠারো বছর বয়সে ‘কারামাজভ ভাইয়েরা’ পাঠের স্মৃতি থেকে আমরা দেখবো পামুক সত্যিকারের একজন ভবিষ্যৎকথাশিল্পীর পাঠ যথেষ্ট কম বয়স থেকেই নিতে শুরু করেছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর পর্যবেক্ষণের চোখ ছিল শব্দশিল্পীর এবং ভাবনার মস্তিষ্ক ছিল শিল্পীর। আমার ইচ্ছে হয় পামুকের সমগ্র দস্তয়েভস্কি-মূল্যায়নের আমি উদ্ধৃতি দিই কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তবু পামুকের এই দস্তয়েভস্কি-বন্দনার মৌলিকতা যথার্থ বলেই মেনে নিতে হবে। খালেদহামিদীর অনুবাদে খানিকটা অনুসরণ করতে পারি তাঁকে:
“কারামাজভ ভাইয়েরা এবং তাঁর অন্য মহৎ উপন্যাসগুলোয় লেখা কী সেই গোপন কথা দস্তয়েভস্কি যা আমার কানে ফিসফিস করে বলেছেন? তা কি এই যে ঈশ্বর বা বিশ্বাস লাভের স্পৃহা আমি অনুভব করব, যদিও, আমাদের মধ্যে যে-কোনো কিছুতে শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখার মতো কিছুই কখনোই থাকবে না। তবে কি এটাই মেনে নেয়ার ছিল যে আমাদের ভেতরে বসবাসকারী এক শয়তান আমাদেরই গভীরভাবে উপলব্ধ বিশ্বাসকে গালাগাল করছে?” উদ্ধৃতি একটু পরপরই দেওয়া চলে। কেননা, দস্তয়েভস্কির মতোন এমন ঔপন্যাসিকের সম্পর্কে অজ¯্র কথায়ও ক্লান্তি আসবার নয়। কী চমৎকার পামুকের কথাগুলো। প্রয়াণের এতোকাল পরেও পিটার্সবুর্গে সমাহিত শব্দজাদুকরেরনিত্য-উপস্থিতিকে এড়ানো অসম্ভব: “দস্তয়েভস্কির মতো লেখকের জন্য পৃথিবী একটি স্থান যা সুন্দর হয়ে ওঠার জন্য প্রক্রিয়াধীন, অপূর্ণাঙ্গ, কোনো-না-কোনোভাবে সীমাবদ্ধ।” ওরহান পামুকের দৃষ্টিতে দস্তয়েভস্কি পাঠে আমরাবুঝতে সক্ষম হই কেন বিশ্বময় দস্তয়েভস্কির এতো অনুরাগী, কেন শুধু শব্দের শক্তি দিয়েই বিশ্ব জয় করে চলেনরুশ ফিওদর। পামুক তাঁর মূল্যায়নে কেবলই অনুরাগী পাঠকের আলো ফেলেন নি, দস্তয়েভস্কির দার্শনিক প্রত্যয়, তাঁর সমকালীন রাশিয়া ও ইউরোপের দ্বান্দ্বিকতা যা হয়তো সমগ্রর ব্যষ্টি-প্রতীক দস্তয়েভস্কির মাধ্যমে আভাসিতহয়, তাঁর ‘দানবেরা’ উপন্যাসে যার ছায়া আমরা লক্ষ করি। দস্তয়েভস্কির জীবনটা খুব স্বস্তির জীবন ছিল না। সমকালীনরাশিয়া ও ইউরোপিয় রাজনীতির স্নায়ুছেঁড়া বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না দস্তয়েভস্কি পাঠের সমান্তরালে। এটাও কী আমরা ভুলতে পারি, মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে না-ই হয়ে যেতেন কথকতার এই মহান শিল্পী। দস্তয়েভস্কি তাঁর রুশ চেতনা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন সমগ্র ইউরোপের মানসকে এবং কেন বিবিধ মানচিত্রে বিবিধ স্বার্থ বিশ্বাস, সংস্কার, ঘৃণা, হিংসা, উগ্রতা এসব হয়ে দেখা দেয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ এসবের ভেতর দিয়ে কিন্তু জীবনের মৌলিক দাবিগুলো যে শেষ পর্যন্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অস্তিত্বেরই লড়াই সে-সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। যে-দস্তয়েভস্কিকে আমরা ভালোবাসি, তাঁকে ভালোবাসবার কারণগুলো আরও একবার আমাদের উপলব্ধি করবার সুযোগ করে দেন ওরহান পামুক। আন্দ্রে জিদের পর এতটা মনোজ্ঞ ও সৃজনশীলভাবে ওরহানকেই আমরা দেখবো দস্তয়েভস্কির সার্থক বিশ্লেষক হিসেবে।
‘আদার কালারস্’ গ্রন্থে ওরহান পামুক যাঁদের নিয়ে লিখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজস্ব ভাষায় অপিচ বিশ্বসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা রচয়িতা। খালেদ হামিদী তাঁর সীমাবদ্ধ কলেবরের ভাষান্তরে যাঁদের নিয়ে আসেন তাঁরাও একেকজন নবদিগন্ত উন্মোচনকারী হিসেবেই স্বীকৃত। কাম্যু, নবোকভ, হুগো কিংবা য়োসা এঁরা কালের ক্রমে হয়তো এক থেকে আরেকের দূর পরম্পরায় অবস্থিত কিন্তু আজকের লেখক-শিল্পী কিংবা আজকের পাঠকের চোখে তাঁরা অনিবার্যতার নিকট আবশ্যকীয়তায় দাঁড়ানো। পামুক আমাদের এই উপলব্ধিতে নিয়ে যান, আজকের যিনি লেখক, এখনই যিনি লিখবেন বলে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁকে সমান গুরুত্বে পাঠ করতে হয় উনিশ শতকের স্তাঁদাল-দস্তয়েভস্কি-হুগো এবং বিশ শতকের কাম্যু-নবোকভ-য়োসা। তাঁর ‘আদার কালারস্’-এর পাঠকহিসেবে নিঃসন্দেহে সবচাইতে উপকৃত হবেন লেখকই যে-লেখক রচয়িতা হয়ে গেছেন এরিমধ্যে এবং যিনি রচয়িতার সারিতে গিয়ে দাঁড়াবেন সামনের দিনে। মানুষ কেন লেখে, আমরা ‘কেন লিখি’ এ-বিষয়ে অনেক লেখকের বক্তব্যই রয়েছে আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে। পামুকের মূল্যায়ন সামনে রেখে সেসবকে ঝালাই করে নেওয়া যায়। মানিক, কমলকুমার, অমিয়ভূষণ, হাসান আজিজুল হকের লেখালেখি সম্পর্কিত আত্মপ্রতিবেদনগুলি মনে পড়ে। কেনআমরা প্রাক্তন লেখকদের লেখা পড়বো তার কারণটাও পামুক দেন চমৎকারভাবে। আমরা পড়বো, কেবল তাঁদের পৃথিবীটাকে বুঝবার জন্য নয়, পরম্পরাটাকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য এবং শব্দের মধ্য দিয়ে যে-ভুবনকে আমরা নির্মাণ করবো সেটিকেও গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য তাঁদের শরণ নিতে হয় আমাদের। হাঁ, পামুক এমনও বলেন, তাঁদের যে আমাদের সর্বদাই প্রয়োজন তা না-ও হতে পারে কিন্তু সৃজনশীলতা দিয়ে নির্মাণের উদ্যোগে তাদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যা লিখবো বা লিখবো না তা লেখা হয়েছে কিনা সেই সংবাদটাওআমাদের নিতে হয় আমাদের সেইসব মহান পূর্বসূরীর কাছ থেকে। ধরা যাক, ‘আ্যাডা’-‘লোলিটা’র রচয়িতাঅভিবাসী রুশ-মার্কিন ভøাদিমির নবোকভের কথা। ওরহানের মূল্যায়ন থেকে: “যদি সৌন্দর্যের ‘সময়হীনতা’একটা বিভ্রম বা মায়া হয়ে থাকে তা হলে তা স্বয়ং নবোকভের জীবন ও কালেরই প্রতিফলন। তা হলে কীভাবে আমিএ সৌন্দর্য দ্বারা প্রভাবিত হই, যেমনটি নিষ্ঠুরতা এবং শয়তানিযোগে একটি ফাউস্টিয় সন্ধি দ্বারা তা অন্তর্লিখিত হয়?” নবোকভ-সাহিত্যের নিষ্ঠুরতা ও সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পামুক চলে যান আরও এক বৃহত্তর পর্যটনে,যেখানে রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকার বিশাল-জটিল বাস্তবতা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপাদান হয়ে ঢুকে পড়তে থাকে নবোকভেরচেতনাজগতে এবং একসময়ে সেসব একে-একে অবারিত হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। কাজেই কোনো লেখককে কেবল কিছু শব্দের ¯্রষ্টা হিসেবে দেখবার বিলাস ঠিক সেই লেখককে কিংবা বৃহত্তর অর্থে সাহিত্যকে বুঝবার পক্ষে কার্যকর কোনো যুক্তি নয়। লেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাঠের প্রক্রিয়ার যে-গভীর ও সান্দ্র সম্পর্ক রয়েছে সেটিকে পামুক তাঁর পাঠাভিজ্ঞতার আলোকে সার্থক বলেই প্রতিপন্ন করেন।
ওরহান পামুকের নির্বাচিত গদ্যের অনুবাদে খালেদ হামিদীর ‘মারিও ভার্গাস য়োসা এবং তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য’ শিরোনামাঙ্কিত রচনাটির নির্বাচন একদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে একজন বিশুদ্ধইউরোপিয় লেখকের সঙ্গে ওরহানের রয়েছে কিছু মৌলিক পার্থক্য। ১৯৮৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে জাপানি-ব্রিটিশলেখক কাজুয়ো ইশিগুরো বলেছিলেন, সালমান রুশদি এবং মো’র মতো অ-ইংরেজ সাংস্কৃৃতিক প্রেক্ষাপটের লেখকেরাও আন্তর্জাতিক এবং ইংরেজ ভুবনের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। একসময় মনে করা হতোইংল্যান্ডই সবকিছুর কেন্দ্র কিন্তু বৈশ্বিক বাস্তবতার ক্রমসম্প্রসারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবহাওয়ায় সেই পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। ইশিগুরো ইংল্যান্ডের সেই কেন্দ্রীয় বাস্তবতার মধ্যে পরবর্তীতে একটি মিশ্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার উদ্ভবের মধ্যে এক নতুন দিগন্তের বিরাজমানতা লক্ষ করেন যেটিকে আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকেনা। এখানে মনে রাখা দরকার, ওরহান পামুকের দ্বিসাত্তিক অবস্থান মানে তুরস্কের সমন্বিত এশিয়-ইউরোপিয়অবস্থানে দাঁড়ানো তাঁর বক্তব্য তাই ভিন্নতর ব্যঞ্জনা পায়। আবার, এ-ও এক সত্য, পামুক এমন এক দেশ-জাতির মানুষ যারা কোনোকালেই উপনিবেশের শিকার হয় নি। সেদিক থেকে তাঁর উপর্যুক্ত রচনায় এককালের উপনিবেশিতপেরুর সাড়াজাগানো ঔপন্যাসিক ভার্গাস য়োসা’র মূল্যায়নের প্রস্তুতিতে যে পামুকের বিউপনিবেশিত মনোজগতটিরও ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক সেটাও একটা মনে রাখবার দিক। কীভাবে এককালের একটি উপনিবেশিত দেশ আর্জেন্টিনা থেকে উঠে এসে বোর্হেস ‘বিশ্বসাহিত্যের একেবারে কেন্দ্রে’ ‘অবিসংবাদিত’ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ’ন সেটা ভূমিকায় আগেভাগেই বলে রাখেন ওরহান পামুক। য়োসা-পর্যালোচনার সূত্রে পামুক তাঁর সার্ত্র-প্রত্যাখ্যানেরবিষয়টি উপস্থাপন করেন যেখানে সার্ত্র বলেছিলেন, সাহিত্য তৃতীয় বিশ্বের অর্থবিপর্যস্ত দেশগুলোর জন্য বিলাসিতা এবং সাহিত্য হলো ‘ধনী দেশগুলোর ব্যাবসা’। তারপরেও য়োসা’র নিকটে সার্ত্র-পাঠের গুরুত্ব কমে না, কারণ,সার্ত্র তার মনের মধ্যে যে-দ্বান্দ্বিকতা জাগিয়ে দেন সেটির সূত্রেই তাঁর পক্ষে তাঁর নিজের পথ খুঁজে পাওয়াটা সম্ভব হয়েছিল। পামুকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রতিভাবান য়োসা’র পেরুভিয় প্রান্তিকতা কেবল তাঁর নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের বহু লেখকের বাস্তব পরিস্থিতি যাঁরা তাঁদের প্রচ- মেধা-প্রতিভা নিয়ে, সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের (দৈশিকতা ও জাতিত্বের) কেন্দ্র-প্রান্তির দূরত্বকে অতিক্রম করে আসতে পারে না। মারিও ভার্গাস য়োসা’র এসব কথার সূত্রে ১৯৬২ সালে আফ্রো-এশিয় সাহিত্য সম্মেলনে উচ্চারিত ফ্রাঞ্জ ফানোঁ’র সেই বিখ্যাত আহ্বানের কথা মনে পড়ে আমাদের যেখানে তিনি লেখকের মূলগত অবস্থানের পরিচিতিকে প্রাথমিক আবশ্যিকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। পরে সেই ধারাতেই সৃজনশীলতার বিস্ফোরণে সমৃদ্ধি আনেন টনি মরিসন যিনি ১৯৯৬ সালে প্রথম আফ্রিকিয় বংশোদ্ভূত নারী লেখক হিসেবে নোবেল পুরস্কারও অর্জন করেছিলেন।
খালেদ হামিদীর ‘ওরহান পামুকের নির্বাচিত গদ্য’ গ্রন্থটি সম্ভবত বাংলা ভাষায় পামুকের নন-ফিকশন জাতীয় রচনার প্রথম সংকলন। সেদিক থেকে তাঁকে পামুক-গদ্যানুবাদের পথিকৃৃতের মর্যাদা দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে। তাছাড়াপামুকের এমন অসাধারণ গদ্যাবলির অনুপ্রাণিত পাঠক পরবর্তীতে হয়তো তাঁর উপন্যাসগুলির দিকেই হাত বাড়াবেন। ভালো বইয়ের প্রতি দ্বিমত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির আগ্রহের কথাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন।
-

সুকান্ত ভট্টাচার্য: বহুচর্চিত, বহুপঠিত এক অনন্য কবি
-
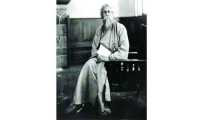
চিত্রাঙ্গদা: দ্বৈত সত্তার শিল্পস্মারক
-
সাময়িকী কবিতা
-

মেঘলা আকাশ বৃষ্টি
-
পোয়েমস দ্যাট কেম টু মি
-
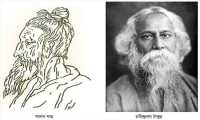
লালন ও রবীন্দ্রনাথ অন্তর্জগতের আলাপন
-

বংশধারা
-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা
-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’
-

ভাঙা ছাদ
-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি
-
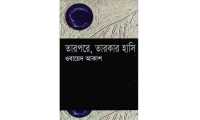
আধুনিক-উত্তর সময়ের নির্মিতি