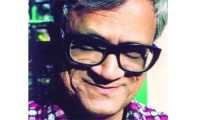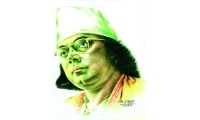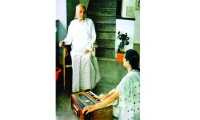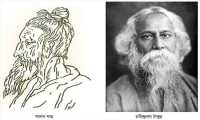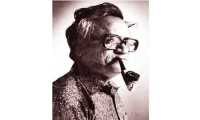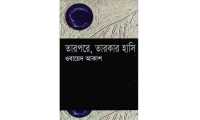৯৭তম জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি
নিজের মতো করেই সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে
আহমদ রফিক
আহমদ রফিক / জন্ম: ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৯
এ মুহূর্তে আমাদের রাজনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রবীণ সাক্ষী ভাষা সংগ্রামী ও লেখক আহমদ রফিক। স্কুল জীবন থেকেই জড়িয়ে আছেন মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অংশ নিয়েছেন তার দেখা সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। লেখালেখিতে সম্পূর্ণ সক্রিয়তার ভেতর দিয়ে পৌঁছেছেন প্রায় শতবর্ষে। তার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতিকে ঘিরে এ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ওবায়েদ আকাশ
ওবায়েদ আকাশ: আপনার বয়স এখন ৯৬ বছর। আবার যদি যৌবন ফিরে পেতেন, তাহলে কি জীবনটাকে নতুন করে সাজাতেন, নতুন কিছু করতেন? কখনো কি মনে হয়, জীবনে অনেক ভুল করেছেন, সেগুলো সংশোধন করতেন?
আহমদ রফিক: হ্যাঁ, অবশ্যই নতুন করে সাজাতাম। নতুন কিছু করতাম। কিন্তু এটা অদ্ভুত একটা ফাসি জিনিস। এটা একটা রহস্য। আমরা তাই মনে করি যে, জীবনে এতগুলো ভুল হলো। যদি আবার নতুন জীবন পাই তাহলে ভুলগুলো সংশোধন করে নতুন করে সাজাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও আর হয় না। মানুষ বারবার একই ভুল করে। জীবনে চলার পথে অনেক ভুলভ্রান্তি হতেই থাকে।
ও. আ.: কখনো কি ভেবেছিলেন, এত বছর বাঁচবেন?
আ. র. : না, কখনো ভাবিনি। আমার পরিবারের কেউ এত বছর আয়ু পায়নি।
ও. আ. : কখনো কি মৃত্যু নিয়ে ভাবেন? সেটা কি আপনাকে আতঙ্কিত করে?
আ. র. : না মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো আতঙ্ক নেই। মৃত্যু যখন আসবে আমি চলে যাবো। এটাকে আমি সহজ করে নিয়েছি। যা অনিবার্য সেটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।
ও. আ. : এত যে লেখালেখি করলেন, এত বইপুস্তক, প্রবন্ধ, সমালোচনা, কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, ভাষা আন্দোলন আরও কত কিছু নিয়ে লিখলেন, এগুলোকে নিজে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
আ. র. : আমার নিজের মূল্যায়ন যদি শুনতে চাও তো বলবো, কিছু ভাল কিছু মন্দ কিছু গড়পড়তা কাজ করেছি। তারচেয়ে বড় কথা আমার সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তো বলবেন সামালোচকরা, নিজের মূল্যায়ন তো আর নিজে করার ব্যাপার না।
ও. আ. : দীর্ঘ জীবন কাটালেন। পিছন ফিরে তাকালে কী মনে হয়?
আ. র. : ফেলে আসা জীবন আমার জন্য মোটেও সুখকর নয়। জীবনে অনেক ভুল করেছি। পরিবারের লোকজন যেমন চেয়েছিল, তেমনভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারিনি। সব পরিবারেই কিছু লোকজন থাকে যারা জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আমার জীবনেও এরকম করেছে কেউ কেউ। আমি যে ঘরসংসার না করে আদর্শবাদী রাজনীতি করেছি, লেখালেখি করেছি, প্রেম করেছি, পিছন ফিরে তাকালে একবার মনে হয় ভুল করেছি, আবার মনে হয় ভুল করিনি।
ও. আ. : আদর্শবাদী রাজনীতি করাটা কি আপনার জীবনে ভুল ছিল?
আ. র. : ভুল ছিল, আবার ভুলও ছিল না। তুমি বলবে, এ আবার কেমনতর কথা। ভুল ছিল না এ জন্য যে, প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তি জীবনে একটা আদর্শ থাকে। সে আদর্শ রাজনীতিও হতে পারে, সমাজ নীতিও হতে পারে, যে কোনো জিনিস হতে পারে। আমার শিক্ষার্থী জীবনটা মোটামুটি ভাল ছিল, আমি বলি মোটামুটি, সবাই বলে খুব ভাল ছিল। সেটা আমি ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারিনি। আমার জীবনটাকে আমি নিজেই নষ্ট করেছি। আবার আমি বলি, আমি তো নষ্ট করিনি। আমার যে নিয়তি। আমার যা করবার আমি তাই করেছি। লেখালেখি করেছি, রাজনীতি করেছি। চেষ্টা করে কিছু করিনি, যা মনে হয়েছে, ভাল মনে হয়েছে সেটা করেছি। পারিবাকি সমস্যা যে আমাকে এভাবে জটিল আবর্তে জড়িয়ে ধরবে সেটা তো আমি ভাবিনি। এটা যদি না হতো তাহলে আমার জীবনটা স্মুথলি নদীর মতো বয়ে যেত।
ও. আ.: আপনি তো জীবনে আপনার ক্যারিয়ারের দিকে তাকাননি। জীবনের অঢেল টাকাপয়সা দান করে দিয়েছেন। এখন কীভাবে চলছেন?
আ. র. : অর্থসম্পদ দান করে দিলে যা হয়, সেভাবে চলছি। নিজের বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছি। এখন ভাড়া বাড়িতে থাকি; আমার বাড়ি ভাড়া মাসিক তেত্রিশ হাজার টাকার উপরে। টাকা পয়সা যা আছে, সিংহভাগ টাকা বাড়ি ভাড়ায় চলে যায়। সম্প্রতি আমি দুটি সম্মাননা পেয়েছি; একটি সমকাল সম্মাননা, পাঁচ লাখ টাকা। আর একটি শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা, পাঁচ লাখ টাকা। এই দুটো দিয়ে এখন চলছি। এতে আমার প্রায় বছর খানেক চলে যাবে।
ও. আ. : আজ পর্যন্ত কোনো সরকার কি আপনাকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করেছে?
আ. র. : কোনো দিন কোনো সরকারের তরফ থেকে আমাকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করা হয়নি।
ও. আ. : যারা শিল্প-সাহিত্য করে, এই প্রজন্ম, আপনাকে ভালবাসে, তাদের সম্পর্কে কী বলবেন।
আ. র. : এই বয়সে, তোমাদের মতো মানুষের ভালবাসা পেয়েছি, এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তবে, কাউকে আমার কিছু বলার নেই। সবাইকে সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে নিজের মতো করে। এবং শুধু বেছে নিলেই হবে না; পথটি আদৌও সঠিক কিনা সেই জ্ঞানটাও অর্জন করতে হবে।
ওবায়েদ আকাশ : এই মুহূর্তে আপনি আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, বর্ষীয়ান। একটি জীবন লেখালেখির সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লিখেছেন। সব লেখকই নিজেকে কবি পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, এমনকি রবীন্দ্রনাথও...
আহমদ রফিক : হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ তো বলতেনই, কবিতা আমার প্রিয় সঙ্গিনী।
ও. আ. : এর বাইরে ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথ, অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস আপনার লেখালেখির বিষয়...
আ. র. : হ্যাঁ, তবে কবিতা এখন লিখছি খুব কম। আমার লেখালেখির কাজগুলো যদি দেখি, তো প্রথমেই ভাষা আন্দোলন, দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ, তারপর রাজনীতি, দেশের রাজনীতি, বিদেশের রাজনীতি, তারপরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখালেখি। এর মধ্যে দেশ বিভাগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমি মনে করি। এবং এটা আমার ছাত্রজীবন থেকে। তখন আমি অসাম্প্রদায়িক বাম রাজনীতি করেছি। সেই বিভাগপূর্ব কালে। সেই থেকে আজ নয় কাল নয় করতে করতে এই তো গত দু’তিন বছর আগে আমি দেশ বিভাগ নিয়ে, দেশ বিভাগের ট্রাজেডি, বহুমাত্রিকতা নিয়ে প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার একটা বই লিখেছি। ট্রাজেডি এই অর্থে, বিদেশিরাও কিন্তু এটাকে বলে ‘সাউথ এশিয়ান ট্রাজেডি’, যেখানে তিন সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ লোক মারা গেল- হিন্দু, মুসলমান, শিখ। এবং তখন কয়েক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হলো। এবং আমি বলব, ধারালো তলোয়ার দিয়ে পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশ ভাগ করা হলো।
ও. আ. : আপনি আসলে কাকে দায়ী করতে চান?
আ. র. : রাজনৈতিক দল, প্রধান রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস এবং লীগ এর জন্য দায়ী ছিল। এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ শাসক। বিশেষ করে শেষ দিকে এসে মাউন্টব্যাটেন সর্বনাশটা করলেন। একটি উদাহরণ দেই : যখন দেশ ভাগ হবে এমন সিদ্ধান্ত হলো, কংগ্রেস একটি নির্বাহী বৈঠক করলো এবং তখন বাম রাজনীতির দুএকজন যেমন রামমনোহর লোহিয়া এবং খান আবদুল গাফফার খান কড়া প্রতিবাদ করলেন। গাফফার খান বললেন, মহাত্মাজী এতদিন আমরা কংগ্রেসের রাজনীতি করলাম আর এখন সেই কংগ্রেস আমাদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে ফেলে দিলো। নেকড়ের মুখে মানে পাকিস্তানের জিন্না সাহেবের মুখে। এবং পরবর্তীকালে ব্যাপারটা তাই হলো। কারণ সীমান্ত প্রদেশে যে অত্যাচারটা হয়েছে, তাতে খান আবদুল গাফফার খান তার বাকি জীবনটা হয় জেলে না হয় নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন। পাকিস্তানে এবং কাবুলে, আফগানিস্তানে। ওরা তো পশতু পাঠান। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস জিন্না সাহেবের পাকিস্তান দাবিটা মেনে নিলো। দায়টা এক্ষেত্রে যদি জিন্না সাহেবের ৬০% ধরি, বাকি ৪০% অবশ্যই কংগ্রেসের। আর পুরো ভূমিকাটা ব্রিটিশ শাসকদের।
ও. আ. : তখন তো আপনার বয়স ১৭/১৮ বছর। এত অল্প বয়সে আপনাকে এমন একটা ঘটনার সাক্ষী হতে হলো।
আ. র. : হ্যাঁ, তখন আমি ছাত্র, এবং তখন থেকেই আমি সাহিত্য, রাজনীতি, বাম-সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছি।
ও. আ. : ‘বাম-সাহিত্য’টাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
আ. র. : ওই সময়েই ভারতীয় স্বাধীনতার বিষয়টা আমার কাছে খুব বড় বিবেচ্য বিষয় ছিল। ঠিক কাজী নজরুল ইসলামের মতো। আমার ঐ সময়ের রাজনীতির মেন্টরের কথা যদি কেউ জানতে চায়, তো আমি বলব, একজন কাজী নজরুল ইসলাম এবং আর একজন সুভাষচন্দ্র বসু।
ও. আ. : রাজনীতির মেন্টর বলছেন নাকি সাহিত্যের?
আ. র. : হ্যাঁ, রাজনীতির মেন্টর। নজরুল তো বিদ্রেহের সঙ্গে, ওই সময়ের বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। লেবার স্বরাজ পার্টি করলেন মোজাফ্ফর আহমদের সঙ্গে। ধূমকেতু, নবযুগ পত্রিকা সম্পাদনা করলেন। উনিই তো প্রথম, ‘ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়’, এই ঘোষণা দিলেন। উনি ঘোষণা করলেন ১৯২২ সালে, কংগ্রেস করল কয়েক বছর পরে।
ও. আ. : এ-কারণে আপনি তার সাহিত্যকে বাম-সাহিত্য বলছেন?
আ. র. : হ্যাঁ, এসব কারণে।
ও. আ. : তখন কি সোভিয়েত সাহিত্য আপনাকে আলোড়িত করেছে?
আ. র. : না না তখনো সোভিয়েত সাহিত্য পড়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু গোর্কির ‘মা’ পড়ে আলোড়িত হয়েছি। বন্ধুদের পড়তে দিয়েছি। ওটাও বাম সাহিত্য। তবে বিপ্লবী রাজনীতি প্রিয় বিষয় ছিল। যেমন তখনকার আমার একটা পুস্তিকার কথা বলি, ‘ভকৎ সিং ও তার সহকর্মীরা’। এটি প্রকাশ করেছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। তাহলে বুঝতে পারো আমার রাজনৈতিক ধারাটা কোনদিকে ছিল। চিন্তা করো আমাদের এখানে এত এত লেখক থাকতে, এত এত ইতিহাসবেত্তা থাকতে যেটাকে বললাম সাউথ এশিয়ান ট্রাজেডি, এটা নিয়ে কেউ কিছু লিখল না। আমি আমার ঐ বইটাতে এ বিষয়টা নিয়ে লিখেছি। অনেক কষ্ট করে অনেক অনেক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমাদের এখানে এ ধারার আর কোনো বই নেই। এইভাবে যে সে সময়ের পশ্চাৎগতির সাহিত্য, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ মার্কা যে পাকিস্তান বন্দনার সাহিত্য, এটা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত একই ধারায় বয়ে গেছে। ১৯৫২ সালে এসে ভাষা আন্দোলন একটা বাঁকফেরা পরিবর্তন ঘটালো, সেটা যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রে। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তনটা অধিকমাত্রায় দেখি তখন কুমিল্লায় একটা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলন হলো। আমি, গাজীউল হকসহ অনেকে মিলে ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম।
ও. আ. : এ বিষয়ে আমরা আর একটু পরে আসছি। আগে জেনে নেই, আপনি আসলে শুরুতে কী ধরনের লেখালেখি দিয়ে শুরু করেছিলেন। প্রবন্ধ, কবিতা, রাজনৈতিক লেখালেখি নাকি অন্য কোনো মাধ্যমে?
আ. র. : সব মিলেই গল্প, কবিতা, সব কিছুই লিখতে শুরু করেছিলাম। আমার ১৯৫৮ সালে যে বইটা বের হলো, সেটা ১৯৫৬ সালে লেখা, বইটির নাম ছিল : ‘শিল্প সংস্কৃতি জীবন’, সেখানে নজরুলের উপর একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ ছিল, বঙ্কিমের উপর একটা প্রবন্ধ ছিল, সেটা অবশ্য সমালোচনামূলকই ছিল বেশি, মীর মশাররফের উপর প্রথম আমার লেখা একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ ছিল।
ও. আ. : আমরা আবার সেই কুমিল্লার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ঘটনায় ফিরে যাই।
আ. র. : তখন আমি, গাজীউল হক ছাড়াও সম্মেলনে গিয়েছিল আমার আরেক বন্ধু আনোয়ারুল হক খান। ও তখন ফজলুল হক হলের জিএস। ঢাকা থেকে মুড়ির টিনের মতো একটা বাসে শিল্পী আব্দুল আলীম, শেখ লুৎফর রহমান, সোহরাব হোসেনসহ আরো অনেকে গিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে হলো ভাষা আন্দোলন, সম্মেলন হলো অগাস্টে। সেখানে নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ইকবালের সেই বিখ্যাত ‘জাগো দুনিয়ার’ গানটি। এরকম আরো পরিবেশনা হলো সেদিন। ফনি বড়–য়া ও রমেশ শীলের ‘যুদ্ধ ও শান্তি’ কবিগান রাতভর আমরা ঈশ্বর পাঠশালার প্রাঙ্গণে বসে শুনলাম। সেই সম্মেলন ছিল জাতীয়তাবাদী বাঙালি চেতনার সম্মেলন। জাতীয়তাবাদী, প্রগতিবাদী, লোকসংস্কৃতি-চেতনার সেই সম্মেলন সম্ভব হলো ভাষা আন্দোলনের কারণে।
ও. আ. : আয়োজক কারা ছিল?
আ. র. : আয়োজক ছিল কুমিল্লারই শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রগতিশীল কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন। ও আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ওই সম্মেলনে তখনই কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ‘নবান্ন’ ও ‘জবানবন্দি’ মঞ্চস্থ হলো। সেই কুমিল্লা সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে, যুক্তফ্রন্ট এত শক্তিশালী ছিল যে, মুসলিম লীগের মতো দল তার কাছে ধরাশায়ী হলো। সেই যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৫৪ সালে কার্জন হলে তিন দিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন হলো। এই সম্মেলনে সুভাষ মুখার্জি, কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু থেকে শুরু করে কলকাতা থেকে ৩০/৪০ জন যোগ দিতে এসেছিলেন। আমার এখনো মনে আছে, লায়লা সামাদ বললেন, ঘোমটা ছেড়ে বেরিয়ে এসো নারী। আজ অহরহ এত নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন হচ্ছে। আমার এখনো মনে আছে, সেই সম্মেলন থেকে মেয়েরা কার্জন হল থেকে আজিমপুর কলোনি পর্যন্ত রাত সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে গেছে। কোনো আক্রমণ হয়নি। ঝামেলা হয়নি। ৫০-এর দশকের এ-জাতীয় পরিবেশ কিন্তু একটা বিরাট ঘটনা ছিল।
ও. আ. : সবাই যেটা আপনাকে জিগ্যেস করে, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে কীভাবে জড়িত হলেন?
আ. র. : আমি স্কুল থেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিলাম। কলেজ জীবনে রাজনীতি করেছি। সেই ১৯৪৮ সালে মুন্সিগঞ্জে ভাষা আন্দোলন করেছি। তখন আমি মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাই। বিশেষভাবে পাঠ নিয়েছি। ওয়েব দম্পতির ‘সোভিয়েত কম্যুনিজম’ বই পড়েছি। ওরা হাসব্যান্ড-ওয়াইফ, দু’জনেই কম্যুনিস্ট। সেই সময়ে কবিতার ওপরে ক্রিস্টোফার কডোয়েলের লেখা ‘ইল্যুশন এ্যান্ড রিয়েলিটি’ পড়েছি। অর্থাৎ সেই সময়ে সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতির জন্য যা যা দরকার সব পড়েছি। তখন আমি লোরকা পড়েছি, নেরুদা পড়েছি। তারপর ১৯৪৯ সালে ঢাকায় এলাম। এরপরে ঢাকায় যতগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে, এগুলোতে অংশ নেয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।
সেই সময়েই সংগঠিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। আমি সংগঠক হিসেবে সরাসরি আন্দোলনে যোগদান করি। আমার কাজ ছিল বিভিন্ন হলে ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, সারা দিন মিছিল-মিটিং করা। আন্দোলনে গুলি চালানোর ঘটনাটা সরাসরি আমার সামনেই ঘটে। বরকত রফিক জব্বার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সে সময়ের ছাত্ররা একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে রাজনীতি শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক পড়াশোনা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে বেশি গুরুত্ব দিত। মওলানা ভাসানী একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বীকার করলেন, যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে ছাত্রদের এবং সাধারণ জনগণের অবদান সবচেয়ে বেশি। তখন আমাদের হোস্টেলের খাবারের খুব সুনাম ছিল। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পরে আমরা আমাদের হোস্টেলে খাওয়ার জন্য তিন প্রধান নেতাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী। তখন খাওয়াদাওয়া শেষে একমাত্র মওলানা ভাসানী এই স্বীকারোক্তি করেছিলেন। যখন কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে, ৯২ক ধারা জারি করে যখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হলো, তখন আমার ফাইনাল পরীক্ষার একমাস বাকি, তারিখটি আমার এখনো মনে আছে, ৩০ মে ১৯৫৪। সেদিন আমরা হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপর বসে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর বক্তৃতা শুনলাম, আমার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল, দেড় বছর আত্মগোপনে কাটিয়ে ফিরে এসে বহু কষ্টে পড়াশোনা শেষ করলাম। পরবর্তী জীবনে আমার আর মেডিকেল লাইনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। ভাল কোনো চাকরিও করতে পারিনি। অথচ মেট্রিকে আমি বিভাগপূর্ব কালে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছিলাম, ইন্টারমিডিয়েটেও আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছিলাম। আমি সর্বাত্মকভাবে বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। তারপরে তো জীবন সংগ্রাম। আমি দেড় বছর বয়সে পিতৃহারা হয়েছি। আমার বড়ভাই সংসার চালাতেন। আমরা চার ভাইয়ের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই একটা চাপ এসে পড়ল। তার পর থেকে ৩/৪ বছর আমার খুব খারাপ সময় গেছে। হেন কাজ নেই যা আমি করিনি। গোয়েন্দা গল্প লেখা, নোটবই লেখা, মিল্লাত পত্রিকায় সাব এডিটরগিরি করা, ছাত্রছাত্রী পড়ানো, এসব বিচিত্র কাজ করেছি। ফার্মাকোলোজি বিষয়টা আমার খুব প্রিয় ছিল। ওটা ড্রাগের ব্যাপার। এলাবার্ট ডেভিডে চাকরি নিলাম। টেকনিক্যাল ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের চিফ হিসেবে। সেখানে ছিলাম সত্তর একাত্তর পর্যন্ত। ওখানে যুক্ত থাকার কারণে বিসিআইসি (বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন)-এ জয়েন করলাম। এর মধ্যে একটি কথা আমি বলি, ১৯৬৪ সালে আমি দুটো কাজের সঙ্গে খুব আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ছাত্র জীবন থেকেই আমার শখ ছিল এসটি সাহিত্য পত্রিকা বের করা। আমার বন্ধু আলীম চৌধুরী ‘যাত্রিক’ নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা চালাতো। আমি ওটার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।
ও. আ. : আপনার সাহিত্য পত্রিকার নাম কি ‘নাগরিক’ ছিল?
আ. র. : হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাগরিক। একেবারে সত্তর সাল পর্যন্ত চালিয়েছি। সেখানে তখনকার এমন কোনো তরুণ লেখক ছিল না, আজকে যারা প্রতিষ্ঠিত লেখক, যে তারা লেখেনি। আমি দুজনের কথা খুব বিশেষভাবে বলি : একজন আবুল হাসান এবং একজন নির্মলেন্দু গুণ, ওদের দুজনের কবিতা আমি ‘নাগরিক’-এ ছেপেছিলাম। ওরা দুজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্প এবং প্রথম কবিতা আমি ছাপি। হাসান আজিজুল হকের প্রথম গল্প আমি প্রথম ছাপি। ওর প্রথম দিককার ৩/৪টা গল্প আমি নাগরিক-এ ছাপি।
এই পত্রিকাটা কেউ কোনোদিন হাইলাইট করেনি। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান এবং শওকত ওসমান। প্রত্যেক সংখ্যায় তারা লিখতেন।
আমি আর একটি কাজ করেছিলাম। তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে বাঙালিদের কোনো স্থান ছিল না। তারা ছিল নিগৃহীত। তাই আমি আর আমার ছয় বন্ধু মিলে ‘ওরিয়ন ল্যাবরেটরিজ’ নামে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি খুলেছিলাম। ‘নাগরিক’ আর ‘ওরিয়ন’ এই দুটো ছিল আমার অন্যতম সৃষ্টি। (সংক্ষেপিত)
-

নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক বলয় অতিক্রমের ক্ষমতা
-

কেরাসিন বাত্তি ও লালচুলা মেয়েটি
-

তাঁর সমকালীনদের চোখে
-

সুকান্ত ভট্টাচার্য: বহুচর্চিত, বহুপঠিত এক অনন্য কবি
-
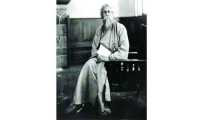
চিত্রাঙ্গদা: দ্বৈত সত্তার শিল্পস্মারক
-

খালেদ হামিদীর দৌত্যে ওরহান পামুক
-
সাময়িকী কবিতা
-

মেঘলা আকাশ বৃষ্টি