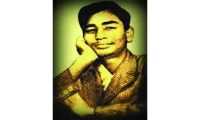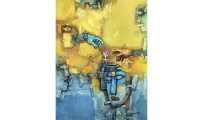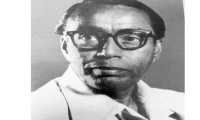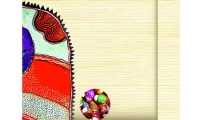সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ
কাঙাল শাহীন
হেলাল হাফিজ / ৭ অক্টোবর ১৯৪৮; মৃত্যু: ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪
হেলাল হাফিজের নাম উচ্চারিত হলেই শ্রোতার মনে এক অদ্ভুত সুর জেগে ওঠে- তা একই সঙ্গে বিরহ বাসনা ও বিদ্রোহের মিশ্র সুর। তিনি এমন এক কবি, যাঁর কাব্যকথা ব্যক্তিগত বেদনা ও সামষ্টিক ইতিহাসকে পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করানোর মাধুর্য দেখায়। মফস্বলে জন্ম নেওয়া এক কিশোর, যিনি শৈশবেই মাতৃহারা; সেই শূন্যতা তাঁর কবিতার প্রথম শ্বাসের সঙ্গে গেঁথে যায়। গ্রামের মাটির গন্ধ, নদীর নীরবতা, মানুষের ক্ষুধা-দারিদ্র্য- এসব অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তরে একটি স্থায়ী জাগরণ রচনা করে, যা পরে তাঁর কাব্যকে প্রতিপন্ন করে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা পেয়েছেন; সেই অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতার ভিতকে ঘন করে, এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, কবিতা কেবল ব্যক্তিগত অনুভব নয়; এটি সামাজিক ঐক্যের ভাষাও হতে পারে। তাঁর ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত অনুভব কাব্যভাষায় মিশে যায়, যেন প্রেম ও রাজনীতি এক কণ্ঠে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।
শৈশবের অভাব, কৈশোরের আকুতি, ছাত্রজীবনের উত্তাল সময়- সব কিছু মিলে তৈরি করে কবির মনের মণিকোঠা। গ্রামের সরলতা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যার চোখে চোখ রেখে কথা বলে, সেই মানুষগুলোর ভাঙা জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি তাঁর কবিতার পটভূমি। তিনি জানতেন কীভাবে ব্যক্তিগত গল্পের ভিতর দিয়ে সমষ্টিগত বেদনা লুকিয়ে রয়েছে; তাই তিনি নিজের প্রেমের স্মৃতি, মাতৃহীনতা ও আর্থিক অনিশ্চয়তার কথা লিখে তা একটি বড় জাতীয় অনুভূতিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। তাঁর কবিতায় প্রেম কখনো কেবল ব্যক্তিগত আবেগ নয়, তা হয়ে ওঠে দেশের প্রতি নিবেদন, বেদনার সঙ্গে এক ধরনের দায়বদ্ধতার ভাষা। ‘হেলেন’ নামের প্রেমিকা যখন তাঁর কবিতায় আসে, তখন তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে জাতির স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেন- প্রেমের ক্ষত যেন জাতির ক্ষতের আক্ষরিক প্রতিফলন হয়ে ওঠে।
সত্তরের দশকের রাজনৈতিক আভাস তাঁকে কবিরূপে গড়ে তোলে। ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ- এই ঘটনাগুলি কেবল ইতিহাস নয়; এগুলো তাঁর লেখার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। “নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়” কবিতার লাইনগুলো কেবল শব্দের খেলা ছিল না; তা ছিল এক সমষ্টিগত আহ্বান। “এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়”- এই ধরনের কণ্ঠস্বর তরুণদের বুক জয় করে নিয়েছিল, এবং কবিতার এই স্লোগানবোধই পরবর্তীকালে তাকে জনমানসে স্থায়ী করে। যুদ্ধের স্মৃতি তাঁর কবিতায় রূপ নেয় মানবিক ক্ষত হিসেবে; ঘরবাড়ি ভাঙার কষ্ট, শিশুদের অনাথত্ব, পরিবারবর্গের নিঃস্বতা- এসব বিষয় তিনি কবিতায় এনে মানুষের অন্তরে ধারণ করেছেন। স্বাধীনতার পর যখন দেখা যায় যে রাজনীতির গলদে দেশ আগের আদর্শের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, তখনও তিনি নীরবে তাঁর কলম চালিয়ে গেছেন- কবিতা হয়ে উঠেছে হতাশা ও পুনর্নির্মাণের আহ্বান।
তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘যে জলে আগুন জ্বলে’ (১৯৮৬) প্রকাশিত হলে বাংলা পাঠক সমাজ যেন নতুন করে আশান্বিত হয়। এখানে কথার সরলতা, অনুভূতির তীব্রতা এবং নাগরিক দায়বোধের এক অনন্য মিশ্রণ পাঠককে বিমোহিত করে। তিনি জটিল অলঙ্কারের বাইরে থাকতেন, কিন্তু সরলতার ভেতর দিয়ে উচ্চারণ করতেন এমন সত্য, যা অনেক সময় জটিল অলঙ্কারে ঢেকে থাকে। তাঁর ভাষা ছিল জনসাধারণের ভাষা- তাই কবিতাগুলো সহজেই মানুষের মনে গেঁথে যায়। সাংবাদিকতা ও সম্পাদকীয় কাজ তাঁকে বাস্তবতার সঙ্গেই রাখতে সাহায্য করেছে; সংবাদপত্রের পাতায় যা ঘটছে, তা তিনি দেখতেন, অনুভব করতেন, এবং পরে কাব্যে পরিণত করতেন- এই প্রক্রিয়ার ফলে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় বাস্তবতার ঘনাটে ছাপ।
বিদেশি কবিদের প্রভাব তাঁর লেখায় স্পষ্ট; তবু তিনি সেই প্রভাবকে কেবল নকল করেননি। তিনি রিলকেতে পাওয়া শৈল্পিক দায়বোধ, নেরুদায় দেখা আশাবাদী বিদ্রোহ এবং টি.এস. এলিয়টের কবিতার অগোচর শক্তিকে স্থানীয় বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে জানতেন। রাইনার মারিয়া রিলকের কথা- “A work of art is good if it has sprung from necessity.” (একটি শিল্পকর্ম তখনই শ্রেষ্ঠ যখন তা অন্তর্গত প্রয়োজন থেকে জন্মায়)- এই ধারণা হেলাল হাফিজের কবিতার সঙ্গে খুব প্রাসঙ্গিক; কারণ তাঁর কবিতা প্রায়শই ভেতরের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত আর সামাজিক জ্বালায় থেকে জন্মায়। পাবলো নেরুদার উক্তি- “You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming” (তুমি যতটা খুশি ফুল কেটে ফেলতে পারো, তবুও বসন্তকে থামানো যাবে না)- এই অমোঘ আশার প্রতিধ্বনিই তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়: কীই বা করা যায় এমন সময়ে যেখানে দমননীতি চরমে পৌঁছায়, কবি তখনও বসন্তকে দাবি করে, নতুন আশা জাগায়। টি.এস. এলিয়টের দিক থেকে ধারণা- “Genuine poetry can communicate before it is understood.” (আসল কবিতা বোঝার আগেই হৃদয়ে কথা বলে)- ওই অর্থেই হেলাল হাফিজের কবিতা প্রথমে সরাসরি হৃদয় স্পর্শ করে, পরে ধীরে ধীরে গভীরতায় প্রবেশ করে পাঠককে চিন্তা করতে বাধ্য করে। এই অপরিহার্য আন্তর্জাতিক প্রভাবগুলো তিনি নিজের মাটিতে গ্রাস করে, তা থেকে স্থানীয় কাব্যভাষা গড়ে তুলেছেন, যা বাংলা পাঠককে অচেনা হলেও প্রাঞ্জলভাবে ছুঁয়েছে।
তাঁর কবিতায় রূপকের ব্যবহার তীক্ষè এবং অনুভূতিপূর্ণ। মাটি, আকাশ, নদী- এসব উপাদান তাঁর কবিতায় ভূতাত্ত্বিক বস্তু হিসেবে থেকে যায় না; এগুলো হয়ে ওঠে মানুষের মনের প্রতীক, স্মৃতি ও আশা-হীনতার প্রতিচ্ছবি। “মাটি ও মানুষ”- এই মিলনে তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অপচনশীল, এবং একেকটি ব্যক্তিগত ক্ষত বহু সময় জাতীয় দুর্দশার দরজাও খুলে দেয়। তাঁর কাব্যচর্চা এমন এক দিক থেকে থাকে, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম সমষ্টিগত চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়। পাঠক প্রথমে হয়তো প্রেমের বা একাকিত্বের কথা পায়, কিন্তু পরের অধ্যায়ে ধরা পড়ে জাতীয় ইতিহাস, সংগ্রামের স্মৃতি ও সামাজিক ব্যর্থতার আভাস।
তাঁর রচনাশৈলীকে সংবেদনশীল ও দৃঢ় বলা যায়। খুব কম সময়েই তিনি অলঙ্কার-ভাণ্ডারে ঢুকে পড়েন; বরং তিনি শব্দের সরলতায় উচ্চারণ করেন সেইসব সত্য, যা অনেক সময় জটিল বিবরণে হারিয়ে যায়। এই সরলতার ভেতরেই আছে এক ধরনের তীক্ষ্ণ তাৎপর্য, যা পাঠককে বারবার ভাবায়। তিনি দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোও কবিতায় মহিমা দিতে জানতেন- এক কাপ চা, একটি ভাঙা জানালা, একটি অনাথ শিশুর চাহনি- এসবকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে মানবিক দায়বোধের সুতায় বেঁধে রাখতেন। রাজনীতি যখন তাঁর ভাষ্যবস্তুর বিষয় হয়, তখনও তিনি মানুষের ক্ষয়কে সামনে রেখেই কথা বলতেন- বিরোধী হবে তা রাজনৈতিক ভাবেই, কিন্তু ভাষা মানবিক থাকবে, যাতে পাঠক শুধু ভাবেই না, অনুভবও করে।
জীবনের সংগ্রাম ও আর্থিক অনিশ্চয়তা তাঁকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে; তবু সেই সব কষ্টই তাঁর কবিতায় গভীরতা আনয়ন করেছে। রোগ, নিঃসঙ্গতা, স্বীকৃতিহীনতা- এসবই কবিকেই এক ধরনের ধৈর্যময় নৈর্ব্যক্তিকতা দিয়েছে, যা তাঁর লেখাকে সময়োত্তীর্ণ করে রেখেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে সত্যিকারের কবিতা ব্যক্তিগত বেদনা থেকে বাড়তি কিছু, তা হলো সমাজ-চেতনার সন্ধান, আর্থ-মানবিক প্রশ্নে বারবার ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা। সমকালীন পাঠক ও পরবর্তী প্রজন্মের কবিরা তাঁর সরলতা ও দায়বোধকে অনুধাবন করেছে এবং তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তরুণ লেখকেরা তাঁর রূপকচিন্তা, তাঁর সামাজিক দৃষ্টি ও ভাষার প্রাঞ্জলতা গ্রহণ করেছে; এতে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।
সমালোচকরা কখনো বলেন, তাঁর সরলতা কখনো কখনো ভাবের গভীরতাকে আড়াল করে; কিন্তু প্রকৃত পাঠক জানেন যে সরলতা অনেক সময় সবচেয়ে কঠিন সত্যকে পৌঁছে দেয়। একটি কবিতার প্রথম ছোঁয়াতে পাঠক যদি মর্মস্পর্শ পায়, তা হলো সেই কবিতার প্রকৃত জাদু- এবং হেলাল হাফিজ তার থেকে চিরকাল সমৃদ্ধ। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি বাস্তবতার কাঁধে দাঁড়িয়ে কবিতাকে বাস্তবে ঢেলে দিয়েছেন; পত্রিকার কলামে যা দেখা যায়, তা কবিতায় নিয়ে এসে তিনি সাধারণ মানুষের ভাষায় অর্থবহ করেছেন। তাঁর অনেক লাইন আন্দোলনের কর্ণফুলির মতো হয়ে উঠেছে- কখনো স্লোগান, কখনো বুকের আর্তনাদ; এবং এই দ্বৈততা তাঁর কবিতাকে অদ্বিতীয় করে তুলেছে।
হেলাল হাফিজের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘কবিতা একাত্তর’ (২০১২) তার লিখিত ইতিহাস ও স্মৃতির গভীরতা নতুনভাবে উপস্থাপন করে। এখানে অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের দংশন এক সঙ্গে উঠে আসে; যুদ্ধ-ভিত্তিক স্মৃতি কেবল ইতিহাসের ফান্ড নয়, তা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অংশ- এমন বার্তাই এখানে প্রচার পায়। এই গ্রন্থের প্রতিটি লাইন যেন একটি প্রচ্ছন্ন ইতিহাসকে সামনে টানে; সেখানে যুদ্ধের ছবি কেবল রণক্ষেত্র নয়, পরিবার, ভালবাসা ও ক্ষতচিহ্নের সাথে জুড়ে যায়। এইভাবে তিনি প্রমাণ করেছেন যে কবিতা কেবল নান্দনিক কিংবা ব্যক্তিগত নয়; এটি ইতিহাস-বচন, মানসিক আর্তনাদ, এবং সমাজ-পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম।
আজও তাঁর কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি আমাদের সময়কেও আগাম চিনেছেন- প্রেম, ন্যায়, স্বাধীনতা, হতাশা- এ সব প্রশ্ন তাঁর পঙক্তিগুলোতে এখনো বারবার জেগে ওঠে। হেলাল হাফিজের কবিতা একটি সময়ের দলিল; প্রতিটি পঙ্ক্তি পাঠককে জাগিয়ে তুল প্রশ্ন করে, ভাবায়, এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে কবিতা যদি অন্তর্নিহিত প্রয়োজন থেকে উঠে আসে, তবে তা জাতির স্মৃতি হয়ে ওঠে এবং মানুষের অন্তরে অনির্বচনীয় চিহ্ন রেখে দেয়।
সমাপ্তির কথা বলার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই- হেলাল হাফিজ কেবল একজন কবি ছিলেন না; তিনি ছিলেন সময়ের আয়নায় দাঁড়ানো এক বীর প্রতিভা, যার কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক হিসেবেই শোনা যায়। জীবনের আঘাত, প্রেমের অমোঘ তৃষ্ণা, জাতিগত সংগ্রামের স্মৃতি- এসব একত্রিত হয়ে তাঁর কবিতাকে করেছে এক অনন্য শক্তির ধারক। সেই শক্তিই আজও তরুণ পাঠককে অনুপ্রাণিত করে, গবেষককে ভাবায়, এবং সমকালীন সমাজকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে। কবিতার ভাষায় তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কীভাবে একজন লেখক নিজের বেদনা ও চেতনার কথা বললে তা অনেক সময় সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করে। তিনি শিখিয়েছেন যে সাহিত্যে সত্যিকারের অর্জন আসে ভেতরের প্রয়োজন থেকে, এবং সেই প্রয়োজনই কবিতাকে করে দেয় অমর ও সময়োত্তীর্ণ। এখানে শুধু একজন কবির জীবনই নয়, বরং একটি জাতির অন্তর্গত মর্মচিন্তাও প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণেই আমরা আজও যখন তাঁর কবিতা খুঁজি, প্রতিটি পংক্তি আমাদের নতুন করে প্রশ্ন করে- কী করে বেদনার ভাষা আশা সৃষ্টি করে। কীভাবে ব্যক্তিগত ক্ষত জাতির স্মৃতিকে জাগায়। উত্তরগুলো সহজ নয়, তবে হেলাল হাফিজের কবিতা সেই প্রত্যুত্তরে ভর করে। তিনি শিখিয়েছেন যে সাহিত্যে সত্যিকারের উপার্জন আসে ভেতরের প্রয়োজন থেকে, এবং সেই প্রয়োজনই কবিতাকে করে দেয় অমর ও সময়োত্তীর্ণ। এখানে শুধু একজন কবির জীবনই নয়, বরং একটি জাতির অন্তর্গত মর্মচিন্তা থাকার প্রমাণিত হয়। সুতরাং তাঁর কবিতা পড়া মানে কেবল পাঠ করা নয়; তা এক অন্তর্গত সংলাপ, একটি অনুশোচনা ও একটি প্রেরণার উৎস। অন্তিমে তিনি মনে করিয়ে দেন, শব্দে লুকিয়ে আছে জীবন ও প্রতিবাদের অনিবার্য শক্তি, আশার অম্লান আলো, চিরন্তন।
-
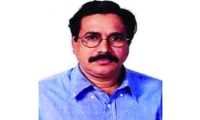
অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক
-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’
-
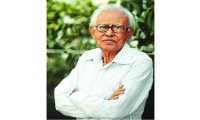
জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক
-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা
-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা
-
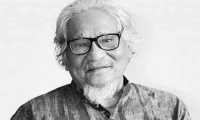
কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর
-
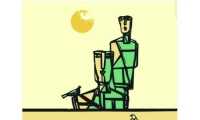
জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’
-
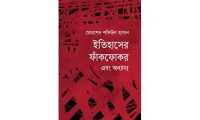
অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে
-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ
-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার
-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন
-

কেন তিনি লালনকন্যা