শামসুর রাহমানের কবিতায় ‘মিথ’
আনোয়ার মল্লিক
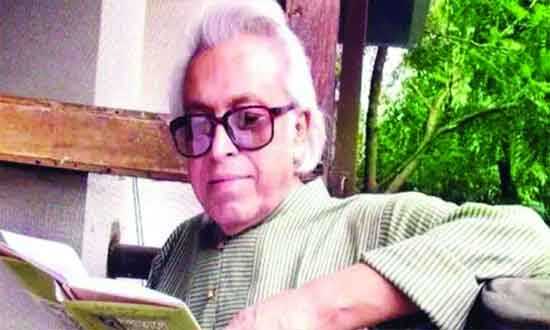
শামসুর রাহমানের কবিতায় ‘মিথ’
আনোয়ার মল্লিক
অর্থগতভাবে মিথ বলতে আমরা বুঝবো গল্প বা কেচ্ছা। আভিধানিক অর্থ পৌরাণিক কাহিনী, অতিকথা, উপকথা কিংবদন্তি ইত্যাদি। আধুনিককালে অবশ্য মিথের অর্থ আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন মিথ বলতে বোঝায় বিভিন্ন অলীক কাহিনী, উদ্ভট কল্পনা, মায়া, কুসংস্কার, বানোয়াট মিথ্যা, আষাঢে গল্প ইত্যাদি। যুগে যুগে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভব বা অভিজ্ঞতাকে মিথের সাহায্যে প্রকাশ করার প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে আমারা লক্ষ্য করি।
বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল মহৎ কবি কবিতায় মিথের ব্যবহার করেছেন। বর্তমান আলোচানায় আমরা শামসুর রাহমানের কবিতায় মিথের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানব সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় মিথের নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। মানব মনের আকাক্সক্ষা এবং প্রত্যাশা পূরণে মিথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মানুষ নিজের কল্পনার রং মিশিয়ে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মিথের আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের অসহায়ত্ব, সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র মানব সভ্যতাকে পথ দেখিয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের এই ধারাকে অনুসরণ করেই শামসুর রাহমান মিথ বা পুরাণের ব্যবহার করেছেন। সমকালীন জীবন এবং ঘটনা প্রবাহকে ব্যাখ্যা করতে এবং জাতির স্বপ্ন ও আকাক্সক্ষাকে এগিয়ে নিতে তিনি মিথের আশ্রয় নিয়েছেন।
শামসুর রাহমানের কাব্য পরিক্রমায় আমরা লক্ষ্য করি, কবিতায় তিনি মূলত গ্রিক তথা ইউরোপীয় মিথের ব্যবহার করেছেন বেশি। ভারতীয় মিথ বা পুরাণও তার অনেক কবিতায় এসেছে। তবে সংখ্যায় তা বেশি নয়। মুসলিম মিথের ব্যবহার তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন অনেকটাই। মুসলিম মিথ ব্যবহারের স্পর্শকাতরতা ও সংবেদনশীলতা হয়তো এর পেছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে।
মিথের প্রতি শামসুর রাহমানের দুর্বলতা ধরা পড়ে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থেই। বিশেষ করে গ্রিক মিথের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে।
রাত্রির পীড়নে উন্মথিত আমি নক্ষত্রের ঝড়ের মত
শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আনি কবিতার অবিশ^াস্য শরীর
সৌন্দর্যের মত রহস্য-ঢাকা নগ্ন আর উন্মীলিত।
আমার সেই নির্মাণে মাননীয় পক্ককেশ প-িত
হন্তদন্ত হয়ে খোঁজেন গ্রিক পুরাণের উল্লেখ।
(কাব্যতত্ত্ব, প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)
কিন্তু কবির এই অনুরাগে একসময় ভাটা পড়ে। মিথ তাঁকে তেমন আকর্ষণ করে না আর। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত “বিধ্বস্ত নীলিমা” কাব্যগ্রন্থের ‘পুরাণ’ নামক কবিতায়: “তোমাদের কারুকাজে শ্রদ্ধা অবিচল, কিন্তু বলোÑ / কী করে পিতার শব কাঁধে বয়ে বেড়াই সর্বদা? / আমাকে জড়ায় সত্য, অর্ধসত্য কিংবা প্রবচন, / তবু জানি কিছুতে মজে না মন বাতিল পুরাণে” (পুরাণ, বিধ্বস্ত নীলিমা)
মিথের প্রতি এই অনীহা তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে আমরা দূর হতে দেখি। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ‘নিরালোকে দিব্যরথ’ কাব্যগ্রন্থে গ্রিক মিথকে ব্যবহার করে প্রকাশ করেন এক কালোত্তীর্ণ কবিতা, টেলেমেকাস। গ্রিক মহাকাব্য ওডিসির শ্রেষ্ঠতম বীর ওডিসিউসের পুত্র টেলেমেকাসের পিতার জন্য বেদনা বিধুর প্রতীক্ষার পটভূমিতে টেলেমেকাস কবিতাটি লেখেন। ষাটের দশকের তৎকালীন শাসকের শোষণ ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ স্বদেশবাসীর স্বপ্ন ও আকাক্সক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে এই কবিতায়। ইথাকার মানুষ যেমন ওডিসিউসের মতোÑ একজন বীরের জন্য প্রতীক্ষারত তেমনি দখলদার পাক বাহিনীর অত্যাচারের নাগপাশ থেকে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা স্বদেশবাসী মুক্তির জন্য একজন বীরের প্রতীক্ষায় বিভোর:
ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দরজা আগলে, পিতা, অধীর তোমারই প্রতীক্ষায়
এখনো কি ঝঞ্ঝাহত জাহাজের মাস্তুল তোমার
বন্দরে যাবে না দেখা? অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ
আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টংকার।
(টেলেমেকাস, নিরালোকে দিব্যরথ)
১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে’ কাব্যগ্রন্থে গ্রিক মিথকে উপজীব্য করে দুটি কবিতা স্থান পেয়েছে। যথা: ‘ট্যান্টালাস’ ও ‘নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি’। ট্যান্টালাস কবিতাটি গ্রিক পুরাণের অভিশপ্ত রাজা ট্যান্টালাসের বেদনাসিক্ত জীবনের করুণ পরিণতি নিয়ে রচিত। ট্যান্টালাসের মতোই অসহায় আজীবন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার আগুনে নির্মজ্জিত মানুষের জীবনের অসহায়ত্ব¡কে তুলে ধরতে কবি গ্রিক পুরাণের চরিত্র ট্যান্টালাসকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।
নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি কবিতায় কবি আফ্রোদিতির যন্ত্রণাকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। ডায়োমিডিসের আঘাতে নিপতিত প্যারিসকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেবী আফ্রোদিতি আহত হয়েছিলেন। আফ্রোদিতির আঘাতের বেদনা কবি নিজের জীবনে অনুভব করেছেন এবং আফ্রোদিতির মতোই কবি ভীষণ অসহায়। কবির ভাষায়Ñ “হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারব না। / আমার মগজে ফণীমনসার বন বেড়ে ওঠে, / দেখি আমি পড়ে আছি যুদ্ধধ্বস্ত পথে কী একাকী; / ভীষণ আহত আমি, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি।” (নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি, বাংলাদেশ স্বপ্নœ দ্যাখে)
‘মাতাল ঋত্বিক’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা ফিনিক্সের গান। গ্রিক মিথের ফিনিক্স পাখি নিজের জ্বালানো আগুনে নিজেই আত্মহুতি দেয় এবং সেই ভস্মরাশি থেকে আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণাদায়ী এবং আত্মত্যাগী চরিত্রের মহত্ত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা বয়ানে ফিনিক্স পাখির প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন শামসুর রাহমানের ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ‘হরিণের হাড়’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা রয়েছে ‘পুরাণের পাখি’ শিরোনামে। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে নিহত ছাত্রনেতা রাজুর আত্মদানকে ফিনিক্স পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে এখানে। যেমন:
ওরা তোমাকে যতই পুড়িয়ে ভস্ম করুক হিংসার আগুনে,
তুমি বার বার আগুন থেকে বেরিয়ে আসবে পুরাণের পাখি।
(পুরাণের পাখি, হরিণের হাড়)
‘ইকারুসেরআকাশ’ (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থে গ্রিক মিথের অসংখ্য চরিত্র নিপুণ দক্ষাতায় চিত্রিত হয়েছে। মিথের বিভিন্ন চরিত্রকে উপজীব্য করে আমরা বেশ কিছু শিল্প সুষমাম-িত কবিতার সন্ধান পাই এই গ্রন্থে। শিল্পী পিতা-ডেডেলাসের পুত্র ইকারুস আত্ম আবিষ্কারের স্বপ্নে তথা তারুণ্যের অস্থিরতায় মোমের পাখা নিয়ে উড়তে উড়তে সূর্যের কাছাকাছি চলে গিয়ে প্রখর সূর্যতাপে পাখা গলে মাটিতে পড়ে নির্মম মৃত্যুবরণ করে। তবু ইকারুসের মহত্ত্ব তার পিতা ডেডেলাস নিজ সত্তায় অনুভব করেছে: “জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্তবলয় / পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ / নিরাপদ নিচে উড়ে উড়ে গন্তব্যে যেতাম তবে কি / পেতাম এই অমরত্ব শিহরন?” (ইকারুসের আকাশ, ইকারুসের আকাশ)
ডেডেলাস কবিতায় শিল্পী ডেডেলাস-এর পুত্র ইকারুসের অকাল মৃত্যুতে পিতা হিসেবে তার হৃদয় অবশই শোকার্ত। তবে সেই শোকার্ত হৃদয় নিয়েই স্বাধীনচেতা পুত্রের সাহসী মনোবাসনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।
তার দিকে, দেখলাম তাকে
পরিণাম বিষয়ে কেমন
উদাসীন, ক্রূর রৌদ্র ঝলসিত সাহসী, স্বাধীন
(ডডেলাস, ইকারুসের আকাশ)
‘ইকারুসের আকাশ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তভুক্ত সার্থক একটি কবিতা ‘ইলেকট্রার গান’। ইলেকট্রার গান কবিতার প্রধান চরিত্র এ্যাগামেমনন। ট্রয় যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এ্যাগামেমনন যুদ্ধ শেষে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলে তার ব্যভিচারী স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা তার প্রেমিক এজিস্থানের সহায়তায় তাকে হত্যা করে। এ্যাগামেমননের কন্যা ইলেকট্রা তার পিতার হন্তারককে হত্যার মধ্য দিয়ে পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এখানে গ্রিক মিথের এ্যাগামেমনন চরিত্র স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিরূপ। বাংলাদেশের পঁচাত্তর পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা কা-কেই যেন তুলে ধরা হয়েছে নি¤œবর্ণিত পংক্তিতে: “নন্দিত সেই নায়ক অমোঘ নিয়তির টানে / গরীয়ান এক প্রাসাদের মতো বিপুল গেলেন ধসে। / বিদেশি মাটিতে ঝরেনি রক্ত, নিজ বাসভূমে / নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাকে সহসা হেনেছে ওরা।” (ইলেকট্রার গান, ইকারুসের আকাশ)
হোমারের স্বপ্নময় হাত (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় মহাকবি হোমারের নামে প্রচলিত পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে কবি শামসুর রাহমান নিজ অস্তিত্বের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। মহাকবি হোমারের মতো তিনিও অমর কাব্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর মনের সেই আকুতির প্রকাশ ঘটেছে এভাবেÑ
যদি এখন আমি খাতার শাদা পাতা স্পর্শ করি, তাহলে সেখানে
বইবে অলকানন্দা, গড়ে উঠবে আর্ডেনের বন,
লতাগুল্মে ঝলসে উঠবে হোমারের স্বপ্নময় হাত।
(হোমারের স্বপ্নময় হাত, হোমারের স্বপ্নময় হাত)
অ্যাকিলিস ছিলেন হোমারের ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত ইলিয়াড মহাকাব্যের একজন বিখ্যাত বীর। গোড়ালি ছাড়া তার সমগ্র শরীর ছিল অপরাজেয়। কিন্তু ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাসে গোড়ালিতেই বিষাক্ত তীর বিঁধে তার মৃত্যুঘটে। কবি শামসুর রাহমান তাঁর চুয়ান্ন বছর বয়সে শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ থাকলেও তার ভয় হয় পায়ের গোড়ালি যেমন এ্যাকিলিসের ছিল একমাত্র দুর্বল জায়গা, তেমনি তাঁর শরীরেরও কোনো দুর্বল অংশ হয়তো তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ হতে পারে। এ্যাকিলিসের নির্মম ভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে কবি নিজের অস্তিত্বের আশঙ্কার কথা এখানে বলতে চেয়েছেন: “যকৃৎ তুখোড় আজো, যা কিছু পাঠাই নিত্য জঠরে / হজম / হয় সবই রীতিমত; যম / অসৌজন্যমূলক ভ্রুকুটি হেনে ঈশ^রের স্তব্ধতার মতো / প্রাচীনতা নিয়ে হাসে, করে পায়চারি ইতস্তত; / ঈগল দৃষ্টিতে খোঁজে খালি / আমার ধ্বস্ত এ অস্তিত্বের এ্যাকিলিসের গোড়ালি,” (এ্যাকিলিসের গোড়ালি, ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই)
অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থে গ্রিক অন্ধ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা টাইরেসিয়াসকে নিয়ে একটি কবিতা আছে, টাইরেসিয়াসের মতো। সোফোক্লিসের ট্র্যাজিক নাটক ইডিপাস রেক্স এর একটি চরিত্র টাইরেসিয়াস, যিনি জন্মান্ধ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বাংলাদেশের গণঅধিকার আদায়ের মিছিলে যোগদানকে তার ভবিতব্য হিসেবে চিহ্নিত করতে টাইরেসিয়াস চরিত্রকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থান করেছেন। হিন্দু পুরাণের চাঁদ সদাগরকে শামসুর রাহমান বর্তমান প্রেক্ষাপটে অসাধারণভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন।
‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’ (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের ‘চাঁদ সদাগর’ কবিতায় দেখা যায় মানবিক বোধে ভাস্বর এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা এক অনমনীয় নতুন চাঁদ সদাগরকে। প্রথাগত ভাষ্যের বদলে এ কবিতায় পৌরাণিক কাহিনীর সমান্তরালে সমসাময়িক বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভিন্ন এক চিত্র ফুটে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের প্রবল পুত্রশোক, বিগত যৌবনের স্মৃতি কাতরতা এবং অনমনীয় আপোসহীন ব্যক্তিত্ব তাকে চিরকালীন এক নায়কের আসনে বসিয়েছে: “যতদিন হিন্তাল কাঠের / লাঠি আছে হাতে, আছে / ধমনীতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে / আমার মহূর্তগুলি ঈষৎ স্পন্দিত হবে, চোখে / নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল, / কবর না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন, / যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ, / ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায় / ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার / গাঙ্গুড়ের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।” (চাঁদ সদাগর, উদ্ভট উঠের পিঠে চলেছে স্বদেশ)
দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের স্যামসন কবিতায় হিব্রু মিথের চরিত্র স্যামসনকে শামসুর রাহমান বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। স্যামসন ছিলেন একজন কিংবদন্তি ইজরায়েলি যোদ্ধা, যিনি অতি প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী একজন বীর। তাকে বন্দী করে তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়, চুল কেটে নেওয়া হয়। তারপরও মাতৃভূমিকে রক্ষার্থে তার দৃঢ সংকল্প অন্ধকারে আলোর পথ দেখায়। যখন জনগণের উপর শাসকের অত্যাচার, নির্যাতন প্রবল হয়, তখন স্যামসনের মতো এক-একজন অকুতোভয় বীরের আগমন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। স্যামসনের চরিত্রের অনমনীয়তা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধে ফুঁসে ওঠার অনন্য উচ্চারণ শোনা যায় নিচের পংক্তিতে:
আমার দুরন্ত কেশরাশি পুনরায় যাবে বেড়ে
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয় তেড়েÑ
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের সব স্তম্ভ
ফেলব উপড়ে, দেখো কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করবো লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।
(স্যামসন, দুঃসময়ের মুখোমুখি)
শামসুর রাহমান আধুনিক বাংলা কবিতায় নিজের জন্য চিরকালীন এক অবস্থান তৈরি করেছেন। কবিতায় তিনি আত্মস্থ করেছেন নিজস্ব এক স্বরভঙ্গি। অজ¯্র প্রচলিত মৌখিক শব্দকে তিনি স্বার্থকভাবে কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এসব কবিতা তাকে স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যা সহজেই অন্যের কবিতা থেকে আলাদা করা যায়। আধুনিক মনন, প্রগতিশীল জীবন বীক্ষা, প্রতিবাদমুখর নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। চারপাশের ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে যখন তিনি বিচলিত, সময়ের বৈরিতায় পরিবেশ যখন বাকরুদ্ধ, তখন মিথের আড়ালে কবি তাঁর বক্তব্য পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মিথ আশ্রয়ী কবিতাগুলোতে শামসুর রাহমানের নিজস্বতা সফলভাবে ধরা দিয়েছে। এবং এই কবিতাগুলো শৈল্পিক মানেও অনেকাংশে সার্থক হয়েছে।
‘সাময়িকী’ : আরও খবর
» কমলা দাশের প্রেমের কবিতা
» সাময়িকী কবিতা
» হননের আগে
» মায়াকন্যা
» লোরকার দেশে
» প্রেম ও নারীর বিষণ্ণ কুহক
» অস্তিত্ববাদী দীর্ঘশ্বাসের অন্তর্গত ছায়ালোক
» বুভুক্ষা শিল্পী ও একথালা ভাত
» লোরকার দেশে
» কয়েকটি নির্ঘণ্ট
» নূরুল হকের অপ্রকাশিত কবিতা
» বিষাদমাখা সুন্দরের ডাকহরকরা
» শিশিরস্নাত পদাবলি
» শিল্পের স্বাধীনতা মানেই মানুষের স্বাধীনতা
» লোরকার দেশে
» বনানীর ঢালু রাস্তা বেয়ে
» দিলারা হাফিজ-এর কবিতা
» বাংলা কবিতার উদ্ভাসিত স্বর
» শরীরী অশরীরী
» বিষণ্ণতার কবি আবুল হাসান
সম্প্রতি

আন্তর্জাতিক: পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তুমুল সংঘর্ষ

অপরাধ ও দুর্নীতি: ব্যাগভর্তি জাল টাকা, হাসপাতালে বিল দেয়ার সময় আটক তিন

সারাদেশ: সীমিত আকারে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি

