সত্যেন সেনের উপন্যাস: মিথ ও ইতিহাসলগ্ন মানুষ
রুমা আক্তার
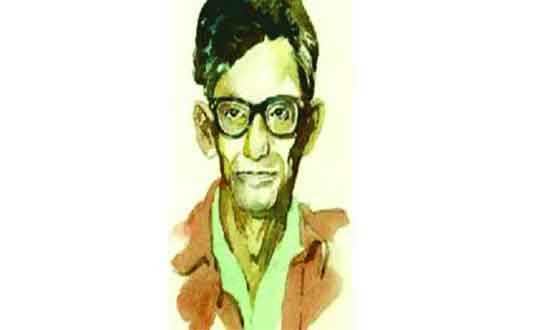
সত্যেন সেনের উপন্যাস: মিথ ও ইতিহাসলগ্ন মানুষ
রুমা আক্তার
বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) ইতিহাসবোধ, জীবন-সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা তাঁকে বাংলা উপন্যাসধারায় প্রাতিস্বিক করেছে। মার্কসীয় জীবনদৃষ্টি ও আবহমান ইতিহাসের সাথে মিথের যূথবদ্ধতা তাঁর সাহিত্যকর্মকে করেছে নানামাত্রিক ও মৌলিক। তিনি ইতিহাস কিংবা মিথকে বিভিন্ন জাতির লিপিবদ্ধ ঘটনাবলির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মানুষের যাপিত জীবন তথা লোকজজীবন, লোকজ বিশ^াস, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি মিথ ও পুরাণের বিচিত্র ধারায় সঞ্চারিত করেছেন। তবে তিনি বিষয় ভাবনায় মিথ ও ইতিহাসের আড়ালে অস্তিত্বকামী মানুষের জীবন সংগ্রামের গতিপ্রবাহকে চিত্রিত করেছেন।
আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় চল্লিশের দশক গুরুত্বপূর্ণ। সত্যেন সেন চল্লিশের দশকের কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক। সেসময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ- আবুল ফজল, জগদীশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শওকত ওসমান, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, সত্যেন সেন প্রমুখ। তবে সত্যেন সেন যুগচেতনা ও যুগযন্ত্রণাকে ধারণ করে হয়েছেন স্বতন্ত্র ও মৌলিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৯), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭), পদাতিক (১৯৬৮), পাপের সন্তান (১৯৬৯), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৯৬৯), কুমারজীব (১৯৬৯), পুরুষমেধ (১৯৬৯), অভিযাত্রী (১৯৬৯), আলবেরুনী (১৯৬৯), মা (১৯৬৯), অপরাজেয় (১৯৭০), জীবনী মনোরমা মাসীমা (১৯৭০), সীমান্তসূর্য আবদুল গাফফার খান (১৯৭৬)। বিভাগোত্তর উপন্যাসে রোম্যান্স ও রোম্যান্টিকতামুখী ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস তাঁর অনুধ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে।
সত্যেন সেনের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীনাথ ভাদুড়ী, শওকত ওসমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবুজাফর শামসুদ্দীন- এঁরা সবাই ইতিহাসকে ধারণ করে উপন্যাস লিখেছেন। তবে এঁদের মধ্যে সত্যেন সেন ইতিহাসনিষ্ঠ উপন্যাসের ভিতরে মিথকে গুরুত্ববহ করে তুলেছেন। তাই তিনি স্বতন্ত্র। ‘অভিশপ্ত নগরী’ উপন্যাসটি বাইবেলের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসটি মিথ-ঐতিহ্যের নবনিমার্ণ নয়, একই সাথে একটি সভ্যতার সংকটময় সময়ের প্রতিবিম্ব। যেরেমিয়া নবী, সে যিরুশালেম থেকে যিহোবার আদেশে তাঁর মত প্রচার করছেন। যেরিমার বিশ্বাস তিনি নিজে কিছু বলেন না, পবিত্র যিহোবা তাঁর মুখ থেকে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করছেন। তিনি অবলোকন করছেন যিরুশালেমের রাজা, সামন্ত প্রভুগণ, লোকপ্রধান, মন্দিরের পুরোহিতগণ সমাজের উপর যে অত্যাচার করছেন, ধর্মের নামে পবিত্র যিহোবার আদেশ লঙ্ঘন করছেন। তাতে কারো মুক্তি নেই, যিহোবা তাদের ধ্বংস করে দেবেন, পাপীদের শাস্তি প্রদান করবেন। “শোন যিরুশালেমবাসী পাপের সন্তানগণ। তোমাদের প্রাচীর ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। স্বয়ং যিহোবা (সৃষ্টিকর্তা) হাত ধরে নিয়ে আসবেন।” (অভিশপ্ত নগরী, সত্যেন সেন)। এ উপন্যসটি কেবল জেরুজালেম নগরীর ধ্বংস বা উহুদি জাতির পতনের কাহিনিমাত্র নয়, এটি সমাজ পরিবর্তনের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনারও রূপান্তর। তিনি ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েও জীবনের জয়গান করেছেন শদরা ও মিকার শ^াশত প্রেমের শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে। ঔপন্যাসিক মিকা চরিত্রটির মাধ্যমে ইতিহাস ও মিথের সমান্তরালে মিকার অস্তিত্ব ও শেকড়ের অনুসন্ধানকে কিংবা সংকটকে বিমূর্ত থেকে মূর্ত করে তোলেন। কারণ ব্যক্তির বেড়ে ওঠা যেখানেই হোক না কেনো, ব্যক্তি তার প্রিয় জন্মভূমি ও শেকড়কে কখনো ভুলতে পারে না। “তুমি ক্যালদীয় নও, তুমি য়িহুদিও নও, তুমি আমার মিকা, তুমি শদরার মিকা, এটাই কি তোমার যথেষ্ট পরিচয় নয়।” (অভিশপ্ত নগরী, সত্যেন সেন)। ‘পাপের সন্তান’ অভিশপ্ত নগরীর দ্বিতীয় খ-। অভিশপ্ত নগরীতে জেরুজালেম নগরী পতনের কথা বর্ণিত। দুটি উপন্যাসের ঘটনা-কালের ব্যবধান কিংবা কাহিনির বিস্তার প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর উপরে। “পাপের সন্তান আমার অভিশপ্ত নগরী উপন্যাসের দ্বিতীয় খ- বলা চলে। এই দুটো উপন্যাসের ঘটনাকালের ব্যবধান অর্ধশতাব্দীর কিছু ওপর। অভিশপ্ত নগরীর শেষাংশে যিরুশালেম নগরীর পতনের কথা বর্ণিত হয়েছে।... য়িহুদি জাতির ইতিহাসে এ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।” (সত্যেন সেন, পাপের সন্তান, ভূমিকাংশ)। পরজাতি স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ইহুদি সন্তানদের পাপের সন্তান আখ্যা দিয়ে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শদরা ও মিকা। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে তার নীলনদের তীরে এসে নতুন জীবন ও পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। যা নবজীবন ও নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত। উপন্যাসটির শুরুতে সংশয়পূর্ণ প্রশ্ন পাঠকের মননে কৌতূহলের জন্ম দেয়।
উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মিকা কবার নদীর তীরে গড়ে ওঠা বাবিল নগরীর নারগেল সারেজের নামে এক ব্যক্তির আশ্রয়ে পালিত হয়। মিকা নিজেকে মনে-প্রাণে ইহুদি মনে করে, কিন্তু নারকেল সারজেরের কাছে আশ্রিত বলে তাকে ক্যালদীয়দের মতো আচরণ ও পোশাক পরতে হয়। মিকা তার নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে পারে না। মিকার অস্তি¡ত্ব সংকট যেন সকল কিছু ছাপিয়ে যায়। “যাহুদা তোমার জন্মভূমি নয়, তুমি তাকে চোখেও দেখনি কোন দিন, তবু তার কথা বলতে বলতে তোমার চোখ অমন ছলছল করে ওঠে কেন, কেন তোমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে, আমাকে বলতে পারো মিকা? (পাপের সন্তান, সত্যেন সেন)। ‘বিদ্রোহী কৈবর্ত’ কৈবর্ত জাতি বরেন্দ্রভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি। সামন্ত রাজা দিব্যের নেতৃত্বে শুরু হওয়া সমকালীন পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০-১০৭৫) পাল সা¤্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি বিপ্লব এবং বিদ্রোহের মাধ্যমে সামন্ত রাজা দিব্যক বরেন্দ্রভূমিকে পাল রাজার অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করে নিজের সার্বভৌম রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়েছেন এবং এ লড়াই একটি জাতির অস্তিত্বের লড়াই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, “কৈবর্তরা ছিল বরেন্দ্রের শক্তিশালী জাতি, দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা দিব্যেকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল।” কৈবর্ত জাতি দুভাগে বিভক্ত। একটি জাতির নাম হ্যালিক অপরটির নাম জ্যালিক। দিব্যক আকান ও ভীম হ্যালিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। কৈবর্তরা মূলত জেলে জাতি। যারা মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তাই তাঁদের ধর্মে প্রাণি হত্যা নিষিদ্ধ এবং তারা অহিংসবাদে বিশ^াস করেন। সেজন্য পাল রাজারা কৈবর্তদের কঠোর হাতে দমন করেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁরা প্রাণি হত্যা পাপ মনে করলেও যুদ্ধের সময় মানুষ হত্যাকে পাপ মনে করেন না। তাই কৈবর্তরা আত্মরক্ষা করার জন্য এ বিদ্রোহ করে। ঔপন্যাসিক এখানে মিথ ও ইতিহাসের সমান্তরালে অস্তিত্বগামী মানুষের জীবন সংগ্রামকে চিত্রিত করেছেন এবং এ উপন্যাসে দিব্যক ও আকান চরিত্রটি কৃষ্ণ ও অর্জুনের চরিত্রে কল্পনা করা যায়। কৃষ্ণ ও অর্জুনের যৌথ পরিকল্পনা, শক্তি ও সাহসে যেমন কৌরবরা পরাজিত হয়েছে তেমনি দিব্যক ও আকানের পরিকল্পনার কাছে দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ বাংলা আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এ বিদ্রোহ যেমন সাময়িকভাবে পালদের তাদের সিংহাসনচ্যুত করে তেমনি চিরস্থায়ীভাবে তাদের শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। ঐতিহাসিক রায়োসুকে ফুরুই মতামতটি উল্লেখযোগ্য- “কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল বাংলার আদি মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি সমসাময়িকভাবে পালদের তাদের পৈতৃক অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে এবং অধস্তন শাসকদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ চিরস্থায়ীভাবে দুর্বল করে দেয়।” তিনি এ উপন্যাসে মিথ ও ইতিহাসের অন্তরালে স্থান-কাল নির্বিশেষে মুক্তিকামী ও সংগ্রামী মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরেছেন। একই সাথে তাদের নব জীবনের অভীপ্সা তাদের অস্তিত্ববাদী করে তোলে। এভাবে তাঁর উপন্যাসের পরতে পরতে সংগ্রামশীল মানুষের ইতিহাসকে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় চিত্রিত করেছেন।
সত্যেন সেন ইতিহাস ও মিথকে ব্যক্তির জীবনলগ্ন করে তোলেন। যাপিত জীবনের নানাবিধ অভিক্ষেপ তাঁর শিল্প মানসকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো বহুরৈখিক এবং সামগ্রিক স্বর। যেখানে মিকা একক স্বর নয়, সে অস্তিত্বসংকাটীর্ণ জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। একই সাথে শদরা ও মিকার প্রেম সংগ্রাম ও সংরাগের প্রতীক। তেমনি দিব্যক চরিত্রটি শুধু কৈবর্ত জাতির নয়, সে সমগ্র অত্যাচারিত ও শোষিত জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে। বিষয়-বৈভবের নানামাত্রিকতা এবং শিল্পের চিরন্তন আবেদন কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনকে স্বতন্ত্র করেছে।
শিল্পবোধ ও নান্দনিক চর্চা শিল্পীকে আত্মমগ্ন করে বিমোহিত করে কখনো শব্দের মায়াজালে কখনো বা ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও মিথের চিরন্তন পথে। সত্যেন সেন শিল্পের এ অনন্ত পথ হেঁটে বাংলা উপন্যাস ধারায় নিজেকে করেছেন বহুমাত্রিক ও মৌলিক।
‘সাময়িকী’ : আরও খবর
» কমলা দাশের প্রেমের কবিতা
» সাময়িকী কবিতা
» হননের আগে
» মায়াকন্যা
» লোরকার দেশে
» প্রেম ও নারীর বিষণ্ণ কুহক
» অস্তিত্ববাদী দীর্ঘশ্বাসের অন্তর্গত ছায়ালোক
» বুভুক্ষা শিল্পী ও একথালা ভাত
» লোরকার দেশে
» কয়েকটি নির্ঘণ্ট
» নূরুল হকের অপ্রকাশিত কবিতা
» বিষাদমাখা সুন্দরের ডাকহরকরা
» শিশিরস্নাত পদাবলি
» শিল্পের স্বাধীনতা মানেই মানুষের স্বাধীনতা
» লোরকার দেশে
» বনানীর ঢালু রাস্তা বেয়ে
» দিলারা হাফিজ-এর কবিতা
» বাংলা কবিতার উদ্ভাসিত স্বর
» শরীরী অশরীরী
» বিষণ্ণতার কবি আবুল হাসান
সম্প্রতি

আন্তর্জাতিক: পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তুমুল সংঘর্ষ

অপরাধ ও দুর্নীতি: ব্যাগভর্তি জাল টাকা, হাসপাতালে বিল দেয়ার সময় আটক তিন

সারাদেশ: সীমিত আকারে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি

