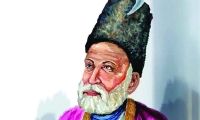????? ?????????????? ?????
অস্তিত্ববাদী দীর্ঘশ্বাসের অন্তর্গত ছায়ালোক
মাহফুজ আল-হোসেন
বাংলা কবিতা যখন ঔপনিবেশিক আধুনিকতার রৈখিক বয়ান থেকে বেরিয়ে এসে অস্তিত্বের গভীরতর রক্ত¯্রােত, মানসিক ছায়া ও সামাজিক-বৈকল্যের উপগাথা নির্মাণ করতে শুরু করল, তখন সেই উত্তরণকে সবচেয়ে শুদ্ধ ও প্রগাঢ় ভাষায় সম্ভব করলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কবিতা বাংলা ভাষাকে এমন এক অভ্যন্তরীণ আলো-অন্ধকারের মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে যেখানে শব্দের স্পন্দন, দেহের আতঙ্ক, নিয়তির আহ্বান- সবকিছু মিলেমিশে তৈরি করে মহাপৃথিবীর অভ্যন্তরে এক অন্তঃসলিলা নদীর মতো উচ্ছ্বাসমান তরল বিস্ময়। শক্তির কবিতা শুধু কল্পনার কুসুমকলি নয়, বরং এটি এক মরমী দ্রষ্টা-সত্তার ক্রমাগত প্রকাশ। তাঁর কবিত্বে রয়েছে আত্ম-অন্বেষার গভীরতর যন্ত্রণাময় অন্বয়, পৃথিবীর নৈঃশব্দ্যে লীন মানব-হাহাকার, আবার রয়েছে প্রেমের অস্ফুট শিশির, প্রকৃতির ভেতরে নিয়ত ক্রীড়োন্মত্ত আশ্চর্য রঙ্গরস। তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দ যেন অস্তিত্বের গোপন রক্তচিহ্ন, প্রতিটি বাক্য একেকটি শ্বাস- যা জীবনকে নির্মাণ করে নবনূতন রূপে। তিনি জীবনানন্দের মতো প্রকৃতির অতিপারলৌকিক আলো বুঝতেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি অনেক বেশি জনমানসিক, নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত, কখনো মাতৃবৎ, কখনো অসহনীয়। তাঁর শব্দের ছন্দে রয়েছে প্রতিদিনের দুঃখের ভাঙন, রাতের বুকে লাল আতঙ্ক, আবার মাঝে মাঝে অঘোরের টান। নিজেই লিখেছিলেন- “আমি কুয়াশার মতো এসে ঢাকি তোমাদের দুঃখ”- এ যেন তাঁর কাব্যসত্তার চিরস্থায়ী অভিপ্রায়।শক্তির কবিতা তাঁর প্রথম প্রকাশেই দেখিয়ে দেয়- তিনি শব্দকে শুধু অর্থের জন্য ব্যবহার করেন না, বরং শব্দের স্পর্শে তৈরি করেন এক নতুন বাস্তবতা। তাঁর প্রথম দিককার কবিতাগুলো- ধূলিপদ, ছায়া ঘন হয়ে আসে আর সেইসাথে মানবিক বিচ্ছিন্নতা, প্রেমের ক্ষয়, সময়ের বিরহ ও জীবনযুদ্ধের ঝাপসা ভঙ্গি প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। পরবর্তী কাব্যপ্রয়াসে এই ভঙ্গি আরও গভীর হয়ে ওঠে। তাঁর “অন্তরঙ্গ” কবিতার একান্ত আকুতি : “আমাকে রাতের সঙ্গে নিয়ে চলো / আমি রাতকে খুব ভালোবাসি।” এই স্বীকারোক্তিতে যে অন্ধকারের মোহ তাতে কোনো ভয়-সংশয়ের লেশমাত্র নেই, বরং রয়েছে যন্ত্রণাকে নিজের করে নেওয়ার মমতা। ‘রাত’ শক্তির কবিতায় যেমন রক্তের মতোই প্রয়োজনীয়, তেমনই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে ভাঙা স্বপ্ন, মৃত সহচর, কিংবা ধ্বংসের ছাই। তাই তাঁর কাব্যস্বরে শুধুমাত্র শরীরী প্রেমের মোহন বাঁশি নয় বরং সেইসাথে অনুরণিত হয় প্রকৃতিমুগ্ধ-তন্ময়তা, আত্মোন্মোচনের ব্যাকুলতা, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ববোধের শুদ্ধস্বর।
তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য’ (১৯৬১) শত সনেটের সুসঙ্কলন, যেখানে একটি কবিতায় কান পেতে রাখা অপেক্ষমানতায় প্রেমের আকুতি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে: “নীলিমা ঔদাস্যে মনে পড়ে নাকো গোষ্ঠের সংকেত / দেবতা, সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে”। তাঁর কবিতায় ব্যক্ত প্রেম বড় বেশি শরীরী নয়, বরং এক ধ্রুপদী নীরবতা। কবি প্রেম-অপ্রেমের খেলায় গভীরতা খোঁজেন প্রেমাসক্ত পরস্পরের হৃদয়ের অতল গভীরে: “তোমাকে বলেছিলাম/প্রেমের কোনো শেষ নেই-/শেষ যদি থাকতেই হয়/তবে থাকে আমাদের ভেতরের গভীরে।” আবার নস্টালজিক ‘খেলনা’ বাল্য প্রেমের অনুষঙ্গে নৈঃশব্দ্য এমনই যে কখনো পাবেনা জেনেও একবার পেয়েই তাই চাওয়াটা থেকে যায় আজীবন নিষ্ক্রিয় প্রয়াসে : ‘পাবো না কখনো তারে আর, /একবার পেয়েছিনু শুধু চাই নিষ্ক্রিয় প্রয়াসে/ চাই পেতে তারে এমনি খেলায়/ গভীর অছন্দে এই প্রেম সব, স্পন্দন পরম, সব; / বাল্য, মনে হয় তুমি/ কেড়ে নিলে খেলনা মরে যাবো।’
শক্তির কবিতায় প্রকৃতি এক অনিবার্য চরিত্র। জীবনানন্দের চিত্ররূপময় প্রকৃতি যেখানে নিসর্গের রহস্যে দীপ্ত, শক্তির প্রকৃতি সেখানে খ-িত, অস্থির, বিপন্ন। তাঁর বিখ্যাত পঙ্ক্তি: “আকাশটা আজ খুব নিচু হয়ে এসেছে/ মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।” এখানে আকাশ আর ওপারের জগত নয়; এটি মনস্তাত্ত্বিক চাদর, যা কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর প্রকৃতিতে মেঘ মানসিক ভার, নদী সময়ের অনিবার্য গতি, বৃক্ষ মানুষের অসহায় দাঁড়িয়ে থাকা। শক্তির প্রকৃতি মানুষকেন্দ্রিক; তিনি প্রকৃতির মধ্যে মানুষ খুঁজে পান, আর মানুষের মধ্যে খুঁজে পান প্রকৃতির অস্থির ছায়া। যে শক্তি “চলে যাই” কবিতায় লিখেছেন: “চলে যাই চলে যাই বলে/ চলে যায় সব মানুষ।” সেই তিনিই আবার “তোমার জন্য” কবিতায় বলেন: “তোমার জন্যই বেঁচে থাকা/ আমার এই একমাত্র কাজ।” এই দুই অবস্থান পরস্পরবিরোধী নয়; বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ দুই বিন্দু। শক্তির কবিতায় মৃত্যু আছে, তথাপি মৃত্যু-আকুলতা নেই। আছে জীবনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে দেখার বাসনা, আছে চলে যাওয়ার বেদনা, কিন্তু কোথাও অন্তিম কোনো ইচ্ছা নেই। সেকারণে তাঁর কবিতা মৃত্যুকে বুঝতে চায় না; বরং মৃত্যুর আগে জীবনের শেষ আলোটুকু দেখতে চায়।
শক্তির ভাষা বাংলা কবিতার মধ্যে এক আলাদা বিস্ময়। বিশেষ করে কবিতায় শব্দ ব্যবহারের কুশলতার কারণে তার সাধারণ কবিতাও হয়ে উঠতো অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে কবিবন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: “শক্তি যেভাবে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করে, সেরকমভাবে আর কেউ পারে না। একেবারে ম্যাজিকের মতো ওর শব্দ ব্যবহার।” শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় তাঁর শব্দচয়ন যেমন মাটির কাছাকাছি, তেমনি দার্শনিক গভীরতায় পরিব্যাপ্ত। কোনো বিশাল মেটাফর নয়; ছোট, দৈনন্দিন, সাধারণ শব্দ শক্তির হাতে রূপ নেয় গভীর বোধের। যেমন: “ঘাসফড়িংয়ের ডানার শব্দে/ একটি শহর ভেঙে যেতে পারে।” এ পঙ্ক্তির মধ্যে যে আতঙ্ক, যে ঝড়, তা কোনো বিশাল শব্দে সম্ভব হতো না। শক্তি জানতেন- কবিতার শক্তি শব্দের নির্বাচনে নয়, শব্দের স্পর্শে। তাঁর কবিতা তাই স্পর্শের কবিতা, দেহের, বেদনার, শ্বাসের, অন্তঃ¯্রােতের।
তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘ধরো নিজের হাত’-এ রয়েছে মানবের আত্ম-প্রত্যয়ের বিরল ভাষা। সেখানে তিনি লেখেন: “নিজেকে ধরো নিজের মতো করে।”এটি একটি সহজ বাক্য, কিন্তু তার অর্থ অসীম। শক্তির কবিতা আমাদের শেখায়- নিজেকে ধরতে গেলে নিজের অন্ধকারকেও ধরতে হয়। শক্তির ভাষায় আত্ম-দর্শন কখনো জাগতিক, কখনো তান্ত্রিক, কখনো দেহাত্মিক। তাঁর শব্দের মধ্যে রয়েছে গৃহবাসী জীবনের গন্ধ, আবার ধ্যানস্থ আরণ্যক সন্তের মহাকালভেদী গভীর নৈঃশব্দ্য।
যে শক্তি “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর”-এ শিশুসুলভ খেলায় মেতে ওঠেন, সেই শক্তিই আবার “কৈশোরকাল” কবিতায় বলেন- “একদিন ঘরে ফিরে দেখি আমার ভিতরকার মানুষটা আর নেই।” এই দুই শক্তির মাঝামাঝি রয়েছে তাঁর চিরকাব্যিক সত্তা- শিশু ও মহাপুরুষের মিলিত রূপ। তাঁর কবিতা কখনো ঝকমকে রঙিন,কখনো রক্তজবার লাল, কখনো ধূসর ছাইরঙা, কখনো সম্পূর্ণ সাদা। সেইসব রঙের আড়ালে থাকে মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক, আছে শারীরিক ভীতি, আছে আকুল প্রেম, আছে তন্ত্রময় বিস্ময়।শক্তির কবিতার এই বহুবর্ণিল স্পেকট্রোমেট্রি তাঁকে আলাদা করে দেয় তাঁর সমসাময়িকদের থেকে। তাঁর অনুভবের চোখটিও যেন সমকালীন আর সব কবিদের মতো নয়। সে কারণেই শক্তি কাঁদেন না, তিনি পৃথিবীকে কাঁদতে দেখেন। শক্তি মৃত্যুকে ভয় পান না, তিনি দেখেন- মৃতদের নীরবতায় পৃথিবী কীভাবে পালটে যায়। সে কারণে তিনি অমোঘ মৃত্যুর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বলে ওঠেন: ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ (১৯৮২)।
তাঁর কবিতায় সমুপস্থিত কখনো নগর,কখনো গ্রাম, কখনো দেহ, কখনো দেহাতীত অদৃশ্য আড়াল , কখনো বিশ্বাস, কখনোবা সংশয়। তাঁর কাব্যব্রহ্মা-ে থাকে মানুষের মুখ, কিন্তু কোনো কোনো মুখ থাকে মুখোশের আড়ালে ঢাকা। সে-কারণেই কি তবে আয়রনিক প্রিসিশনে তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও সেইসব দ্বিচারিতা মূর্ত হয়ে ওঠে: ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ (১৯৬৫)। তাঁর কবিতায় নদী থাকে, কিন্তু সে নদী চলে না; বরং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের মতো। শেষাবধি সবকিছুই মানুষের প্রতিরূপে দাঁড়িয়ে যায়। সেকারণে শক্তি মূলত প্রকৃতির আদলে মানুষেরই কবি। একবার কোনো রাখঢাক না করে তিনি সরাসরি লিখলেন: “মানুষই মানুষকে নির্মাণ করে/মানুষই মানুষকে ভেঙে দেয়।” তাঁর কাব্যস্বরে মনুষ্যকুলের এই মানবিকতা ও বিমানবিক নিষ্ঠুরতা ভাষা খুঁজে পেয়েছে সরাসরি বয়ানে।
শক্তির কবিতা পড়লে বোঝা যায়- তার নন্দনশাস্ত্র চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং আহত মানবসত্তার সৌন্দর্যের জন্য। তাঁর কবিতার শরীর অবিন্যস্ত, তবু মায়াময়। তাঁর শব্দ-সুর তীক্ষè, তবু কোমল। সে কারণেই কী তিনি কবিতার নাম বদলে পাকাপাকিভাবে ‘পদ্য’ রেখেছিলেন? অন্ত্যমিল থাকুক বা নাইবা থাকুক তাঁর অনেক কবিতায় একই বাক্যালাপ পুনরাবৃত্ত হয়ে ফিরে ফিরে আসতো সাঙ্গীতিক আবহে। আবার নান্দনিক বিদ্রোহে প্রচলিত ছন্দের বন্দিত্ব ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কাঠামোহীন নতুন ভাঙচুরে: ‘আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল’ (১৯৭৬)।
তাঁর কাব্যভাবনা গ্রাম্য ভুয়ো দর্শনের মতোই অতলান্ত গভীর, অথচ সেই কণ্ঠস্বর পুরোপুরি নাগরিক। প্রকৃতপক্ষে শক্তি কবিতা লেখেন না, শক্তি নিজেই কবিতা হয়ে ওঠেন কবিতার শক্তিতে। তাঁর প্রতিটি পঙ্ক্তি শুষে নেয় দুঃখ, ফিরিয়ে দেয় আলো। বিচ্ছুরিত সেই আলো গবাক্ষপথ পেরোলেই একের পর এক খুলে যেতে থাকে চৈতন্যের বন্ধ দরোজা- যার ভিতরে প্রবেশ করলে পাঠক নিমেষেই পৌঁছে যান এক জ্যোতির্ময় অন্তর্লোকে। তাঁর কবিতা মুহূর্তেই সমাজ আরোপিত আমাদের চেনা পরিচয়-অপরিচয়ের গ-ি ভেঙে দেয়, আবার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পুরোনো পরিচয় ভেঙেচুরে নির্মাণ করে আনকোরা নতুন পরিচয়। তাঁর কবিতা আমাদেরকে নিরন্তর প্রশ্ন করে- “তুমি কে?” আবার উত্তরও দেয়: “তোমার ভেতরে যে তোমাকে চেনে, সেই তুমি।” সে কারণেই তার কবিতা হয়ে ওঠে আত্ম-উন্মোচনের পথ। তাঁর কবিতা যেন শহুরে নৈঃশব্দ্যের ভেতর হঠাৎ উড়েএসে বসা কোনো এক বুনো বুলবুলি- দুঃখের ভিতরের আলো, আলোয় অন্ধকার, আত্মদর্শনের প্রকৃতি কিংবা প্রকৃতির কোলে মিশে যাওয়া অতল মানবগভীরতা। সেকারণে শক্তির কবিতায় জীবন-মৃত্যুর সংলাপ কখনো নিঃশব্দ, কখনো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ,কখনো শিশিরের শব্দের মতো জীবনানন্দীয় কোমল, আবার কখনো কখনো নরকের আগুনের হল্কার মতো বীভৎস। তাঁর কবিতায় ভাষা শুধু ভাষা নয়, অস্তিত্বের পদচিহ্ন। তিনি এমন এক কবি, যিনি বলেন: “মানুষ বড় কাঁদে, আর আমি সেই কান্নার পথ ধরে হেঁটে যাই।” অথচ এই কান্নার পথেই তিনি খুঁজে পান আলোকময়তার দ্যুতি। এটাই শক্তির স্বাতন্ত্র্য- অন্ধকারকে অস্বীকার করে নয়, বরং তাকে গ্রহণ করে আলোর সোপান হয়ে ওঠা।
বাংলা কবিতার আধুনিক পর্বে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এমন এক উচ্চারণ যিনি ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেননি, বরং ভাষাকে নিজের অন্তর্জগতের মতোই হাঁটতে-চলতে-নিদ্রায়-জাগৃতিতে হঠাৎ পথ হারাতে দিয়েছেন। তাঁর কবিতা যেন এক চলমান জীবনের দেহ, যেখানে প্রতিটি শব্দ শ্বাস নেয়, প্রতিটি লাইন কোনো গভীর অরণ্যের ভেতর আলো-আঁধারির মতো পাল্টাতে থাকে। শক্তি আমাদের দেখান- কবিতা শুধু চিত্রকল্পের খেলাঘর নয়, বরং এটি অন্তর্লৌকিক ভূদৃশ্য- যেখানে মানুষের আর্তি, প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি, দেহ-মনের দ্বন্দ্ব, নাগরিক ধুলোবালির ক্লান্তি ও দেশজ মাটির সন্তানসুলভ উষ্ণতা একসঙ্গে প্রবহমান।
শক্তির কবিতায় এসে প্রথমেই ধরা পড়ে তাঁর কাব্যভাষার নির্ভার নৈসর্গিক নিজস্ব সৌন্দর্য। তিনি শব্দকে বাঁধন দেন না; শব্দ আপন গতিতেই তাঁর কাছে আসে লতাগুল্মের মতো, ফুলের মতো ফোটে, আবার কখনো অন্তর্গহ্বরের মতো অন্ধকারে ডুবে যায়। দেশজ শব্দ তার কবিতায় কেবল লৌকিক স্মৃতির প্রতিধ্বনি নয়; বরং আধুনিকতাকে শিকড়ে বেঁধে রাখার এক নীরব প্রতিরোধ। আধুনিক কাব্যে যেখানে শহুরে জীবনের চাকচিক্য অনেকের কাছে ‘উন্নত রুচি’র পরিচায়ক ছিল, শক্তি সেখানে সপ্রতিভ দুঃসাহসে ফিরিয়ে আনলেন বাংলার অভ্যন্তরীণ স্বর- কাদা, ধুলো, টিনের ছাদ, পান্না-সবুজ গাছ, গ্রামীণ উচ্চারণ, ভ্রমণরত পথিকের শ্বাস- এইসব সহজিয়া শব্দের অনন্য দীপ্তি। আর এই শব্দশৈলীর ভেতরে রয়েছে গভীর মানবতাবাদ। শক্তির কবিতা তাই মানুষকে অন্যায্য উচ্চাসনে বসায় না; বরং মানুষের ভয়, ক্ষুধা, ভ্রম, তৃষ্ণা, অনিদ্রা, অপরাধবোধ- এসবকেই আশ্রয় করে তার জন্য এক নতুন পৃথিবী নির্মাণ করে। “জীবন” তার কাছে কোনো তত্ত্ব নয়; বরং এক ঐহিক অভিজ্ঞতা, যা ভুলের মধ্য দিয়েও আলো খুঁজে ফেরে। এই মানবতাবাদই তাকে এমন সাহস দেয়- নিজেকে জরাসন্ধের মতো দ্বিধাবিভক্ত, ছিন্নমস্তক, তবু জীবিত হিসেবে তুলে ধরতে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার চাপ, নাগরিক নিঃসঙ্গতা, ইতিহাসের ভাঙচুর- এসবই তাকে বিভক্ত করেছে, কিন্তু সেই বিভক্তিতেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন দুর্লভ কবিতার দুর্নিবার শক্তি। অপ্রার্থিত অপ্রস্তুত ভাঙনের? চুরমারই যেন তাঁর সৃষ্টির প্রেক্ষণবিন্দু।
শক্তির কবিতার দার্শনিকতা তাই অস্তিত্ববাদী হলেও অমসৃণ, মাটির গন্ধে ভেজা। তিনি অস্তিত্বের সংকটকে ল্যাবরেটরিতে বসে বিশ্লেষণ করেন না; বরং রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের কলরব, বৃষ্টিজল মাখা রাত্রির নেশা, পথের ধুলোর ধোঁয়াশা- এসবের মধ্য দিয়েই অনুভব করেন নিজের দ্বন্দ্বময় সত্তাকে। আর তাই তাঁর কবিতা চরমভাবে ব্যক্তিগত অথচ আশ্চর্যরকম সার্বজনীন। এক কবিতায় তিনি পথিক, আরেক কবিতায় ভ্রমণপিপাসু বাউল, আবার কখনো এমন শহুরে মানুষ, যার ভেতরে আদিম বনফুলের গন্ধ লুকিয়ে থাকে।
প্রকৃতি তার কবিতায় শুধুই মুগ্ধতার বস্তু নয়, বরং শরণ। নদী, বাতাস, গাছ, অরণ্য- এসব তার ভ্রমণতৃষ্ণার সঙ্গী, আবার মানসিক আশ্রয়ও। শক্তির প্রকৃতিচেতনা কোনো রোমান্টিক অলঙ্কার নয়; বরং বেঁচে থাকার ক্ষুধার মতোই গভীর ও দেহাবদ্ধ। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তাকে শোনেন, তাকে পিঠ চাপড়ে এগিয়ে যান। যেন প্রকৃতি তাকে বারবার নিজের কাছে টেনে নেয়, আর বিপরীতে শহর তাকে তাড়া করে- এই টানাপোড়েনেই জন্ম নেয় তীব্র আবেগময় চিত্রকল্প।
অন্যদিকে বলতে হয়- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এক ধরনের নীরব বিদ্রোহ কিংবা সরব শান্তির সপক্ষে গমগম আবহ। কবি পশ্চিমা আধুনিকতার তত্ত্ববিলাসী বাগাড়ম্বর প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব স্বাভাবিক স্বকীয়তায় মত্ত থেকেছেন আজীবন। তার কবিতার আধুনিকতা কোনো ভঙ্গি নয়, বরং নিজস্ব যন্ত্রণার আলোয় পুড়িয়ে নেয়া সত্য। তাই শক্তির কবিতা পড়লে মনে হয়- মানুষ হাঁটছে, পথ হারাচ্ছে, আবার পথ খুঁজে পাচ্ছে। কবি যেন নিজ পেয়ালার দ্রাক্ষাসুধায় মগ্ন হয়ে আপনমনে কথা বলে চলেছেন নিজের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে, দুঃসময়ের সঙ্গে, দূরাগত নক্ষত্রের সঙ্গে এমনকি অনঙ্গ অন্ধকারের সঙ্গেও। প্রাণবন্ত মানবদেহের মতোই চলিষ্ণু তাঁর কবিতা- কখনো মৃদু শান্ত সমীরের মতো, কখনো উদ্দেশ্যহীন অচীন পরিব্রাজকের মতো। সেকারণেই হয়তো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক মুগ্ধকর আরণ্যক নিবিড়তা কিংবা কঠোর কঠিন বাস্তবতার রৌদ্রদগ্ধ মুক্তাঞ্চল- যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি বাৎসল্যে একাকার, শর্তহীন প্রেম-অপ্রেমের অবাধ আসা যাওয়া, সোঁদা মাটির গন্ধমাখা নিজস্ব ভাষাভঙ্গি, অস্তিত্বিক-দ্বন্দ্ব এবং কাব্যিক স্বেচ্ছাচারিতা মিলেমিশে গড়ে তোলে এমন এক নন্দনবিশ্ব যা একইসঙ্গে স্বপ্নময় অথচ নিদ্রাহীন, অস্থির অথচ নিবিড়, যেন বাউলের গানের মতো সহজ অথচ জীবনজটিলতার দুর্গম বাঁক পেরিয়ে পরাবাস্তব অসীমের প্রান্ত ছুঁয়ে যায় অবেলায়।
শক্তির কবিতাকে বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হয় তাঁর প্রকৃতিনির্ভর নন্দনতত্ত্বের কথা। প্রকৃতি শক্তির কাছে কেবল একটি পর্যবেক্ষণ নয়, তা হলো তাঁর ভিতরের গভীরতম মানবসত্তার প্রতিচ্ছবি। ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’-এ তিনি লেখেন: “হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান,/যে সমস্ত চিঠির ঠিকানা আমি জানি না,/সেগুলোও আমাকে বিলোতে হয়।” এই অরণ্য শুধুই ঋতুর গাছপালা নয়; এটি কবির নিজের মনোজগত। অরণ্য- পোস্টম্যান- অজানা ঠিকানা- সব মিলিয়ে এক অভিনব অস্তিত্ববোধ। মানুষ সমাজে থাকলেও সে নিঃসঙ্গ, যে নিজেকেই চেনে না, যে অজানা আবেগ বয়ে বেড়ায়- শক্তির কবিতা সেই অনির্বচনীয়তারই ভাষা। আরও সামনে তিনি লিখছেন: “ঢেকে যায় রাস্তা, পাতারা উড়ে এসে চিঠির ওপর পড়ে, যেন সেই চিঠিও আমার নয়।” এই চিঠি মানবসম্পর্কের রূপক, যা জীবনে আসে কিন্তু কখনোই পুরোপুরি ধরা দেয় না। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের এই যে দ্যোতনামূলক সম্পর্ক- এটাই শক্তিকে তাঁর সমসাময়িকদের থেকে পৃথক করে রাখে।
অন্যদিকে তাঁর ‘অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে’ শীর্ষক কবিতাটি যেন আত্মবীক্ষণের এক মুহূর্তিক দর্পণ: “অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে,/ তাতে নিজের মুখও দেখলাম এক মুহূর্ত,/তারপর অন্ধকার এসে ঢেকে দিল/আমি জানলাম- আমার মুখও অন্ধকারে জন্মায়।” এখানে কুয়া শুধু স্থানের চিহ্ন নয়; এটা অতল আত্মদর্শনের পাত্র। শক্তি প্রকৃতিকে আত্মজিজ্ঞাসার উপমা হিসেবে প্রয়োগ করেন, এবং এই প্রয়াস এতটাই অনন্য যে তা বাংলা কবিতার ভাষাকে নতুন নন্দনচেতনায় সমৃদ্ধ করে।
শক্তির ভ্রমণপিপাসা ও পথিকসত্তাও তাঁর কাব্যকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। ‘মুঠো করা রঙ-বেরঙ টিকিট’ কবিতার বড় অংশে তিনি লিখছেন: “মুঠো করা রঙ-বেরঙ টিকিট/ ধরে আছে আমার ভিতরের সব-হারা শিশু,/ যে প্রতিটি টিকিটে দেখে একটি ভ্রমণ/ যে প্রতিটি ভ্রমণে দেখে একটি নতুন দেশ/ যে প্রতিটি দেশে খুঁজে ফিরে একটি মানুষের মুখ।” এখানে ‘শিশু’ তাঁর অবিনশ্বর, অমলিন সত্তা- যে অবাক হয়ে পৃথিবী দেখতে চায়। শক্তির ভ্রমণ আসলে মানুষ খোঁজার ভ্রমণ। মানুষ খুঁজতে খুঁজতে তিনি নিজেকেও খুঁজে পান। কবিতাটি শেষে এসে বলে: “যাত্রা শেষ হয়নি কখনো, / আমি টিকিটগুলো মুঠোর ভিতরেই রাখি-/ যেন পরের দেশ, পরের মানুষ আমাকে ভুলে না যায়।” এ অসাধারণ মানবতাবোধ- শক্তির কবিতার মর্মরেখা।
‘চতুরঙ্গ’ কবিতায় তিনি সমাজ-জটিলতার চিত্র এঁকেছেন: “চারদিকে খেলা চলছে/ আমি কেবল এক কোণে চাপা পড়া মোহর,/তবু খেলা থেমে গেলে বোঝা যায়-/এই খেলা আমার ছাড়া চলতই না।”
এটি সমাজ-অস্তিত্বের দার্শনিক পাঠ। মানুষ যন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হলেও মানুষই সমাজের কেন্দ্রে। এটি শক্তির অন্তর্নিহিত মানববিশ্বাসের প্রতিফলন।
এখানে আসতেই হয় হাংরি আন্দোলনের প্রসঙ্গে। ষাটের দশকের সূচনায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হাংরি আন্দোলনের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ। এই আন্দোলনের বিদ্রোহ ছিল ভাষাবোধের বাঁধাধরা রুচির বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রসৃষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সামাজিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে। এই সময় শক্তির ভাষা হয়ে ওঠে অগ্নিভ, উন্মাদ, দহনমুখী। কিন্তু শক্তির গভীর সত্তা চেয়েছিল আরও বিস্তৃত অর্থে মানবতাবাদ। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদ্রোহ যথেষ্ট নয়- প্রেম দরকার, দার্শনিকতা দরকার, দরকার কাব্যভাষার স্বাতন্ত্র্য। তিনি বুঝলেন- কেবল রাগ নয়, আবেগের পূর্ণতা চাই। তাই তিনি মূল কবিতার ধারায় ফিরে এলেন। এবং এই ফিরে আসা কবির ব্যক্তিগত পরিণতির মতোই বাংলা সাহিত্য ইতিহাসেও এক গভীর তাৎপর্য রেখে যায়। এই প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ভাষা আরও পরিণত, আরও দেশজ, আরও দার্শনিক হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতার “আমি”- একান্ত ব্যক্তিগত থাকলেও মানুষের গভীর হৃদয়বৃত্তিকেই আলোকিত করে। তিনি জানতেন- বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবী, ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষতবিক্ষত মানসিকতা, নাগরিক জীবনের অবক্ষয়- এসবের গভীরতা বোঝাতে আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। তাই তাঁর শব্দচয়ন এত অকপট:
“চাই না”, “যাব”, “থাকুক”, “মরে যাই”- এরকম সাধারণ শব্দ তাঁর কবিতায় অদ্ভুত একটা শক্তি বহন করে।এই সাধারণ শব্দেই তিনি লেখেন “হৃদয়টা খোলা রেখে দিয়ে গেছি,/যেমন রেখে যায় খেতের মাঝখানে/একটা মানুষের ছায়াবিকেলের রোদে।” শব্দগুলো যেন নিজের আলোয় জ্বলছে, কোনো অলংকার ছাড়াই।
১৯৫৩ সালে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন ‘কৃত্তিবাস’-এর কবিদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম প্রধান দুই কবি হিসেবে নিত্যনতুন নিরীক্ষা ও সৃষ্টিশীলতায় আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন অভিমুখ রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বন্ধুত্বে, ইন্দ্রিয়শাসিত উদ্দাম আড্ডায় এবং কবিতাযাপনে আনন্দমুখর সময় কাটাতেন। তবে এতো কিছুর মধ্যেও শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে নিজস্ব নিভৃত কাব্যসাধনায় নিমগ্ন থাকতে পেরেছিলেন বলে তিনি বাংলা আধুনিক কবিতার বিস্তৃত ক্যানভাসে নিজস্ব কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।
বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের কবিতায় জীবনানন্দ-উত্তর যে নন্দনচেতনা জন্ম নিচ্ছিল- দৈনন্দিনতা, বিষণœতা, নাগরিক একাকীত্ব, অস্বস্তি, ভ্রমণ, প্রকৃতির প্রতীকায়ন- সবকিছুই শক্তি এক নতুন ধারায় উপস্থাপন করেন। তাঁর কবিতা কখনো বিমূর্ততা ছাড়ে না, আবার কখনো লোকজ উচ্চারণের রুক্ষতাও গ্রহণ করে। এই দ্বৈততা তাঁকে অনন্য করে তোলে। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী কবি আবার অস্তিত্ববাদীও। তিনি প্রকৃতিনির্ভর, আবার শহুরেও। তিনি লোকজ ভাষার কবি, আবার দার্শনিকও। এমন বৈপরীত্যই তাঁকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতে পরিণত করেছে। এ কারণেই আজ আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য বাংলা আধুনিকতার স্বতন্ত্র আলো। তবে কবির অন্তর্গত দ্বিধা, বিভাজন ও আত্মজিজ্ঞাসার সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রতীক হলো ‘জরাসন্ধ’ এটি তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে। তিনি লিখছেন: “ফিরিয়ে নেব না আমি/জরাসন্ধ প্রতি জন্ম রোগ-/এ প্রসব ভুল নয়,/ভুল নয় এই অন্ধকার। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে ‘জরাসন্ধ’ তাঁর সত্তার ভাঙা দুই অংশের প্রতীক। যেমন মহাভারতের চরিত্র জরাসন্ধ দুই অর্ধেক দেহে জন্মেছিলেন, শক্তিও অনুভব করেন যেন তাঁর ভেতরে অনুরূপ দুটি সত্তা। এর একটি দেশভাগের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিচ্ছিন্নতার বোধ অপরটি অভিন্ন আকাশের নিচে উড়ে বেড়ানো এক ‘পাখি আমার একলা পাখি’, সেই পাখি বৌদ্ধিক ডানা মেলে পৌঁছে যায় চিরমানবের অন্তর্লোকে। শক্তি তাঁর এই দ্বিভাজিত সত্তাকে কখনোই লুকোননি। তিনি তাকে গ্রহণ করে তবেই নিজের কবিতাকে পূর্ণতা দিয়েছেন; সেই দীক্ষা ও আহ্বানের মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করে চলেছেন অধুনাবাদী নির্মাণের অমিত শক্তি। আর সময়ে অসময়ে আমাদের সামষ্টিক অবচেতনের অবরুদ্ধ দুয়ারে এসে এই বলে কড়া নাড়েন: “অবনী বাড়ি আছো?”