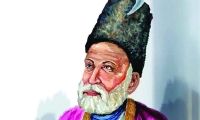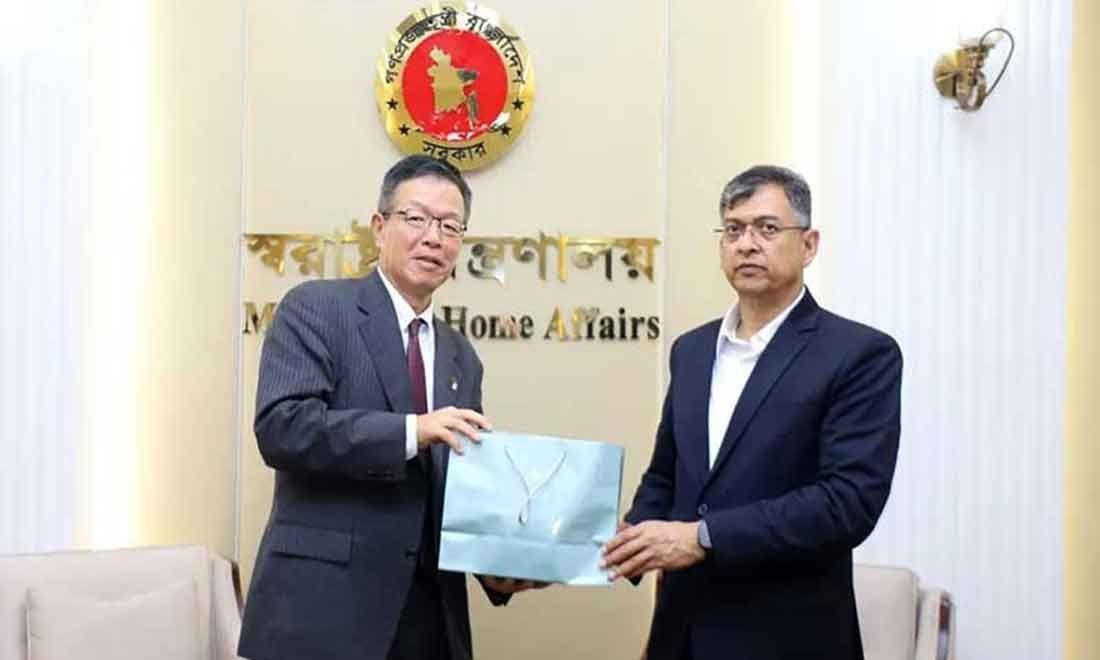রাস্কিন বন্ড-এর গল্প
ডেরায় লাগানো বাবার গাছগুলো
অনুবাদ : ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়
(পূর্ব প্রকাশের পর)
রাস্তার উপর গড়ে উঠেছে নতুন সব ভবন কিন্তু পুলিশ স্টেশনটা আজও আছে সেই পুরনো চুনকাম করা বাংলোটায়। দু’জন পুলিশ আংশিক ইউনিফর্মে, হাতে হাত ধরে ঘোরাফেরা করছে ঘাসের প্রাঙ্গণে। তাদের হয়তো তখন কাজের অবকাশ। উত্তর ভারতে হাত ধ’রে মানুষদের ঘুরতে প্রায়ই দেখা যায়, যদিও তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ সম্পর্ক বিরাজ করে না।
আমি এই ছোট্ট পুলিশ স্টেশনটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। ১৯৪৭ সালের আগে এই পুলিশ স্টেশনটির আশেপাশে কোনোই উত্তেজক ঘটনা ঘটতে দেখা যায় নি। তার পরই ডেরায় বেধে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তখন দিনে দিনে ঐ খাল থেকে তোলা হতো মৃতদেহ, তারপর তাদের ডাই মেরে রাখা হতো পুলিশ স্টেশন প্রাঙ্গণে। যখন আমি পাঁচিলের উপর দিয়ে উঁকি মেরে সে দৃশ্য দেখি, তখন আমি নিতান্তই বালক, আমাকে কেউ তখন গ্রাহ্য করেনি। তারা শুধু আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল, আর তারা একথা জানতো যে আমি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। যখন হিন্দু এবং মুসলিম পরস্পরের উপর হামলা চালাচ্ছে, তখন একজন শেতাঙ্গ বালক নিরাপদে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারে। কেউই তখন ইউরোপীয় মানুষের প্রতি কোনো কৌতূহল বোধ করেনি।
ডেরায় মানুষেরা প্রকৃতিগতভাবে হিং¯্র নয়। আর শহরে ইতোপূর্বে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু যখন হাজার শরণার্থী উদ্বাস্তু এসে জমা হলো পাঞ্জাব থেকে, শহরের মানুষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। ঐসব শরণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল শিখ। তারা তাদের ঘরবাড়ি, জীবিকা হারিয়ে চলে এসেছে এদেশে, অনেকে দেখেছে তাদের প্রিয়জনদের বীভৎস মৃত্যু। তারা এসেছিল ভয়ঙ্কর, প্রতিহিংসাপরায়ণ মন নিয়ে। ডেরায় শান্ত, নিঝুম পরিবেশ ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। দু’মাস ধরে চলল হত্যা আর লুটপাট। যেসব মুসলিম পারলো তারা পালিয়ে গেল। সমাজের দরিদ্র অংশকে নিয়ে রাখা হলো শরণার্থী ক্যাম্পে, যতদিন না সেই হত্যালীলা শেষ হয়। তারপর তারা ফিরে এলো তাদের পুরনো পেশায়, ভীত সন্ত্রস্ত মন নিয়ে। কেউ আর কাউকে বিশ^াস করতে পারে না। ঐ বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা তাদেরই একজন।
আমি খাল পার হয়ে রাস্তা ধরলাম, যে রাস্তা ধরে আমি পৌঁছে যাবো নদীগর্ভে। এটাই ছিল আমার বাবার অতি প্রিয় একটি হাঁটার জায়গা। তিনি প্রায়ই প্রচুর হাঁটতেন। মাঝে মাঝে ছুটিতে যখন তিনি বাড়িতে থাকতেন, আমাকে বলতেন, “রাস্কিন, চল আমরা গিয়ে একটু হেঁটে আসি”, আর অমনি আমরা বেরিয়ে পড়তাম, চলে যেতাম নদীগর্ভ পর্যন্ত অথবা রেললাইন পার হয়ে চলে যেতাম আখের ক্ষেত কিংবা জঙ্গলের ভিতর।
এইরকম একটা হাঁটার সময় (সে ছিল স্বাধীনতার আগে), আমার মনে পড়লো, তিনি বললেন, “যুদ্ধ শেষ হ’লে আমরা ইংল্যারন্ড চলে যাব। তুমি সেটা চাও”? আমি বললাম, “আমি জানি না। আমরা কি ভারতে থাকতে পারি না”?
“এ দেশটা এখন আর আমাদের থাকবে না”। “এ দেশটা কখনও কি তা ছিল”? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
তিনি বললেন, “অনেক দিন তা’ ছিল। দুইশ’ বছর যাবৎ। কিন্তু এখন আমাদের সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে”। তখন সবেমাত্র আমার নয় বছর বয়েস। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কাদের ফিরিয়ে দেব”?
তিনি বললেন, “ভারতীয়দের”।
তখন পর্যন্ত যে ভারতীয়দের আমি জানতাম তারা হ’ল, আমার আয়া, বাবুর্চি, বাগানের মালি ও তার ছেলেমেয়েরা। আমি ভাবতেও পারতাম না তারা আমাদের ছাড়া থাকতে চায়। ওদের ছাড়া আর মাত্র একজন যে ভারতীয় আমাদের বাড়িতে এসেছিল তিনি হচ্ছেন ডা. ঘোষ। তার সম্বন্ধে কথা উঠলে প্রায়ই বলা হতো, তিনি একজন ইংরেজের চেয়ে বেশি ইংরেজ। আমি বাবাকে তখনই বুঝতে পারতাম, যখন তিনি বলতেন, “যুদ্ধের পরে আমি ইংল্যান্ডে গেলে চাকরি পাবো। কিন্তু আমার জন্যে এখানে আর কিছুই থাকবে না”।
প্রথমদিকে যুদ্ধকে খুব একটা দূরবর্তী ঘটনা বলে মনে হতো। কেমন করে যেন সেটা এগিয়ে আসতে লাগলো। আমার এক কাকি যিনি তার দুই সন্তান নিয়ে বাস করতেন লন্ডনে, তিনি তার দুই সন্তানকে নিয়েই মারা যান বোমা বর্ষণে। তারপর আমার বাবার ছোট ভাই মারা গেলেন আমাশয়ে ভুগে। বার্মা থেকে দীর্ঘ পথ ধরে ভারতে আসার পথে ঘটনাটা ঘটলো। এই দু’টি মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বাবা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। বাবার স্বাস্থ্য কখনও খুব ভালো ছিল না (তিনি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতেন), তার উপর যতবারই তিনি বাড়ি ফিরতেন, ততবারই তাকে আরও দুর্বল মনে হতো। তার ব্যক্তিগত জীবন কখনও খুব সুখী ছিল না, মায়ের সাথে ছাড়াছাড়ির পর মা আবার বিয়ে করেছিলেন। ঐ বয়সে আমি যতটুকু বুঝতাম তাতে মনে হতো বাবা যেন আমার সাথে দিন কাটাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। আমি তার কাছে এমনই ছিলাম, যার কাছে বারবার ফিরে ফিরে আসা যায়, যাকে নিয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা করা যায়, যে সবসময় তার কাছ থেকে কিছু শিখতে চায়।
ডেরা ছিল তার বসবাসের উপযুক্ত স্থান। তিনি গাছপালাদের মধ্যে থাকলেই সুখী থাকতেন, আর সেই সুখ আপনাআপনি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হতো। আমার মনে হতো যেন আমি ক্রমেই আরও তার নিকটে পৌঁছে যাচ্ছি। মনে পড়ে, আমি যেন বসে আছি বারান্দায়, তার পাশে, আর সিঁড়িগুলো আমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। আমরা যেখানে বসেছিলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে‘ঐ রকম চমৎকার বাগানে সময় সকল অর্থ হারিয়ে ফেলেছিল‘একটা লতানো গাছের শুঁড় ধীরে, অতি ধীরে, আমার কাছ থেকে ক্রমেই বাবার দিকে মরে সরে যাচ্ছে। কুড়ি মিনিট পর দেখলাম বারান্দায় সিঁড়িগুলো পার হয়ে স্পর্শ করেছে আমার বাবার পা। ভারতে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর অভিবাদনের ভঙ্গী।
গাছের প্রতিটি আচরণের নিশ্চয়ই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে‘ তাতে বারান্দার উপর পড়া আসে এবং উষ্ণতার একটা ভূমিকা আছে‘কিন্তু আমার মনে হয়, তাদের এই এগিয়ে চলার পিছনে বাবার প্রতি ভালোবাসাও কাজ করে। কখনও কখনও আমি যখন নির্জনে বসে থাকি একটা গাছের নিচে, মনে হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলি, মনে হয় আমি একান্ত, নিঃসঙ্গ। যখনই বাবা এসে আমার পাশে বসেন, পরিবেশটা ঝলমল করে ওঠে, গাছেরা যেন আরও বন্ধু হয়ে যায়।
বাড়ির চারপাশের সব ফলের গাছই বাবার হাতে লাগানো; কিন্তু তিনি শুধু বাগানে গাছ লাগিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। বর্ষার দিনে হাঁটতাম আমরা দু’জনে নদীর পাড় ধরে, আমাদের হাতে থাকতো গাছের চারা এবং কাটিং। তাই নিয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেগুলো লাগিয়ে দিতাম শাল আর শিশু গাছের ফাঁকে। ওগুলো ছিল সব সপুষ্পক উদ্ভিদ।
প্রথমে আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, “কিন্তু ওখানে তো মানুষজন আসে না। কে দেখবে ওদের”? “কখনও কেউ এ পথে আসতে পারে। মানুষ যদি শুধু গাছ কেটেই চলে তাহলে তো একদিন বন উজার হয়ে যাবে, আর এই পৃথিবীটা একদিন পরিণত হবে একটা বিশাল মরুভূমিতে”, তিনি বললেন, একটা বৃক্ষশূন্য পৃথিবীর চিন্তা আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতো, তাই আমি বাবাকে বিপুল উৎসাহে গাছ লাগানোর কাছে সাহায্য করতাম।
তিনি বলরেন, “একদিন এই গাছগুলো চলতে শুরু করবে। এরা হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সময় ছিল যখন এরা মানুষেরই মতো হেঁটে চলে বেড়াতো। তারপর একদিন একজন এক মন্ত্রবলে এদের এক জায়গায় স্থির, অনড় করে দিল। কিন্তু তারা সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছে সচল হবার‘ দেখ ওরা কেমন হাত বাড়িয়ে আছে”!
আমরা শুকিয়ে যাওয়া নদীর বুকে একটা দ্বীপ, একটা পাথুরে দ্বীপ, খুঁজে পেলাম। পাহাড়ের পাদদেশে অনেক শুকিয়ে যাওয়া নদীর দেখা মিলতো, এটা তারই একটা। এরকম নদীখালগুলো গ্রীষ্মে একেবারেই শুকিয়ে যায় আবার বর্ষায় ফুলেফেঁপে দু’কূল ছাপিয়ে প্লাবিত করে দেয়। সবেমাত্র তখন বর্ষা শুরু হয়েছে, ¯্রােতস্বিনীকে তখনও হেঁটে পার হওয়া যায়। তখনই আমরা কয়েকটা তেঁতুল, মাদার আর আমলতাস গাছের চারা আর কাটিং নিয়ে রওনা হলাম। সারাদিন ধরে আমরা সেগুলোকে ঐ দ্বীপটায় লাগালাম, তারপর একটা বুনো কূলগাছের ছায়ায় বসে আমরা মধ্যাহ্নভোজ সারলাম।
ঐ গাছের চারা লাগাবার অল্প কয়েকদিন পরেই বাবা চলে গেলেন। তিন মাস পর তিনি কলকাতায় শেষ নিঃশ^াস ত্যাগ করেন।
আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো বোর্ডিং স্কুলে। আমার দাদু ঐ বাড়ি বিক্রি করে ডেরা ছেড়ে চলে গেলেন। স্কুল শেষে আমি গেলাম ইংল্যান্ডে। বছরগুলো একে একে পার হয়ে যেতে লাগলো, দাদু মারা গেলেন, আর আমি যখন ভারতে ফিরলাম তখন আমিই ভারতে আমার পরিবারের একমাত্র সদস্য।
এখন আমি আবার ডেরাতে ফিরে এসেছি, দাঁড়িয়ে আছি নদীখাতে যাবার সেই রাস্তায়। সুন্দর সুসজ্জিত বাগানওয়ালা বাড়িগুলো পিছনে ফেলে এসেছি, আমি হেঁটে চলেছি প্রস্ফুটিত সরিষা ফুলের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে। সেই হলুদ ফুলগুলো যেন একটা গালিচা পেতে দিয়েছে, আর তা চলে গেছে দূরের বন পর্যন্ত এবং সেখান থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত।
ও সময় নদীখাতটা থাকে শুকনো। একদল হাড়জিরজিরে বাদামী রংয়ের গরু বনের প্রান্তের একফালি সবুজ ঘাসের মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছিল। বনের শাল গাছগুলো পাতা ঝরিয়ে শূন্য, রিক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বনগুলো কি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে? আমাদের দ্বীপটা কি টিকে থাকতে পারবে নাকি এক প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট প্লাবনে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?
শুষ্ক জলের ধারার দিকে দৃষ্টি দিতেই চোখে পড়লো থোকা থোকা মান্দার ফুল। সামনে শুকনো নদীখাতের বিপরীতে সবুজ ঘাসের ছোট্ট দ্বীপটা যেন একটা মরূদ্যান। আমি গাছগুলোর কাছে হেঁটে যেতেই দেখি একঝাঁক টিয়াপাখি গাছটিতে বাস করতে শুরু করেছে। একটা কোয়েল পাখি “তুমি কে, তুমি কে” বলে চেঁচিয়ে সতর্ক করে দিলো আমাকে?
কিন্তু গাছগুলো মনে হলো আমাকে চিনতে পারলো। তারা নিজেদের মধ্যে ফিস্ফিস্ করে ইশারা দিতে লাগলো। দেখলাম অন্য গাছ, বুনো লতাগুল্ম আর ঘাস গজিয়েছে আমাদের গাছগুলোর নিচে। ঐ গাছগুলোই তাদের রক্ষা করে আসছে পরম ¯েœহে।
এতদিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর এই বিস্মৃত এক প্রান্তে আমার বাবার স্বপ্ন যেন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে, এবং গাছেরা আবার চলতে শুরু করেছে। (সমাপ্ত)
লেখক পরিচিতি
রাস্কিন বন্ড (জন্ম: ১৯ মে ১৯৩৪) একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে ভারতের মুসৌরিতে থাকেন। ‘আওর ট্রিস স্টিল গ্রো ইন দেহারা’ লিখে ১৯৯২ সালে তিনি সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান। তিনি ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১৪ সালে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন।
বন্ডের ঐতিহাসিক উপন্যাস “এ ফ্ল্যাইট অফ পিয়গন্স” থেকে হিন্দি চলচ্চিত্র ‘জুনুন’ করা হয়েছে। এটি তৈরি করেছিলেন শশী কাপুর এবং পরিচালনা করেছিলেন শ্যাম বেনেগাল। রাস্কিন বন্ডের ছোটগল্প “সুসানার সেভেন হাসবেনডস” উপর ভিত্তি করে বিশাল ভরদ্বাজের চলচ্চিত্র “৭ খুন মাফ” তৈরি করা হয়েছে।
বন্ডের জীবনের বেশিরভাগ কাজ হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড় স্টেশন দ্বারা অনুপ্রাণিত, এখানে তিনি তার ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। তিনি তার প্রথম উপন্যাস ‘দ্য রুম অন দ্য রুফ’ লিখেছিলেন ১৭ বছর বয়সে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল যখন তার বয়স ২১ বছর। এই সময়টা দেরাদুনে তার বাড়ির ছাদে ছোট ভাড়া রুমে তার বন্ধুদের সঙ্গে আংশিকভাবে থাকার ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। তার কিছু বিখ্যাত রচনা: দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দৈলি, আওর ট্রিস স্টিল গ্রো ইন দেহারা, হন্টিংগস্, দ্য আইস্ হাভ ইট, দ্য ইন্ডিয়া আই লাভ, ওয়ান্স আপন এ মুনসুন টাইম, দ্য পান্থেরস মুন, দ্য রোড টু দ্য বাজার প্রভৃতি।