উপ-সম্পাদকীয়
মুক্তিযুদ্ধ ও কিছু প্রশ্ন
শঙ্কর প্রসাদ দে
প্রথম প্রশ্ন হলো- মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক আদর্শ কী ছিল? কোন আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়েছিল? আমাদের আদর্শই বা কী ছিল? মুসলিম জাতীয়তাভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক আদর্শের লড়াই চলেছে তেইশ বছর ধরে। বিজয় দিবসের দিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় হয়েছিল।
দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো- অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ কি জয়ী হয়েছিল? এটি শতভাগ জয়ী হয়েছে এমন বলা যাবে না। মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একঝাঁক তরুণ রাজনৈতিক কর্মীর মোহভঙ্গ হয় দ্রুত। তারা শুরু থেকে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। তাদের বক্তব্য পূর্ববাংলায় জনগণ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলে একত্রে বসবাস করে। বড় মাছ ছোট মাছ যেমন একত্রে পুকুর দীঘি নদীতে বাস করে বাঙালির অবস্থানও তেমনি পাশাপাশি কাছাকাছি এমনকি একসঙ্গে। এ দেশের শহরগুলো দেখুন, একই বিল্ডিংয়ে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান একসঙ্গে থাকে।
পুরোপুরি জয়ী হইনি এজন্য যে, বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ছেলে-মেয়েদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় না। অথচ বিশাল ভারতে মুসলিম ছাত্ররা ছাড়াও অন্য সব সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা সংখ্যায় কম হলেও একসঙ্গে পড়ে। মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হলে জ্ঞানের বহু দরজা খুলে যেত। অবশ্য কম হলেও অনেক ইংরেজি বাংলার শিক্ষক মাদ্রাসায় চাকরির সুযোগ পেয়েছে। সহশিক্ষা আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাস্তবতা হলো গোটা দেশে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অযৌক্তিক এবং অসম্ভব। এই নীতি মাদ্রাসা শিক্ষার বেলায়ও প্রযোজ্য। মাদ্রাসায় সহশিক্ষা চালু হলে বহু মেয়ে অন্তত অক্ষর জ্ঞান অর্জন করতো। একাত্তরের বিজয় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। আমরা সেটা অনেকাংশে পারলেও ব্যর্থতার দায়ভার বেশি।
তৃতীয় মৌলিক প্রশ্ন হলো- নারীর ক্ষমতায়ন মুক্তিযুদ্ধের সব লক্ষ্যের মধ্যে একটি অগ্রগামী চেতনা ছিল। বিজয়ের তেপ্পান্ন বছর পর এই একটি ক্ষেত্রে জাতি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ দেশের মেয়েরা আজ প্রশাসন চালায়, দেশ চালায়, সেনাবাহিনীসহ সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে এ দেশের মেয়েরা সিপাহী থেকে এসপি বা মেজর জেনারেল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছেন। এ দেশের মেয়েরা বিমান চালায়, গার্মেন্টস শিল্পে তো মেয়েরাই প্রাণভোমরা।
কিন্তু এ রাষ্ট্র নারীদের জন্য অভিন্ন উত্তরাধিকার আইন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সহজ কথায় মেয়েরা নিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকারী মাত্র। জীবনসত্তা বা মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিকানার বাইরে হিন্দু নারীরা তেমন কিছুই পায় না। স্ত্রী ধন, সেটা এক জটিল চ্যাপ্টার। বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে নারী পুরুষে কোন ভেদাভেদ রাখা হয়নি। মুসলিম সমাজেও নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে বহু বির্তক চোখে পড়ে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার অভিন্ন নারী নীতি অর্থাৎ সম্পত্তিতে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ছেলে-মেয়ের সমান উত্তরাধিকারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হলো তার প্রস্তাবনা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরোধিতার মুখে খড়খুটার মতো উড়ে গেছে। রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সংবিধান প্রদত্ত নারী পুরুষ সমান উত্তরাধিকার বিষয়ে।
চতুর্থ মৌলিক প্রশ্ন হলো, শোষণ মুক্তির ইস্যুটি মুক্তিযুদ্ধের শীর্ষস্থানীয় আকাক্সক্ষা ছিল। বঙ্গবন্ধু বাকশাল করে শোষিত মানুষের মুক্তির একটি উপায় বের করতে চেয়েছিলেন। তিনি ওই উদ্যোগ নেয়ার জন্য সপরিবারে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। বিজয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এ দেশের বিকাশ চলছে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুরোপুরি বড়লোক কর্তৃক গরিব শোষণ ও ধনী গরিব বৈষম্য একেবারে বিলুপ্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। ধনবাদী রাষ্ট্র কাঠামো দুটো কৌশল প্রয়োগ করে বৈষম্য কমানোর পদক্ষেপ নেয়। একটি হলো ধনীর ওপর বেশি ট্যাক্স আরোপ এবং দ্বিতীয়টি হলো নানা ধরনের ভাতার (মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ইত্যাদি) মাধ্যমে বড়লোকের ট্যাক্সের টাকা গরিবদের মাঝে বিতরণ।
দুটো বিকল্পের প্রথমটি অনেকটা ব্যর্থ। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিমাণে অল্প হলেও ব্যক্তি সংখ্যার দিক থেকে ট্যাক্স বেশি দেয়। বড়লোকেরা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় বেশি। ধরুন কোন শিল্পপতি নিয়মানুযায়ী ১ কোটি টাকা ট্যাক্স দেয়ার কথা অথচ উনি দেন বড় জোর ৫ লাখ টাকা। আইনজীবী হওয়ায় ট্যাক্স সংক্রান্ত মামলাগুলো আমাকে ব্যথিত করে। কিছু সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়। অভিযোগ আনা হয় জ্ঞাত-আয়ের সঙ্গে সম্পদ অসঙ্গতিপূর্ণ। এদের প্রায় সবাই নিম্নস্তরের কর্মচারী। বড় আমলাদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদের জন্য কখনো মামলা হয় না।
এ দেশের ধনিক শ্রেণী মূলত জায়গা বাড়ি ফ্ল্যাট কিনেন বিদেশে। সুতরাং ট্যাক্স ওরা যা দেয় তা ওই সব বিদেশি রাষ্ট্রেই দেয়। দেশে এরা যেসব জায়গা জমি কিনে তা আবার ব্যাংকে বন্ধক দিয়ে ঋণ নেয় কোটি কোটি টাকা। এরপরও মামলা হয় যে সারাজীবন কষ্ট করে ১টা ফ্ল্যাট বা প্লট কিনেছে, তার বিরুদ্ধে বলে নথিতে টাকা দেখানো হয়নি। প্রশ্ন হলো এতো ঝামেলা সাধারণ মানুষ বুঝারও কথা নয়। জমি রেজিস্ট্রির সময় সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নেয়, তাহলে আয়কর নথিতে পূর্ব থেকে টাকা থাকতে হবে এর যৌক্তিকতা কি?
এরপরও এ রাষ্ট্রের মূল আর্থিক জোগানদাতা এ দেশের গরিব মানুষ। ভ্যাট এক ধরনের ট্যাক্স। যে যেখানে ভ্যাট দেয় তা বিক্রীত পণ্যের সঙ্গে যোগ করে দেয়। অর্থাৎ আড়ং থেকে আপনি ৫০০ টাকার লুঙ্গি কিনলে ৫০ টাকা অতিরিক্ত নিবে ভ্যাট হিসেবে। একজন রিকশাওয়ালা বউয়ের জন্য শাড়ি কিনলে ভ্যাট দিতেই হয়। আসলে বিজয়ের অন্যতম প্রধান আকাক্সক্ষা বৈষম্য বিলোপ দূরের কথা কমানোও সম্ভব হয়নি।
তবুও কথা থেকে যায়, দেশ স্বাধীন না হলে আমরা থাকতাম ইরাকের কুর্দী, মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনি, বার্মার রোহিঙ্গা বা পাকিস্তানের পাঠান বালুচদের চেয়েও মানবেতর জীবন সংগ্রামে। আরো অনেক কিছু হলে ভালো হতো; যা হয়েছে তাও কিন্তু কম নয়।
[লেখক : আইনজীবী]
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
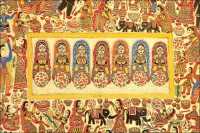
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?
-
সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব
-
প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক
-

বিকাশের পথকে পরিত্যাগ করা যাবে না
-
বর্ষা ও বৃক্ষরোপণ : সবুজ বিপ্লবের আহ্বান
-
প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষকের করণীয়
-
পারমাণবিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক ভণ্ডামির প্রতিচ্ছবি
-
পরিবেশের নীরব রক্ষক : শকুন সংরক্ষণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন
-
মশার উপদ্রব : জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা
-
ভুল স্বীকারে গ্লানি নেই
-
ভাঙনের বুকে টিকে থাকা স্বপ্ন
-
একটি সফর, একাধিক সংকেত : কে পেল কোন বার্তা?
-
দেশের কারা ব্যবস্থার বাস্তবতা
-
ইসলামী ব্যাংক একীভূতকরণ : আস্থা ফেরাতে সংস্কার, না দায়মুক্তির প্রহসন?
-
রম্যগদ্য : চাঁদাবাজি চলছে, চলবে







