উপ-সম্পাদকীয়
নীল আর্মস্ট্রংয়ের স্পেস স্যুট
শঙ্কর প্রসাদ দে
ওয়াশিংটনকে বিশে^র রাজধানী বললে বেশি বলা হয় না। আমেরিকান রাজনীতিকরা তেমনটাই মনে করেন। বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য বড় ৭১৩৬২ বর্গমাইলের ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম রাজ্য হিসেবে অঙ্গীভূত হয় ১৮৮৯ সালে। স্প্যানিশরা ১৮১৯ সালে এবং ১৮২৫ সালে রাশিয়া রাজ্যটির ওপর তাদের অধিকার ত্যাগ করে ব্রিটিশের কাছে। ব্রিটিশরা ১৮৭২ সালের সালিশি রোয়েদাদ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে স্বত্ব ত্যাগ করে।
১৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় পৌঁছে গেলাম নাসার বিজ্ঞান জাদুঘর ‘স্মিথসোনিয়ান এয়ার স্পেস অ্যান্ড মিউজিয়ামের’ প্রবেশদ্বারে। চিরকুমার ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জেমথ স্মিথসন ১৮২৯ সালে মৃত্যুর পূর্বে করা উইলে শর্ত দেন যে, ভাগ্নে হাঙ্গারফোর্ড নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি আমেরিকান সরকারের কাছে চলে যাবে জ্যোর্তিবিদ্যা ও জ্ঞান অন্বেষণে ব্যবহারের জন্য। স্মিথসনের উইলের প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্রিটিশ সরকার তার সমস্ত সম্পত্তি মার্কিন সরকারের একটি প্রতিনিধি দলের হাতে তুলে দেয়। অতঃপর মার্কিন সরকার একটি বিল পাস করে প্রতিষ্ঠা করে ‘স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট’। সোজাকথায় বিজ্ঞান ও গণিতকে কেন্দ্র করে এই ইন্সটিটিউট ৪৫টি অঙ্গরাজ্যে ২০০টিরও বেশি জাদুঘর ও গবেষণাকেন্দ্র পরিচালনা করে। ১.২৫ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করে মার্কিন সরকার।
১৮৪৬ সালের ১০ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত এই মহতী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ জাদুঘরটি হলো ওয়াশিংটনের নাসার স্মিথসোনিয়ান এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম। ঢুকতেই রিসেপশান কাউন্টারের পাশের স্ট্যান্ডে নীল আর্মস্ট্রংয়ের স্পেস স্যুট দেখে থমকে দাঁড়ালাম। এপোলো-১১ চন্দ্রাভিযানে এটি পড়েই তিনি আকাশের কপালে সাদা টিপ খ্যাত চাঁদে এঁকে দিয়েছিলেন মনুষ্য পদচিহ্ন। মানুষ দেখিয়ে দিল চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কোন দৈব শক্তি নয়। প্রাচীন সময় থেকে ভয়ার্ত মানুষ খামোকা এদের দেবতার আসনে বসিয়েছে। প্রতিনিয়ত শত সহ¯্র গ্রহ উপগ্রহ তারার জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে, পদার্থবিদ্যার নিজস্ব নিয়মে। স্পেস স্যুটটি কয়েক সেকেন্ড স্পর্শ করে বুঝলাম, এ যে মানব প্রজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন। বিস্ময়ে আপ্লুত হলাম এই ভেবে যে, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে এসব স্পেস স্যুট সাধারণ শার্ট প্যান্টে পরিণত হবে। শতবর্ষ পরে শত সহ¯্র মানুষ স্পেস শাটলে করে চাঁদে মহাকাশ স্টেশন বানাবে।
এলন মাক্স ঘোষণা দিয়েছেন, দ্বাবিংশ শতক হবে মঙ্গলে মনুষ্য বসতি গড়ার সোনালি সময়। বায়ুর চাপ খুবই কম, ওজন স্তর নেই, অতীতে পানি থাকলেও এখন তা মাটির নিচে, মেঘ নেই বলে বৃষ্টি হয় না। তাতে কি? এলেন মাক্সের সোজা কথা পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে মঙ্গলে মেঘ সৃষ্টি করা হবে। বৃষ্টি হবে। ওজন স্তর সৃষ্টি হবে। পানি দেখা পেলেই মঙ্গল হয়ে উঠবে মনুষ্য বসতির উপযোগী।
চমক আরো অপেক্ষা করছিল। জাদুঘরের নিচতলার প্রধান প্রদর্শনীটি হলো রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই প্রথম বিমানটি। ২৯ সেকেন্ড উড়েছিল ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সালে রাইট ভাইদ্বয় ডজন ডজনবার মনুষ্যবিহীন মসলিন কাপড়ের পাখার বিমান উড়িয়েছিলেন। এসব পরীক্ষামূলক উড়ানগুলোকে ঘুড়ির নাটাইয়ের মতো দড়িতে আটকিয়ে উড়ানো হয়েছিল। রাইট পরিবার ছিল সাইকেল ব্যবসায়ী। ঐতিহাসিক প্রথম ফ্লাইটির ইঞ্জিন ডিজাইন করা হয়েছিল কাঠের বক্সের ভিতর মটরের হুইলারের সাথে সাইকেলের চেইন ফিট করে। উইলবার ছোট ভাই অলভিরকে এতই ভালোবাসতেন যে উড়ানোর সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বলতেন।
শেষপর্যন্ত প্রথম ফ্লাইটে অলভির উড়তে পেরেছিলেন নর্থ কেরোলিনার বালুকাময় প্রান্তরে। তারপর ধপাস করে হলেন ভূ-পাতিত। উপস্থিত স্বল্প সংখ্যক দর্শক চিৎকার করে বিশ^বাসীকে জানিয়ে দিলেন সভ্যতার মহত্ত্বম আবিষ্কার। বিমান আজ এই গ্রহের দ্রুততম যান। রকেট আন্তগ্রহের সবচেয়ে দ্রুততম ব্রহ্মা- যান। দুই ভাইকে চমৎকার সঙ্গ দিয়েছিলেন তাদের দোকানের মেকানিক চার্লি টেলর। অপর তিন ভাই বিয়ে করে সাংসারিক হয়েছিলেন। বিমান আবিষ্কারের নেশায় উইলবার আর অরভিল থেকে গেলেন চিরকুমার। তাতে কি? প্রথম সকল বিমান ছুঁয়ে দেখে শ্রদ্ধা জানালাম দুই ভাইয়ের স্মৃতির প্রতি।
এরপর এলো স্বচক্ষে চাঁদকে অনুভব করা। মাঝারি একটি চন্দ্রপাথর ডান পাশের ডিসপ্লেতে আছে। বাম পাশে ৩টি কমান্ড মডিউল। প্রথমটি এপোলো-১১ এর ঐতিহাসিক কমান্ড মডিউলটি। এটি থেকে নীল আর্মস্ট্রং অনন্ত কাব্যিক রসের উৎস চাঁদে নেমেছিলেন। সাথে নেমেছিলেন বাজ অলড্রিন। মাইকেল কলিংস সার্বক্ষণিক চালু থাকা লুনার মডিউলে বসে উপভোগ করছিলেন মহাজাগতিক অভিযানের সার্থক দুরন্ত স্পর্শ।
এপোলো গ্রিক ও রোমান মিথ অনুযায়ী জ্ঞানের দেবতা। চন্দ্র মিশনের নাম এপোলো রাখার মধ্যে অতীতের ঐতিহ্য আছে। বর্তমানের মার্কিন দক্ষতা আছে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে। এপোলো-১ মিশন পরীক্ষা শুরুর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৩ নভোচারীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ব্যর্থতার স্মারকে পরিণত হয়। এপোলো-২, এপোলো-৩, এপোলো-৪, এপোলো-৫, এপোলো-৬ ছিল মূলত বিভিন্ন কোম্পানির নির্মিত চন্দ্রযানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এপোলো-৭ পরীক্ষায় স্ট্যাটার্ন মডেলের চন্দ্রযানের সফলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এপোলো-৮ এপোলো-৯ এপোলো-১০ দিয়ে আরো বহু দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৬ জুলাই ১৯৬৯ উৎক্ষেপণ করা হয় ৩ নভোচারীসহ এপোলো-১১। ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন প্রায় ২১ ঘণ্টা চাঁদে ঘুরে ফিরে কমান্ড মডিউলে অপেক্ষারত কলিংসয়ের সাথে মিলিত হন।
এপোলো-১১ এর সার্ভিস মডিউল ছিল সবচেয়ে পেছনের লম্বা অংশটি। পৃথিবীর গ্র্যাভিটি ছিন্ন করে পৌঁছে দিয়েছিল কক্ষপথে। এবার পাইলট কলিংস লুনার মডিউল অর্থাৎ সবচেয়ে সামনের অংশ দিয়ে (কমান্ড মডিউলসহ) পৌঁছে যান চন্দ্রপৃষ্ঠে। ২১ ঘণ্টার ভ্রমণ ও চাঁদের মাটিসহ আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন কমান্ড মডিউলে ঢুকে পড়ার সাথে সাথে লুনার মডিউল উড়াল দিল পৃথিবীর পথে। ২৪ জুলাই কমান্ড মডিউল আছড়ে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরে। ত্বরিত তোলা হলো কমান্ড মডিউল। বেরিয়ে এলেন কলাম্বিয়া স্পেস শাটলের ৩ নভোচারী। আদর করে চন্দ্রযানটির নাম রাখা হয়েছিল ‘ঈগল’। ৩ নভোচারীর বসার জায়গাটি এতোই ছোট যে, অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আর অনুভব করতে চাইলাম প্রায় উল্টো শায়নাসনে এরা ছিলেন দীর্ঘ ৮ দিন। জয় হোক নাসার। জয় হোক বিজ্ঞানের।
তৃতীয় তলায় মঙ্গল অভিযানের পরীক্ষাকালীন স্পেস ক্রাফটগুলো ডিসপ্লে করা আছে। মঙ্গলে পাঠানো পারসিভিয়ারেন্সের যে মডেলটি নাসা পরীক্ষা করেছিল সেটি দেখলে বুঝা যায়, এলেন মাস্কের স্পেস এক্স পারুক না পারুক, নাসা ঠিকই একদিন মঙ্গলে মনুষ্য পদচিহ্ন এঁকে দেবে। হয়তো সেদিন এ প্রজন্মের কেউ সাক্ষী হবো না। দোতলা এবং তৃতীয় তলার বিমান প্রযুক্তির জটিল প্রযুক্তিগত স্মারকগুলো না দেখলে বুঝা যাবে না, কেন বিমান এতো দামি জিনিস।
বিমান ইঞ্জিনগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে একটা কথাই মনে এলো- প্রযুক্তিতে পশ্চিমা বিশ^ এশিয়া আফ্রিকার হিন্দু মুসলিমের চেয়ে অন্তত ৫শ বছর এগিয়ে রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আফ্রিকার মানুষগুলো নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ব্যয় করছে লাখো কোটি মূল্যবান শ্রম ঘণ্টা। ঠিক একই সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত ইউরোপ আমেরিকা ব্যয় করছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির পেছনে। আমরা যতো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করি না কেন, বিমানে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার সময় ভাবছিলাম, এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব গ্রামীণ ঝুপড়ি চা দোকানের অলস মনুষ্য গালগল্পের বেশি কিছু নয়। পশ্চিমা বিশ^ বিজ্ঞানের দরজা আমাদের জন্য কখনই বন্ধ করেনি। আমরা দিনরাত ওদের গালি দেই। সেসব তোয়াক্কা না করে পশ্চিমা বিশ^ই আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপ দিয়ে পড়াতে নিয়ে যায়।
শুধু কি তাই? চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর প্রেসিডেন্ট নিক্সন নভোচারীদের বিশ^ভ্রমণে পাঠিয়েছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৯৬৯ নভোচারীরা সস্ত্রীক এসেছিলেন ঢাকায়। এতোদিন পর ভাবী এরপরও কি আমাদের বিজ্ঞান চেতনার সামান্যতম অগ্রগতি হয়েছে? বিজ্ঞানচেতনা দ্রুততর করা না গেল সামনের দিনগুলো নিমজ্জিত হবে আরো গভীর অন্ধকারে।
[লেখক : আইনজীবী, আপিল বিভাগ]
-
ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম
-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
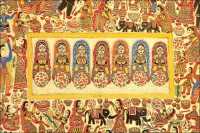
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?
-
সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব
-
প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক
-

বিকাশের পথকে পরিত্যাগ করা যাবে না
-
বর্ষা ও বৃক্ষরোপণ : সবুজ বিপ্লবের আহ্বান
-
প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষকের করণীয়
-
পারমাণবিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক ভণ্ডামির প্রতিচ্ছবি
-
পরিবেশের নীরব রক্ষক : শকুন সংরক্ষণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন
-
মশার উপদ্রব : জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা
-
ভুল স্বীকারে গ্লানি নেই
-
ভাঙনের বুকে টিকে থাকা স্বপ্ন
-
একটি সফর, একাধিক সংকেত : কে পেল কোন বার্তা?
-
দেশের কারা ব্যবস্থার বাস্তবতা
-
ইসলামী ব্যাংক একীভূতকরণ : আস্থা ফেরাতে সংস্কার, না দায়মুক্তির প্রহসন?
-
রম্যগদ্য : চাঁদাবাজি চলছে, চলবে







