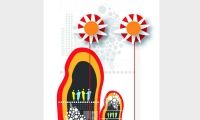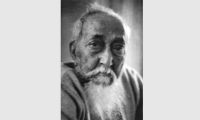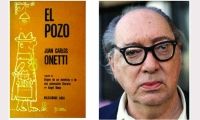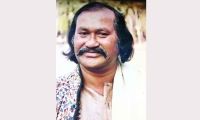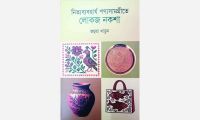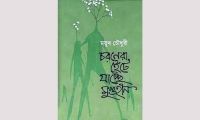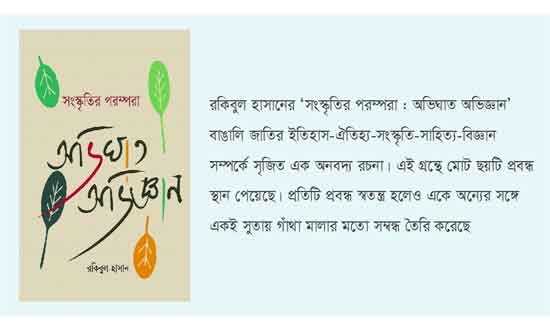
সংস্কৃতির পরম্পরা, অভিঘাত-অভিজ্ঞান ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণ
জান্নাতুল যূথী
বর্তমানকালে কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের জগতে যাঁদের সুদৃঢ় পদচারণা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ড. রকিবুল হাসান অন্যতম। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও মননে ধরা দিয়েছে বাঙালির আবহমান রূপ। আমরা জানি, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের কালো থাবা থেকে বহু সংগ্রাম-সংঘর্ষ ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বিনির্মাণে সক্ষম হয়। তবু এ জাতির ললাট রঞ্জিত হয়েছে পুনঃপুনঃ বেঈমানি ও রক্তাক্ত ইতিহাসের দোলাচলে।
রকিবুল হাসানের ‘সংস্কৃতির পরম্পরা : অভিঘাত অভিজ্ঞান’ বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে সৃজিত এক অনবদ্য রচনা। এই গ্রন্থে মোট ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র হলেও একে অন্যের সঙ্গে একই সুতায় গাঁথা মালার মতো সম্বন্ধ তৈরি করেছে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির সুবাস বা পরিপূর্ণতা সঠিকরূপে ধরা সম্ভব নয়।
আমাদের অজনা নয়, বাঙালিকে তাঁদের সংগ্রাম, যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও শক্তির মধ্যে দিয়েই চিহ্নিত করা যায়। এও জানি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সংগ্রামী ও বিপ্লবী জাতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর! এই জাতির সেসব ঐতিহ্য-কৃষ্টি ও সংগ্রাম এখানে তুলে ধরেছেন লেখক। গ্রন্থটি বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে, ‘ব্রিটিশ-ভারত থেকে বাংলাদেশ সংগ্রামে-স্বাধীনতা’; ‘বাংলা সাহিত্যচর্চা চর্যাপদ থেকে নজরুল’; ‘ভাষা-ধর্ম-ঐতিহ্য সংস্কৃতিসূত্রবন্দি’; ‘সংস্কৃতি ও সদাচার জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের ঐতিহ্য’; ‘বিজ্ঞানচর্চা বাঙালির উদ্ভাবন ও কৃতিত্ব’ এবং ‘বাঙালির বিপ্লব রক্ত-সোপানের কাব্য’। প্রতিটি প্রবন্ধের বাক্যে-বাক্যে মিশে আছে লেখকের দেশপ্রেম-চেতনা, ইতিহাসকে ফিরে দেখার প্রবল তাগিদ, বাংলা ভাষা ও জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আবেগ-অনুভূতি, বাঙালি বিপ্লবীদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও তাঁদের দুঃসাহসিক বিপ্লবী কর্মযজ্ঞের বর্ণনা।
‘ব্রিটিশ-ভারত থেকে বাংলাদেশ সংগ্রামে-স্বাধীনতা’ প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্য দিয়েই এখানে কী বিষয়ে আলোকপাত করা হবে, সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিক কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছেন। মূলত, ব্রিটিশ ভারত থেকে কীভাবে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সে কথাই এই প্রবন্ধের উপজীব্য। ভারত-বিভাগ বাঙালি জাতির জন্য এক চরমতম আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল। যার জের আজও বাঙালি জাতি বুঝতে সক্ষম! জাতীয়তাবোধের অভাবে সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয় এবং এই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমন; অতঃপর প্রায় দুশো বছরের শাসন-শোষণ-নিপীড়ন শেষে ব্রিটিশদের পতন ঘটে।
ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য এ সময় গড়ে ওঠে বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মোন্নতি সমিতি (১৮৯৭), হরিকুমার চক্রবর্তীর চব্বিশ পরগনার চিংড়িপোতা দলের মতো বেশ কিছু সংগঠন। যাদের লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তৈরি করে অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং বিপ্লব ঘটানো। রাসবিহারী বসু বিদেশি শক্তির সহয়তায় দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেন। সংঘবদ্ধ উপায়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করেন বাঘা যতীন। বাঘা যতীনের বৈপ্লবিক আদর্শকে ধারণ করে ১৯৩০ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হয়। এরপর বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ইংরেজদের উৎপীড়নে প্রতিবাদ করেন হাজং চাষীরা। ১৯০৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ পরবর্তীকালে সুভাষ বসু, মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতৃত্বে ভারতে অধিকার আদায়ের আন্দোলন চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখ-িত হয়। এর নেপথ্যে ধর্মীয় কারণ থাকলেও বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা। তবু থামেনি ষড়যন্ত্রের কালো থাবা! পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বৈষম্য করতো। এমনকি পাকিস্তানের শতকরা ৫৬.৪০ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও সেদিক থেকেও বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তান।
ভাষার দাবিতে উত্তাল পূর্ব পাকিস্তান একসময় স্বীকৃতি পায় এবং এর মধ্যে দিয়েই স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। প্রবন্ধে পাই, ‘‘পাকিস্তানের সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠেনি। বৈষম্যের অগ্নিশিখা সর্বক্ষেত্রে তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল-তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। পৃথিবীর মানচিত্রে রচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি রাষ্ট্রের।’’
‘বাংলা সাহিত্যচর্চা চর্যাপদ থেকে নজরুল’ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদসহ নজরুলের সাহিত্য রচনা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজারের বছরের অধিককালের পুরোনো। এই দীর্ঘ ইতিহাসের ভাষাগত নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: প্রচীন যুগ (৬৫০-১২০০); মধ্য যুগ (১২০১-১৮০০) এবং আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্প্রাচীন যুগকে ৬৫০ থেকে নির্ধারণ করলেও এই মতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ বেশ কয়েকজন ভাষাতত্ত্বিক। তাঁদের মতে, প্রাচীন যুগ (৯৫০-১২০০)। এ দুটি প্রধান মত ছাড়াও ভিন্ন মতের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। আবার মধ্যযুগের (১২০১-১৩৫০) এই দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে অন্ধকারযুগ হিসেবে চিহ্নিত। কারণ এ সময় বর্গিদের আক্রমণে বাংলায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। কিছু মতপার্থক্য থাকলেও প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নির্দশন যে চর্যাপদ সে বিষয়ে সবাই একমত। এবং এই গ্রন্থটি নেপালের রাজদরবারের রাজগ্রন্থগার থেকে ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ তথা প্রথম নিদর্শন বড়ু চ-ীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল ধর্মনির্ভর। এ সময় মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য প্রভৃতি রচিত হয়।
উনিশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ। এ সময় বাঙালি-প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ও কৃষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০)। এই কলেজে ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যের উন্মেষ ঘটে। বাংলায় সাময়িক পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্র গদ্যের ইতিহাসকে বিনির্মান ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) সার্থক উপন্যাস। তাঁরই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্য নির্মাণ করেন। মধুসূদন সার্থক মহাকাব্য, ট্রাজেডি নাটক, প্রহসন রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বলয়ের বাইরে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্নিঝলসানো কবিতা রচনা করেছেন। “বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের কৃতিত্ব অপরিসীম।”
‘ভাষা-ধর্ম-ঐতিহ্য সংস্কৃতিসূত্রবন্দি’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি যে জাতি সম্মান হারিয়ে ফেলে সে জাতির মধ্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশপ্রেম এবং মূল্যবোধ কিছুই থাকে না। বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালি জাতিকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই ইতিহাস আজ শুধু মলাটবদ্ধ বইয়ে সীমাবদ্ধ! বাঙালি জাতি তাঁর নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থেকে সরে এসেছে! সেই স্থান দখল করেছে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি! যা জাতির জন্য বড় হুমকি। পরিবাররথা ভেঙে গেছে, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে ঐতিহ্য ধুলোয় মিশে যাচ্ছে আর যদি অবক্ষয়ের এই ভয়াল থাবা চলতেই থাকে তবে ভয়াবহ এক অন্ধকার আমাদের গ্রাস করবে! এর থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য প্রাবন্ধিকের পরামর্শ হলো, শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।
“সংস্কৃতি ও সদাচার জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের ঐতিহ্য” প্রবন্ধে সংস্কৃতি ও সদাচারই যে জাতির আত্মপরিচয়কে নির্দেশ করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যে-কোনো জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক শিকড় উপড়ে ফেলতে পারলে সেই জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা সহজ। আর সংস্কৃতির সঠিক চর্চাই পারে মানুষকে সদাচারী করে তুলতে। আচার-আচরণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতিবান মানুষ তার দেশের প্রতি, আচরণ ও মানসিকতার প্রতি যতœবান। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন, “দৈনন্দিন আচার-আচরণ-চিন্তা-চেতনা-মানসিক গঠন ও পরিবর্তন এবং নৈতিকতাবোধ সংস্কৃতির সাথে যেমন জড়িত তেমনি একজন মানুষের স্বকীয় হয়ে উঠার পিছনে সদাচারের ভূমিকা অনন্য ও অনস্বীকার্য।”
‘বিজ্ঞানচর্চা বাঙালির উদ্ভাবন ও কৃতিত্ব’ এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালিদের অবদানকে তুলে ধরেছেন লেখক। জাতি হিসেবে বাঙালি নিজেদের অস্তিত্বকে মূল্যহীন মনে করলেও বিশ্বদরবারে বাঙালি জাতির ইতিহাস সুনাম ও গর্বের। বাঙালি বিজ্ঞানীদের এই অবদানকে তুলে ধরতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তেত্রিশ জন বাঙালি বিজ্ঞানীর কথা বলেছেন। যারা বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানের যাত্রাকে সমৃদ্ধ করতে মেধা-মননকে কাজে লাগিয়েছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতেন্দ্রনাথ বসু, ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. মাকসুদুল আলমের মতো জ্ঞানী-গুণীরা এই প্রবন্ধে স্থান করে নিয়েছেন। বাঙালি এই বিজ্ঞানীরা তাঁদের উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব দরবারে আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।
সবশেষে ‘বাঙালির বিপ্লব রক্ত-সোপানের কাব্য’ এই প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক এমন অসংখ্য বিপ্লবীর কথা তুলে ধরেছেন যাঁদের অদম্য সাহস ও বিদ্রোহ জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন। বিপ্লবীদের মনে ব্যাপক সাড়া জাগাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান রচনা করেন যা বিপ্লবীদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। স্বদেশী আন্দোলনে শুধু হিন্দুরাই নয় বরং মুসলমানদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ধীরে ধীরে বাঙালি জাতি এগিয়ে যায় ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বিপ্লবী বাঘা যতীন, বিনোদবালা দেবী, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী দীনেশ দাশ, বিনয় কৃষ্ণ বসু, মাস্টারদা সূর্যসেন, কল্পনা দত্ত, রমেশ আচার্য, মাখনলাল সেন, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুস্তফিজুর রহমান খান, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, সোমেন চন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের নাম উল্লেখযোগ্য।
ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এঁরা সশস্ত্র বিপ্লব বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের রক্তস্রোত আর আত্মবলিদানের ফলেই আজকের এই স্বাধীনতা। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন রেখেছেন, ‘এই স্বাধীনতা কি মহান এই সব বিপ্লবীদের প্রত্যাশিত ছিল? কোন কিছু না ভেবেই এর উত্তর বুদ্ধিবিবেকবোধ সম্পন্ন একজন সাধারণ নাগরিকও বলে দিতে পারেন-খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা তাঁদের প্রত্যাশিত ছিল না, আর বাংলাকে ভাগ এটা তো অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু রাজনীতির খেলা কত নিষ্ঠুর ও নির্মম হতে পারে ভারতভাগ তার বড় প্রমাণ।’
প্রাবন্ধিক রকিবুল হাসান প্রবন্ধগুলোতে ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য- বাঙালি বিজ্ঞানী, বিপ্লবীদের সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্য দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রবন্ধগ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-ভাষাপ্রেম আরো একবার পুনর্জীবন পেয়েছে। আমরা জানি, যেকোনো জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে হলে ভাষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। তেমনই বাঙালি জাতিকে ভালোভাবে বুঝলে হলে, জাতিগতভাবে উন্নত হতে হলে জাতির এমন ইতিহাস জানার বিকল্প নেই। পাশাপাশি সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষার চর্চা, ইতিহাসের শহীদ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা অবিশ্যম্ভাবী। ইতিহাস-ঐতিহ্য-ভাষা-সাহিত্য-বিপ্লব ও বিপ্লবী সম্পর্কে জানতে রকিবুল হাসানের ‘সংস্কৃতির পরম্পরা: অভিঘাত অভিজ্ঞান’ গ্রন্থটি অনবদ্য ভূমিকা রাখবে।