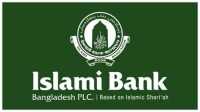মুদ্রাস্ফীতি : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়
ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত
বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি এখনও ৮ শতাংশের ওপরে অবস্থান করছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বোচ্চ, যেখানে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় তা নেমে এসেছে এক অঙ্কের নিচে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের আগস্টে দেশের সামগ্রিক (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.২৯ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৩ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত খাতে ৭.১ শতাংশ। খাদ্যশস্য, পেঁয়াজ, চাল, তেল ও ডিমের দাম স্থিতিশীল হলেও শাকসবজি, মাংস ও দুধজাত পণ্যের দাম উচ্চ থাকার কারণে সামগ্রিক সূচকে উল্লেখযোগ্য চাপ রয়েছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারের বাজার তদারকি ও খাদ্য মজুত বাড়ানোর উদ্যোগ কিছুটা ফল দিয়েছে, তবে কাঠামোগত ব্যয়বৃদ্ধি ও মুদ্রার অবমূল্যায়ন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে নীতিগত সুদহার অপরিবর্তিত রেখে মুদ্রাসরবরাহ সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— যাতে দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রকাশিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৭ শতাংশ, গত অর্থবছরে গড় বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১০ শতাংশে— যা অন্তত ২০১৩ সালের পর সর্বোচ্চ। একই সময়ে মালদ্বীপ ও পাকিস্তানে এই হার ৪.৫ শতাংশ, নেপালে ৪.১ শতাংশ এবং ভারত ও ভুটানে আরও কম।
এডিবি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি ৮ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে সেই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সেটিও হবে সর্বোচ্চ হার।
অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার পথে এগোচ্ছে। তবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো দেশে খাদ্য ও জ্বালানি খাতে মূল্যস্ফীতি এখনও বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে। বিপরীতে, ভারত ও শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে— কঠোর মুদ্রানীতি, কার্যকর বাজার তদারকি এবং উৎপাদন উৎসাহমূলক নীতি গ্রহণ করলে মূল্যস্ফীতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খাদ্য ও জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ব্যয়ই মূল চালক হিসেবে কাজ করছে। অপরদিকে, ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ও বাজার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করছে। শ্রীলঙ্কা ব্যয় সংকোচন ও কঠোর নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সফল হয়েছে।
বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও গত দুই বছরে একাধিকবার নীতিমালা কঠোর করেছে। ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১১ দফায় নীতিমূল্য হার বাড়িয়ে ১০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। তবুও কেন ফল আসছে না, এই প্রশ্নই এখন নীতি-নির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কঠোরতা দেখাতে দেরি করেছে। যদি সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া যেতো, তাহলে ফলাফল ভিন্ন হতো। এখন অনেকটা দেরিতে নেওয়া পদক্ষেপ বা ‘টু লিটন, টু লেট’ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুদ্রানীতির পাশাপাশি সরবরাহ-পক্ষের দুর্বলতাও বড় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ মূলত আমদানি-নির্ভর। ফলে টাকার অবমূল্যায়ন দাম বাড়াচ্ছে, যা মুদ্রানীতির প্রভাবকেও খর্ব করছে।”
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত টাকার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। এতে আমদানি-নির্ভর পণ্যের দাম বেড়ে গেছে বহুগুণ। ব্যাংকের সর্বশেষ নীতিমালা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টাকার অবমূল্যায়নের কারণে আমদানি ব্যয় বেড়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারে।” রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভয়াবহ বন্যায় সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়, যা খাদ্যপণ্যের দামকে আরও অস্থির করে তোলে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাজার থেকে ১.৭ বিলিয়ন ডলার কিনেছে, যার অর্থ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় মুদ্রা ছাপিয়ে। এভাবেই বাজারে অতিরিক্ত টাকার প্রবাহ তৈরি হচ্ছে।
গত এক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিনিয়োগ স্থবিরতাও মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। বাজারে পণ্যের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, টাকার মানও কমেছে। ফলে উৎপাদন ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যয় বেড়েছে,” বলেন তিনি। তার মতে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এলে সরবরাহ-পক্ষের বাধা দূর হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমতে পারে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইতোমধ্যেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছে— ‘‘টাকার অবমূল্যায়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রভাব ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও দাম বাড়াতে পারে। সরকারি কর্মচারীদের সম্ভাব্য বেতন বৃদ্ধি এবং নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের অতিরিক্ত ব্যয় মুদ্রাস্ফীতিকে আবারও চাঙা করে তুলতে পারে। তাই ২০২৬ সালেও স্বস্তি পাওয়া কঠিন হবে। দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।
পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০২৫ সালের আগস্টে বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ২.০৭ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক (আরবিআই) একাধিকবার জানিয়েছে, মূল্যস্ফীতিকে ৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার নিচে রাখতে তারা সফল। ভারতের খাদ্য খাতে মূল্যবৃদ্ধি সীমিত রাখায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে দুধ, গম ও শাকসবজির দাম তুলনামূলক কম থাকায় ভোক্তা-সূচক নেমে এসেছে।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, উৎপাদনশীল কৃষি নীতি, যথাযথ ভর্তুকি এবং ভোক্তা বাজারে দ্রুত সরবরাহের কারণে ভারত বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে স্থিতিশীল অর্থনীতিগুলোর একটি।
পাকিস্তানে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬ শতাংশ। গত দুই বছর ধরে দুই অঙ্কের ওপর ঘোরাঘুরি করার পর এটি একটি ইতিবাচক সংকেত। তবে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে, আমদানি পণ্যের মূল্য ও জ্বালানি সরবরাহে চাপ থাকায় সামনে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কর বৃদ্ধি— এই তিন কারণেই সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আগের মতো বাড়ছে না।
নেপালে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী— বার্ষিক মূল্যস্ফীতি প্রায় ৫.২ শতাংশ।
খাদ্য ও পোশাক খাতে দাম কিছুটা বেড়েছে, তবে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কমায় সামগ্রিক চাপ কমেছে। দেশটি ভারত ও চীন থেকে পণ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল, ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর মূল্যস্তর সরাসরি প্রভাব ফেলে। নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘দাম স্থিতিশীলতা’ বজায় রাখতে অর্থ সরবরাহ সীমিত করেছে।
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর শ্রীলঙ্কা এখন স্থিতিশীলতার পথে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে দেশটির বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ১.৫ শতাংশে। ২০২২ সালে যেখানে এই হার ছিল ৫০ শতাংশের বেশি, সেখানে এখন তা কার্যত একক অঙ্কে নেমে এসেছে। মুদ্রানীতি কঠোর করা, বাজেট ঘাটতি কমানো ও আন্তর্জাতিক ঋণ পুনর্গঠন— এই তিনটি পদক্ষেপের কারণে দেশটির অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভারসাম্যে ফিরছে।
ভুটানে সাম্প্রতিক মাসে মূল্যস্ফীতি গড়ে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। খাদ্য ও পরিবহন ব্যয় কিছুটা বাড়লেও সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থা দামকে সহনীয় রেখেছে। অপরদিকে, মালদ্বীপে পর্যটন খাতের পুনরুদ্ধারের পরও দাম তুলনামূলক স্থিতিশীল। ২০২৫ সালের মধ্যভাগে দেশটির মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ৩ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের নিচে।
-

বাজারে সেলসফোর্স এর ‘মিউলসফট এজেন্ট ফেব্রিক’
-

বাংলাদেশের বাজারে ভিভো’র নতুন স্মার্টফোন ভি৬০ লাইট উন্মোচন
-

সেপ্টেম্বরে তৈরি পোশাক রফতানি কমেছে ৫.৬৬ শতাংশ
-

আইএমএফের প্রতিনিধিদল আসছে এ মাসে, রাজস্ব আয়ের শর্ত পূরণ হয়নি.
-

ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
-

পোশাক শিল্পে ডিএফপি চালু করতে চায় বিজিএমইএ ও ডিবিপি
-

গার্ডিয়ান লাইফ ও ক্লিনিকলের চুক্তি
-

বিদেশে খরচ চালাতে বছরে ৩ হাজার ডলার পাঠাতে পারবে এসএমই প্রতিষ্ঠান
-

উত্তরা ফাইন্যান্সে মূলধন ঘাটতি ৭১২ কোটি টাকা
-

সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এলো ২.৬৮ বিলিয়ন ডলার
-

বাংলাদেশি কসমেটিকস শিল্পে বৈশ্বিক আগ্রহ
-

ট্রাম্পের প্রতিকৃতি সংবলিত ১ ডলারের মুদ্রা ছাড়ার পরিকল্পনা
-

জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিউট ও হাসপাতালে এবি ব্যাংকের কালেকশন বুথ উদ্বোধন
-

ভালো শেয়ারেও বাজার মন্দা, কাটছে না খরা
-

বাংলাদেশ-সৌদি আরব বিজনেস সামিট শুরু হচ্ছে সোমবার
-

স্বর্ণের দামে রেকর্ড, ভরি ১ লাখ ৯৭ হাজার
-

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করছে এমজেএল বাংলাদেশ
-

রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার জারি করলো বাংলাদেশ ব্যাংক
-

ভারত থেকে আমদানি বাড়াবে রাশিয়া, ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের ফল
-

মাকে ৩৬ কোটি টাকার শেয়ার উপহার দিলেন মির্জা আব্বাসের ছেলে
-

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান ও সাবেক ১৯ কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে দুদক
-

প্রাইম ব্যাংকের নারী গ্রাহকদের জন্য গো গার্লস ভ্রমণ প্যাকেজে ছাড়
-
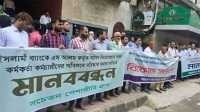
এবার ‘অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের’ চাকরি বাতিল চেয়ে ইসলামী ব্যাংকের সামনে মানববন্ধন
-

মুনাফা কমলেও রেকর্ড লভ্যাংশ দেবে ইবনে সিনা ফার্মা
-

ফাঁকি রোধে মাঠ পর্যায়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম বাড়াচ্ছে এনবিআর
-

কুমিল্লা ইপিজেডে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী বিদেশিরা, প্রয়োজন আরো প্লট
-

সোনালী ব্যাংকের ৯০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি
-

বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা কমেছে: এফএও