উপ-সম্পাদকীয়
ভারতের পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল
গৌতম রায়
ভারতে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। একমাত্র তেলেঙ্গানা বাদে বিরোধী দল কংগ্রেস কোথাও ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য মিজোরাম, সেখানে ভোটের ফলে বড় রকমের কোনো অদল-বদল ঘটেনি। আগামী বছরের (২৪) শুরুতেই ভারতের সাধারণ নির্বাচন। বলা যেতে পারে, এই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার ভোটের ফলাফলকে কেন্দ্র করে ভারতের আসন্ন লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গেল।
বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগে যেসব আগাম সমীক্ষা গত কয়েক দিন ধরে প্রচার মাধ্যমে উঠে আসছিল, সেগুলোর একটাও প্রকৃত ফলাফলের সঙ্গে মেলেনি। পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার এই ফলাফল আগামী লোকসভার ফলাফলের ইঙ্গিতবাহী- এমন কথা বলবার পক্ষে এটা অনেকটাই সময়ের আগে বলে দেওয়া কথার মতো যে হয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু একটা কথা বলতেই হয় যে, এই ফলাফল গোটা সাম্প্রদায়িক শিবিরকেই এখন থেকে একটা বাড়তি মনোবল দিতে শুরু করে দেবে।
মধ্যপ্রদেশে এর আগের বিধানসভা ভোটে মানুষের রায়ে জেতা কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি; কিন্তু দেখা গেল, সেসব অতীত ঘিরে সাধারণ মানুষ এখন আর বিশেষ ভাবছে না। তাহলে কি মধ্যপ্রদেশে জনগণের রায়কে অস্বীকার করে, পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে এমন কিছু সুশাসনের পরিচয় বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি দেখিয়েছে, যার জেরে সে রাজ্যের মানুষ আবার বিজেপিকে ফিরিয়ে আনলো?
এই প্রশ্নের ভিতরে ঢোকবার আগে যে কথাটা বলতে হয়, সেটি হলো- প্রশাসন-দল পরিচালনা এসব প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে রেখে গোটা দেশে গত লোকসভা ভোটের পর (১৯) বিজেপি সাফল্যের সঙ্গে যে কাজটা করেছে, সেটা হলো- গদি মিডিয়াকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আরএসএসকে তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আড়াল করতে পেরেছে। আর তার সুযোগ নিয়ে দেশজুড়ে আরএসএস তাদের সামাজিক কাজের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িক কর্মসূচিগুলোকে আশ্চর্যরকম ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হয়েছে। এই কর্মসূচির প্রথম এবং প্রধান লক্ষণই হলো সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। এই মেরুকরণের সুযোগ নিয়ে একদিকে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন। সেই বিভাজনকে ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত করা।
অপরদিকে মেরুকরণকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু ভোটের সংহতি ঘটিয়ে, সেই ভোটকে বিজেপির ঝুলিতে একত্রিত করা। এই হিন্দু ভোটের সংহতিকরণের প্রশ্নে আরএসএসের উগ্রতার ফসল জমা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির দিকে। আর বিরোধী কংগ্রেস, সেই মেরুকরণের উগ্রতার মোকাবিলায়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে বেছে নিয়েছে নরম হিন্দুত্ব। এই নরম হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতাকে, মৌলবাদী মানসিকতাকেই আরো পুষ্ট করেছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ হিন্দুধর্ম নয়, হিন্দুত্বের প্রশ্নে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে ‘নরম’ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ভরসা তো করতে পারেইনি। তারা বিশ্বাস করেছে বিজেপির ওপর। ভরসাও করেছে।
বিজেপির এই খানিকটা অপ্রত্যাশিত সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে ইতোমধ্যেই আরএসএসের ভূমিকাকে আড়াল করবার একটা প্রচন্ড রকমের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ। মধ্যপ্রদেশে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে বিজেপির জয়ের পিছনে সেখানকার সরকারের ডোল রাজনীতির সাফল্যকে তুলে ধরবার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ‘রেউড়ি’ সংস্কৃতি ঘিরে সাফল্য ঘরে তুলেছে বিজেপি- মধ্যপ্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা একাংশের সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে; কিন্তু মধ্যপ্রদেশের এই ‘রেউড়ি’ জনগোষ্ঠীকে ঘিরে সেই রাজ্য এবং ছত্তিশগড়ে হিন্দুত্ববাদীদের যে কর্মকান্ড, তার গোটা পরিকল্পনা এবং কার্যপদ্ধতিই যে আরএসএস দ্বারা পরিচালিত- সেই কথাটা কিন্তু উঠে আসছে না।
‘রেউড়ি’ জনগোষ্ঠী হলো সূর্যবংশোদ্ভূত এবং এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দশরথনন্দন রামের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে- এই মিথের ব্যবহার ঘটিয়ে মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়ে নিবিড় সামাজিক প্রযুক্তি চালিয়েছে আর এস এসের শাখা সংগঠন ‘বনবাসী কল্যাণ আশ্রম’। এই সামাজিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে সম্বল করে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের জমিতে তথাকথিত রামমন্দির তৈরির বিষয়টি।
আপাতভাবে অনেকেরই মনে হতে পারে আগামী ২০২৪ সালের শুরুতেই ওই রামমন্দির উদ্বোধন ঘিরে হিন্দুত্ববাদীদের যে তোড়জোর তা গোবলয়েই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মধ্যভারতে এই মন্দির উদ্বোধন ঘিরে রেউড়ি সংস্কৃতির যে শ্যভিনিজম অত্যন্ত নীরবে অথচ প্রক্ষিপ্ত কৌশলে আরএসএস করে চলেছে; তা নিয়ে সাধারণ মানুষ, কংগ্রেস দল, এমনকি জাতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থিসহ গোটা বিরোধী শিবির কতটা ওয়াকিবহাল থেকেছেন? সচেতন থেকেছেন?
সংবাদমাধ্যম ভারতের সদ্য সমাপ্ত পাঁচটি বিধানসভার ভোটে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, ডোল রাজনীতি (মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের, মমতার আদলে ‘লাডলি বহেনা’) এসব নিয়ে অনেক কথা লিখেছে। সুনীল কানুগোলু, কংগ্রেসের ভোট কুশলী, তাকে ঘিরেও প্রচারের শেষ ছিল না। কিন্তু একবারও কি ‘রেউড়ি’ সংস্কৃতি ঘিরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের কিছু কিছু জায়গাতে সঙ্ঘের নীরব কার্যকলাপ- সে সম্পর্কে একটিও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে?
যে রাজস্থানের কয়েকটি জায়গাতে সিপিআইর (এম) বেশ প্রভাব ছিল, সেসব অঞ্চলে কি সঙ্ঘের সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাল্টা কোনো সামাজিক প্রযুক্তির পথে হেঁটেছে ওই দলটি? শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষ্যে সিপিআইর (এম) যে কর্মসূচি, আদর্শগত অবস্থান, সে সবগুলোকে বজায় রেখেও সঙ্ঘের যে সামাজিক প্রযুক্তি, তার মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী সামাজিক সংস্কৃতির প্রয়োগ না ঘটালে জাতীয় স্তরে বা বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি আর তাদের দোসর, প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা করে নির্বাচনী সংগ্রামে সাফল্য আনা সম্ভবপর নয়। এই বাস্তবতার জায়গাতে সীতারাম ইয়েচুরি, মহ. সেলিমের মত সিপিআই (এম) নেতাদের কার্যক্রম দেখে মনে হয় না, তাদের এতটুকু দ্বিধা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওই দলের রাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল কে ঘিরে। তারা কি এই বাস্তবতাকে বুঝছেন? বুঝলে কেবলমাত্র মোদিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক বাণ না শানিয়ে, গুজরাট গণহত্যার নায়ক মোদিকে যারা ‘ব্রান্ডিং’ করেছে, সেই আরএসএসের সামাজিক প্রযুক্তি ঘিরে তারা অনেক বেশি সচেতন হতেন।
কনভেনশনাল পথে আর এস এসের মত ফ্যাসিবাদী শক্তি নিয়ন্ত্রিত বিজেপিকে বামপন্থীরা রাজনৈতিক ভাবে কতখানি মোকাবিলা করতে পারবে- গত প্রায় দশ বছরের অভিজ্ঞতায় এই প্রশ্নটা উঠে আসছে। ভারতের মত বহুত্ববাদী দেশ, যেখানে বহুত্ববাদকে গিলে খাওয়াই হলো ফ্যাসিস্ট আরএসএস-বিজেপির লক্ষ্য, সেখানে নিজেদের বস্তুবাদী রাজনৈতিক দর্শনকে অক্ষুণ্ন রেখেই সমসাময়ীকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, সাযুজ্য বজায় রেখে রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে সমস্ত ধরনের ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তিকে ঠেকাতে।
গোটা অবিজেপি শিবিরকেই সদ্যসমাপ্ত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের সম্পূর্ণ কার্যক্রমের নিরিখে বুঝতে হবে আরএসএস কৌশলগত প্রক্ষিপ্ততাকে বজায় রেখে কি ধরনের সামাজিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির অনুকূলে ভোটারদের প্রভাবিত করে। মধ্যপ্রদেশ বা ছত্তিশগড়ে সঙ্ঘ যে কৌশলে তাদের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরিচালিত করে, মূল লক্ষ্য এক রেখে, সেই কৌশলই তারা কিন্তু রাজস্থানে প্রয়োগ করেনি। প্রতিটি জায়গার আঞ্চলিক বিন্যাসই হলো সঙ্ঘের সামাজিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশলের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য।
বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগে যেসব আগাম সমীক্ষা গত কয়েক দিন ধরে প্রচার মাধ্যমে উঠে আসছিল, সেগুলোর একটাও প্রকৃত ফলাফলের সঙ্গে মেলেনি
সঙ্ঘের এই বৈশিষ্ট্যই হলো সদ্য সমাপ্ত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। মোদি ব্রান্ডিং শহরে প্রভাব কিছুটা ফেললেও মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বা রাজস্থানের গ্রামাঞ্চল, যেখানে ধর্ম-জাতপাত-অন্ধ কুসংস্কার, প্রথাগত শিক্ষার অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্য ঘিরে চরম অরাজকতা- এসব জায়গাতে কোনো রাজনৈতিক নেতার ব্রান্ডিংয়ের যে দিন নেহরু- ইন্দিরা জামানাতে ছিল, তা এখন ইতিহাস। বস্তুত ফেসভ্যালুনির্ভর ভোটের যে রেওয়াজটা রাজীব গান্ধী জীবিত থাকাকালীনও কিছুটা বজায় ছিল, সেটা এখন আর আদৌ নেই।
এই না থাকাটা ভারতের গদি মিডিয়া খুব ভালোভাবেই জানে। সেটা জেনেই তারা মোদির ফেসভ্যালু নির্মাণের চেষ্টা শুরু করেছিল। সেই চেষ্টা এখন ও ভারতের গদি মিডিয়া বজায় রেখেছে। এটা বজায় রাখবার উদ্দেশ্য হলো, বিজেপিকে জেতাতে আরএসএসের যে ভূমিকা এবং অবদান, তার সবটাই লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা। নিজেদের অরাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন বলে সঙ্ঘ যে দাবি করে, সেই দাবিকে এভাবেই সিলমোহর দিতে চায় গদি মিডিয়া। এই সিলমোহর দেওয়ার পিছনেও সঙ্ঘের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই থাকে সব থেকে বেশি কার্যকরী। সেই উদ্দেশ্যটা হলো- নিজেদের অরাজনৈতিক, সামাজিক তকমার ভিতর দিয়ে যেন, আরো বেশি বেশি করে রাজনৈতিক কার্যক্রম করে যেতে পারে বিজেপি।
বিজেপির সাফল্যের পিছনে আর এস এসের অবদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই কি কংগ্রেস দল নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে সোনিয়ার নরম হিন্দুত্বের পথে হাঁটছে? বিজেপির বাড়-বাড়ন্তের পর বহুবার কংগ্রেস দেখেছে, নরম সাম্প্রদায়িকতার পথে কোনো ভোট রাজনীতির সাফল্য তাদের আসছে না। বরং মুসলিম ভোট তারা হারাচ্ছে। ওয়াইসির মতো ভারতের সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক শিবিরের দিকে ভারতের সংখ্যালঘুদের একটা অংশ নিজেদের অস্তিত্বের সংকট থেকে ঝুঁকছে। এই প্রবণতা তীব্র হলে তা আদৌ ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক হবে না।
এমন একটা সময়ে যে বিচক্ষণতার অভাব, অপরিপক্বতা কংগ্রেসের নীতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে- তা কেবল উদ্বেগজনকই নয়, যথেষ্ট হতাশাদায়কও। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক প্রবণতাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে গেলে হাঁটতে হবে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পথে। আর এই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে সব থেকে আগে প্রয়োজন সংখ্যাগুরুদের দায়িত্ববোধের উদ্রেক সংখ্যালঘুদের জন্য। সংখ্যালঘুকে আধিপত্যবাদী সংখ্যাগুরুর আধিপত্যের মানসিকতা থেকে বের করে আনতে গেলে সংখ্যালঘুর স্বাধিকারের প্রশ্নে যে লড়াই প্রয়োজন, ভারতে অবিজেপি দলগুলো সেটা আদৌ কখনো করছে না।
[লেখক : ভারতীয় ইতিহাসবিদ]
-
ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব
-
কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে
-
জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি
-
প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি
-
দেশটা কারো বাপের নয়!
-
বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা
-
আর কত ধর্ষণের খবর শুনতে হবে?
-
সংস্কারের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতার রাজনীতি
-
মধুমাসের স্মৃতি ও দেশীয় ফলের রসাল সমারোহ
-
মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
-
লিঙ্গের রাজনীতি বা বিবাদ নয়, চাই মানবিকতার নিবিড় বন্ধন
-
বাজেট : বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
-
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পারমাণবিক আলোচনার স্থবিরতা
-
রম্যগদ্য: “বাঙালি আমরা, নহি তো মেষ...”
-
সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল
-
শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়
-
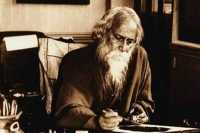
ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা
-
ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা
-
দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব
-
অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য
-
রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?
-
বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন
-
তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত
-
কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা
-
‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
-
ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান
-
সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
-
কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম







