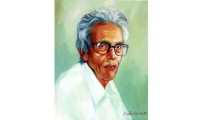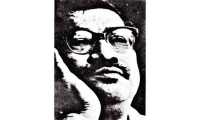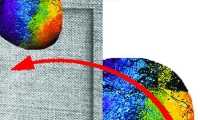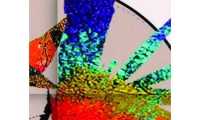সংবাদ থাকুক সংবাদ-এর মতোই
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
‘সংবাদ’ আর আমি সমান বয়সী, এজন্য পত্রিকাটির সঙ্গে আমার একটা একাত্মবোধ আছে। আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, যদিও এর সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে ষাটের দশকে, যখন আমি ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ে পড়তে আসি। অনেক দিন পর, বাংলাদেশ ইন্টারনেট যুগে প্রবেশ করলে, ‘সংবাদ’-এর আর্কাইভস থেকে পুরনো কোনো লেখা বা ছবি কেউ অন্তর্জালে ছড়িয়ে দিলে, ‘সংবাদ’-এর কোনো বিশেষ সংখ্যায় এর পুরনো সংখ্যাগুলি নিয়ে কেউ কিছু লিখলে, কোনো ইতিহাসবিদ অথবা পত্রিকাটির গুণগাহী কারো গবেষণায়, ‘সংবাদ’-এর পাঠক অথবা লেখকদের স্মৃতিচারণে পঞ্চাশ দশকে এর পথচলার যে ছবিটা দেখতে পাই, তাতে বুঝতে পারি, সমকালকে ধারণ করতে, এর নানা সমস্যা, সম্ভাবনা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে, যেসব আদর্শ-উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করছিল সেগুলিকে দৃষ্টির কেন্দ্রে স্থান দিতে কাগজটির যে আন্তরিকতা আর দক্ষতা ছিল, সেজন্য একদিকে যেমন এটি জনপ্রিয় ছিল, অন্যদিকে রুচিশীল, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধে বিশ^াসী পাঠকরা একে নিজের বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অন্যান্য দুয়েক সংবাদপত্রের সঙ্গে আমি প্রায় প্রতিদিন কাগজটি পড়তাম। এবং দেখতাম, প্রতিদিন চোখের সামনে আমি যা দেখছি, তারই প্রতিফলন ঘটছে এর সংবাদ পরিবেশনায়। ষাটের দশকে খুব বেশি দৈনিক ঢাকা থেকে বেরুতো না, কিন্তু সমাজে তাদের একটা বড় অবস্থান ছিল। এর প্রধান কারণ খবরের অন্য যে বিকল্প ছিল- বেতার, ও পরে টেলিভিশন- সেগুলির খবর কেউ বিশ^াস করত না। একদিন, অথবা দুইদিন পুরনো হলেও সংবাদপত্রই ছিল একমাত্র বিশ^স্ত মাধ্যম। পত্রিকাগুলির উপসম্পাদকীয়তে থাকত নানা বিশ্লেষণ ও মতের প্রতিফলন। সরকারের সেন্সর-উন্মুখ কর্তা আর গোয়েন্দাদের টেনে দেয়া লাল রেখার ভেতরে থেকেও তারা নানা কৌশলে, ঈঙ্গিতে যে কথাগুলি লিখতেন, স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে সেগুলি ছিল ‘চিন্তার জন্য খাদ্য’। সময়টা সত্যিকার অর্থেই ছিল সংবাদপত্রের, তেজস্বী সম্পাদক, নিবেদিত সংবাদকর্মী- ফটো সাংবাদিকের। সংবাদ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল। আমি যে কারণে কাগজটি পড়তাম, তা ছিল প্রধানত এর সংবাদ প্রকাশের বস্তুনিষ্ঠতা, গ্রাম বাংলার খবরকে প্রাধান্য দেয়া, এবং তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমকালীন রাজনীতিকে দেখার জন্য।
ষাটের দশকে বাংলাদেশ উত্তপ্ত ছিল রাজনীতি নিয়ে। ষাটের মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফার ঘোষণা থেকে নিয়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলন এবং একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটে গেল তার ঘনিষ্ঠ প্রতিফলন ‘সংবাদ’-এর পাতায়। ‘সংবাদ’ ছিল বামধারায় সম্পৃক্ত সংবাদপত্র। এ কারণে পত্রিকাটি তরুণদের কাছেও জনপ্রিয় হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে যেভাবে মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছিল, তার সব খবর থাকত ‘সংবাদ’-এর প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। আমার মনে আছে আমার দু’এক বন্ধু নিউমার্কেটের কাছে একটা খবরের কাগজের স্টল থেকে সকাল বেলাতেই ‘সংবাদ’ কিনে হলে ক্যান্টিনে আসত। তাদের থেকে অনেক সময় কাগজটা নিয়ে আমিও পড়তাম। পত্র পত্রিকার সংবাদকর্মীরা ঊনসত্তরের গণআন্দোলন শুরু হওয়ার পর মধুর ক্যান্টিনকেই প্রেস ক্লাব বানিয়ে ফেলেন। তখন তো ব্রেকিং নিউজের প্রচলন ছিল না- ব্রেকিং নিউজ কথাটাই আমি শুনেছি অনেক পরে- কিন্তু মধুর ক্যান্টিনে আমরা যেতাম ব্রেকিং নিউজের আশায়। আমাদের মতো ছোট আরেকদল মানুষও ওখানে থাকতো, যাদের আমরা টিকটিকি বলতাম। গোয়েন্দা বিভাগের এরকম দু’এক জনের সংগে সাংবাদিকরা খাতির জমিয়ে অনেক আগাম তথ্য আদায় করে নিতেন। তাই হয়তো ‘সংবাদ’-এ মাঝেমধ্যে যা আভাস দেয়া হতো, বাস্তবে তাই ঘটত।
ষাটের দশকে আমাকে প্রভাবিত, উদ্দীপ্ত এবং আশাবাদী করত যেসব ঘটনা, ‘সংবাদ’-এর পাতাতে তার প্রতিফলন দেখতাম। ‘সংবাদ’-এর সঙ্গে আমার সমান্তরাল যাত্রা এ কারণে আমার কাছে অর্থবহ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় পড়ে দেখতাম, আমার চিন্তার সঙ্গে এগুলোতে প্রকাশিত মতামত বেশ মিলে যেত। এই মিলটা স্বাধীনতার পরও বজায় রইল। আমি ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেই ১৯৭৪ সালে। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমি দু’জন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই, যাদের কারণে সংবাদের পাঠকপ্রিয়তা নিশ্চিত হয়েছিল। এদের একজন সন্তোষ গুপ্ত, অন্যজন মোনাজাত উদ্দিন। প্রথমজন ছিলেন সংস্কৃতবান বিদগ্ধজন। তাঁর পড়াশোনার পরিধি ছির ব্যাপক। মার্ক্সবাদ নিয়ে তার গভীর কিছু অনুধাবন ছিল- তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ হতো, বুঝতাম এসব অনুধাবন কতভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। তাঁর লেখা উপসম্পাদকীয়গুলি ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তা জাগানিয়া। তাঁর তুলনায় মোনাজাত উদ্দিন ছিলেন মাটিতে সমর্পিত, গ্রামজীবনের প্রতিদিনের চালচিত্রের একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক। গ্রামবাংলাকে- বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের, মঙ্গাপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের ভুগোলটাকে- তিনি জানতেন তার হাতের তালুর মতো। তথাকথিত মফস্বলের চাকচিক্যহীন, অভাবক্লিষ্ট, নানা সমস্যায় জর্জরিত জীবনে তিনি অনুসন্ধানী আলো ফেলতেন, এবং চমৎকার বর্ণনায় তাঁর নানা অভিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব তথ্য ও সত্যগুলি সংবাদ-এর ‘মফস্বল’ পাতায় পরিবেশন করতেন। মোনাজাত উদ্দিনের এই নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং সততার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে ‘চারণ সাংবাদিক’ হিসেবে অভিধা দিয়েছিলেন সাধারণ পাঠক থেকে নিয়ে সহযোগী সাংবাদিকরা। তিনিই হয়েতো বাংলাদেশের প্রথম ও এবং এ পর্যন্ত শেষ চারণ সাংবাদিক। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মোনাজাত উদ্দিন অকালে পরলোকবাসী হলেন, কিন্তু তাঁকে আমি এখনও স্মরণ করি সাংবাদিকতায় একটি উজ্জ্বল ধারা সৃষ্টি করার জন্য।
১৯৭৬ সাল থেকে নিয়ে টানা পাঁচ বছর উচ্চশিক্ষা নেয়ার জন্য আমি দেশের বাইরে ছিলাম। দেশে ফিরলে আমার ঠিকানা হলো বিশ^বিদ্যালয়ের অদূরেই, এবং ‘সংবাদ’-এর গ্রাহক হিসেবে আমি নাম লিখলাম। একই সঙ্গে এর পাঠক থেকে লেখকের অবস্থানে নিজেকে দেখতে পেলাম। ‘সংবাদ’ তখন বিখ্যাত, অনেক কিছুর সঙ্গে, এর সাহিত্য সাময়িকীর জন্য, এবং এই সাময়িকীর সম্পাদক, আবুল হাসনাত, ছিলেন সংবাদ-এর জনপ্রিয়তার পেছনে এক নীরব শক্তির যোগানদার। একসময় ছাত্র ইউনিয়ন, পরে কম্যুনিস্ট পার্টির নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, উঁচু দরের সাহিত্যরুচি, প্রজ্ঞা আর ধৈর্যের অধিকারী আবুল হাসনাত- যাকে প্রথম পরিচয় থেকেই আমি হাসনাত ভাই বলে সম্বোধন করতাম- ছিলেন ধীরস্থির, এবং বিনয়ী, যদিও সম্পাদক হিসেবে আপোসহীন। বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পাদকের মধ্যে অতি উন্নত বিচারবোধ আর পেশাদার মনোভাবাপন্ন যে ক’জন আছেন, তাঁদের মধ্যে হাসনাত ভাই ছিলেন একজন। তিনি যখন একতা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, তখন থেকেই আমাকে লিখতে অনুরোধ করতেন। একতায় আমি দু’তিনটি লেখা লিখেছি, একটি শিল্পী কামরুল হাসানকে নিয়ে, যা পড়ে তিনি আমাকে তাঁর একটি রেখাচিত্র উপহার দিয়েছিলেন। হাসনাত ভাই আমাকে দিয়ে মাঝে মধ্যে তাঁর সাময়িকীর জন্য লেখা আদায় করে নিতেন। ‘সংবাদ’-এর সাহিত্য সাময়িকীতে লেখা ছাপানোটা তখন ছিল তরুণ লেখকদের জন্য একটা স্বপ্ন। আমি লিখতাম। সাময়িকীতে লিখতেন সৈয়দ শামসুল হকও। হাসনাত ভাই কীভাবে জানি সৈয়দ হককে রাজি করালেন, একটা নিয়মিত কলাম লিখতে, তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ‘হৃৎকলমের টানে’। একসময় আমাকেও বিশ^সাহিত্য নিয়ে একটা কলাম লেখার অনুরোধ করলেন হাসনাত ভাই। আমি শুরু করলাম ‘অলস দিনের হাওয়া’। গুগল-ইন্টারনেটের যুগের আগে তথ্য পাওয়া যেত একমাত্র বইতে- নিজের বই আর লাইব্রেরিতে। ওই পাক্ষিক কলামটি যত না আমাকে কলম হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছে, তার থেকে বেশি করেছে পড়তে। যতদিন এই কলাম লেখা চলল, ততদিন চলল আমার পড়াশোনা- যেন আরেকটা পিএইচডি ডিগ্রি নিচ্ছি, সেরকম মনে হতো নিজের কাছে। আমার ত্রিশ-চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা ও পড়ায় এভাবে সময় দিতে আমাকে বাধ্য করার জন্য হাসনাত ভাই আর ‘সংবাদ’-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
‘সংবাদ’-এর জনপ্রিয়তার আরো কারণ ছিল- একটি তো এর দীর্ঘদিনের পাঠক মাত্রই শুরুতেই বলবেন- এর উপসম্পাদকীয়গুলি। যেদিন আমার শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ‘গাছপাথর’ ছদ্মনামে ‘সময় বহিয়া যায়’ শীর্ষক উপসম্পাদকীয় বা কলামটি লিখতে শুরু করলেন পত্রিকাটির কাটতি তার পর থেকে অনেকটাই বেড়ে গেল। তাঁর কলামটি ছিল, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা এবং পুঁজির প্রভাবে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং উগ্রতার প্রসার- এসব বিষয় নিয়ে। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্তি এবং বস্তুনিষ্ঠ বিচারের মাপকাঠিতে উঁচুমানের, ভাষা ছিল মেদহীন এবং শাণিত। তাঁর বিশ^াস ছিল বাম-আদর্শে, যাতে শ্রমিক-কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের পূর্ণ অধিকার থাকে সর্বাগ্রে, তাঁর আশা ছিল তারুণ্যের জাগরণে, শ্রেণি বিপ্লবে, তবে সেই বিপ্লব শোষিত মানুষের একত্র হওয়ার মধ্য দিয়ে, সহিংস নয়। বলাবাহুল্য তিন-সাড়ে তিন দশক পরও তিনি নিশ্চয় দেখছেন, গরিব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা তো হয়ইনি, বরং যেটুকু ছিল- যেমন নিজের একটা কুঁড়েঘর, এক টুকরা জমি- সেসবও চলে গেছে। ‘সময় বহিয়া যায়’ মাঝে মধ্যে সমস্যার প্রভাব নিয়ে কথা বলেছে, উৎস নিয়েও। উৎস হচ্ছে শিক্ষার দীন অবস্থা, পুঁজির শাসন, সংষ্কৃতির বিপন্নতা। প্রভাবের একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অভিভাসন, গ্রামের মানুষের শহরে এসে ভিড় করা। সমস্যার আরো গভীরে আছে আমাদের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ও রাজনীতিবিদদের নৈতিক দেউলিয়াত্ব- এসব নিয়েও কলামটিতে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনেক লিখেছেন। সুফল মিলত যদি সমাজ শিক্ষিত ও বিবেকবান হতো। এর কোনোটাই হয়নি, যদিও একাডেমিক ডিগ্রিধারী এবং ধনবান মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।
‘সংবাদ’-এ কলাম লিখতেন সন্তোষ গুপ্ত, একসময় লিখতে শুরু করেন মনিরুজ্জামান (যিনি অনেক পরে এর সম্পাদক হয়েছিলেন) এবং সোহরাব হাসান (যিনি প্রথম আলো ছেড়ে এখন একটি অনলাইনে কর্মরত)। এ দু’জনের কলামের আমি ছিলাম একনিষ্ঠ পাঠক। এই দু’জনেরই লেখনি ছিল ক্ষুরধার, যুক্তি ছিল অকাট্য। তারাও সমাজ, রাজনীতি- এসব নানা বিষয়ে লিখতেন। তাঁদের চিন্তাভাবনায় সচেতন পাঠকের চিন্তার প্রতিফলন ছিল, তবে আরো বেশি যা ছিল, তা ছিল স্পষ্টবাদিতা।
‘সংবাদ’-এর কিছু কিছু অপূর্ণতা ছিল- যেমন খেলাধুলা নিয়ে এর তেমন কোনো আয়োজন থাকত না- এর ক্রীড়া সাংবাদিকতা ছিল গতানুগতিক মানের। অন্য অনেক পত্রিকায় যখন ফ্যাশন বড় জায়গা করে নিচ্ছে, ‘সংবাদ’ ছিল এ ব্যাপারে উদাসীন। শিক্ষা নিয়ে এখন অনেক কাগজ যা করে- নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি সারতে সাহায্য করে, অনেক সময় ‘মডেল উত্তর’ লিখে দেয়- এসব সংবাদ কখনও করেনি। নারীদের নিয়ে আলাদা পাতা করার কথা ভাবেনি, যেহেতু নারীরা আছেন জনসংখ্যার অর্ধেক জুড়ে, তাদের সেই অর্ধেক জায়গাই প্রাপ্য। ‘সংবাদ’ সংস্কৃতিকে বরাবর প্রাধান্য দিয়েছে, যেহেতু তাতে আছে আমাদের জেগে ওঠার শক্তি।
সংবাদ ‘রঙিন’ হয়েছে- তাও সীমিত পরিসরে, যেখানে অনেক পত্রিকা সাদাকালো যুগকে পেছনে ফেলে রঙিন যুগে ঢুকে পড়েছে। এর কারণ এর বিজ্ঞাপনের ঘাটতি। ‘সংবাদ’ এখনও সংবাদ আছে, যেহেতু এটি কর্পোরেট সংষ্কৃতির অধীনে চলে যায়নি। এজন্য এখনও পত্রিকাটি তার নিজস্বতা, দায়-দায়িত্ব এবং পাঠকের প্রতি কর্তব্যবোধ ধরে রেখেছে।
আমি আশা করি ‘সংবাদ’ মধ্যসত্তরের বয়সের ভার অনুভব করবে না, যেমন আমি করছি, ঝিমিয়ে পড়বে না। বরং পশ্চিমের কোনো কোনো সংবাদপত্রের মতো একশ’ পেরিয়ে দু’শোর দিকে যাত্রা করবে, দু’শোর দিকে, কিন্তু এর দৃষ্টি ধূসর হবে না, তীক্ষè এবং অন্তর্দর্শী থাকবে। ‘সংবাদ’ যেন থাকে ‘সংবাদ’ হয়েই।