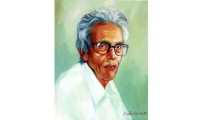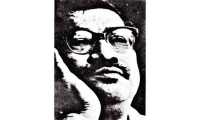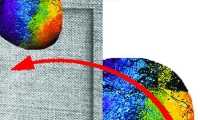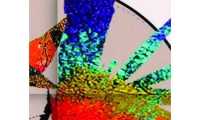গণতন্ত্রের জন্যে অপরিহার্য মুক্ত ভাবনার সুরক্ষা
মুজতবা আহমেদ মুরশেদ
গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই, সংগ্রাম এ দেশে বহু বছর ধরে। কিন্তু গণতন্ত্রে কী এই চাওয়া? গণতন্ত্র শুধুমাত্র কী বাক স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ? নিশ্চয়ই তা নয়। এর মূল ভিত্তি হলো জনগণের চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র গঠনে তাদের অংশগ্রহণের অবারিত সুযোগ। গণতন্ত্রের ধারণা একদিকে জনতার জন্যে ক্ষমতার প্রাপ্তি এবং অন্যদিকে দমন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
বাক স্বাধীনতার প্রসঙ্গ যখন আসে, তখন একটি প্রশ্নও সামনে দাঁড়ায়; তা হলো, গণতন্ত্র কী শুধু এলিটদের জন্যে সীমাবদ্ধ? এর উত্তর নির্ভর করে সমাজে ভারসাম্য যুক্ত কাঠামো, সৃজনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং জনগণের সচেতনতা কী রকম করে কার্যকর। গণতন্ত্রে সব মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত, এটি যেমন সত্য, তেমনি আমাদের দেশে রাজনৈতিক বাস্তবতা বেশ ভিন্ন। এখানে ক্ষমতাসীন শ্রেণিই সব ধরনের সুবিধা ভোগ করে। বাকি সকলেই খেলার মাঠে দর্শক। গণতন্ত্র কী তাহলে সোনার হরিণ আমাদের জন্যে?
একটু চোখ বুলিয়ে নিই পশ্চিমা প-িতরা কী বলছেন গণতন্ত্র নিয়ে, যেই স্কেলে আমাদের দেশের বাস্তবতা ফেলে কিছুটা হিবেস কষা যেতে পারে। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের গভর্নেন্স স্টাডিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যারেল ওয়েস্ট বলেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজগুলো জনগণকে তাদের মত প্রকাশের, আইনের শাসনে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার, অনুমানযোগ্য শাসনের নিয়মগুলো প্রয়োগ করার, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন পরিচালনা করার এবং একটি স্বাধীন গণমাধ্যমকে সমর্থন করার অধিকার রক্ষা করে। ওয়েস্ট সিলিকন ভ্যালির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে। তিনি আরো বলেছেন, “[যুক্তরাষ্ট্রে] এমন একটা পরিবেশ আছে যা মানুষকে কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করতে ও অপ্রচলিত ধারণাগুলো বিকাশিত হতে দেয়, মূলত এমনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ করে দেয় যা কর্তৃত্ববাদী সমাজগুলোতে প্রায়শ সম্ভব হয় না।”
ত্বাত্তিক দৃষ্টিতে দেখলে, বাংলাদেশের সংবিধানের মাধ্যমে জনতার জন্যে গণতন্ত্র পাওয়া এবং তার সুরক্ষায় সংবিধানে নির্দিষ্ট ধারা আছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এম, এন, এ আমার পিতা অ্যাডভোকেট মোহম্মদ আজিজুর রহমান ২৬ অক্টোবর ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে এম, সি, এ (মেমবার অব কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লি) হিসেবে সংবিধানের খসড়ার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, “এই সংবিধানের ৫৫, ৫৬, ৫৭ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলতে চাই যে, একটা দায়িত্বশীল, সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা আমরা দিয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম, বিচার বিভাগ থেকে নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকরণ। আমরা চেয়েছিলাম আইন-পরিষদ, সংসদীয় বিভাগ এবং আইনের শাসন। আমরা যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি। আমাদের এখানে এই সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে আছে যে, শাসনতন্ত্র সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হবে। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, সংবিধানের আরও এক স্থানে- সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে আছে: “সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক-দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।
আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার। আমরা মনে করি, আমরা মানুষকে বলি, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’। আইনের দ্বারা শাসন হবে। বিচার বিভাগ পৃথক হয়ে গেল। বহুদিনের আশা, নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগ থেকে পৃথক হবে এবং তা পৃথক হলো।”
কিন্তু এর পরেও বাংলাদেশে গণতন্ত্র বা তার চর্চা এখনও ত্রুটিপূর্ণ। ঐ সকল অনিয়মের বিরুদ্ধেই এখনো একটা লড়াই চলমান। বলা যায়, এ লড়াই হলো দেশের রাজনীতিতে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম এক সুদীর্ঘ এবং চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া। এর মধ্য দিয়ে আমরা পেতে চাই মুক্ত চিন্তার অধিকার, যেহেতু গণতন্ত্রের ভিত্তি নির্মাণে মূল উপাদানটি অবিচ্ছেদ্যভাবে ‘মুক্ত ভাবনা’। আসলে মূল হলো, যে জাতি গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত, তার সেই সমাজে মুক্ত চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিরাজমান থাকতে হয়। আবার সেই সমাজের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে। এমন নির্বাচন হতে হবে, যা সঠিকভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে জনগণের মতামত প্রকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়। দুঃখজনক হলো, সেখানে বিপুল ঘাটতি।
গণতন্ত্র নিয়ে বিস্তর বিশ্লেষণে প্রকাশিত, নির্বাচনের সুষ্ঠু ধারায় বিঘœ থাকায় দেশের মাঝে সাধারণ জনগণের জন্যে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত নয়। এসবের বাস্তবায়ন সম্ভব কেবলমাত্র একটি উন্নত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে। এই পরিবেশ কিছু শর্ত পূরণের দাবি করে। বলা উচিৎ, নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র একটি উচ্চমানের মানব পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা মূলত শিক্ষার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধার মাধ্যমে অর্জিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার মান উন্নয়ন, সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জনগণের জীবনের মান বৃদ্ধি করা। সুতরাং, গণতন্ত্র অর্জন মানে জনগণের আয়ের বৃদ্ধি এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি টেকসই পদ্ধতি। এ জন্যে দরকার একটি রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে একটি সমৃদ্ধ সমাজ এবং শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তি।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমি উন্নয়নের প্রবৃদ্ধি কেবল বোঝাতে চাইনি। সরকারি উন্নয়নের পরিসংখ্যান মানেই গ্রোথ দেখানো। মাথা পিছু আয় বেড়ে যাওয়া, রাস্তা-ঘাটগুলো চওড়া চওড়া হওয়া, ঝকঝকে বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ। কিন্তু একটা দেশ এগিয়ে যায় যে জাতিকে নিয়ে, সেখানে অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন থাকবে এবং মানুষের অন্তরভূমি হবে- মানুষ মানুষের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন তৈরিতে। দেশপ্রেম বোধ থাকবে। দেশপ্রেমটাই আসলে খাঁটি জিনিস, সেটা মানুষের অনেক মূল্যবোধের একটা মিশ্রিত উপাদান। যা কিনা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে। কেননা, জন্ম-জন্মান্তরে মানব থেকে মানবের প্রেম, এক থেকে সমষ্টিতে প্রবহমান হয় ভালোবাসবার জন্যে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরার এবং একে অন্যের জন্য সমতাকেন্দ্রিক হওয়ার জন্যে।
অথচ আমরা কোথায় যেন পরাজিত হচ্ছি। লোভের কাছে, বৈষয়িকভাবে পরাজয় মানছি। মানুষেরা এখন ব্যস্ত সম্পদ প্রদর্শনে। তাদের কাছে জীবনযাপনে যতটুকু অর্থ দরকার, তারও বাইরে অনেক অনেক বেশি অর্থ প্রয়োজন। প্রকাশটা এমন- আমি মস্ত বড় ধনী অথবা এই ধনের প্রকাশটা তখন বিশাল বিশাল দুর্দান্ত এপার্টমেন্টের মালিক। অথবা দুই দশটা দামী গাড়ি, যার একেকটা কোটি টাকার ওপরে কেনা। প্রায়ই ইংল্যান্ড-আমেরিকায় পরিবার নিয়ে মাসের পর মাস ঘুরতে যাওয়া এমন দাম্ভিকতা প্রকাশের এই লোভ তার প্রবল। অর্থাৎ সমাজে ব্যক্তির অবস্থান নির্মাণ হচ্ছে অর্থভিত্তিক। ওটার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার মিশ্রণ। আজকাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে বা সেই বলয়ে থাকলে অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত ফলবান হওয়া যায়। অর্থনৈতিক বিকাশটা ঘটে দানবীয় ধারায়। চুরি-ডাকাতিটা হালাল হয়ে যায়। এমন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে একটা লুটেরা সমাজ।
আপাত এই পরাজয়ের বিপরীতে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যায়, সেখানকার গণতন্ত্র অনেক শক্তিশালী। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে যে গণতন্ত্র, তা তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কখনোই সহজ ছিল না। আমাদের মুক্তি সংগ্রাম পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পথকে আরও কঠিন করে দিয়েছে। বাংলাদেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পেছনে দাতাদেশ এবং কোনো কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির কুটিল ভূমিকাও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর স্বার্থনির্ভর অবস্থান এ প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে। দাতা দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি, উন্নয়ন ও নীতি প্রণয়নে নগ্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউএসএইড বা জাইকার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক সহায়তা দিলেও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বিভিন্ন নীতি শর্ত। এসব শর্ত সাধারণত বাজার উদারীকরণ, কাঠামোগত সংস্কার বা বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার প্রশ্নে তারা তেমন চাপ প্রয়োগ করে না। বরং অনেক সময় দেখা যায়, যে সরকার তাদের অর্থনৈতিক বা ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করে, সেই সরকারের গণতান্ত্রিক ঘাটতি কিংবা নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনিয়ম নিয়ে তারা নীরব থাকে। এর ফলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হওয়ার বদলে বরং দুর্বল থেকে যায়। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ বা গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না দিয়ে প্রায়ই আন্তর্জাতিক শক্তির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। সে এক অদৃশ্য সুতোর টান। এতে করে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো বিদেশি সমর্থন পাওয়ার দিকেই বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে দাতাদেশ ও বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার বিভাজন আরও তীব্র রূপ নেয়, দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের যা ক্ষতিকর। সেই ক্ষতি পূরণে গণতন্ত্রের সুরক্ষা ও উন্নতি করার মিছিলে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র যদি জনগণের মতামত, চিন্তা ও অভ্যন্তরীণ আলোচনা সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়, তবে সে দেশটির গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী হয়।
সুতরাং গণতন্ত্রের সুস্থ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনও জরুরি, যেখানে কোনো ব্যক্তি এককভাবে কোনো গভীর স্বার্থে জনগণকে প্রতারিত করতে সক্ষম হবে না এবং দাতা গোষ্ঠীর কাছেও মাথা নোয়াবে না। দাবি এমন হলেও আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এখনো ব্যক্তিপ্রধান এবং একপেশে। এখানে গণতন্ত্রের সহায়ক কোনো ব্যবস্থা নেই। বরং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের কারণে গণতন্ত্রকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। গণতন্ত্র তখনই সঠিকভাবে কাজ করে, যখন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হয় এবং জনগণের মতামতকে সম্মানিত করে। যদি রাষ্ট্রের মসনদে বসে থাকা ব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে চান, তবে গণতন্ত্র তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যাবস্থা অনেক সময় ব্যক্তির শক্তিকে প্রাধান্য দেয় বলেই তা গণতন্ত্রের মূল চেতনার সাথে মেলে না। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বিভিন্ন রাজনৈতিক পথপরিক্রমায় আমাদের সামাজিক কাঠামো কখনোই গণতন্ত্রের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। তবুও কি লড়াই থেমে থাকে? গণতন্ত্র পাবার সংগ্রাম শূন্য হয়ে পড়ে? মোটেও তা হয় না। আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে যাতে করে জনগণের অধিকার সুরক্ষার আওয়াজ ওঠে। সেই অধিকার প্রয়োগে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। ইতিহাসের এই ধারাক্রমে দেখা যায়, ‘সংবাদ’ পত্রিকার ৭৫ বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির জন্য ‘সংবাদ’ ছিলো অন্যতম হাতিয়ার। সেই সময় থেকেই সংবাদ কেবল খবর পরিবেশনই করেনি, বরং বিভিন্ন সময়ে দেশ ও সমাজের অন্ধকার প্রান্তরগুলোকে আলোকিত করার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। এর মাঝে তিক্ত সত্য হলো, আমাদের দেশে নানা সময় বিভিন্ন সংবাদপত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়েছে প্রতিনিয়ত। সংবাদমাধ্যমের উপর চাপানো হয়েছে অব্যাহত সরকারি নিয়ন্ত্রণ। এতে করে গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে জনতার স্বাধীনতার স্বীকৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মূলত, এমন সরকারি কার্যক্রমে যখনই সংবাদপত্রের মুক্ত চলাচল থমকে দেয়া হয়, তখুনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতন্ত্রের পরিকাঠামো।
সবশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার অদলবদল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস, এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, এ সকল কিছুই গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশে মস্ত বাধা। এ সকল নেতি ডিঙ্গোতে জোর দেয়া দরকার শিক্ষার দিকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সমাজে অবশ্যই শিক্ষার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক চর্চা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মিশেল প্রয়োজন। গণতন্ত্র কখনোই এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এটি একটি সার্বিক প্রচেষ্টা, যা রাষ্ট্র, জনগণ, সংবাদমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ে অর্জিত হয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত করতে হলে মুক্ত চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখতেই হবে। এ জন্যে দরকার সমাজে সকল স্তরে জনগণের সুতীব্র সচেতনতা যাতে করে গণতন্ত্রের প্রতি তারা দায়িত্ব অনুভব করতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হলে সরকার, রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক শক্তি এবং সংবাদমাধ্যম সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। গণতন্ত্রের আসল শক্তি হলো জনগণ, আর তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার পথে লড়াই করাই হলো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।