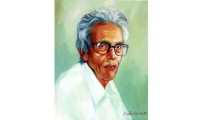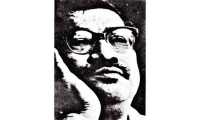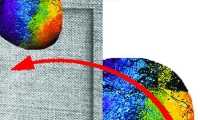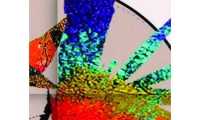সংস্কৃতি কি বাঁচাবে আমাদের?
শরীফ আতিক-উজ-জামান
‘যখন জাতি বুড়িয়ে যায়, তখন শিল্পও জুড়িয়ে যায়
আর বাণিজ্য গাছে গাছে বাসা বাঁধে।’
-উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা থেকে অনূদিত
সংস্কৃতির বহুমাত্রিক সংজ্ঞার মাঝে একটাকে বেছে নেওয়া বেশ কঠিন। প্রতিটা সংজ্ঞাতেই চিন্তার ঐক্য ও ভিন্নতা- দুই-ই রয়েছে। বিভিন্ন মতের একটি সংশ্লেষ নির্মাণ করে বলা যায় যে, সংস্কৃতি মানুষের জীবনযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা তার চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের আবেগ ও অনুভূতির শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সঙ্গীত, নৃত্যকলা, বাদ্যকলা, নাট্যকলা, শিল্পকলা, চলচ্চিত্র, সাহিত্য ইত্যাদি মানুষের আবেগ-অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান রীতিনীতি ও ঐতিহ্য পরম্পরা তাদের সংস্কৃতির সম্পদ যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্থানান্তরিত হয়। আর ভাষা হলো এ সবকিছুর বাহন। একই ভাষাভাষির জনগোষ্ঠী সেই ভাষা ব্যবহার করে সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ অনুভূতি নির্মাণ করে। আমাদের সুদীর্ঘ কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন রয়েছে, তাকে টিকিয়ে রাখার একটি লড়াইও রয়েছে। কারণ সংস্কৃতিরও শত্রু আছে। আমরা কি সেই লড়াইয়ে জয়ী হয়েছি? উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে উৎসব, লোক-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্কৃতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হতে চলল। এই সময়ে সংস্কৃতির মূল সংকট হিসেবে বিশ্বায়নের প্রভাব, বাণিজ্যিকীকরণ, প্রযুক্তিনির্ভরতা, অবক্ষয়, ঐতিহ্যবিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়গেুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বাংলাদেশে সংস্কৃতির দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অনেক সংকট রয়েছে যার সহজ সমাধান নেই। বর্তমানে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ, স্বীকৃতি ও সমর্থনের অভাব, সৃজনশীলতার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থতা, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপক্ষে লড়াইয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, কেন্দ্র ও প্রান্তের বৈষম্য ইত্যাদির সাথে শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-হিংসা-বিদ্বেষ সংস্কৃতির সামাজিক-বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।
সংস্কৃতির একটি তাত্ত্বিক কাঠামো আছে, তবে তা তত্ত্ববিদদের কাছে যতটা প্রিয়, প্রায়োগিক ও আনুষ্ঠানিক দিক নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুশীলন, পরিবেশনা ও প্রশংসাই তাদের প্রত্যাশা। আজকের দিনে অনেক সংস্কৃতিকর্মীই সংস্কৃতির অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ পান না। সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা কি আমাদের সমাজ-জীবনে কমে আসছে? মৌলিক চাহিদা পূরণের তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের কাছে সংস্কৃতি কি শুধুই বিনোদন? উত্তরাধুনিক রাষ্ট্রের সরকার কি এভাবেই সংস্কৃতিকে বিবেচনা করতে শেখাচ্ছে? কারণ মানুষ তার জীবনের একটা বড় অংশ দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ক্রয় করে। আরাম-আয়েশ, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার অনুভূতি তাদের এতই ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যে, তাদের অনেকেই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়া চলতে চান। কিন্তু মানবচিন্তন, আচরণ, অভিব্যক্তি, মূল্যবোধ, পরিবেশনা-দক্ষতার ক্রমবিকাশই যদি সংস্কৃতি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সমাজ কতখানি সংস্কৃতি-অভিপ্রেত (Culture-intent) সমাজ? যেখানে সংস্কৃতির উপস্থিতি ও অনুশীলন কিছু বিশেষ মানুষের সাথে সীমাবদ্ধ, তাকে ছড়িয়ে দিতে না পারার ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সংস্কৃতির একটি বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে না কি?
সংস্কৃতি প্রশ্নে আমাদের সমাজে প্রয়োজন ও প্রয়োজনহীনতার একটি বড়সড় দ্বন্দ্ব রয়েছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এর প্রয়োজন উপলব্ধি করতে না পারলেও প্রয়োজনহীনতার পক্ষে অজ¯্র কুযুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদয়িক পরিচয় সেক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে। সংস্কৃতি চর্চায় সাম্প্রদায়িক বিষটোপ গিলে গিলে কত আর নীলকণ্ঠ হওয়া যায়! গলায় আটকে থাকা বিষ এখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। না আছে ওঝা, না আছে ডাক্তার। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-লালন বাংলার সংস্কৃতির তিন প্রতীক। আমাদের আনন্দময় উপভোগে যেমন তারা ঘুরেফিরে আসেন, আবার আমরা তাদের কাছে ছুটে যাই আমাদের সংকটে। কিন্তু এও তো সত্যি যে, তারাও বার বার সংকটে পড়েছেন, আর এদেশের সংস্কৃতিসেবীরা তাঁদের উদ্ধার করেছেন। দুর্বৃত্তের খপ্পর থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রধান অস্ত্র সাম্প্রদায়িকতা যা দিয়ে তাকে বারংবার ঘায়েল করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে নজরুলকে দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু তিনিও সেই একই অস্ত্রে রক্তাক্ত হয়েছেন। আর আঘাতকারীরা ভিন্ন কেউ নয়, সেই একই চিহ্নিত গোষ্ঠী যাদের ভাবনার ক্ষেত্রটি সংকীর্ণতার সীমানা ভেঙে উদার অসাম্প্রদায়িক বলয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি। সম্ভবও ছিল না, কারণ চৈতন্যের গঠন বোধ হয় বদলায় না। যারা রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করতে কোমর বেঁধে নামেন, তারাই নজরুলকে ‘কাফের’ বলে গালি দেন এবং তাঁর রচনার ‘হিন্দুয়ানি’ শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপন করেন। এই বালসুলভ অবিমৃশ্যকারিতা সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্র কারো মঙ্গল করেনি। এই গ্রহণ-বর্জনের সংকটের মূলে যে সাম্প্রদায়িকতার কঠিন অর্গল তা কি ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়েছে? এক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিকর্মীরা কি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন? তারাও কি এই দুই বলয়ে বিভক্ত থাকেননি? তাদের চর্চায় কি পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকট হয়ে ধরা পড়েনি? সত্যিই কি আমাদের চর্চায় রবীন্দ্র-নজরুল আদর্শের সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে? তাঁরা আমাদের জীবনের সাথে জুড়লেন কই?
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বছরের পর বছর চেনা-পরিচিত কয়েকটি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক পড়ানো হয়। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য পড়ে। তাদের যাপিত জীবনে এই পঠনপাঠনের দৃশ্যমান কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। সংস্কৃতি অঙ্গনেও ঘুরেফিরে পরিচিত কিছু গান ও কবিতার পরিবেশনা শোনা যায়, কিন্তু এর বাইরে তাঁদের সৃষ্টির বিশাল ভা-ারের সাথে আমাদের তেমন পরিচয় ঘটে না। বিশেষ করে তাদের প্রবন্ধ সাহিত্যের সাথে। শত বছর আগে লিখিত সেইসব প্রবন্ধের সাথে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের বিস্মিত করে। আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করতে শেখায়। কিন্তু আমরা কি উপলব্ধি করতে চাই? সংস্কৃতির যেসব চিহ্নিত ফেরিওয়ালা এদেশে ছবক দিয়ে বেড়ান, তাদের ঝুলিতে সবসময় ভালো কিছু পাওয়া যায় না। তারা তত্ত্ব দেন, আবার বদলান, বারবার বদলান। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা হতাশা থেকে উচ্চারণ করি ‘এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা। এখনো মরণ-ব্রত জীবনে হল না সাধা।’ কিন্তু আঁধার কি যায়? সে তো ঘুরে ঘুরে আসে, তাই তো আলো জ্বালতে হয়। সংস্কৃতিকর্মীদের সেই আলো জ্বালবার দায়িত্বটা এসে পড়ে। আর কেউ কেউ তো আলো হবেন। নইলে আলোকিত মানুষ হবে কী করে! ভার্জিনিয়া উলফের দোহাই দিয়ে বলা যায়, কোনো কিছুর ওপর আলো ফেলার প্রচেষ্টা শেষমেশ নতুন অন্ধকার আবিষ্কার করার শামিল। এসব মোকাবেলায় আমাদের ‘মরণব্রত সাধা’র প্রস্তুতি আছে কি?
লালনকে আমরা অভিজাত মঞ্চে সেভাবে ঠাঁই দিইনি। লালন আমাদের সংস্কৃতিচর্চায় এখনো ব্রাত্য। বাউল-সুফিদের মাঝে তাঁর চর্চা সীমিত, কিন্তু সেখানেও তিনি নিরাপদ নন। বাউলদের চুল-দাড়ি কেটে, একতারা-দোতারাগুলো ভেঙে তাদের গ্রামছাড়া করে দেওয়ার মতো অজ¯্র ঘটনা ঘটেছে। অনৈসলামিক তকমা দিয়ে লালন উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রুখে দাঁড়ানোর মতো পর্যাপ্ত শক্তি ও সাহস সংস্কৃতিকর্মী-বুদ্ধিজীবী-জনতা দেখাতে পারেননি। কারণ রাষ্ট্রযন্ত্রের এক অদ্ভুত নীরবতা সংস্কৃতি-বিরোধী এই কুকর্মে তার সমর্থন জ্ঞাপন করে। অজ্ঞানতা ও পাপবোধ সমার্থক- যা সংস্কৃতির বিপরীতে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যায়। ধর্মে পাপের যে সরল সংজ্ঞা রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির পথ আগলে দাঁড়ায়, এগোতে দেয় না। গায়ের জোর মস্তিষ্কের শক্তিকে দমন করতে চায়, পারেও। লালনকে যারা ধারণ করেন তাদের বুকে আজ উগ্রবাদীর ছুরি। আগে নিন্দা হতো, রাস্তায় মানববন্ধন হতো, এখন প্রাণের ভয়ে তাও হয় না। লালনের সৃষ্টিকে ধর্মবিরোধী বলে খারিজ করতে চাওয়া লোকেরাই আবার কনসার্টে পাঞ্জাবি সুফিসাধক বুল্লে শাহর ‘মেরা পিয়া ঘর আয়া ও লালনি’ কিংবা সিন্ধু অঞ্চলের সুফিসাধক লাল বাবা শাহবাজ কালান্দারের সম্মানে আমীর খসরুর প্রার্থনা সঙ্গীত অবলম্বনে এই বুল্লে শাহরই ‘দমাদম মাস্ত কালান্দার’ শুনে উদ্বাহু নৃত্য করেন। আত্মনিবেদনের আবহটি এই পরিবেশনায় খুঁজে পাওয়া যায় না! পাঞ্জাবি সুফি গানের অর্থ না বুঝে তাকে গ্রহণ করছি, আর লালনকে ভুল বুঝে পরিত্যাগ করছি। এর মধ্যে লাভালাভের কোনো বিষয় নেই, পুরোটাই ক্ষতি। লালনকে আমরা জীবনে ধারণ করি না, ব্রাত্য রয়ে যান হাছন রাজা, শাহ আব্দুল করিম, বিজয় সরকাররা। সংস্কৃতি সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সঞ্চারিত করে; ব্যক্তি সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করতে শেখে, কিন্তু মোতাহের হোসেন চৌধুরী যে বলেছিলেন, ‘সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম’, তা আর হলো কই? অবৈধ ভোগবিলাসী জীবনযাপনে বিন্দুমাত্র পাপবোধ না জন্মালেও, সংস্কৃতি উপভোগে এদের অবচেতনে পাপ বোধ হয়।
এই সমাজের একটি বড় অংশের কাছে সংস্কৃতির কোনো মূল্য নেই, সংস্কৃতি ছাড়াই তারা বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এরা ভোগের আবরণে উপভোগকে ঢেকে দিতে চায়। এদেশ এখন উঁচু ভোগবাদী সমাজের স্বপ্নে বিভোর- সেই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকা- পরিচালিত হচ্ছে, তাই সংস্কৃতিও সেখানে পণ্য। শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রও তাই বাণিজ্য-নির্ভর ও শিল্প-নির্ভর এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। ‘লাল সবুজের পালা’ ‘ঘুড্ডি’ ‘রূপসা নদীর বাঁকে’র মতো ছবিগুলো যখন লগ্নিকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে পারে না, তখন ‘বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না’ ৬ মাস ধরে সিনেমা হলে চলে। দুই হুমায়ূনের মধ্যে আহমেদের বই হাজার হাজার বা লাখ লাখ কপি বিকোয়, কিন্তু আজাদ শতক অতিক্রম করতে পারেন না। বেশিরভাগ মানুষ আজকের সমাজে শিল্প-সাহিত্যকে তাদের আগ্রহের বাইরের বিষয় বলে মনে করে।
শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। তাদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি সাধারণ জনগণের অনাগ্রহের নিন্দা করার সময় তারা অনেক বিষয় বিবেচনায় নেন না। শিল্পীদের মনস্তত্ত্বে ‘জনপ্রিয়তাই শেষ কথা’, ‘প্রশংসা আমার একার’- এরকম বিষয়গুলো যথেষ্ট নগ্ন হয়ে ধরা দেয়। এক শিল্পী অন্য শিল্পীর মন খুলে প্রশংসা করেন- এরকম খুব কম দেখা যায়। তারা মিললেও মিশে না। আরেকটি বিষয়ও বেশ ভাবায়। আজকের তরুণদের চোখে পড়ার মতো সংস্কৃতি বিচ্ছিন্নতার কারণ কী? অনেকদিন থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকা-ে ছেলে অপেক্ষা মেয়েদের অংশগ্রহণ বেশি। সাংস্কৃতিক কর্মকা-ে এক ধরনের শূন্যতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তেমনই আশংকা তৈরি করে। রাষ্ট্রের আচরণ সাম্প্রদায়িক হোক বা না হোক, তা সৃজনশীলতাকে সেভাবে উৎসাহ জোগায় না, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংকুচিত করে। আবার সমাজের বিত্তশালী অংশ সাংস্কৃতিক কর্মকা-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ন্যূনতম কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না। গান-টান, নাটক-ফাটক, কবিতা-টবিতা, নাচ-ফাচ করা ছেলেমেয়েরা ‘ফালতু’ কাজে সময় নষ্ট করে। তাদের শৈল্পিক দক্ষতা আজকের অভিভাবকের কাছে সেভাবে গুরুত্ব পায় না। কবেইবা পেয়েছে! সরকার যত শাসন করতে চায়, তত দায়িত্ব নিতে চায় না। তবে সংস্কৃতিতে সরকারি অর্থে নিজ দলীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যতিব্যস্ত সরকার সংস্কৃতিকে এক ধরনের বাগানবিলাসের মতো কর্মকা-ে সীমিত করে ফেলেছে। যেমন, প্রতœতত্ত্ব সংরক্ষণ সরকারি দায়িত্ব হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার সুষ্ঠুভাবে সে দায়িত্ব পালন করে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কাজ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মাধ্যমে জনবিচ্ছিন্নতা তৈরি করে, যা সংস্কৃতি বিকাশের অন্তরায়।
সরকার বাগানবিলাসের মতো যে সংস্কৃতি চর্চা করে তা হলো, গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নামে মেলা বা উৎসব- যেখানে সরকারি অর্থের ব্যাপক অপচয় হয়, কিন্তু তাতে সংস্কৃতি সেভাবে উপকৃত হয় না। এখন এসব অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা আমন্ত্রিত হন না। এই ধরনের সরকারি অনুষ্ঠানে সভামুখ্য থেকে শুরু করে অভিভাষণ প্রদানকারী, আলোচক সবাই প্রায় আমলা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা। এছাড়াও সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রচুর টাউটের উৎপাত আছে, যাদের কাজ সাংস্কৃতিক কর্মকা-ের ওপর ভর করে সুবিধা লুটে নেওয়া। শাসন ক্ষমতার পালাবদল হলেও এরা বদলান না। এতে প্রকৃত সাংস্কৃতিককর্মীরা হতাশ হন। আজীবন বাবা-মায়ের কাছে ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর অপবাদ সওয়া এই মানুষদের এসব মানতে কষ্ট হয়। কিন্তু ঠিকমতো বনের মোষ তাড়াতে পারলে বনসম্পদ রক্ষা পায়। স্বার্থহীনভাবে সেই দায়িত্ব পালন করার পরেও তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। আজ এই সংকটকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আনন্দে মুখ ডুবিয়ে রাখা তরুণ-তরুণীরা কি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে? সংস্কৃতির লড়াইয়ে শামিল হবে?
শিল্প-সাহিত্যের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার একটি অভিযোগ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে শোনা যায়। আর অশ্লীলতার সংজ্ঞাও বহুমাত্রিক, একইসাথে আপেক্ষিকও বটে, কারণ স্থান-কাল-পাত্রভেদে অশ্লীলতার সংজ্ঞা ভিন্ন হতে পারে। এক সমাজে যা অশ্লীল হিসেবে বিবেচিত, অন্য সমাজে তা স্বাভাবিক। আর নগ্নতাই অশ্লীলতা কিনা, সে ব্যাপারে ব্যাপক বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন নগ্নতা ও অশ্লীলতা সমার্থক নয়। নগ্নতা সমাজের ট্যাবু বা লুকানো বিষয়গুলো তুলে ধরতে সাহায্য করে এবং সামাজিক রীতিনীতির দুর্বলতা প্রকাশ করে। তাহলে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যৌনতা কী? নিঃসন্দেহে যৌনতা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এটা স্বপ্নের জগৎ থেকে শুরু করে শারীরিক কর্মকা- পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পে তার প্রকাশ কেমন হবে তার কি কোনো বাঁধাধরা নিয়ম আছে? কতটুকু প্রদর্শনযোগ্য তা কি কেউ নির্দিষ্ট করে দিতে পারে? নাকি শিল্প¯্রষ্টার নিজস্ব বিবেচনার ওপর তা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ? সবকিছু কি প্রদর্শনযোগ্য? একবার এক ভক্ত সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছে বারংবার জানতে চাইছিলেন যে, উনি কীভাবে এতো ভালো লেখেন। উনি হেসে এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। শেষমেশ এক পর্যায়ে বললেন, ‘দেখুন, আমি আমার সন্তানগুলোকে দেখাতে পারি, সন্তান জন্মের পদ্ধতি নয়। ‘মানুষের সম্পর্কের বিশেষ এক অপরিহার্যতা হলো যৌনতা, যা প্রেম-ঘৃণা-ঈর্ষা ও অন্যান্য গভীর আবেগ প্রকাশ করে, কারণ যৌনতা একটি মানবিক অভিজ্ঞতা, নিষিদ্ধ কিছু নয়। নগ্নতা যৌনতার একটি অংশ যা সবসময় অশ্লীল নাও হতে পারে। সমাজের নৈতিকতার মানদ- (যা বিতর্কমুক্ত নয়) লঙ্ঘিত না হলে তাকে অশ্লীল বলা যায় না।
যাত্রাশিল্প কি অশ্লীল ছিল? সেখানে কারা অশ্লীলতা আমদানি করেছিল? সারারাত অভিনয় দেখা মানুষদের কারা ‘ডানা কাটা পরীদের ঝুমুর ঝুমুর নাচে’ আকৃষ্ট করে তুলেছিল? যারা অশ্লীলতা আমদানি করলেন, তারাই আবার অশ্লীলতার অজুহাতে যাত্রাশিল্প বন্ধ করে দিলেন। প্রান্তিক মানুষের বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম শেষ হয়ে গেল। আর এই পেশার সাথে জড়িত হাজার হাজার শিল্পীরা বেকার হয়ে গেলেন। চিত্রকলার মিনিয়েচার ফর্মের মতো ২ ঘণ্টার যাত্রা উৎসব করা হচ্ছে রাজধানীতে। কিন্তু এতে কিছু সরকারি অর্থের শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। যাত্রাশিল্পকে বাঁচাতে হলে তাকে গ্রামে ফিরিয়ে দিতে হবে যাদের কাছে এর প্রকৃত কদর রয়েছে। কোথায় গেল গ্রামের সার্কাস, জারিগানের আসর? সংস্কৃতি চুরি হলে তাও সহ্য পায়, কিন্তু ডাকাতি হলে সহ্য হয় না। আমাদের অনেক ঐতিহ্য ডাকাতি হয়ে গেল, রক্ষা করা গেল না।
সংস্কৃতি-চর্চায় আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো কেন্দ্র ও প্রান্তের বৈষম্য। সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম কেন্দ্র বা রাজধানীকে ঘিরে গড়ে ওঠে যেখানে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ তেমন থাকে না। আবার অনুশীলনের সেই ধারা প্রান্তে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরা সেভাবে আগ্রহ অনুভব করেন না। স্থানীয় সাংস্কৃতিক বিকাশে বাধা সৃষ্টিকারী এই বৈষ্যমের মূল কারণগুলোর অন্যতম হলো, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কেন্দ্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের পছন্দসই সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেয়। প্রভাবশালী সামাজিক শ্রেণি বা গোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতিকে আদর্শ মেনে প্রান্তিক মানুষের সংস্কৃতিকে নিম্নরুচির ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। শিক্ষার মান সংস্কৃতির মানকে প্রভাবিত করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ভৌত-অবকাঠামোর উন্নয়ন হলেই কেন্দ্র ও প্রান্তের যোগাযোগের দূরত্ব কমে না যদি মানসিকভাবে সেই দূরত্ব কমানো না যায়।
তাহলে এই সংকট মোকাবেলার সংস্কৃতিকর্মীদের করণীয় কী? আমরা কি তা নির্ধারণ করেছি? সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি ও সক্ষমতা আছে? আমাদের সমাজে সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া মানুষের সংখ্যা কম, দিনে দিনে আরো কমে আসছে। এখন প্রতিটি অনুষ্ঠান দর্শক শূন্যতায় ধুঁকতে থাকে। একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে বারংরার অনুরোধ করে বা জোর করে দর্শক ধরে আনতে হয়, নইলে ওই দিনে আমন্ত্রিতদের অনেকের ‘বিশেষ জরুরি কাজ’ পড়ে যায়। তাহলে সংস্কৃতিকর্মীরা কী করবেন? রাগ করে নিজের ঘরে আগুন লাগালে তো লোকালয় পুড়ে যায়। যখন তারা গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠেন ‘আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো’ তখনও তারা আলোই জ্বালতে চান, ক্রোধের আগুন নয়।
সংস্কৃতি কি বৃদ্ধ হয়? আর বৃদ্ধ হলে কি পৌরুষ হারিয়ে ফেলে? সেই অর্থে আমাদের চর্চিত সংস্কৃতি কি পুরুষত্বহীন? লালন-রবীন্দ্রনাথ-ডিএল রায়-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুল-হাছন রাজা-শাহ আব্দুল করিম-বিজয় সরকারের সৃষ্টি কি পারবে আমাদের জাগিয়ে তুলতে? এই মানুষেরা সারাটা জীবনে মানবতার জন্য সৃষ্টি করে গেলেন, মানুষকে মানুষের সাথে মেলাতে চাইলেন, ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মাঝে একতার গান গাইলেন, কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে বিবেচিত হলেন না। সঠিকভাবে তাঁদের গ্রহণ করতে না পারার দায় অবশ্যই আমাদেরই। শৈশবে থেকেই সবাই শুনে শুনে বড় হয়, ধার্মিক হও, ধর্মাচরণ করো। ভালো হওয়ার সেটাই একমাত্র শর্ত। আমরা কজন আমাদের জীবনকে সংস্কৃতির মানদ-ে অর্থবহ করে তুলতে চেয়েছি? এই জীবনের এমনিতে কোনো অর্থ নেই। তাকে অর্থবহ করে তুলতে হয়। সেই প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কী আছে! কিন্তু সেই হাতিয়ার কি আমরা কাজে লাগাতে পারব? পারব কি আমাদের রক্ষা করতে? সরলীকরণ না করেও বলা যায়, গভীর সাম্প্রদায়িক মন আর ধর্মনিপেক্ষ মুখ আমাদের আর কত বিভ্রান্ত করবে? সংস্কৃতি কবে পরিপূর্ণভাবে আমাদের হয়ে উঠবে? আমরা যাকে আঁকড়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখি, তা কি সত্যিই আমাদের বাঁচাবে?