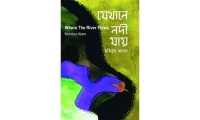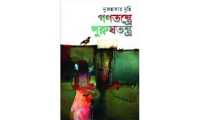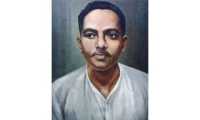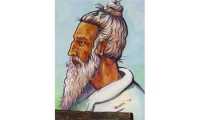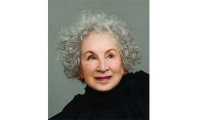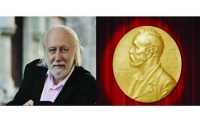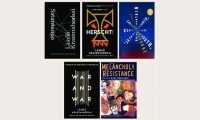উত্তরাধুনিক সাহিত্যের সুলুক সন্ধান
শরীফ আতিক-উজ-জামান
শিল্পী : সুনীল কুমার
যে কোনো মতবাদকে ভারি, দুর্বোধ্য, দূরবর্তী এবং পণ্ডিতপ্রবরদের চর্চার বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়ার একটি সার্বক্ষণিক প্রবণতা আমাদের মাঝে বিদ্যমান। আবার অনেকের জ্ঞানের অহংকার মতবাদকে জটিল করে উপস্থাপনে উৎসাহ জোগায়। ফলে গড়পড়তা মেধার মানুষের কাছে তা অগম্য এক বিষয় হিসেবেই রয়ে যায়। দার্শনিক মতবাদে যুগবৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি অপরিহার্য এক বিষয়। মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবে সেই বৈশিষ্ট্যের মাঝেই বসবাস করে চলে। তারপরও তার চর্চা খুব সাবলীল ও ব্যাপক, এমন নয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে একসময় উত্তরাধুনিকতাবাদের ব্যাপক উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা গেছে এবং শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা, ফ্যাশন, যোগাযোগ, প্রযুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষ দিকে শুরু হওয়া এই মতবাদ কারো কারো মতে এখনো চলমান, আবার কেউ কেউ মনে করেন তা শেষ হয়ে গিয়ে উত্তর-উত্তরাধুনিক যুগবৈশিষ্ট্য শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ক্ষমতার নতুন মেরুকরণ, বিমানবিকীকরণ ও পুঁজিবাদের ভয়াবহ আগ্রাসনের সাথে এর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।
উত্তরাধুনিকতার সাথে আধুনিকতার যোগসূত্রের বিষয়টি নামের মাঝেই প্রকাশিত। বিশ শতকের প্রথম পাদে শুরু হওয়া আধুনিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় উত্তরাধুনিক শিল্প ও সাহিত্য গতিধারার সূচনা হয়েছে। কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের সংযুক্তি ও কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সংস্কার এই আন্দোলনকে নতুন অবয়ব দান করেছে। ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস, টিএস এলিয়ট, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, উইলিয়াম ফকনার প্রমুখ পরীক্ষামূলকভাবে নানা শৈলী নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। আধুনিকতাবাদীরা সত্যানুসন্ধানে ব্যক্তির চৈতন্যের ওপর নির্ভর করেছেন। আর তাই চেতনাপ্রবাহ (Stream of Consciousness), দৃষ্টিকোণ (Point of view)-এর মতো শৈলী সৃষ্টি হয়েছে। তারা সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিসত্তার ওপর নির্ভর করেছেন। হেমিংওয়ে মনে করতেন যে একজন তরুণ লেখকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো যা সত্য বলে শেখানো হয়েছে তার বদলে তিনি যা অনুভব করেন সঠিকভাবে তার সত্যতা যাচাই করা। উত্তরাধুনিকতাবাদে ব্যক্তিসত্তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ভণিতার ভিতর দিয়ে মানুষ নিজের যে প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম, প্রকৃতপক্ষে সেটাই তার আসল রূপ। সুতরাং ভণিতা করার সময় আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা আমাদের থেকেও বৃহৎ শক্তির হাতে জিম্মি হয়ে আছি। কিংবা ¯œায়বিক তাড়নায় আমাদের সৃষ্টি হয়েছে।
কুর্ট ভনিগার্টের উপন্যাসে দেখা যায় কোনো চরিত্র নেই, কোনো নাটকীয় সংঘাত নেই। কারণ প্রতিটা মানুষ এতটাই অসুস্থ এবং বৃহৎ শক্তির হাতের ক্রীড়নক- যা মূলত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট। তাই তারা কোনো চরিত্র হয়ে উঠতে পারে না। আধুনিকতাবাদে শিল্প ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওয়ালেস স্টিভেন্স-এর মতো উত্তরাধুনিক কবিরা মনে করেন যে অবিশ্বাসের এই যুগে কবির দায়িত্ব হলো তার নিজের মতো করে বিশ্বাসের তৃপ্তি জোগানো। ভাষা ব্যতিরেকে আমরা বাস্তবতা থেকে কোনো ধারণা লাভ করি না। ভাষা শুধু বাস্তবতা বর্ণনা করে না, তাকে অবয়বও দান করে। নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে মানুষ যা চিন্তা করে এবং যেভাবে জগত দেখে ভাষা সেইভাবে তাকে অবয়ব দান করে।
আধুনিকতাবাদীরা হাহাকার করেন যে কেন্দ্র কোনো কিছু ধরে রাখতে পারে না, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। উত্তরাধুনিকতাবাদীরা মনে করেন যে, সত্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা আদতে মিথ্যা। এইসব ধারণা থেকে মুক্ত হওয়াই ভালো। কেন্দ্রের সব ভেঙেচুরে যাওয়াতে হাহাকারের কিছু নেই। সেটা একদিক দিয়ে ভালোই। উভয় মতবাদ উঁচু ও নিচু শিল্পের মধ্যকার বিভেদরেখা মুছে দিতে চেয়েছে। উত্তরাধুনিকতা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিচু শিল্পকে উঁচু শিল্পের সাথে, অতীতকে ভবিষ্যতের সাথে এবং সাহিত্যের এক শাখাকে আরেক শাখার সাথে মেশাতে চেয়েছে। ভিন্নধর্মী ও সঙ্গতিহীন উপাদান মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক রূপ (Parodz) নির্মাণের ঝোঁক কিংবা অন্য শৈলীর অনুকরণ (Pastiche) উভয় মতবাদেই বহুল ব্যবহৃত। এই ধরনের কলকব্জা ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া যে এই রচনা বা সৃষ্টি বাস্তব নয়; কাল্পনিক ও আরোপিত। আধুনিক ও উত্তরাধুনিক রচনা খ-িত, অসম্পূর্ণ এবং খুব সহজে একটি সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করে না। এই কারণেই এই রচনাগুলো অস্পষ্ট এবং তার বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব। এখানে উপস্থাপিত বিষয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বা জীবনের একটি লক্ষ্য প্রকাশ করে না। বিমানবিকীকরণের মধ্য দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হারানোর পরিবর্তে তা হয়ে ওঠে কোনো যুগ বা সভ্যতার প্রতিনিধি। যেমন, এলিয়টের ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এর টাইরেসিয়াস।
আধুনিকতাবাদ বর্তমান বিশ্বকে বিয়োগান্ত মনে করে খ-িত ও বিকেন্দ্রিভূত হিসেবে তুলে ধরে। জীবনের সংহত ও কেন্দ্রীয় রূপ হারিয়ে যাওয়ার জন্য বেদনাবোধ করে এবং শিল্প আধুনিক জীবনের সর্বস্তরে সংহতি, ঐক্য, ধারাবাহিকতা ও হারিয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। আধুনিক বিশ্ব নিষ্ফলা বলে এলিয়ট হাহাকার করে উঠেছিলেন এবং ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ কবিতার কাঠামোতে সেই বিচ্ছিন্নতা, বিচূর্ণন প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তিনি জীবনের হারানো অর্থ ও সংহতি পুনরুদ্ধারে প্রাচ্য সংস্কৃতির কাছে ছুটে আসেন।
উত্তরাধুনিকতায় বিচূর্ণন ও বিচ্ছিন্নতা মোটেও বিয়োগান্ত নয়, বরং তা বিচূর্ণনকে স্বাগত জানায়, কারণ বিচূর্ণন ও বিকেন্দ্রিকতা অস্তিত্ব ধরে রাখার সম্ভাব্য পথ; তা বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যেতে উৎসাহ জোগায় না। এখানেই উত্তরাধুনিকতাবাদ ও উত্তরকাঠামোবাদ একসাথে এসে মিশেছে। এই দুই মতবাদই সুসংহত কেন্দ্রের ধারণাকে খারিজ করে দেয়। দেরিদা বলতে চেয়েছেন যে কেন্দ্র সবসময় প্রান্তের দিকে এবং প্রান্ত কেন্দ্রের দিকে সর্বদা সঞ্চরণশীল। অন্য অর্থে, কেন্দ্র যা ক্ষমতার উৎস, প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশীল নয়। তা ক্রমেই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে আবার প্রান্ত, যাকে ক্ষমতাহীন মনে করা হয়, তা ক্ষমতাশীল হয়ে উঠতে চায়। তাই বলা চলে যে কেন্দ্র বলে কিছু নেই অথবা অনেকগুলো কেন্দ্র রয়েছে। এভাবে কেন্দ্রকে খারিজ করে দেওয়ার ফলে কেন্দ্র ক্ষমতা ধরে রাখতে কিংবা আরো ক্ষমতাবান হতে মরিয়া হয়ে ওঠে যাকে দেরিদা বলছেন Differance। এই ফরাসি শব্দটি দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ঐক্য, প্রচলিত অর্থ ও সংহতি অনবরত বদলে যায়।
সংহতি ও মিলের বিষয়ে অবিশ্বাস ও সন্দেহ উত্তরাধুনিকদের সাথে আধুনিকপন্থীদের মৌলিক পার্থক্যের আরেকটি। আধুনিকতাবাদীরা মনে করেন সঙ্গতি বা মিল থাকাটা সম্ভবপর, আর তাই যুক্তি ও শৃঙ্খলার ওপর জোর দেন। যত যুক্তি তত শৃঙ্খলা- আধুনিকতাপন্থীদের এই বক্তব্যের সাথে উত্তরাধুনিকতাবাদীরা একমত নন। তাদের মতে সমাজের কোনো অংশে শৃঙ্খলা থাকলে অপর অংশে বিশৃঙ্খলা প্রবল। যুগল-বৈপরীত্যের (Binary Opposition) কথা বলতে গিয়ে কখনো কখনো নৈরাশ্যবাদীর মতো বলে থাকেন যে জগতের সবকিছুতেই বিশৃঙ্খলা।
আধুনিকতাবাদীদের মহান বৃত্তান্তের (metanarrative) ধারণাকে উত্তরাধুনিকরা খুব যৌক্তিকভাবেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। তারা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং বিনির্মাণ করেন। কোনো সমাজ বা সংস্কৃতি তার বিশ্বাস ও চর্চা নিয়ে অনবরত যে গল্প বলে চলে সেটাই মহান বৃত্তান্ত। যেমন, ভারত সবসময় বলে চলে সেটা একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু সেখানে অজ¯্র গণতন্ত্র-বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী আছে যারা বিপরীত স্রোতে চলে। তার মানে ভারত একটি মিথ্যা বিশ্বাসের চর্চা করে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এখানে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মহান বৃত্তান্ত বা meta-narrative। সংক্ষেপে মহান-বৃত্তান্ত একটি মহৎ প্রচারণা, কিন্তু তা সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি মিথ্যা ধারণা তুলে ধরে। উত্তরাধুনিকতাবাদ উপলব্ধি করে যে মহান-বৃত্তান্ত বিরোধিতা, অস্থিরতা বা অসঙ্গতির প্রসঙ্গ লুকিয়ে রাখে, নীরব থাকে বা অস্বীকার করে। উত্তরাধুনিকতাবাদ উৎসাহ জোগায় সীমিত বয়ান (mini-narratives) উপলব্ধিতে যার মাধ্যমে ছোট ছোট সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা বা অভ্যাস, স্থানিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি উঠে আসে কোনো প্রকার সর্বজনীনতার ভণিতা ছাড়াই। কোনো চর্চার শেষ কথা বলে কিছু নেই এবং ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মহান বৃত্তান্তের পুরোটাই শাসকদের গালগল্প যা মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
উত্তরাধুনিকরা সচেতন ও পদ্ধতিগতভাবে সাহিত্যে বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে Meta-fiction পদটি ব্যবহার করছেন। কথাসাহিত্যের মৌলিক কাঠামো নিরীক্ষার সাথে সাথে তারা গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির বাইরের জগতের সম্ভাব্য কল্পিত বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। সাহিত্য সবসময় তার নিজস্ব কৃত্রিম জগতের দিকে মনযোগ কাড়তে চায়। নিজস্ব কল্পিত জগত সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। পাঠক বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে সর্বদা নিজের প্রতিফলন দেখতে পায়। সবসময় মনে মনে বলে, ‘এতো আমি।’ চরিত্ররা বৈচিত্র্যহীন ও নীরস। তারা ব্যক্তিত্বহীন ও গভীর অনুভূতিহীন। ব্যক্তির বিষয়ে উত্তরাধুনিকরা সবসময়ই সংশয় প্রকাশ করেন। পারমাণবিক বিস্ফোরণ, হলোকাস্ট ইত্যাদি মহাপ্রলয়তুল্য ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ থাকে।
একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত বাস্তবতাকে বিনির্মাণের মাধ্যমে উত্তরাধুনিকতাবাদ ভাষার ধারণায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আধুনিকপন্থা অনুযায়ী, বাস্তবতা ও যৌক্তিক মন তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভাষা একটি স্বচ্ছ ও যৌক্তিক মাধ্যম। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু উত্তরাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী, গভীরতা বলে কিছু নেই, আছে শুধু ভাসা ভাসা উপরিতল। ফরাসি দার্শনিক বদ্রিলার্দ উত্তরাধুনিক উপরিতলের সংস্কৃতিকে ভ্রান্ত প্রতিমূর্তি (simulacrum) বলে ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মিডিয়া ও অন্যান্য আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো একটা ভুয়া ও দূরবর্তী বাস্তবতা তুলে ধরতে চায়। এটা শুধু অনুকরণ বা নকল নয়, বরং ভুয়া আদলে মূলের একটি বিকল্প নির্মাণ করে। সমসাময়িক জগত ভুয়া, কারণ সেখানে ভুয়া প্রতিরূপের মাধ্যমে প্রকৃত বাস্তবতার প্রতিস্থাপন ঘটে থাকে। যেমন, Gulf war-এর খবরাখবর আমরা যা সংবাদপত্রের মাধ্যম পেতাম তার সাথে প্রকৃত ঘটনার খুব সাদৃশ্য ছিল না। ওই যুদ্ধের ভুয়াচিত্র তখন বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সেগুলো বাস্তব অপেক্ষা বেশি বাস্তব মনে হতো। উত্তরাধুনিক আদর্শে মূল বলে কিছু নেই, সব ভুয়া প্রতিরূপ; কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই শুধু মানচিত্র ছাড়া; কোনো বাস্তবতা নেই শুধু ভান বা অনুকরণ ছাড়া। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, আমরা বাস্তবতা ও কৃত্রিমতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি। যেভাবে আমরা জীবনের বাস্তবতার সাথে সংশ্রব হারিয়ে ফেলেছি ঠিক তেমনি যেসব পণ্য আমরা ব্যবহার করি সেগুলো বাস্তবতা থেকেও আমরা দূরে সরে গেছি। যদি গণমাধ্যম উত্তরাধুনিকতার একটি বড় চালিকাশক্তি হয়ে থাকে, বহুজাতিক পুঁজি ও বিশ্বায়ন আরেকটি। উত্তরাধুনিকতা পুঁজির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছে। ১৮-১৯ শতকের প্রথম পর্যায়ের বাজার অর্থনীতি বাষ্পচালিত যানের মতো প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে সাথে নিয়ে চলেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চালিত মোটরগাড়ির সাথে সাথে একচেটিয়া পুঁজি ও আধুনিকতা দেখতে পেয়েছে। উত্তরাধুনিক যুগ পারমাণবিক, ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ও ভোক্তাপুঁজির সাথে যুক্ত হয়েছে যেখানে বিপণন, বিক্রয় ও ভোগ উৎপাদনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বিমানবিকতা ও বিশ্বায়নের খপ্পরে পড়ে বহুজাতিক বিপণনের পক্ষে ব্যক্তি ও জাতিগত পরিচয় মুছে যাচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে উত্তরাধুনিকতাবাদ লায়োটার্ড, বদ্রিলার্দ, জেমারসন, হেবারমাস ও ফুকোর কাছে ঋণী। দেরিদার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নারীবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উত্তরাধুনিকতাবাদকে দেখা হয়েছে। একেবারে বাঁধা ছকের মধ্যে ফেলে এই দর্শনকে দেখার সুযোগ নেই, কারণ এখানে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এই তত্ত্ব নির্মাণে বহু বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।
উত্তরাধুনিকতাবাদ বাস্তবসত্যকে অস্বীকারের মাধ্যমে নির্মাণবাদী (constructivism) তত্ত্বকে অস্বীকার করেছে এবং সবকিছুই আদর্শিকভাবে নির্মিত এই ধারণাকে খারিজ করে দেয়। উত্তরাধুনিকতাবাদ বলে যে গণমাধ্যম আমাদের ‘পরিচয় নির্মাণে’ ও বাস্তবতা তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে। উত্তরাধুনিকতাবাদ বর্তমানের ইলেকট্রোনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রতি সক্রিয় সাড়া প্রদান করে এবং জগতের প্রাচীন পদ্ধতির বিবর্তন প্রত্যাশা করে। নির্মাণবাদ সবসময়ই আপেক্ষিকতার পথে হাঁটে। আমাদের পরিচয় নির্মিত হয় এবং সামাজিক পরিবেশসূত্রে বদলে যায়। আর তাই বহু ও বিচিত্র পরিচয়, নানাবিধ সত্য, নৈতিকসূত্র এবং বাস্তবতা ধারণের সুযোগ থাকে। বস্তুনিষ্ঠ সত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং উত্তরাধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী তার মাঝে ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রতিফলন থাকে। সত্যের অজ¯্র চেহারা রয়েছে তা গতানুগতিক। ব্যক্তির বিশ্বাস বা ধারণার ওপর নির্ভরতা বা প্রভাবিত হওয়ার অর্থ নতুন স্থানিক ও বিশেষ অভিজ্ঞতা বৈ আর কিছু নয়। আর তা মোটেও সর্বজনীন নয়, বরং বিমূর্ত। তা মহান-বৃত্তান্ত নয়, সীমিত বয়ান।
চূড়ান্তভাবে উত্তরাধুনিকতার সবকিছুর বিশ্লেষণে বিনির্মাণবাদের ওপর নির্ভর করে। উত্তরাধুনিকতাবাদ সবসময় সমালোচকের আক্রমণের শিকার হয়েছে। এই মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ‘অবিশ্বাস’ যা সমাজ ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা অস্বীকার করে। যেমন, এটা দাবি করা সহজ যে উপসাগরীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। কিন্তু অজ¯্র হত্যাকা-, উদ্বাস্তু মানুষের বেদনা, নির্যাতন ইত্যাদির ব্যাখ্যা কী? আমাদের দেশের একজন দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধী একদা দাবি করেছিলেন যে এদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এখানে কোনো গণহত্যা সংঘটিত হয়নি দাবি করে অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও তাদের দুষ্কর্মের এদেশীয় সহযোগীরা বিবৃতি দিয়ে আসছিল। তাহলে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির দালিলিক প্রমাণের ব্যাখ্যা কী? উত্তরাধুনিকরা মনে করেন ‘সত্য’ বলে কিছু নেই, আছে ‘সত্যসমষ্টি’। ইতিহাস (History) তাদের কাছে গল্প (Story)। প্রকৃত ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক। একটি ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আবার একটি ঘটনা না ঘটেও প্রকৃত সত্যের চেয়েও অধিক সত্য হয়ে উঠতে পারে। কখনো কখনো গল্পের সত্য সংঘটিত সত্য অপেক্ষা বেশি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।
উত্তরাধুনিকতাবাদ যাপিত জীবনের বড় শক্তি সংস্কৃতি সম্পর্কেও এক ধরনের গভীর হতাশাবাদী (cynicism) দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। যে শক্ত আদর্শিক ভিত্তির ওপর মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে উত্তরাধুনিকতাবাদ তাকে একবারেই খারিজ করে দিয়ে সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করে- যা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য জরুরি। শেষমেশ যখন তৃতীয় বিশ্ব ইউরোকেন্দ্রিক নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শুরু করলো তখন উত্তরাধুনিকতাবাদ ঘোষণা করল যে প্রান্তের ক্ষমতা সীমিত ও সাময়িক। যেহেতু ইউরোপ তার ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি, উপনিবেশগুলোর নতুন অর্জিত ক্ষমতাও টিকে থাকবে না।
সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিকতাবাদ যুক্তি ও বিজ্ঞান বিকাশের কাল (Enlightenment)-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বেশিমাত্রায় নির্ভর করেছে বিনির্মাণ, বিচূর্ণন, প্রশ্নবোধক বর্ণনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর। আধুনিকরা যেখানে একটি বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে একটি অর্থপূর্ণ শৃঙ্খলা খুঁজেছেন, উত্তরাধুনিকরা সেখানে খেলাচ্ছলে অর্থ খোঁজার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে গেছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে কৌতুক (parodz) করেছেন। সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও আত্মসচেতনতার প্রতি অবিশ্বাস উত্তরাধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য। বহু ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের একাধিক শাখার সংমিশ্রণ সাহিত্যের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হতো না। উত্তরাধুনিকতাবাদ বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্য সম্পর্কিত একটি umbrella term যা অ্যাবসার্ড নাটক, বিট জেনারেশন ও ম্যাজিক্যাল রিয়েলিজমকে অন্তর্ভুক্ত করে। স্যামুয়েল বেকেট, হোর্হে লুই বোর্হেস, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, নাগিব মাহফুজ, অ্যাঞ্জেলা কার্টার, মিলন কুন্ডেরা, উমবার্তো একো প্রমুখের লেখনীতে বৈশ্বিক বাস্তবতার ও অভিজ্ঞতার একটি জটিল অবস্থা অনুসন্ধানের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জীবনে সময় ও স্মৃতির ভূমিকা, সত্তা ও বিশ্বের ঐতিহাসিক নির্মাণ এবং ভাষার জটিল চরিত্র নিয়ে উত্তরাধুনিকরা নতুন মতাদর্শ সামনে তুলে এনেছেন।