মতামত » উপ-সম্পাদকীয়
লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যতের লাইব্রেরি
সাজ্জাদুল করিম
লাইব্রেরিতে এখন আর কেউ যায় না। প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে বই পড়ার সময় কোথায়। গুগল করলেই যখন সব কিছু হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় তখন কে আর কষ্ট করে লাইব্রেরিতে যায়? তাই বই পড়া একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ আর লাইব্রেরি তো এখন পুরোপুরিই অপ্রাসঙ্গিক। এরকম কথা এখন আমরা হর-হামেশাই শুনে থাকি। তাহলে সত্যিই কি লাইব্রেরি তার উপযোগিতা হারিয়েছে? ভবিষ্যতে লাইব্রেরি কি বিলীন হয়ে যাবে? এ কথার উত্তর আসলে এক কথায় দেয়াটা মুশকিল। তাই এই লেখার সূত্রপাত।
আচ্ছা, লাইব্রেরি বলতে আসলে কি বুঝায়? কবে থেকে এবং কেন এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হলো বা এর প্রয়োজনীয়তাই কেন উপলব্ধি হলো? সত্যি বলতে কী- লাইব্রেরির ইতিহাস অতি প্রাচীন। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মূলত যার সূচনা। নৃ-বিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী আদিম গুহাবাসী মানুষ যখন থেকে তাদের মনের ভাব, চিন্তা-কল্পনা গুহার দেয়ালে, পাথরে, মাটিতে, চিত্র ছবি বা সংকেত আকারে লিখে রাখতে প্রয়াসী হয় তখন থেকেই মূলত লাইব্রেরির যাত্রা। তার কারণ মানুষ তার লব্ধ ও সংগৃহীত জ্ঞান স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে রাখার তাগিদ থেকেই মূলত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে। আর মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা-জ্ঞান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা মূলত গুহাবাসী আদিম মানুষই শুরু করে (জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ, লিপির উৎপত্তি : প্রসঙ্গ কথা)। তাই আমার কাছে মনে হয় লাইব্রেরির ইতিহাস ও লিপির ইতিহাস সমার্থক যদিও পদ্ধতিগতভাবে সাজানো লাইব্রেরি বলতে আমরা যা বুঝি তার যাত্রা শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে নিনেবাহেতে (উত্তর ইরাকে অবস্থিত ইরাকের একটি প্রদেশ)। আসিরীয় রাজা আসুরবানিপাল যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি (খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫), নালন্দা মহাবিহার লাইব্রেরি (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক), পারগামাম লাইব্রেরি (খ্রিস্টপূর্ব ২৪১) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাচীন লাইব্রেরির কথা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি (মু. মনিরুল ইসলাম কনক, লাইব্রেরি : প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান)। তবে মজার বিষয় হচ্ছে প্রাচীন এই লাইব্রেরিগুলোতে কিন্তু এখনকার মত কাগজে মুদ্রিত বই বা অন্যান্য পাঠসামগ্রী থাকতো না। পোড়ামাটির ফলক, প্যাপিরাস, পার্চমেন্ট, ভেলাম, পাথর, গাছের পাতা, কাঠ ইত্যাদিতে খুদিত বা অংকিত পাঠসামগ্রী ছিল তখনকার লাইব্রেরির প্রধান উপকরণ (কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, বিবর্তনের ধারায় সমাজ, তথ্য ও গ্রন্থাগার)। এ থেকে বুঝা যায় যে, কাগজ-কলম আবিষ্কারেরও অনেক আগে লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়।
বাংলা পরিভাষা থেকে যদিও মনে হয় গ্রন্থ বা বইয়ের সংগ্রহশালাই হলো গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি তথাপি এ ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। তাছাড়া আমাদের সমাজে ‘লাইব্রেরি’ শব্দটির বেশ কিছু অপপ্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- লাইব্রেরি বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয় যারা বই ও স্টেশনারি মালামাল কেনাবেচা করে। আবার অনেকে লাইব্রেরি বলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অফিসকক্ষও বুঝে থাকে। কেউ কেউ মনে করে কিছু বই একসঙ্গে জমা করে রাখলেই সেটি লাইব্রেরি। আসলে এর কোনটিই সঠিক নয়, এগুলো নিছক ভুল ধারণা। লাইব্রেরি হলো- মানুষের
চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আচরণ, তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদির পদ্ধতিগত সংগ্রহ, সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে যাকে আমরা জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বলতে পারি; কিন্তু আমরা লাইব্রেরি বলতে সাধারণত কাগজে মুদ্রিত কিছু বই বা গ্রন্থের সংরক্ষণাগার হিসেবেই মনে করি। তাছাড়া লাইব্রেরিতে শুধু বই থাকে না এর পাশাপাশি সংবাদপত্র, সাময়িকী, অভিধান, বিশ্বকোষ, প্রতিবেদন, ছবি, ম্যাপ, প্রামাণ্যচিত্র, দলিল, নথি, পান্ডুলিপি, নকশা, ডিস্ক, কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইত্যাদিও সংরক্ষণ করা হয়।
প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পাঠসামগ্রীর ধরনও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে যা লাইব্রেরির ধারণা ও পরিধিকেও সম্প্রসারিত করছে। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী লাইব্রেরির কার্যক্রমেও প্রতিনিয়ত নতুনত্ব যোগ হচ্ছে, যা এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে।
এখন লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যতের লাইব্রেরি নিয়ে চলুন একটু ভাবা যাক। আমরা এতক্ষণ বলার চেষ্টা করেছি যে, লাইব্রেরি হলো জ্ঞান-নির্ভর প্রতিষ্ঠান; শুধু বই বা কাগজ নির্ভর কোন প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং আধুনিক এ সময়ে এসে কাগুজে বইয়ের ব্যবহার কমে যাওয়ায় আমরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করছি ‘লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে’ আমি তা মনে করি না। তার কারণ লাইব্রেরির সঙ্গে মূলত কাগজের নয়, জ্ঞানের সম্পর্ক। একারণেই আমরা দেখেছি কাগজ আবিষ্কারের অনেক আগেই লাইব্রেরির জন্ম। তাছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস ও সামগ্রী সংরক্ষণ ও বিতরণ পদ্ধতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল যা আমরা অতীতেও দেখেছি। সামনের দিনগুলোতেও লাইব্রেরির পাঠসামগ্রী, কার্যপদ্ধতি ও সেবার ধরনেও যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে যাচ্ছে তা চোখ বন্ধ করেও বলা যায়। তো কেমন হতে পারে আগামীর লাইব্রেরি চলুন কল্পনার ডানায় ভর করে একটু দেখে আসি।
প্রথমত, লাইব্রেরির গঠনগত পরিবর্তন হবে। যেমন- ই-লাইব্রেরি, ভার্চুয়াল লাইব্রেরি, অনলাইন লাইব্রেরি ইত্যাদি। অর্থাৎ লাইব্রেরির ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল সত্ত্বায় রূপান্তরিত হবে যা সময়, স্থান ও প্রবেশের সীমাবদ্ধতা দূর করবে।
দ্বিতীয়ত, লাইব্রেরির পাঠসামগ্রীও কাগজের পরিবর্তে নিত্য-নতুন বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে। যেমন- ই-বুক, অডিয়ো বুক, পডকাস্ট, অ্যাপ, অ্যানিমেশন, ভিডিয়ো, ডেটাবেইজ, ওয়েবসাইট, ব্লগ, সার্ভার, অনলাডনি রিপোজিটরি ইত্যাদি (এম নাসিরউদ্দিন মুন্সী, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও করণীয়)।
তৃতীয়ত, লাইব্রেরির অভ্যন্তরীণ কাজের ধরনেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে। যেমন- এআই, আইওটি, রোবোটিকস, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লাইব্রেরির নৈমিত্তিক কাজ ও সেবার ধরনে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটাবে (ক্লাউস শোয়াব, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব)।
সর্বোপরি, আমাদের আর্থ-সামজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, পরিবর্তিত পাঠক চাহিদা, পাঠোপকরণ ও পাঠাভ্যাস, তথ্যের মহাবিস্ফোরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে লাইব্রেরিতে প্রথাগত সেবার পাশাপাশি উদ্ভাবনী ও সময়োপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম যুক্ত হবে। যেমন- তথ্যকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন। দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান আয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক ও সচেতনতামূলক সেশন, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা ইত্যাদি।
লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের যে উদ্বেগ তা মূলত আমাদের অস্পষ্ট ও সংকীর্ণ ধারণা প্রসূত। লাইব্রেরি তার পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আমাদের মাঝে টিকে থাকবে আগামী দিনেও। কেননা লাইব্রেরি হারিয়ে যাওয়া মানে মানবসভ্যতা হারিয়ে যাওয়া; যেটি কোনভাবেই কাম্য নয়।
[লেখক : জেলা লাইব্রেরিয়ান, শেরপুর]
-
উড়াল দিচ্ছি চাঁদে
-
আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘাত
-
জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপির অস্বস্তি
-
নেশার কবলে গ্রামবাংলা
-
পুরনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না!
-
ভাষাপ্রকৌশল ও কালচারাল হেজিমনি: শব্দের আড়ালে ক্ষমতার রাজনীতি
-
ক্ষমতার ছায়া ও সমাজের আয়না
-
বই মেলার বোল কুমড়া
-
প্রসঙ্গ: খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল
-
নতুন সরকারের কঠিন সমীকরণ
-
ভাষাপ্রকৌশল ও কালচারাল হেজিমনি: শব্দের আড়ালে ক্ষমতার রাজনীতি
-
মানবদেহে রোজার সুফল
-
নিরাপদ সড়কের দাবি
-
ভাষা, স্বাধীনতা ও সাহিত্য : ইতিহাস থেকে সমকাল
-
অপাহাড়ি প্রতিমন্ত্রী ও শান্তিচুক্তি
-

মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন!
-
চেকের মামলায় ভুল ঠিকানায় নোটিস
-
শান্তির স্বপ্ন বনাম বাস্তবের দোলাচল
-

ভাষা আন্দোলন বাঙালির বিপ্লব ও আন্দোলনের ভ্যানগার্ড
-
বিয়ে রেজিস্ট্রি কেন জরুরি
-
ভাষা নিয়ে ভাসাভাসা কথা
-
বিএনপি পাস, জামায়াতও পাস
-
ব্যালট থেকে বাস্তবতায় বিএনপি
-

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: একুশের ইতিহাস, বিশ্বস্বীকৃতি ও আমাদের দায়িত্ব
-
ফুলের নিচে চাপা পড়া ভাষার আর্তনাদ
-
নতুন সরকারের কাছে পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা
-
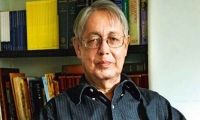
আন্দ্রে বেতেই : মানবিক সমাজবোধের অনন্য উত্তরাধিকারী
-
‘নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস’










