উপ-সম্পাদকীয়
শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ও প্রাথমিক শিক্ষা
সন্ধ্যা রানী সাহা
শিক্ষক বলতে আমরা সাধারণত নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্ব যিনি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করে থাকেন তাকেই বুঝে থাকি। কিন্তু এই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকই কি একমাত্র ব্যক্তি যার ওপর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ নির্ভর করছে! অভিভাবক (পিতা-মাতা-কাকা-মামা-প্রতিপালক ইত্যাদি) যে কত বড় শিক্ষক তা আমরা ভাষা শিক্ষার বিষয়টি একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারি। তারা ভাষা শিক্ষার কোনোরূপ নিয়মকানুন রপ্ত না করেও শিশুকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের ভাষাটি শিখিয়ে থাকেন। অথচ বিদেশি বা অন্য একটি ভাষা শিখতে কত কষ্টই না করতে হয়। কত যতœশীল হতে হয়।
সুতরাং অভিভাবক যে শিশুর প্রথম শিক্ষক এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আবার বিদ্যালয়ে যতক্ষণ শিশুরা অবস্থান করছে ততক্ষণ শিক্ষকরাই তাদের অভিভাবক। তাহলে মাতা-পিতা/অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক এরা সবাই বস্তুত শিশুর শিক্ষক এবং অভিভাবক বটে। অতএব এই উভয় প্রকার শিক্ষক এবং অভিভাবকের মধ্যে শিশু/শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সু-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা শিশুর উন্নত জীবন গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক।
বিদ্যালয়ে শিশুকে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার প্রারম্ভিক ভিত্তি হলো অভিভাবক প্রদত্ত নানাবিধ শিক্ষা। যাকে ভিত্তি করে শিক্ষক শিশুদের ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিতে থাকেন। তাই শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতাই একজন শিক্ষকের শিক্ষকতা করার জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবক প্রদত্ত নানাবিধ জ্ঞান এবং দক্ষতা শিক্ষককে তার পেশা পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। অভিভাবক কর্তৃক সম্প্রদানকৃত এ সহযোগিতার মমার্থ হলো শিক্ষকের মধ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে সমকক্ষতার উপলব্ধি সৃষ্টি। শিক্ষকদের এ উপলব্ধিই আবার বিদ্যালয় প্রদত্ত নানাবিধ শিক্ষা শিশুর জীবনে স্থায়ী করার জন্য অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করে থাকে।
বিদ্যালয়ে অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক আদর্শ বিকাশের জন্য, উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং যথাযথভাবে সামাজিকীকরণের জন্য যে শিক্ষা দেন তা অনুশীলনের ক্ষেত্র হলো মাতা-পিতা অভিভাবক পরিবেষ্ঠিত শিশুর বৃহত্তম জীবন পরিবেশ। গৃহ পরিবেশে অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের যদি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা অনুশীলনের সুযোগ না দেন তবে বিদ্যালয়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং শিক্ষক এবং অভিভাবকদের শিশু/শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পারস্পারিক সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক তাদের কাজ ও দায়িত্বের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের ধারাকে যে ত্বরান্বিত করতে পারে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।
শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক যখন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক কতটা কার্যকর আছে তা কিছুটা পরিমাপ করার সময় এসেছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধীসহ সকল শিশুকে একই শিক্ষক দ্বারা একই পরিবেশে এক সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষা দান করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য-দল (target-group) নয় বরং বাংলাদেশের যে কোনো শিশুর মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য সরকার কাজ করে চলেছে। প্রতি বছর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যালয় আকর্ষণীয় করা, নতুন ভবন তৈরি, ওয়াশ ব্লক তৈরি, ক্ষুদ্র মেরামত, বড় ধরনের মেরামত, শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান, খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান, ইত্যাদি সব প্রচেষ্টা জোরালোভাবে চলমান রয়েছে।
স্কুল-ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সব শিশুর ভর্তি (মারাত্মক রকমের শারীরিক অসুবিধাগ্রস্থ ছাড়া) নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্টজনদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সংকট যেন কাটছেই না। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে দুর্বল। মাত্র শতকরা ৮ (আট) ভাগ শিক্ষার্থী সিলেবাস বহির্ভূত “Kaniz reads in a Primary School, She goes to School everyday” এই ইংরেজি বাক্যটি পড়তে সক্ষম। বিদ্যালয় সমূহে ভর্তিকৃত সকল শিশুর প্রতিদিনকার উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় না। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণির দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৈরি করা হয় না।
পাঠ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট পাঠসমূহের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রণয়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না। যদিও প্রশিক্ষণকালে শিক্ষকরা তা ভালোভাবেই রপ্ত করে থাকেন। শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সাধারণের সঙ্গে (শিক্ষক, অভিভাবক, এলাকাবাসী, বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে) কার্যকর যোগাযোগ না থাকায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নানাভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে শিক্ষা নিরুপায় মানুষের সন্তানদের অজর্নযোগ্য থাকে না।
এমনো দেখা যায় যে, কোনো ক্লাসের ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র চার-পাঁচজন যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অঙ্ক কষে দিতে পারছে। শ্রেণীতে শিক্ষক, শিক্ষিত এবং ধনী অভিভাবকদের সন্তানেরা অর্থাৎ যাদের বাড়িতে শিক্ষা লাভের উপায় রয়েছে কেবল তারাই পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর প্রদান করতে পারে। এটা যেন ঠিক তেলা মাথায় তেল ঢালার মতো অবস্থা। এ অবস্থা চলতে থাকলে আজকের এই ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে সমবেত উদ্যোগে দেশের অভ্যন্তরীণ গ্রামীণ দারিদ্র দূর করার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ কি সফল হতে পারবে?
শিক্ষকদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিখন ফল অর্জিত না হওয়া এবং প্রতিদিনই বেশ কিছু শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষকবৃন্দ প্রকারান্তরে সেই অভিভাবককেই মূলত দোষারোপ করে থাকেন। তাদের ভাষায় অভিভাবকরা শিক্ষিত নয়, অসচেতন, পিতামাতার ডিভোর্স হয়েছে, দোকানে কাজে দিয়েছে, কোভিড-১৯ এর প্রভাব ইত্যাদি কথা বলেন। আমরা দেখেছি কোভিড-১৯ কালে উন্নত বিশে^র শিশুদের কিভাবে online-এ শিক্ষাদান করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষকগণের নগন্য সংখ্যক এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের সরকারও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছিলেন। সময়মতো বিশ^ এবং সরকারের সঙ্গে তাল না মেলানোর দায়ভার কার?
যাই হোক, আমাদের অভিভাবকরা তাদের শিশুদের শিক্ষা লাভ করানোর ইচ্ছায় বিদ্যালয়ে পাঠান। শিক্ষকগণ এবং সংশ্লিষ্ট তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষা-প্রশাসন নিয়োজিত উপজেলা শিক্ষা অফিসার-সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের অভিভাবকদের ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছাকে পেশাগত দায়িত্বের কারণে অবশ্যই মেলাতে হবে। না হলে সার্থকতা আসবে না। অভিভাবকদের বেশিরভাগ দারিদ্র বলে তাদের এবং তাদের শিশুদের এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। শিক্ষক এবং তৃণমূল পর্যায়ের পরিদর্শকরা সাধারণত শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপনের তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।
পরিদর্শকরা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের PTA (Parent-Teacher Associaion) নামক ১০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি আছে কিনা, থাকলে এ যাবৎ (এক বছরে) কতটি সভা হয়েছে; এতটুকু জানতে চান এবং নির্ধারিত ছকে সন্নিবেশিত করেন; কিন্তু এই কমিটি শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রিক কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে কতটা সক্রিয় তা পরিমাপ করেন না। যার ফলে বিদ্যালয় বাবদ SLIP (School Level Improvment Plan) ফান্ডে স্থানীয় অনুদান সাধারণত শূন্য (০) পাওয়া যায়। অথচ ৩৩ শতাংশ জমি দান করে স্থানীয়রাই সরকারকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এক সময় দেশের শিক্ষাকাজে সহায়তা করেছিল। আজকে PTA এবং SMC এর সভায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সকল সদস্য উপস্থিত হয় না। শিক্ষক অভিভাবক তথা এলাকাবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন যে সম্ভব নয় এ কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। এ সম্পর্ক স্থাপনে এখন থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
অভিভাবক যে শিশুর প্রথম শিক্ষক এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আবার বিদ্যালয়ে যতক্ষণ শিশুরা অবস্থান করছে ততক্ষণ শিক্ষকরাই তাদের অভিভাবক।
সরকার যতগুলো ইউনিয়ন ততজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করেছেন। তাদেরকে প্রথমত যথাযথভাবে কাজে লাগতে হবে। একটি ইউনিয়নে সাধারণত ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তাদের প্রতি মাসে ১০টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে উন্নয়নের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক। এ কাজে ১০ দিন ব্যয় হলে (সাপ্তাহিক ছুটির আট দিন বাদ দিয়ে) বাকি থাকে ১২ দিন। এই ১২ দিন তারা শিক্ষার্থীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীদের হোম ভিজিট এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সুসম্পর্ক রয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন। শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়কেই তারা বিদ্যালয় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ সব আর্থ-সামাজিক বিষয়ে উৎসাহিত করবেন। তারা শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।
শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জ্ঞান, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, উদ্যোগ গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। এই কোভিড-১৯ কালে বাল্য বিবাহের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য, কিশোর অপরাধ, ভেজাল শিশুখাদ্য বিপণন সহ নানা সমস্যায় মানুষ জর্জরিত। আমাদের শিক্ষিত এবং মেধাবী সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ এসব নির্মূলের জন্য কাজ করবেন। অর্থাৎ পুরোনো সমাজ থেকে এই বিশ^ায়নের যুগে চলনসই সমাজ বিনির্মাণের কারিগর হিসেবে কাজ করবেন সহকারী উপজেলা শিক্ষসা অফিসাররা। তাদের সহযোগিতা করবেন উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ উপজেলা প্রশাসনের সব কর্মকর্তা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ধারা ৬৩, তৃতীয় তফসিল এবং অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে one stop service প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরেরঅধীনস্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণকে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্ধারিত কক্ষে বসে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এ আদেশকে পাশ কাটিয়ে তারা উপজেলা শিক্ষা অফিসে অবস্থানের কারণে আমাদের শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশ, ম্যানেজমেন্ট কমিটি, একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি যেন শুধু একটা formality-তে পরিণত হয়েছে।
কার্যত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক, শিক্ষিত এবং সচেতন অভিভাবকদের সন্তান ব্যতিরেকে কেউ এগোতে পারছে না। এ অবস্থায় অভিভাবকরা সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে সে লক্ষ্যে বিগত ০৬/০৪/২০২২ খ্রিস্টাব্দ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে হস্তান্তরিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের (অপরাপর ৬টি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের অফিসের সঙ্গে) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্ধারিত কক্ষে বসে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে পুনরাদেশ প্রদান করা হয়। এটিকেও উপেক্ষা করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ উপজেলা শিক্ষা অফিসে বসেই অফিস করছেন। নিজ জেলায় চাকরি করার ফলে শিক্ষকগণের অনেকেই তাদের পূর্ব পরিচিত, বন্ধু এবং রক্তের সম্পর্ক/বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়। শুধু শিক্ষক নন সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি ইত্যাদি ব্যক্তিরাও তাদের আত্মীয়। এরা সাধারণত জেলা শহরে বসবাস করেন।
কাজেই গ্রামীণ জনসাধারণের সঙ্গে তাদের দূরত্ব সমুদ্র সমান। বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েও শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সহযোগিতা, শিক্ষক-অভিভাবক সুসম্পর্ক স্থাপন, বিদ্যালয়েরর জন্য নানাবিধ স্থানীয় সহযোগিতার আহবান জানানোর পরিবর্তে তারা আমলাতান্ত্রিক খবরদারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। অতএব অনতিবিলম্বে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের জেলার বাইরে বদলি নিশ্চিত করতে হবে। এদের স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যানদের আওতায় ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মনোন্নয়নে কাজ করতে বাধ্য করতে হবে। তবেই বাংলাদেশের সব শিশুর মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা সহজ হবে।
[লেখক : উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ]
-
জমি আপনার, দখল অন্যের?
-
সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস
-
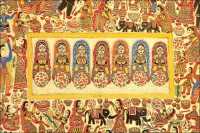
বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা
-
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান
-
তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া
-
দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা
-
খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত
-
আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?
-
প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ
-
ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়
-
রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’
-
ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?
-
সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব
-
প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক
-

বিকাশের পথকে পরিত্যাগ করা যাবে না
-
বর্ষা ও বৃক্ষরোপণ : সবুজ বিপ্লবের আহ্বান
-
প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধে শিক্ষকের করণীয়
-
পারমাণবিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক ভণ্ডামির প্রতিচ্ছবি
-
পরিবেশের নীরব রক্ষক : শকুন সংরক্ষণে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন
-
মশার উপদ্রব : জনস্বাস্থ্য ও নগর ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা
-
ভুল স্বীকারে গ্লানি নেই
-
ভাঙনের বুকে টিকে থাকা স্বপ্ন
-
একটি সফর, একাধিক সংকেত : কে পেল কোন বার্তা?
-
দেশের কারা ব্যবস্থার বাস্তবতা
-
ইসলামী ব্যাংক একীভূতকরণ : আস্থা ফেরাতে সংস্কার, না দায়মুক্তির প্রহসন?
-
রম্যগদ্য : চাঁদাবাজি চলছে, চলবে
-
বায়ুদূষণ : নীরব ঘাতক
-
ইসরায়েলের কৌশলগত ঔদ্ধত্য







