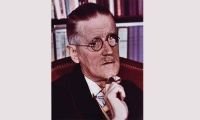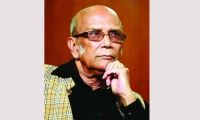মধুসূদনের সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদ
খসরু পারভেজ
সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮০৬-১৮৩৯) মধুসূদনের পূর্ব সময়ে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কোনো ইজম বা মতবাদ মধুসূদনকে আক্রান্ত করবে, এমন সুযোগ ঘটেনি। ফরাসি লেখক ও চিন্তাবিদ আন্দ্রে ব্রেঁতো (১৮৯৬-১৯৬৬) বলেছেন:
“আমাদের মনের স্বপ্নালোক তথা সমগ্র অবেচেতন মন আমাদের সাহিত্যে রূপলাভ করতে বাধ্য। সত্তা হলো যাবতীয় স্বপ্ন, সৃষ্টি, সম্ভাবনার স্বল্পতম অন্ধকার, যেখানে মানুষের চিরন্তন রূপকল্প, মিথ এবং তার মৌল প্রতীক অতি নিঃশব্দে কাজ করে।”
ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকেই ব্রেঁতো নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। লেখকের অবচেতন মনেই রূপায়িত হয় সাহিত্যের প্রতিমূর্তি। ভেতরে যা সঞ্চারিত, অনুরণিত, তাইই স্বতোঃৎসারিত হয়ে সাহিত্যের উপাদান হয়ে প্রতিভাত হয়। মধুসূদন জাতকবি। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি পুরাণাশ্রিত। তারপরও তাঁর অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। যার ভেতর ফুটে উঠেছে গভীর বেদনাবোধ, নৈঃসঙ্গ্য চেতনা। তাহলে মধুসূদন কি নৈরাশ্যবাদী নৈরাশ্যবাদ বা পেসিমিজম শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লেখক সেখানে অনেকটা অসহায়। নিৎসে যেমনটি বলেছিলেন-
“জীবনে পরিত্রাণহীন দুঃখ-যন্ত্রণাই নিত্যসঙ্গী। একে কেবল অতিক্রম করা যায় শিল্প-সংগীত দিয়ে।”
আলবেয়ার ক্যামু সেই কথায় ফিরে আসি- যেখানে তিনি বলেছেন, “মৃত্যুচিহ্নিত পৃথিবীতে জীবনের নিকটতম তুলনা শিল্প”। মধুসূদনের মতো আত্মপ্রবঞ্চিত, জীবনদহিত কবি পেসিমিজমে আক্রান্ত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।
পরাধীন ভারতের মাটিতে জন্ম নেয়া মধুসূদন স্বভাবতই ঔপনিবেশিক চেতনায় জারিত। যেখানে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা অনিবার্য, কিন্তু তা হতাশায় পর্যবসিত। জাতির আশা-প্রত্যাশা সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। মধুসূদনের সাহিত্যে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রচ- ইচ্ছাশক্তি,অদম্য আকাক্সক্ষা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে জীবনের বিচিত্র বন্দরে। একটি দীর্ঘশ্বাস, নৈরাশ্যবোধ তাঁকে পর্যুদস্ত করেছে বারবার। মধুসূদনের এই নৈরাশ্য তাঁর একার নয়, তাঁর সমাজেরও। মানুষ যখন বিচ্ছিন্ন হয়, বিছিন্নতাবোধ তাঁকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) এই বিচ্ছিন্নতাকে ত্যাগ করা, বিক্রি করা, অধিকার বিনষ্টের ভেতর চিহ্নিত করেছেন। তবে কাল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) হেগেলের ভাববাধী দর্শনকে অস্বীকার করে বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে এই বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা দেন। তাঁর ধারণা, ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা থেকেই বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব হয় এবং এই বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে নিক্ষেপ করে নৈঃসঙ্গ্যের অতল গহ্বরে। বিচ্ছিন্ন মানুষ তাঁর চেতনায় পোষণ করে ধ্বংসাত্মক মানসিকতার পাশাপাশি উত্তরণের আকাক্সক্ষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজে যে উত্থান, সেখানে অবক্ষয়ও ছিল, ছিল পুঁজিবাদের উত্থান, সম্পদ-সম্পত্তির বিকাশ, মোহ, তার পাশাপাশি মুক্তির আকাক্সক্ষা। মধুসূদনের মতো সৃষ্টিশীল মানুষ সময়ের এই দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতির শিকার।
ধনীপুত্র মধুসূদনের জীবন ছিল সমস্যা সংকুল। যতবারই তিনি সমস্যামুক্ত থাকতে চেয়েছেন; ততবারই হয়েছেন সমস্যাক্রান্ত। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক আর্থার শোপেন হাওয়ের (১৭৮৮-১৮৬০) এমনই মতবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, সম্পূর্ণরূপে সমস্যামুক্ত জীবন যারা কামনা করেছে, শেষপর্যন্ত তাঁরাই নৈরাশ্যবাদী হয়েছে। নৈরাশ্যবাদী মানুষ কখনও স্বাধীন নয়। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখব মধুসূদনের জীবনে এই নৈরাশ্যবাদ কতখানি আশ্রিত হয়েছে।
আকৈশোর ইংরেজি সাহিত্যের বড় কবি হওয়ার স্বপ্ন ছিল মধুসূদনের। ইংরেজি সাহিত্যে প্রচুর পঠন-পাঠন,পাশ্চাত্যের সাহিত্যদর্শন, সংস্কৃতির সংস্পর্শ তাঁকে তাড়িত করেছে ছাত্রাবস্থাতেই। অ্যালবিয়ানসের তীরে পৌঁছনোর জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হয়েছে কবিতায়:
দূর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিঃশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ;
নাহি সেথা আত্মজন; তবু লঙ্ঘি অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অ-নামা সমাধি।
জনক-জনকী-ভগ্নী আছে মোর; স্নেহ পরকাশি,
তারা মোরে ভালোবাসে; আমিও তাদের ভালোবাসি;
তবু ঝরে অশ্রু বেগে, হেমন্তের শিশিরের সম,
কাঁদি শ্বেতদ্বীপ তরে, যেন সেই জন্মভূমি মম।১
খুব সহজে শ্বেতদ্বীপে যাওয়া হয়নি মধুসূদনের। ইংরেজি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখে প্রশংসা পেলেও সফল হতে পারেননি। যে কাব্য লিখে তিনি ইংল্যান্ডের বড় কবিদের পাশে নিজের নাম লেখাবেন; সেই ‘ঞযব ঈধঢ়ঃরাব খধফরব’-এর পরতে পরতে কবির দীর্ঘশ্বাস। বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার আগে তিনি ইংরেজি ভাষায় অনেক কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতার দুই চারটি বাদে সবগুলো অতৃপ্তি, কান্না, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাসে ভরা।
একটা সময় মধুসূদন ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা ছেড়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন, মোহভঙ্গ ঘটেছে তাঁর। অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক নাটক ইউরোপীয় আদর্শে ‘শর্ম্মিষ্ঠা’ নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। একের পর এক তিনি রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যে গ্রিক আদর্শে লেখা প্রথম নাটক ‘পদ্মাবতী’; প্রথম সার্থক ট্রাজেডি ‘কৃষ্ণকুমারী’; সমকালীন ঘটনা নিয়ে প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’। নাটক-প্রহসন রচনার পাশাপাশি পরপর প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম গ্রন্থ ‘তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য’; নবতর চেতনার গীতিকাব্য ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’; বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ’; বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য ‘বীরাঙ্গনা’। প্রচ- আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহসকে ভর করে তিনি এগিয়ে গেছেন আলোকজ্জ্বল মঞ্চের দিকে। যশ-খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেও তাঁর জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোনোদিন বাসা বাঁধেনি। আশাহত, প্রেমাহত কবি ঘর বেঁধে, ঘর ভেঙেছেন। আভিজাত্য, প্রচুর অর্থোপার্জনের স্বপ্ন, ইউরোপীয় কবিদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লরেল মুকুট পরার আকাশচুম্বী প্রত্যাশায় বারবার তিনি হোঁচট খেয়েছেন। ঘুরপাক খেয়েছেন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির এক অস্থির টানাপোড়েনে। কাব্য-নাটকে তার ছায়াপাত ঘটেছে। কবির স্বপ্নালোকে, অবচেতন মনে সংঘটিত বেদনাবোধ প্রতিবিম্বিত হয়েছে রচনায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকে একটি ব্রাহ্মসংগীত রচনার অনুরোধ করলে তিনি লিখে দেন হাহাকার ধ্বনিময় ‘আত্ম-বিলাপ’। সমালোচকের ভাষায় যা “আগ্নেয়গিরির গৈরিক নিঃ¯্রাবের তুল্য অগ্নিময়ী-মর্মের অতলতল স্পর্শিনী অপূর্ব কবিতা।” যেখানে নিরাশার নদীতীর দাঁড়িয়ে তিনি বিলাপ করেছেন:
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
তাই ভাবি মনে
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,-
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না এ কি দায়!
এমন মর্মন্তুদ জীবনমথিত পঙ্ক্তিমালা মধুসূদনের আগে আর কোনো কবি রচনা করেছেন কিনা আমার জানা নেই।
মধুসূদনের ‘ব্রজাঙ্গনা’-এ রাধাবিরহ, ‘বীরাঙ্গনা’-এ প্রতিবাদের পাশাপাশি নারীদের আর্তি; ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে রাজকুমারী কৃষ্ণার বিয়োগান্তক পরিণতি- মহারাজ ভীমসিংহের অসহায়ত্ব- নিজ কন্যাকে হত্যার পরিকল্পনা; ‘শর্ম্মিষ্ঠা’-য় শর্ম্মিষ্ঠার নির্বাসন; ‘পদ্মাবতী’-তে রাজা ইন্দ্রনীলের রাজাসন ত্যাগ; এসব কিছুর মধ্য দিয়ে যে বেদনাবোধ, ট্রাজেডি প্রতিফলিত হয়েছে, সেখানে যেন লেখকের জীবনের বেদনাবোধ একাকার হয়ে যায়। আর শেষ নাটক ‘মায়া-কানন’-এ পাষাণ মূর্তির পাদদেশে রাজকুমারী ইন্দুমতী আর রাজা অজয়ের জীবনাহুতি যেন কান্নার কালি দিয়ে লেখা মধুসূদনের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবননাটকের এক করুণ পরিণতি।
বিলেত যাত্রার আগে মধুসূদন জন্মভূমি-জননীর কাছে গভীর আকুতি জানিয়েছেন তাঁকে মনে রাখবার জন্য। কী এক অপার বেদনাবোধ:
রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,- নাহি খেদ তাহে।
মানুষ মরণশীল, জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অনিবার্য। দেশ যারে মনে রাখে, দেশের মানুষ যারে মনে রাখে, মানবকুলে সেই তো ধন্য। কিন্তু কবির কী গুণ আছে, দেশ তাঁকে মনে রাখবে!
মধুসূদন ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে নিজের মননের সংযোগ সাধন করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন অনুশীলন তাঁর চেতনাকে শাণিত করেছে ঠিকই, কিন্তু জগতকে নিঃস্ব করে দেখার যে পাশ্চাত্য-প্রবণতা, ইউরোপীয় মিথে লালিত হতাশা, আত্মনিগ্রহ ও নৈরাশ্যচেতনা তাঁকে আক্রান্ত করেছে। পাশাপাশি প্রাচ্যের সাহিত্যে যে বিরহ-যন্ত্রণাবোধ, অপ্রাপ্তি, হাহাকার, যোজন-যোজনব্যাপী যে বিচ্ছেদী চেতনা সেটিও তাঁর সাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছে।
২.
মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য। পাশ্চাত্যের সাহিত্যাদর্শে তিনি এই কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন, বাঙালিও হয়েছে গর্বিত। হোমার (খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক)-এর ‘ইলিয়ড’; দান্তে (১২৬৫-১৩২১)-এর ‘ডিভাইন কমেডি’; ট্যাসো (১৫৪৪-১৫৯৫)-এর ‘জেরুজালেম ডেলিভার্ট’; মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪)-এর ‘প্যারাডাইস লস্ট’ এবং প্রাচ্যের অমর মহাকাব্য বাল্মীকি (খ্রিস্টপূর্ব চারশ শতক)-এর ‘রামায়ণ’; কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস (খ্রিস্টপূর্ব চারশত অব্দ)-এর ‘মহাভারত’-কে সামনে রেখে তিনি রচনা করলেন ‘মেঘনাদবধ’। চিরায়ত পুরাণ আর তাঁর ক্ষুরধার প্রতিভার অনবদ্য রসায়নে রচিত একাব্য মহাকাব্যের বীররস ধারণ করেও শেষ পর্যন্ত এক করুণ ও বিয়োগাত্মক বিষাদসিন্ধুতে পরিণত হয়েছে।
কাব্যের শুরুতে আমরা দেখি সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করলে রাবণপুত্র বীরবাহু নিহত হয়েছেন; সেই শোকে শোকাতুর রাবণ। দূতমুখে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁর বীরত্ব জাগরিত হয়েছে। প্রাসাদ শিখরে উঠে নিহত পুত্র ও যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে রাজসভায় ফিরে এসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছেন তিনি। বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদার আহাজারিতে শোকবিহ্বল রাজসভা। লঙ্কা টলে উঠেছে, গর্জে উঠেছে সাগর। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রমোদউদ্যান থেকে রাজসভায় ফিরে এসেছেন যুদ্ধংদেহী মেঘনাদ। এক ভাবগম্ভীর ও শঙ্কিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেনাপতি পদে তাঁর অভিষেক ঘটেছে।
‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে দেবতারা রামচন্দ্রের পক্ষে। দৈবশক্তির ষড়যন্ত্র বারবার রাবণকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। নিজ শক্তিতে বলিয়ান রাজা রাবণকে আমরা বিধির বিধানের প্রতি দেখি শঙ্কিত হতে। দৈবশক্তির চেয়ে মানবশক্তি অনেক বড়, এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা কাব্যে মধুসূদনই প্রথম প্রয়োগ করেন। কিন্তু ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে আমরা ব্যক্তি শক্তির উত্থান দেখি; দৈবশক্তির পরাজয়ও দেখি না। ব্যক্তিশক্তি বা মানবশক্তির যে উত্থান দেখি, তা সাময়িক। সীতাকে অপহরণের সময় আকাশযুদ্ধে জটায়ুুর পরাজয়ে রাবণের যে জয়, তা কি সত্যিকারের জয় অন্যদিকে সীতাহারা রাম বরাবরই দৈবশক্তির বলে বলীয়ান; তাঁর নিজস্ব কোনো শক্তি বা কর্তৃত্ব নেই, এটা স্পষ্ট। শেষ পর্যন্ত তাই রামের কাছে রাবণের পরাজয়ে প্রকৃতপক্ষে দৈবশক্তির জয় হয়েছে। মধুসূদন ভাগ্যবিড়ম্বিত। ভাগ্যান্বেষণে আজীবন তিনি ছুটে চলেছেন সোনার হরিণের পিছে। কাব্যে সেই দুর্ভাগ্যকে চিহ্নিত না করে উপায় থাকে না। অর্থ, যশ, খ্যতির জন্য মধুসূদনকে আমরা বারবার ভাগ্যের হাতে পরাজিত হতে দেখি। ‘কবিতার জন্য প্রয়োজনে পিতা-মাতাকে ত্যাগ করো’- আলেকজান্ডার পোপের এই সর্বনাশা পঙ্ক্তি তিনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। ধর্মত্যাগ করে গৃহচ্যুত হয়েছিলেন। সেটা কি পাপ ছিল ধর্মের ছকে পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মাদ্রাজে প্রিয়তমা স্ত্রী রেবেকা ম্যাকটাভিসসহ চার চারটি শিশু সন্তানকে ফেলে এসে কলকাতায় হেনরিয়েটাকে নিয়ে ঘর বাঁধার যে অধ্যায় তিনি রচনা করেছিলেন, তা অমানবিক তো বটেই; পাপ বৈকি! ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এ সীতাকে অপহরণ করে রাবণের যে পাপ, তা তাঁর গৌরব, প্রতিপত্তি, দম্ভকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এ যেন মধুসূদন নিজেই।
মধুসূদন আধুনিক জীবনযাপন করলেও, উন্নত চিন্তাকে লালন করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সামাজিক যে হতাশাবোধ, যে অমানবিক সংস্কার, তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যে মধুসূদন নারী স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়েছেন তাঁর সাহিত্য ও সংবাদপত্রে। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে মাদ্রাজ থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতা পর্যন্ত। সেই মধুসূদন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে মেঘনাদপতœী প্রমীলাকে বিধবা দেখাতে চাননি। যে কারণে মেঘনাদের শবযাত্রায় আমরা ‘পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে’- এই প্রত্যয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে প্রমীলাকে সহাস্যে চিতায় আরোহণ করতে দেখি। প্রমীলাকে মধুসূদন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন স্বামীর পাশে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য, সেই প্রমীলাকে চিতার আগুনে নিক্ষেপ করতে তাঁর দ্বিধা নেই, এ কোন মধুসূদন প্রসঙ্গত বলে রাখি, কাব্যে প্রমীলার আগে কোনো নারীর যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেনি। প্রমীলা যতখানি আধুনিক, ততখানি পশ্চাৎপদ; না হলে তাঁকে চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি, কেন মধুসূদন সংস্কারপন্থী, প্রথাবিরোধী মুক্তচিন্তার আধুনিক মানুষ, কিন্তু কাব্যে তিনি সংস্কার-প্রথায় বিশ্বাসী। এই বৈপরীত্য নৈরাশ্যবাদিতার পরিচয়কে নির্দিষ্ট করে।(সংক্ষেপিত)