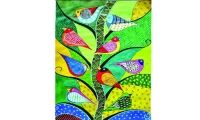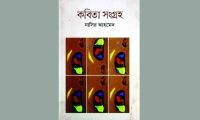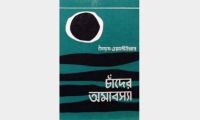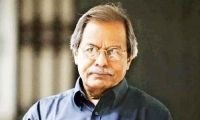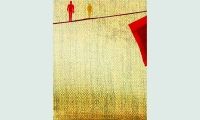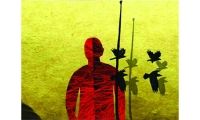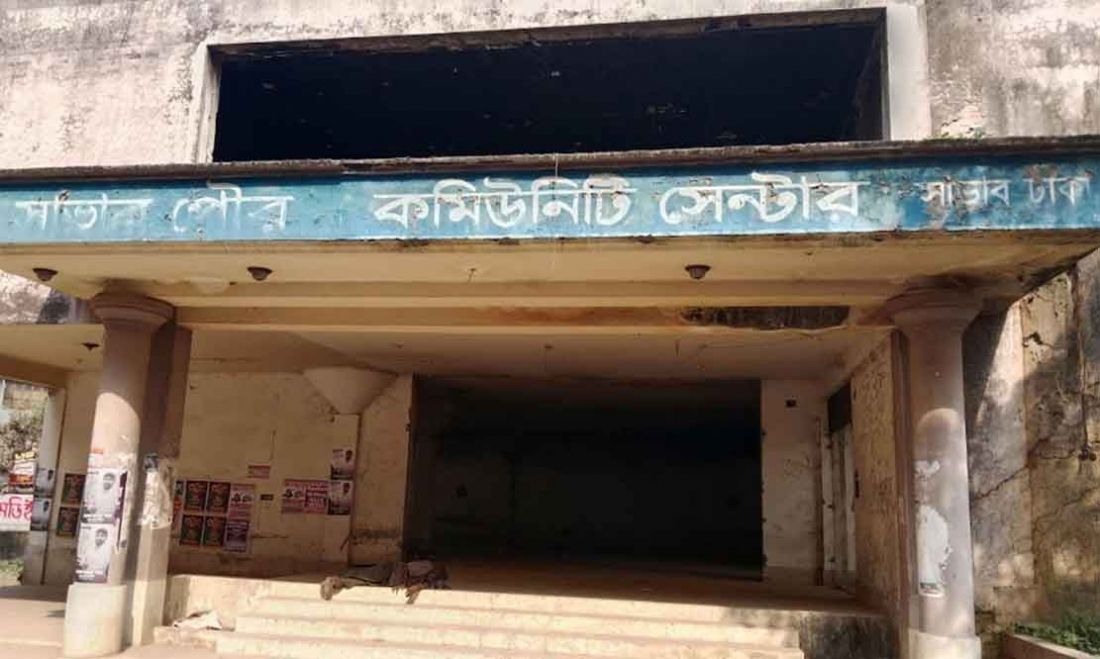দেশভাগের বিপর্যয় ও ‘জলপাইহাটি’র জীবনানন্দ দাশ
নূর-ই আলম সিদ্দিকী
কথাসাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথে আধুনিক কালে সৃষ্টি হয় উপন্যাস। বাস্তব জীবনের প্রক্ষেপণে লেখকের প্রজ্ঞার আলোকে প্রভাসিত এক জীবন-অভিজ্ঞানের নন্দন-ভাষ্য এই শিল্পরূপ। নির্দিষ্ট সমাজ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপ যখন ঔপনাস্যিকের প্রাণ-প্রাচুর্যময় জীবনবোধে অঙ্কিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে শিল্পিত প্রজ্ঞায় দীপ্তিমান। শিল্পির হাতে নির্মিত এ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয় দেশ, কাল, ব্যক্তি, সমাজ এবং তার পারিপাশি^ক যাপিত জীবনের সামগ্রিক প্রতিচিত্র। উপন্যাসের ভিতর ঔপন্যাসিক নিজের চোখে দেখা কালের রথে ঘটে যাওয়া মর্মন্তুদ ঘটনাকে শৈল্পিক নিবেদনে নিবিড়ঘন রূপ দেন। এ শিল্পাঙ্গিকের মধ্যে তাই দৃশ্যায়িত হয় শিল্পীর নিজস্ব জীবনের বর্ণিল শিল্পোশোভন আন্তর বিবিক্ষা।
রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক আলোচিত নাম কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলাভাষী মানুষের কাছে এ নামটি একটি ট্রাজিক নামও বটে। বিংশ শতাব্দীর বিপন্নকালে সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব। এ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তন হয়। দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, ভারতবর্ষের বিক্ষিপ্ত রাজনীতি, কালমার্কসের দর্শন এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিদ্যার প্রভাব মানুষের চেতনায় ঝড় তোলে। লেখক মাত্রই সংবেদনশীল সামাজিক মানুষ। সময়ের বুকে বহমান বাস্তব ঘটনা তাঁকে প্রেরণা দেয় আপন প্রতিভার নির্লিপ্ত সৃষ্টির অঙ্গীকার পরিস্ফুট করতে। ফলে রবীন্দ্রনাথের পথে না গিয়ে ভিন্ন এক পথে নোঙর করেন ত্রিশ দশকের লেখকরা। তাঁদের লেখায় সৌন্দর্য ও মানবতার পরিবর্তে জায়গা পায় ব্যর্থতা আর নিরাশা। কবি জীবনানন্দ দাশ এ লেখকদের সমগোত্রীয় কিন্তু তাঁর শিল্পভাবনার রূপায়ণ ‘আমি একা হতেছি আলাদা’পথে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সৃষ্টিজগত নির্মাণ করেছেন, ‘নতুন এক ভাব ও স্বপ্ন দিয়ে। তাঁর হাতে কথাসাহিত্যের পৃথিবী নির্মিত হয়েছে মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত জীবনের নানমাত্রিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দেশভাগে বিপর্যস্ত মানুষের বেদনাকে ঘিরে। ভারতবর্ষের ত্রিশ/চল্লিশ দশকের রাজনীতির ভয়াবহ ঘটনা জীবনানন্দের সংবেদনশীল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। একই সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের বিড়ম্বনায় তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনায় তোলে প্রচ- কাঁপন। মানসিক কষ্টে অস্থির ও বিচলিত এলেখক তাঁর উপন্যাসের ভিতর বিপন্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনবাস্তবতাকে শিল্পরূপ দেন অসামান্য দক্ষতায়। সাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশ উপন্যাস লিখেছেন দুই পর্বে। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসের সময়সীমা তিরিশের দশক এবং দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন চল্লিশ দশকে। আমাদের আলোচিত জলপাইহাটি উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪৮ খ্রি.। দেশভাগের অব্যবহিত পরে একই সময়ে প্রকাশিত হয় প্রবোধ কুমার স্যানাল রচিত উপন্যাস ‘হাসুবানু। দুটি উপন্যাসের মূল বিষয় দেশভাগের মর্মন্তুদ পরিণতি। যেখানে কাহিনির ভিতর দিয়ে চিত্রিত হয়েছে উপমহাদেশের বৃহত্তম ট্রাজিক ঘটনার দহন ও বীভৎসতা। জলপাইহাটি উপন্যাসের প্লট নিবিড় হয়েছে দুটি স্থানের ঘটনাকে নিয়ে। উল্লিখিত জায়গার একটি স্বাধীন ভারতের কলকাতা এবং অন্যটি হলো পূর্ব-পাকিস্তানের জলপাইহাটি গ্রাম। কাহিনিতে প্রতিফলিত হয়েছে দেশভাগের পরের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসংকট, কালোবাজারি কারবার এবং দেশভাগের কারণে মানুষের উদ্বাস্তু জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ নেমে আসে। লেখক শৈল্পিক দক্ষতায় সমসাময়িক সময়কে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। উপন্যাসের প্লট জটিল হয়ে এগিয়েছে দাম্পত্য সমস্যা, যুদ্ধ তাড়িত মানুষের অসহায়তা, রাজনীতির উত্তাল হাওয়ায় বিপর্যস্ত সমাজ এবং ছিন্নমূল মানুষের মানবিক অবক্ষয়ের ক্লেদাক্ত কর্মকা-ে। আরো আছে নর-নারীর জটিল সম্পর্কের রসায়ন। উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় দিক হলো উন্মূল মানুষের আর্থনীতিক সংকট যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তির অন্তর্মুখী অবনমন। চল্লিশ দশকে অর্থ-মন্দার কবলে পড়ে পূর্ব-বাংলা। এ-বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে জলপাইহাটি গ্রামের বাসিন্দারা একে একে পার হতে থাকে ওপার বাংলায়। উপন্যাসের নায়ক নিশীথ জলপাইহাটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। দীর্ঘ চব্বিশ বছর এ কলেজে চাকরির পরও সংসারের দারিদ্র্র্য ঘোচেনি তার। শুধু তাই নয় কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পায়নি যোগ্য সম্মান ও আর্থিক আনুকূল্য। বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিশীথও অর্থিক সুবিধা ও সম্মানের আশায় পাড়ি জমায় কলকাতায়। পেছনে পড়ে থাকে অসুস্থ্য স্ত্রী সুমনা ও দুই মেয়ে ভানু ও রানু। দেশভাগের বিপাকে পড়ে সে সময়ের মানুষ যে দিশেহারা হয়ে যায় নিশীথ চরিত্রটি তার জীবন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশভাগ চোখের নিমিষে পারিবারিক জীবনকে করে অনিশ্চিত। স্বামী নিশীথের স্বাধীন দেশে দেশত্যাগের অভিপ্রায়ে স্ত্রী সুমনা তাই ক্ষিুব্ধ মনে বলে ওঠে, ‘স্বাধীন হয়েও শান্তি নেই। ছেলেমেয়েগুলোর এই দশা। উনি কলেজটাকে এক পাশে ফেলে জলপাইহাটির ঘর ভেঙ্গে চলে গেলেন যা নেই তার ভিতর হারিয়ে যেতে। বড্ড বেকায়দায় পেয়েছে দেশের স্বাধীনতা আমাদের কজনকে। ‘দেশভাগ কীভাবে মানুষের জীবনকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেয় উপন্যাসিক নিশীথের জলপাইহাটি ত্যাগের ভিতর দিয়ে তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। নিশীথের এই চলে যাওয়া শুধু সম্মান আর আর্থিক নিশ্চয়তার জন্য নয়। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে বিপরীত ভাবনা ক্রিয়াশীল জীবনানন্দ দাশ সেটিও তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায়। দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে প্রত্যাশার বিপরীতে নতুন সংকটের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়ে নিশীথ। যে বন্ধুদের উপর ভরসা করে সে কলকাতায় আসে তারাও তাকে নানাভাবে অযোগ্য প্রমাণ করে। নিশীথ কলকাতায় যে তিনজন অধ্যাপকের কাছে আশ্রয় নেয় তারা তার পূর্ব পরিচিত। কলকাতায় পরিচিত তিন বন্ধু আজ আজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। পোড় খাওয়া নিশীথ বুঝে যায় তাদের এই উন্নতি কলকাতায় দীর্ঘদিন থাকার কারণে হয়নি বরং তিনজনের ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে বৈশ্বিক বুদ্ধি ও সুযোগ সন্ধানী প্রবৃত্তির কারণে। দেশভাগের কারণে উৎসাদিত মানুষ কলকাতায় এসে নিজেদের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে মান-সম্মানের দিকে না তাকিয়ে হীনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ তিন অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যে নীতিহীন সমাজের অনৈতিক উপায়ে ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতি আমাদের ইঙ্গিত করেছেন। যারা সবকিছু ছেড়ে শূন্য হাতে এসেছিল কলকাতা শহরে। আজ সময়ের অনুকূলে পা ফেলে নিজের অবস্থান করেছে সুদৃঢ়। ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয় নিশীথের ভিতর। মনের গহীনে অনুভব করে,‘যারা নীচে পড়ে আছে, ঠিক সময় ঠিক কাজ করতে পারেনি, দেরি করে ফেলেছে, সময়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি, তারা কুড়ি-পঁচিশ পার করে আজ একটা অদ্ভুত পৃথিবীতে পাক খাচ্ছে।’আমরা বুঝতে পারি এই কাতরতা শুধু নিশীথের একার নয় বরং ছিন্নমূল সকল মানুষের। দুরবস্থার চরম মুহূর্তে কলকাতার ব্যক্তিস্বার্থ জীবনে নিশীথ নিজেকে আবিষ্কার করে একজন ব্যর্থ মানুষ হিসেবে। দীর্ঘ সময় প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধ করে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্তগ্রামে ফিরার সিদ্ধান্ত নেয় নিশীথ সেন। কিন্তু ততদিনে স্ত্রী সুমনা পারনিসাস এনিমিয়ায় আক্রান্ত রোগে মৃত্যু পথযাত্রী। কন্যা ভানুও থাইসিসে রোগে হাসপাতালে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় গুনছে। ছোট মেয়ে রানু প্রতিবেশী যুবক নরেন মিত্তির যৌন লালসার শিকার হয়ে নষ্ট পথে হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে পুত্র হারীত স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হয়ে কাক্সিক্ষত স্বাধীনতা অর্জন না হওয়ায় গ্রামে ফিরে এসেছে। এবার সে মনোনিবেশ করেছে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর উন্নতির ভাবনায়। মর্মভেদী যাতনা আর নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পেতে গ্রামে ফিরে আসে নিশীথ সেন। আমরা কাহিনিতে দেশভাগ সময়ের ছাপ সুস্পষ্ট লক্ষ্য করি কিন্তু তাকে নিয়ে কোনো মনোবিক্ষোভে আন্দোলিত হতে দেখিনা নিশীথ ও হারীতকে। দেশবিভাগের কারণে জীবনানন্দ দাশ জন্মভূমি ত্যাগ করেন। আর্থিক সুবিধার জন্য চাকরি নেন এবং অবস্থা পরিবর্তন না হওয়ায় তা ছেড়েও দেন। কিন্তু এ নিয়ে উপন্যাসে কোনো জটিলতা আমরা দেখতে পাইনা। ফলে কাহিনিতে শৈল্পিক নিরাসক্তি দেখাতেও লেখক পুরোপুরি সার্থক হয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সবকিছু হারিয়ে দেশে ফিরে অসহায় নিশীথ প্রতিবেশী মেয়ে সুলেখাকে বিয়ে করে মুক্তির কথা ভাবতে থাকে। পিতা নিশীথ আর পুত্র হারীতের মধ্যে সুলেখাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ইডিপাস কমপ্লেক্ষ। এই সুলেখার সঙ্গে হারীতের সুসম্পর্ক ছিলো একসময়। প্রায় চারশো পৃষ্ঠার উপন্যাস জুড়ে আমরা দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব না দেখলেও দেশবিভাগের অভিঘাতে মানুষের সীমাহীন কষ্টের শিল্পিত সত্যকে খুঁজে পাই। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিশীথ সেন যার মধ্যে আমরা জীবনানন্দকেই প্রত্যক্ষ করি। যিনি নিজের নির্জনতা ও নিশ্চেতনার জন্য বার বার ডুব দেন নিজের মধ্যে। বিরূপ ও প্রতিকূল প্রতিবেশে নিজেকে আড়ালের জন্য শৈল্পিক নিবেদনে কাটাছেঁড়া করেন বার বার এবং প্রতিবার। সেই ভাবনার স্বরূপ উপলব্ধির যন্ত্রণাবোধ থেকে জলপাইহাটি উপন্যাস। যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমালোচক বলেন, ‘জলপাইহাটিতে দেশবিভাগজনিত বিপুল বেদনা রয়েছে অন্তঃশীল হয়ে। আবার এও তো মনে হয় শুধুমাত্র দেশবিভাগ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য নয়। দেশ বিভাগ একটি উপাদান মাত্র, চল্লিশের দশকে পৃথিবীব্যাপী যে ক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই শতাব্দীর এক মহৎ কবি, তাই-ই তো এই উপন্যাসের নানান স্তরে নানান ভাবে এসেছে। চালচিত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খ-িত বঙ্গ, স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের বিধ্বংসী চেহারা, মৃত্যু, ধ্বংস সব-ই রয়েছে।’