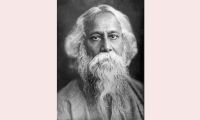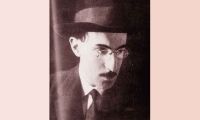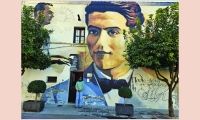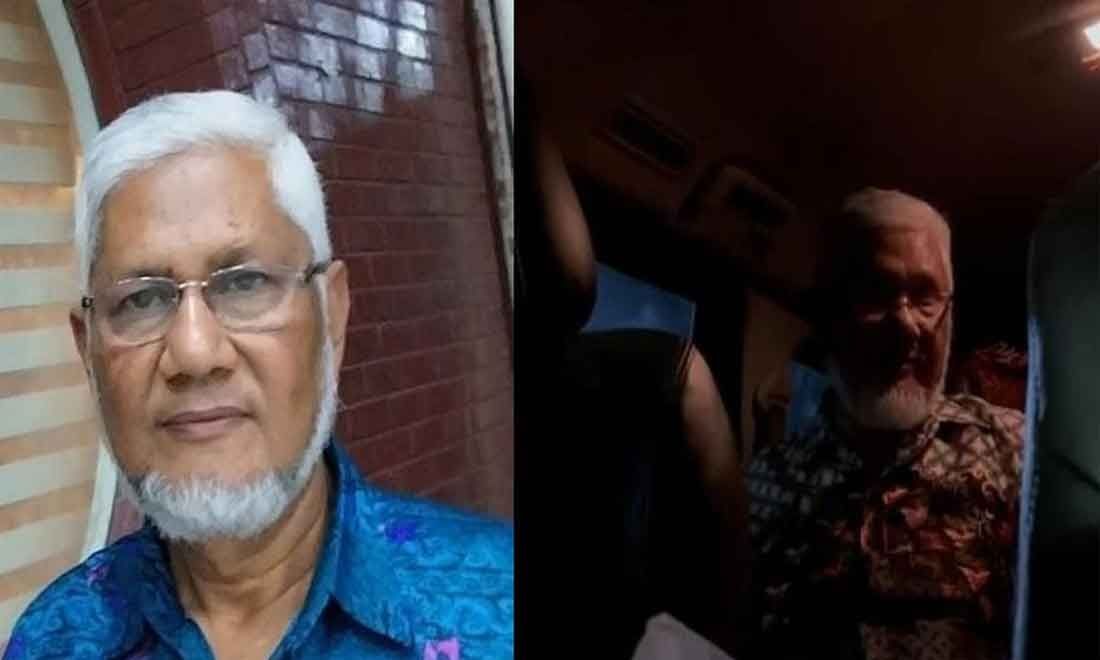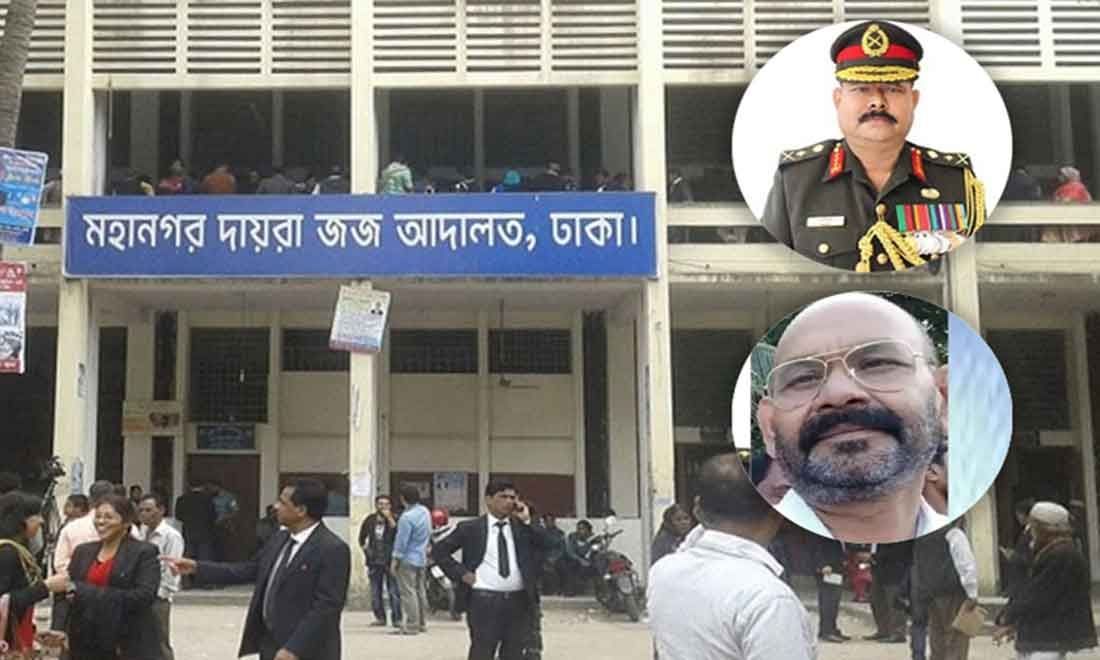ধূসর পাণ্ডুলিপি পরিবহন
পিয়াস মজিদ
করুণ মাল্যবান
রবীন্দ্রনাথের কাছে সে চিত্ররূপময়।
বুদ্ধদেব বসুর কাছে নির্জনতম কবি।
আবদুল মান্নান সৈয়দের কাছে শুদ্ধতম কবি।
অম্বুজ বসুর কাছে নক্ষত্রপ্রতিম।
আমার জীবনানন্দ সকল সংজ্ঞাতিক্রমি।
চিত্র নির্মাণ করে পরক্ষণেই চিত্রের ঘেরাটোপ ভেঙে এক সারিতে দাঁড় করায় যে রূপসনাতন আর অরূপরতনকে তাকে কি কেবল ‘চিত্ররূপময়’ অভিধাভুক্ত করে রাখা যায়? আমি তো তার কবিতায় শুনি ইতিহাস-ভূগোলের আবহমান কাকলি। তবে তাকে ‘নির্জনতম’ বলি কেমনে? আমি তো তার কবিতায় শুদ্ধ কল্পনা আর চূড়ান্ত বাস্তবের ভেদ লুপ্ত হতে দেখি। তাই তাকে ‘শুদ্ধতম’ সম্বোধনে খ-িত মনে হয়। আমি তো তার কবিতায় জ্যোতির পাশাপাশি দেখি তমসের দীপ্তি। তাই তাকে নক্ষত্রের সীমানায় বাঁধতে পারি না।
এমনই আমার জীবনানন্দ। কলকাতায় বা বরিশালে বসে চৈতন্যে ধারণক্ষম বেবিলন, লিবিয়া কিংবা সিংহল। মাটিতে বসে অনুভব করে যে নক্ষত্রের আয়ুক্ষয়। যার কবিতায় তারার পাশে চুপচাপ শুয়ে থাকে তিমির। বেলার পিছে দাঁড়িয়ে থাকে কালবেলা।
জ্যোৎস্নার ভেতর সবাই ভূত দেখে না। যে দেখে সে-ই জীবনানন্দ। পৃথিবীতে যার কোনো বিশুদ্ধ চাকুরি নেই সে-ই জীবনানন্দ। যখন সবাই স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর তখন নরকের নবজাতে মেঘের দিকে প্রব্রজ্যা যার সে-ই জীবনানন্দ। জীবনের রাত্রিভোর কারুবাসনা যাঁর সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দেয় সে-ই জীবনানন্দ। ট্রামনিয়তি গ্রহণ করে যে শম্ভুনাথ প-িত হাসপাতালে ধুঁকে ধুঁকে মরে যায় সে-ই জীবনানন্দ। পৃথিবীতে ঢের শালিকের ভিড়ে যে জনমভর অজ্ঞাত তিনটি শালিক খুঁজে ফেরে সে-ই জীবনানন্দ।
চারদিকে কত মাছের কাঁটার সফলতা, কত সোনাদানা! এর কোথাও আমার জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ নিদ্রার ভেতর সংঘারাম জেগে থাকলে যে যুগপৎ বর্তমান ও আটবছর আগের কোনো একদিনে বিচরণ করে একমাত্র সে-ই জীবনানন্দ। অর্থ কীর্তি কিংবা সচ্ছলতা নয়; বিপন্ন বিস্ময়ের সূত্র জানা যার সে-ই জীবনানন্দ।
আমার জীবনানন্দ জগতের যাবতীয় সুতীর্থে খাপ না খাওয়া এক করুণ মাল্যবান মাত্র।
এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কি না
এইখানে সরোজিনী শুয়ে থাকে। এইখানে সরোজিনী শুয়ে থাকে না।
মহাপৃথিবীর এইসব দিনরাত্রিতে আমাদের যে অধিবাস তাতে সবারই অন্বিষ্ট জিজ্ঞাসার স্থির উত্তর। কিন্তু জীবন তো এই ছকের চুরমার। জীবন এক অমীমাংসিত সরোজিনী যেন। যার অস্তিত্ব একই সঙ্গে জাগ্রত ও বিলীন।
বাংলা কবিতা যখন অন্ধকারভেদী ‘আলো, এতো আলো’তে নিমজ্জিত তখন জীবনানন্দ দাশের করতল থেকে বেরিয়ে এলেন সরোজিনী দেবী। তিনি শেখালেন জোর করে আলো আনা যায় না। মানুষমনের তমস-পরিসর চাইলেই গুঁড়িয়ে ফেলা যায় না। বরং সংশয়ী হাওয়া এসে সাজানো বাগান এলোমেলো করে দেয়। তখন বিষম ধন্ধে পড়ে যাই। এই সরোজিনীকে দেখি তো এই দেখি না। অবচেতনা বলে একে উপেক্ষা করাও নিরর্থ কেননা এর মতো খাঁটি চেতনা আর কিছু হয় না। চেতনা তো আর অশ্বডিম্ব নয়; আমার মনোলোকেরই প্রতিভাস সে। সুতরাং সরোজিনীর শয়ন-পরিস্থিতিই এখন আমার চেতনা।
জীবনানন্দের পূর্বের কোনো কবি আঁকলে নিশ্চিত সরোজিনীকে আঁকতেন পরি হিসেবে। কিন্তু জীবনানন্দের বলেই সরোজিনী মানুষী। জীবনানন্দের বলেই সরোজিনী ফাঁপা মুক্তির গান গায় না। জীবনানন্দের বলেই সরোজিনী আমাকে এমন সত্যের মুখোমুখি করে যে, দুঃসহ দেবতাজন্মের হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি। নিতান্ত মানুষজন্ম আমার। দেব হলে জেনে যেতাম এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে কি না। সব রহস্য তো শেষ হয়ে যেতো তৎক্ষণাৎ।
কিন্তু দেবতা না, রক্তমাংসের এক মানুষ বলে আমি জানি আবার জানিও না সরোজিনী ঠিক কোথায়। আর এই ধাঁধাটি আছে বলেই তো রহস্যের রেশমি গিঁট খোলার অপেক্ষায় বেঁচে থাকি।
জীবনানন্দ যাপন
মনে আছে গত শতাব্দির কথা। ১৯৯৯-একটি শতাব্দি এবং সহ¯্রাব্দও যখন হেলে পড়েছে নতুন এক সহ¯্রাব্দ -শতাব্দির দিকে। জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষের বছরও বটে।
কুমিল্লায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উৎসাহী সদস্য আমি; ইতিহাস দর্শন সাহিত্যের গভীর সব পাঠচক্রের নিয়মিত শ্রোতা। বুঝি না বুঝি, শুনে যাই শুধু। শ্রুতির ভেতর ঢুকে পড়ে মিনার্ভার পেঁচার দীপ্ত উড়াল কিংবা চারবাক দর্শনের আহত ডানা, আধুনিক কবিতার হাড়গোড়, প্রথাভাঙা আখ্যানের ধড়। এরই মাঝে আড্ডার কোনো এক অগ্রজ বাংলা একাডেমির উত্তরাধিকার পত্রিকার ঢাউস জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা হাতে নিয়ে আসেন ঢাকা থেকে কুমিল্লায়। উল্টে-পাল্টে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। এত সব অনন্য শিরোনামের লেখা আর লেখার সাথে চিত্রকরদের আঁকা অভিনতুন যত ছবি। মনে আছে সংখ্যাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় রীতিমতো। বয়সে ছোট বলে আমি এর ভাগ পাই বহু পরে। ততোদিনে কবি আরিফ হাসান রাণীর দীঘির পাড়ে বসে সমুখের নারকেলবীথিতে সমাগত সন্ধ্যার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ান- “সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয় / কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি...”
বুঝি এ এক অন্যতর কবি, অন্যতর তার ভূমি ও আকাশ, জল ও পাতাল।
লালাপুকুর পাড় বলে এক এলাকায় কোনো এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে তার বাসায় গেলাম এক দুপুরে। সবাই যখন শেষকৃত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ভীষণ আমার তখন বারবার চোখ যাচ্ছিল সে বাড়ির ছোট্ট বুককেসে রাখা এক মায়াময় বইয়ের দিকে, শুদ্ধতম কবি, লেখক- আবদুল মান্নান সৈয়দ। তখনও জানিনা কে এই ‘শুদ্ধতম কবি’! পরে জানা হলো জীবনানন্দ দাশ। এ বইয়ের লেখক মান্নান সৈয়দের সঙ্গে বছর কয়েক বাদেই যে স্থাপিত হবে নিবিড় যোগাযোগ- তা কি জানতাম তখনও!
শহর কুমিল্লায় দেখেছি শান্তনু কায়সারকে। তাঁর এত এত বইয়ের মধ্যে আমার বিশেষভাবে ভালো লাগতো এই বইটির নাম- গভীর গভীরতর অসুখ গদ্যসত্তার জীবনানন্দ। গদ্যের বিপুল সম্ভার যে অনাদৃত স্বর্ণস্তূপের মতো জমা ছিল মরচে পড়া সব ট্রাঙ্কের ভেতরে- সে তথ্য জেনে চমকে উঠেছি আর ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেছি তার গদ্যের গহন অরণ্যে।
একুশে বইমেলা থেকে কিনে মাহবুব মামা আমার বোন রূপাকে উপহার দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। আমার বোন সে বই পড়তো কি না জানিনা তবে আমি পড়তাম প্রায়শই, বুঝে বা না বুঝে। তখন বিদ্যমানে বসত করেও হারিয়ে যেতাম দূর পৃথিবীর গন্ধে, চলাফেরার ধূসর রাস্তা তখন হয়ে উঠতো সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে সবুজ, সবচেয়ে সুন্দর। তারপর আদালতপাড়ার সরকারি পাঠাগারে পেলাম মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র।
কুমিল্লা থেকে পত্রিকা বেরুত, এখনও বের হয় দৈনিক রূপসী বাংলা। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক- কবি আবদুল ওহাব। কবি বলেই হয়তো পত্রিকার নাম রেখেছেন এমন। জীবনানন্দের বইয়ের নামধারী এই পত্রিকাতে প্রকাশিত আমার প্রথম কবিতার নাম ছিল ‘জীবনানন্দ দাশকে কিছু প্রশ্ন’। সংরক্ষণে নেই এখন কিন্তু অন্তর্গত বয়ানটি মনে আছে আজও- রূপসী বাংলা হেজে মজে গেছে, বনলতার সেনরা পথে পথে নির্যাতিত- এইসব দেখে শুনে আপনি কেমন আছেন জীবনানন্দ? এমন জিজ্ঞাসা জাতীয় কিছু একটা ছিল সে কবিতাচেষ্টা।
তারপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জীবনানন্দকে পেলাম একান্ত অনুভাবনে, বিশদে-বিস্তারে। এখানকার প্রকৃতি, সকাল-সন্ধ্যা, দুপুর-বিকেল আর রাতের কড়ানাড়ার ভেতর চুপটি করে বসে পেতাম জীবনানন্দকে, তার সপ্তসিন্ধু এবং দশ দিগন্তকেও। একই ক্যাম্পাসের সৃজনী প্রতিবেশী মোহাম্মদ রফিক জীবনানন্দ নিয়ে একেবারেই ভিন্ন আঙ্গিকের একটি বই লিখলেন, সেলিম আল দীন লিখলেন ‘রূপসী বাংলার ভূমিরেখা’ নামের অনন্য-উন্মোচক এক গদ্য। তাঁদের লেখার ভাবনারেখাও আমাকে ছুঁয়ে গেছে ভীষণ।
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বেকার আমি ঢাকার রাস্তায় হাঁটছি উদ্দেশ্যহীন। হঠাৎ কবি বেলাল চৌধুরীর ফোন, জীবনানন্দগ্রস্ত কবি-লেখক, সম্পাদক ডা. ভূমেন্দ্র গুহ বক্তৃতা দেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে। আমি ভাবলাম জীবনানন্দের চিকিৎসা বিষয়ে কিছু বলবেন কিন্তু গিয়ে শুনি ভারতবর্ষে শল্যচিকিৎসার আদিঅন্ত বিষয়ে বলছেন তিনি, জীবনানন্দের কথা সেখানে একেবারেই আসেনি। তবু ভূমেন্দ্রের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির উড়ে আসায় আমি যেন আসতে দেখলাম আমার জীবনানন্দকেও, হয়তো এই শ্বাসে মিশে আছে ১৯৫৪-এর অক্টোবর-প্রান্তিকের তার বিদায়বেলার শ্বাস। ভূমেন্দ্র গুহের মতো ময়ূখ গোষ্ঠীর তরুণরাই তো শুশ্রƒষার দীপ হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার জীবন- অন্ধকারে।
গল্প লিখবো ভাবিনি কখনও। এক সকালে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ঢাকা ফিরছি বাসে। অসহ্য যানজটে বন্দি যাত্রাবাড়িতে, বাসের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি- ‘বনলতা হোটেল’; হঠাৎ মনে হলো ভেতর-গোঁজা জীবনানন্দ কতভাবে বিস্তারিত এই ঢাকায়! মাথার খাতাতেই যেন লেখা হয়ে গেল ‘নগর ঢাকায় জনৈক জীবনানন্দ’ গল্পটি। প্রকাশ হলে আশাতীত পাঠপ্রতিক্রিয়া পেয়েছি, দু’দুজন পরিচালক টেলিছবি করার প্রস্তাব নিয়ে এলেন। শেষ পর্যন্ত এই নামে টেলিছবি করলেন আশুতোষ সুজন, প্রচারিত হলো চ্যানেল আইয়ে- একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করতে হলো আমাকেও।
এতটা তো আমি ভাবিনি। আর এতটা বিষয়নির্ভর গল্পও আমি লিখতে চাইনি। আমি চেয়েছি মনের ভেতরকার নির্জন মিছিলের ছবি গল্পের ভাষায় আঁকতে, এই সময়ে বসত করেও চিরসময়ের আখ্যান বুনে যেতে। তবু জীবনানন্দের হাত ধরেই আমার হাতে লেখা হলো এমন একটি বিষয়নির্ভর অজীবনানন্দীয় গল্প। পরে নগর ঢাকায় জনৈক জীবনানন্দ শিরোনামেই প্রকাশিত হলো আমার প্রথম গল্পের বই। যে জীবনানন্দ আমার কাছে ছিল বিজন উদ্যাপনের বিষয়, সে চলে এলো এতটা প্রকাশ্যে আমার। আসুক, জীবনানন্দই তো আমাদের সমূহ অপ্রকাশের ভার।
জীবনানন্দের জন্ম ও মৃত্যুভিটেয়
২০০৮-এর শীতবেলা। জীবনানন্দ-পরবর্তী কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃভিটে মাদারীপুরের মাইজপাড়ায় গিয়েছিলাম বন্ধু সাব্বির আহমেদ সুবীর এবং আমি। ফেরার পথে বরিশাল হয়ে ঢাকা আসা সাব্যস্ত হলো।
বরিশাল যাবো আর জীবনাননন্দে যাবো না তা কি হয়?
বগুড়া রোড। আমি আর সুবীর। দুপুর হয় হয়। এক্কেবারে জীবনানন্দীয় প্রহর।
বাড়িতে ঢুকতেই জীবনানন্দ গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের ফোন- যিনি তখন পর্যন্ত বরিশাল আসেননি। আমি জীবনানন্দের ভিটেয় শুনে বললেন ওখানে এখনও কবির সময়কার একটি খুঁটি বহাল আছে, দেখে নিন।
দেখলাম, স্পর্শ করলাম। স্পর্শের বাইরে ঐন্দ্রজালিক অনুভবের জলে ¯œান সারলাম। মায়াভরা জঙ্গুলে আবহাওয়া, বাড়ির সামনে এক চিলতে উঠোন, পেছনে মালঞ্চমধুর। এখন অন্যসব পরিবারের বসত, পাশেই জীবনানন্দ দাশ জাদুঘর মতো কিছু একটা ব্যাপার। কোনো আগ্রহ জন্মালো না, আমার বরং ভালো লাগছিল সাদামাটা সর্বানন্দ ভবন। না নেই সেখানে কোনো স্মারক বা স্মৃতিচিহ্ন তবু ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে যে তাঁরই পদচ্ছাপ- যেমনটা ঠিক বাংলা কবিতার বুকে তাঁর অমোচ্য পদচ্ছাপ।
২
২০১৫’র এপ্রিল। কলকাতা এসেছি প্রথম কিন্তু শম্ভুনাথ প-িত হাসপাতাল যাবো না- তাই কি হয়! বহু আগে কবি মজনু শাহের কবিতায় পড়েছিলাম ‘ডেকেছিল তাকে লাক্ষারঙ যবনিকা।’ যেন নিরুজ্জ্বল জীবন শেষে বর্ণিল যবনিকার ডাকে জীবনানন্দ তাঁর শেষ শ্বাস ফেলেছেন শম্ভুনাথে। লড়াই করেছেন মৃত্যুর সঙ্গে অথবা আলিঙ্গন।
কবিবন্ধু জুবিন ঘোষ সঙ্গে ছিল, বলল কলকাতার লোকেদের অনেকেই তো জানে না তুমি জানো কী করে শম্ভুনাথের কথা?
বলি- জানতেই হবে। জীবনানন্দ আমার অসুখ ও আরোগ্য। ঠিক যেমন এ হাসপাতাল- তাই তাঁর কাছে তো আসতেই হবে। এলাম, দেখলাম, কত রোগ আর রোগহর ওষুধের ছবি আর বিবরণে ভরা হাসপাতাল; নার্স, ডাক্তার, রোগী।
আরে ওই তো জীবনানন্দ দাশ, ল্যান্সডাউন রোড থেকে রক্তমাখা গা নিয়ে এইমাত্র এলেন, ওই তো ভূমেন্দ্র, ওই তো ময়ূখগোষ্ঠী, বাংলা কবিতার মায়াময় ধারা।
না, সঙ্গে ফোন ছিলো না, জুবিনের ফোনেও ছিলো না ভালো ক্যামেরা। অতঃপর মনের অ্যালবামে ধারণ করে এলাম জীবনানন্দ-প্রয়াণের পুণ্য, করুণভূমি। দূরে একটা ভবন, দাশ নয় জীবনানন্দ দাস ভবন, হায় ভুল নাম ও ভুল সময়ের মাঝে এক গোলকধাঁধায় খাবি খেতে খেতে দুপুরের চিলচিৎকারে হঠাৎ শুনি এক মিহি কণ্ঠের ডাক-
বন্দরের কাল হলো শেষ। অমর্ত্য জাহাজ ছাড়লো বলে।
শম্ভুনাথ প-িত হাসপাতাল ছেড়ে জীবনানন্দ কেওড়াতলার ছাইভষ্মের বাড়িতে চলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনেকে। জীবনানন্দ চলে যান, চলে গিয়ে আবার অক্ষরের ডানায় ভরে উড়ে আসেন। পড়ি, পড়তেই থাকি। জীবনানন্দ দাশ।