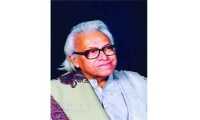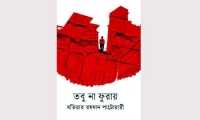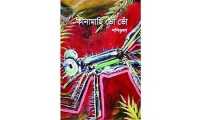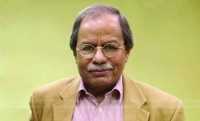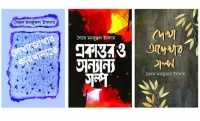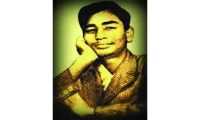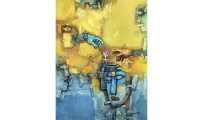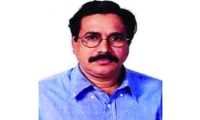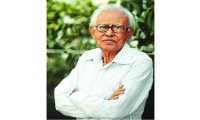ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী-১৪
লোরকার দেশে
চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ
(পূর্ব প্রকাশের পর)
তরিফা থেকে সেভিয়া যাবার পথে শুরু হলো সাগর ও পাহাড়ের লুকোচুরি খেলা। তা দেখতে দেখতে আঁকাবাঁকা রাস্তায় বাসে চড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। বাস কখনো উঠছে তো উঠছেই, মনে হয় একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাবে। আবার নামছে তো নামছেই, যেন সাগরে ডুব দেবে। হঠাৎ নিচ্ছে বাঁক, মনে হচ্ছিল বাস উল্টে যাবে। তবে এসব ভয় মূলত আমারই। ফারজানা, নাবিল ও নাতাশা বেশ উপভোগ করছে পাহাড়ি পথের দু’পাশের মনোরম শোভা। বাম পাশে আটলান্টিকের নীল জলে ভোরের কাঁচা রোদ, মাঝখানে আমরা, ডান পাশে পাহাড়ের কোলে কোলে সবুজ গাছপালা ও রঙ-বেরঙের ফুল। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে ঘন সবুজ উপত্যকা, সেখানে পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে ছোট বড় সব সৈকত, তার ওপর আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ- সব মিলিয়ে যেন এক অপার্থিব দৃশ্য।
যেতে যেতে সবুজের মাঝে ভেসে উঠল কমলা রঙের ছোঁয়া। ভাল করে দেখলাম- কমলা বাগান- যেন কোনো শিল্পী সবুজ চিত্রপটে কমলা রঙের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। যতই সেভিয়া-র দিকে যাচ্ছি ততই এ রঙ বিস্তৃত হচ্ছে। এর মাঝে সাগর ও পাহাড় বিদায় নিয়েছে, শুরু হয়েছে সমতল ভূমি, যার ওপর বাগান আর বাগান- কমলা, জলপাই, ডালিম ও আরো কত ফলের! তবে কমলা বাগানই বেশি, যাদেরকে সাথে নিয়ে ঢুকলাম সেভিয়া শহরে।
এসতাসিঁও দি প্রেদো দি সান সেবাসতিয়ান- ফলকের ওপরের লম্বা নামটি পড়লাম, যখন এ স্টেশনটিতে বাস এসে ঢুকল ভর দুপুরে। এতো বাস স্টেশন নয়, যেন এক আর্ট গ্যালারি। স্কাই লাইট দিয়ে আলো এসে পড়েছে দালানের ভেতরের দেয়ালে, চমৎকার ৮টি ম্যুরালে- যা তুলে ধরেছে আন্দালুসিয়া-র মানুষ ও নিসর্গকে। এখান থেকেই শুরু। এরপর অগণিত স্ট্রিট আর্ট ও ম্যুরাল দেখেছি সেভিয়া-র পথে-প্রান্তরে।
নাতাশা বরাবরই চায় শহরের কোলাহলের বাইরে থাকতে। তাই সেভিয়া শহরের বাইরে হোটেল নিয়েছি, জায়গাটির নাম লা আলহাবা, নামটি মনে হচ্ছে আন্দালুসিয়ায় আরবদের শাসনের এক চিহ্ন।
সেভিয়া শহর কেন্দ্র থেকে লা আলহাবা-য় হোটেলে টেক্সিতে যেতে বিশ মিনিটের মতো লাগল। আবারও কমলা বাগান- চলছে রাস্তার দুপাশে সারি সারি। হোটেলের লবিতেও বসে কমলা শুধু দেখছি না, তার মিষ্টি ঘ্রাণও পাচ্ছি। ভাবলাম, পাশের রেস্তোরাঁয় হালকা খেয়ে এক কমলা বাগানের ভেতরে যাব সূর্য ডোবার আগেই।
তবে নাবিল ও নাতাশা যাবে না বাগানে! তারা বলল, কারো বাগানে এভাবে ঢোকা ঠিক নয়, এ শুধু আনফেয়ার নয়, এটি হবে ট্রেসপাস, যা বেআইনি। ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করাতে হোটেল ম্যানেজার বললেন, ‘তোমরা পাশের বাগানে যেতে পার, আমাদের হোটেল থেকে অনেকে যায়, আমরা ফোন করে তোমাদের নাম বলে দেব।’ বলেই ফোন করলেন, আর বললেন, ‘আমি কথা বলেছি মালিকের সাথে, নাম গেভারা সোসা, ভাল লোক, কোন অসুবিধা হবে না। কিছু দরকার হলে আমাকে ফোন করবে।’
হোটেল থেকে খানিক হেঁটে পেঁৗঁছলাম পাশের কমলা বাগানে। শীতের দুপুরের মিষ্টি রোদ, তার আলো বাগানের সবুজ ও কমলা রঙের উপর পড়েছে, মাঝে মাঝে আলো-ছায়া- সব মিলিয়ে এক ¯িœগ্ধ পরিবেশ। আশে পাশে কাউকে দেখলাম না। ভূমি থেকে একটু উঁচু করে সারি সারি গাছ লাগানো, উচ্চতায় ১০-১২ ফিট, গাছগুলিতে ধরে আছে থোকা থোকা কমলা। গাছের দুটি সারির মাঝে সরু পথ, যা দিয়ে হাঁটা যায়, তা পানি নিষ্কাশনেরও পথ। আর একটু হেঁটে পৌঁছি বাগানের মাঝখানে- সেখানে একটি বড় রাস্তা, তবে কাঁচা, তাই ট্রাক্টরের চাকার বড় বড় দাগ বসে আছে। আমরা সে পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ মাথায় দেখি একটি দোচালা বাড়ি। তার বাইরে কয়েকটি ট্রাক্টর ও লরি, ভেতরে সার, কীটনাশক ঔষধ, স্প্রে মেশিন এবং পাশে ছোটখাট এক ওয়ার্কশপ। সামনে সুঠাম দেহের একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। অনুমান করলাম তিনিই বাগানের মালিক। কাছে যেয়ে বললাম, ‘ওলা, সিনর সোসা!’ তিনি মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন।
গেভারা সোসা জানতে চাইলেন, কোথা থেকে এসেছি, আমাদের মাতৃভূমি, ভাষা ইত্যাদি। স্পেনে কেউ কখনো এসব জিজ্ঞেস করে না। পরে বুঝতে পারলাম কারণ। গেভারা শুরু করলেন, ‘সামনে এই যে কমলা বাগান, এ কমলার উৎপত্তি তোমাদের এশিয়ার চীন থেকে। তা এই স্পেনে নিয়ে আসে মুররা দশম শতাব্দীর দিকে, সাথে ছিল ডালিম। কমলাগুলি দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু খেতে তেমন ভাল নয়, কারণ এগুলি টক আর তেতো।’ নাতাশা আস্তে করে বলল, ‘Grapes are sour!’ নাবিল যোগ করল, ‘All that glitters is not gold!’ গেভারা বলতে থাকল, ‘তবে এসব কমলার সুন্দর রঙ, এদের সুগন্ধি ফুল, এবং ঘন সবুজ গাছের জন্য মুররা তা ব্যাপক হারে চাষাবাদ করে। ধীরে ধীরে তেতো কমলার প্রধানতম এলাকা হয়ে উঠে সেভিয়া, আর এ কমলার নাম হয়ে যায় ‘সেভিল অরেঞ্জ’। কমলাগুলি এখানে তেমন কেউ খায় না। তবে তার ফুল থেকে পারফিউম তৈরি করা হয়। আমরা বেশিরভাগ কমলা বাইরে, মূলত ব্রিটেনে রফতানি করি। তারা এসব তেতো কমলা দিয়ে মার্মালেড তৈরি করে।’
‘মার্মালেড’ শব্দটি শুনেই নাতাশা বলে উঠল, ‘আমাদের প্রিয় একটি মুভি ‘প্যাডিংটন’-এ আমরা দেখেছি কীভাবে মার্মালেড বানানো হয়। গল্পটি এক ছোট ভালুকের, যে পেরুর জঙ্গল থেকে ভূমিকম্পে তার বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় লন্ডনে পাড়ি দেয়। সাথে ছিল একটি লাল হ্যাট ও দুমড়ানো মচকানো একটি স্যুটকেসে এক বয়াম মার্মালেড। লন্ডনের ‘প্যাডিংটন’ স্টেশনে ব্রাউন দম্পতি ভালুকটিকে খুঁজে পায়, আর স্টেশনটির নামে তার নাম দেয় ‘প্যাডিংটন’।’ সেভিয়া-র তেতো কমলা যেন মার্মালেড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পুরো পৃথিবীতে!
কমলা বাগান দেখা শেষ করে গেভারা সোসাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। ফেরার পথে দেখি একটি কাঠের বাক্সের ওপর বিক্রির জন্য কিছু কমলা রাখা আছে। এক একটি ব্যাগে ১০টি করে কমলা, দাম ৩ ইউরো। পাশে কেউ নেই, মূল্য দেয়ার জন্য একটি প্যাকেট রাখা আছে। তাতে ৫ ইউরোর এক নোট ফেলে আমরা এক ব্যাগ কমলা কিনলাম। হোটেলে ফিরে আসলাম, যেন কমলা বাগানকে সাথে নিয়ে; রুমটি পাকা কমলার মিষ্টি ঘ্রাণে ভরে উঠল।
মনে পড়ে গেল লোরকার কবিতা ‘আমার বোন, ইসাবেলার জন্য’:
কমলালেবুর জন্য
আমার ছোট বোন গায়
“পৃথিবী একটা কমলালেবু”
চাঁদ ফুঁপিয়ে বলে
‘আমি কমলালেবু হতে চাই’
হতে পারবে না তুমি- আমার আদুরি-
তুমি গোলাপি হয়ে গেলেও
কিংবা সামান্য পাতিলেবু
কতো দুঃখের।’১
ছোট বোন ইসাবেলাকে উদ্দেশ্য করে লোরকা কবিতাটি লিখেছিলেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে লোরকা ছিলেন সবচেয়ে বড়। এক ভাই খুব ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল। বাকি দুই ভাই, দুই বোনের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে আদরের ছিল ছোট বোন ইসাবেলা। তার লেখাপড়া, গান-বাজনা সব শেখা লোরকার কাছে। একটি ছবি দেখেছিলাম গ্রানাদার ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা মিউজিয়মে, ১৯১৪ সালের ছবি, যেখানে লোরকা পড়াচ্ছেন ইসাবেলাকে। ১৯৩৬ সালে লোরকা-র মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ইসাবেলা বেলজিয়াম পালিয়ে যান। পরে যুক্তরাষ্ট্র এসে বসবাস করেন এবং স্পেনীয় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। তবে ১৯৫১ সালে তিনি স্পেনে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ভাই লোরকার স্মৃতির সন্ধানে গ্রানাদা ও আশেপাশে ভ্রমণ করে ‘Recuerdos Mios’ (আমার স্মৃতি) নামে এক বই লিখেন, যা লোরকার এক উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ। ইসাবেলা বাকি জীবন লোরকার জীবন ও কাজের স্মৃতি সংগ্রহ ও গবেষণায় অতিবাহিত করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ‘গার্সিয়া লোরকা ফাউন্ডেশান’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০০২ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।
আমি লোরকা ও ইসাবেলাকে নিয়ে ভাবার মাঝেই সবাই তৈরি হয়ে আসল, উদ্দেশ্য- ঘুরতে বের হওয়া, গন্তব্য- সেভিয়া শহর।
শহরেও কমলা বাগান- তবে এগুলোর আকার ছোট। যেদিকে তাকাই গাছে গাছে ধরে আছে থোকা থোকা কমলা। পর্যটন অফিসের একজন বলল, এ শহরে ৪০ হাজারের ওপর কমলা গাছ আছে। পৃথিবীর আর কোনো শহরে এত কমলা গাছ লাগানো হয়নি। শুধু শহরের সৌন্দর্যের জন্য এতগুলি গাছ লাগানো, আর তা যতœ করে বাঁচিয়ে রাখা, সোজা ব্যাপার নয়। তেতো আর টক হোক, এসব কমলার সৌন্দর্য, সাথে ফুলের ঘ্রাণ- সত্যিই অপূর্ব! মনে হয় সারাদিন বসে বসে দেখি আর ঘ্রাণ নিই। তবে নাবিল ও নাতাশার যে অনেক কিছু দেখার আছে, কমলা গাছের জন্য এত সময় নেই।
কমলার আলাপের মাঝে কানে বাজল এক ঠক ঠক ধ্বনি। কিসের শব্দ ভাবতেই দেখি এক ঘোড়ার গাড়ি, এরপর আর একটি, পরে আরো ক’টি, চলছে অবিরত। ঘোড়ার খুর ও নাল রাস্তার ইট-পাথরে সৃষ্টি করেছে এ টগ-বগ শব্দ- ছন্দোময় এক শব্দ মূর্ছনা। মনে হচ্ছে অশ্ব-শকটে চড়ে স্পেনীয় বীর এল সিদ ফিরে এসেছে তার বাহিনী নিয়ে সেভিয়া-তে। এক আধুনিক শহরে ঘোড়ার গাড়ি- যেন ইতিহাসের হাতে হাত দিয়ে চলা। শেষ কবে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছি, মনে পড়ছে না। এখন যখন সুযোগ পাওয়া গেল এ গাড়িতে চড়ার, একটু ঘুরে দেখি। একটি গাড়িতে চারজনের বসার ব্যবস্থা। তবে তার দরকার হলো না। নাবিল ও নাতাশা ঘোড়ার গাড়িতে চড়বেনা। আবৃত্তি করলাম ছোট বেলার সেই ছড়া, ‘পড়ালেখা করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।’ কাজ হলো না। তারা বলল, ‘ঘোড়ার গাড়ি আনফেয়ার, তা পশুদের প্রতি নির্মমতা।’ বললাম, ‘পশুদের প্রতি নির্মমতা ভুল, তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের প্রতি নির্মমতা পরিহার।’ তারা বলল, ‘দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।’
নাতাশা ভেবে এক ‘উইন-উইন সলিউশন’ নিয়ে আসল, ‘ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে এখন রিভার ক্রুজে যাই। এরপর তুমি ঘোড়ার গাড়িতে বেড়াতে পার, আর আমরা যাব ‘মাসরুমে’ শুধু গাড়িতে চড়ে, ঘোড়াতে নয়। পরে সবাই সেখানে মিলিত হব।’
একটু এগোতেই পেয়ে গেলাম সেভিয়া-র সবচেয়ে বড় রাস্তা পাসেও দি ক্রিস্টোবাল কলোন। তার পাশেই এক বাঁধানো চত্বর-পাসেও দি লাস দেলিসিয়াস- ওক গাছের সারি, মাঝে মাঝে ফোয়ারা, নকশা-করা ল্যাম্পপোস্ট, পাথরের সুন্দর মনুমেন্ট, রঙিন ফুলের বাগান, কমলা গাছের গুচ্ছ- সব মিলিয়ে যেন চিত্রপটের এক ছবি। ফাঁকের বেঞ্চে বসেই আমরা সবাই দেখতে পেলাম পাশে বয়ে যাওয়া নদী গুয়াদিলকিভির।
এই সেই গুয়াদিলকিভির, যাকে প্রথম দেখেছি লোরকার কবিতায়:
গুয়াদালকিবির, ওই কমলাবনের ফাঁকে ফাঁকে
বাতাস, বাতাস, উঁচু বুরুজ, বুরুজ।
দাউরো, হেনিল, সারা পথ
ডোবাপুকুরের পাড় দিয়ে দিয়ে মরাঝরা ঢিবি।
হায়, ভালোবাসা,
চলে গেলে বাতাসের পথে।’১
লোরকার আঁকা গুয়াদালকিবির নদীর পাশে কমলাবন, বাতাস, বুরুজ- সবই আছে, এসব প্রাচুর্য ও ক্ষমতার প্রতীক। বিপরীতে, দাউরো ও হেনিল নদী দুটি ক্ষীণকায়া। আমরা গ্রানাদায় দেখেছি ছোট দাউরো নদী মিশেছে হেনিল নদীতে, যা আরো পশ্চিমে গিয়ে মিশেছে গুয়াদালকিবির এর সাথে, ফলে তা হয়ে ওঠে এক বড় ¯্রােতস্বিনী। এ তিন নদী নিয়েই লোরকার কবিতা ‘তিন নদীর বালাদিকা’। নদীগুলির মিলিত প্রবাহে ফুটে ওঠে আন্দালুসিয়ার নিসর্গ, তার মাঝেই শোনা যায় হারানো ভালোবাসার জন্য কবির এক দীর্ঘশ্বাস! ক্রমশ...
Ref:
১. আমার বোন, ইসাবেলার জন্য, অনুবাদ:মলয় রায়চৌধুরী
২.Baladilla de los res rios, তিন নদীর বালাদিকা, অনুবাদ: দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
-

এলোমেলো স্মৃতির সমরেশ মজুমদার
-
সাময়িকী কবিতা
-

বিমল গুহের কবিতার অন্তর্জগৎ ও শিল্পৈশ্বর্য
-

কবিতার সুনীল সুনীলের কবিতা
-

রূপান্তরের অকথিত গল্পটা
-
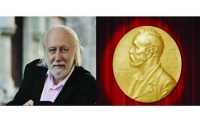
মানব সভ্যতার আত্মবিশ্লেষণের আয়না
-
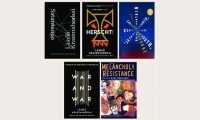
বাইরে একটা কিছু জ্বলছে
-
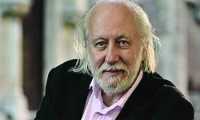
‘কাফকার মতো হবো বলে আইন পড়েছিলাম’
-

সত্যেন সেনের উপন্যাস: মিথ ও ইতিহাসলগ্ন মানুষ
-
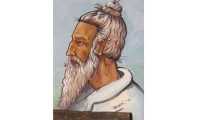
বিস্ময়ের সীমা নাই
-
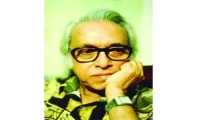
নগর বাউল ও ত্রিকালদর্শী সন্ত কবি শামসুর রাহমান
-
সাময়িকী কবিতা