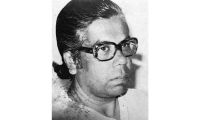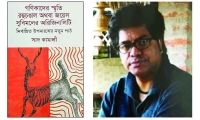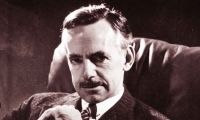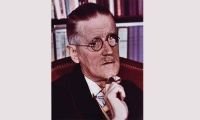আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথাভাঙা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত
নীহার মোশারফ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন স্রষ্টামানস যুগপৎ আবিষ্কারক ও সাহিত্যে বিবেচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বাংলা কবিতার প্রথাভাঙা মহাকবি। তিনি কবিতার প্যাটার্ন ভেঙেছেন অতি সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে। কবিতা পাঠে বাঙালিকে দিয়েছেন নতুন এক স্বাদ। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বারবার। রচনার বিষয়, প্রকরণ, ছন্দ, শব্দ, তাল, মাত্রা সর্বোপরি সামগ্রিক কাব্যকলার উত্তরণে তিনি ছিলেন যুগ¯্রষ্টা। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা বাংলার নবজাগরণের প্রসঙ্গ আসে অনায়াসে। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, মধুসূদনের সময়কে বাঙালার নবযুগ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তিনি প্রাণে প্রাণে নব সূর্যের উদয় ঘটিয়েছেন। সাহিত্যের বাঁকে বাঁকে নতুন হাওয়া লেগেছে সর্বত্র। মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টিতে জীবনের জিজ্ঞাসা আছে। আছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদ ও দেশপ্রেম। তাঁর সাহিত্যে পাঠক খুঁজে পেয়েছে মানব মহিমার এক উজ্জ্বল উচ্চারণ। মধুসূদন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে জানান দিয়েছেন আমাদের একটি সুন্দর অতীত আছে। আছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। আমাদের বয়ে যাওয়া নদী আছে। প্রাণের ভাষা আছে। মানুষে মানুষে আছে সম্প্রীতি। আমাদের সাহিত্য ইউরোপীয় ছকে বাধা নয়। আমাদের সাহিত্যে নিজস্ব স্বকীয়তা আছে। এই উপলব্ধিটি কবি প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে সরে এসে এক অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানব মহিমার উদার জয় ঘোষণা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার রচনায় দেশপ্রেমকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাধান্য দিয়েছেন উদার মানবিকতাবোধকে। মধুসূদন তাঁর কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও প্রহসনে এই সত্যকে মেনে চলতেন। তাই উচ্চারণ করেছেন-
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শতধিক তারে।
১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয় ঘটে। ইংরেজদের দুইশ বছরের শাসনের পাশাপাশি সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। তাদের দীর্ঘকালের শৌর্য-বীর্যে ভারত শাসিত মুসলিম সমাজের উদ্যমহীনতা, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার ফলে বাংলায় সৃষ্ট জাগরণ সংঘটিত হয় হিন্দু সমাজের নেতৃত্বেই। আর হিন্দুদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। এই নবজাগরণের মানসে যাঁরা পুষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ^রচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বঙ্গীয় সমাজে তাঁদের অগ্রসর চিন্তা, নবতর বোধ আলোকবর্তিকা হয়ে আসে। তাঁদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যাঁর আলোয় আলোকিত হয় অন্ধকারময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অচলায়তন। বাঙালিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি মধুসূদন থেকেই আমাদের জাতীয় মানসে প্রথম সঞ্চারিত হয়। বাংলার নবজাগরণের দুরন্ত তূর্যবাদক। নব্য প্রমিথিউস মধুসূদন।
মধুসূদন সবসময়ই আধুনিক ও সাম্প্রতিক। আধুনিক বাংলা কবিতার জনকপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে জঙ্গম চঞ্চল অস্থির বৈপ্রতীপ্য এসে মিলেছিল। অতিদ্রুত সময়পটে মাইকেল ও নজরুল যে বিপ্রতীপকে ধারণ ও সহ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে এক দীর্ঘ সময়-বিসারে রূপান্তরিত করেছিলেন শান্ত ও সহিষ্ণু অঙ্গীকারে। রবীন্দ্রনাথের জীবন যেহেতু আপাতপক্ষে ছিল স্বস্থ, এবং মাইকেল ও নজরুলের অস্থির ও সংরক্ত, তাই রবীন্দ্রমানসের বিলোড়োন আমাদের ঠিক চোখে পড়ে না। অবশ্য ওই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথই বরং ধ্রুপদী ঐশ^র্যের মালিক; কেননা জীবনকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন স্বস্থ, অনস্থির, নির্মোহ এক দর্শনে। মাইকেল ও নজরুল যেন আপনাপন শরীরমানসের সবখানিজুড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি প্রদীপাধারের শিল্পাগ্নিতে জ¦ালিয়ে তুলেছিলেন।
মাইকেল হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান হলেও সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে ছিলেন সনাতনী আর্য-ব্রাহ্মণানুসারী। তিনি গীতগোবিন্দ রচয়িতা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের ভক্ত ছিলেন। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় বৃন্দাবনের রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপীদের লীলা সম্পর্কের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন গীতগোবিন্দ কাব্যে। মধুসূদন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার অনেক কবিদের প্রতি মুগ্ধ ছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য। তাঁর রচনায় সংস্কৃত ভাষার আধিক্য এবং সনাতনী ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রীতি বিপুলভাবে লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার ইতিহাস ঐতিহ্য তার রচনায় যতটা না ফুটে উঠেছে তার চেয়ে আর্য-সংস্কৃতি বেশি প্রকটিত হয়েছে।
মাইকেলের জীবন ছিল যেহেতু ঘটনাঘন ও ঝঞ্ঝারক্তিম, তাঁর না-লেখা কিন্তু সম্ভাব্য কাব্যনাট্যের মতোই সংরক্ত, তাই আমাদের কৌতূহল অনেক সময় সেই জীবননাট্যের রঙ্গেই ধেয়ে যায়। কিন্তু কবি হিসেবে মাইকেল এখনো নিঃশেষিত নন-বরং জীবিত ও আবিষ্কারযোগ্য, এখনো নবীন কাব্য-পাঠকের প্রবেশ বিফলে যাবে না। এখনো নতুন সমালোচনার প্রতি আমন্ত্রণকারী।
যৌবনের শুরুতেই তিনি পাশ্চাত্যের ভাব ও আদর্শের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। অবশ্য জীবনের শেষ সময়ে এসে মধুসূদন বুঝতে পারেন বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ ও সাহিত্য সাধনায়ই তাঁর মগ্ন থাকা উচিত ছিল।
মধুসূদন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়- মধুসূদন ত্যাজ্যপুত্র ছিলেন। ধর্মান্তরের পর তাঁর নামের প্রারম্ভে ‘মাইকেল’ যোগ হয়। খ্রিস্টান হয়ে মধুসূদন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আশ্রয় নেন। পুত্রের এই আকস্মিক কর্মে রাজনারায়ণ দত্ত হতাশ, ব্যথিত, বিমূঢ় হলেও পুত্রকে ত্যাজ্য করার মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। পুত্রকে উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েও আশাবাদী ছিলেন যে, তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। পুত্রের জন্য অন্তর পুড়েছে সবসময়। সামাজিক লজ্জায় প্রকাশ্য না হলেও গোপনে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হতো। ধর্ম ত্যাগের পর মধুসূদনের পক্ষে হিন্দু কলেজে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি অর্থের অভাবে। তখন মধুসূদন ভর্তি হন বিশপস কলেজে। সেখানে যাজক হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। বেতন, আবাসিক খরচ সম্পূর্ণ বহন করত কলেজ কর্তৃপক্ষ। মধুসূদন ছিলেন একমাত্র পেইং স্টুডেন্ট। রাজনানায়ণ দত্ত পুত্রের জন্য প্রতিমাসে কলেজের বেতন, থাকার খরচ ও হাত খরচসহ মোট একশত চার টাকা বরাদ্দ করেন। হয়তো মায়ের কাছ থেকেও টাকা পেতেন তিনি। পিতার পীড়াপীড়িতে স্বধর্মে ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা না থাকায় একপর্যায়ে পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় সম্পূর্ণরূপে।
যখন বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা ছিল অনেকটা আঞ্চলিক এবং ক্ষুদ্র পরিসরে ঠিক তখনই মহাকবি মধুসূদনের আবির্ভাব। কবি মধুসূদনই সেই বিদ্রোহী কবিদের মধ্যে আধুনিক ভাষার চিন্তাধারা ও কাব্য সৃষ্টির নবতর এবং যুগোপযোগি ধারার বিরাট প্রাবল্য ছিল। ঐশ^র্যময় শব্দ সম্ভার, অনুপ্রাস, আড়ম্বরপূর্ণ শব্দচয়ন, চিত্ররূপ নির্মাণ ও উপমা বিন্যাস, ভাষা নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা তাঁর সাহিত্যকর্মকে এক নতুন সৃজনশীল স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর জীবনের আলেখ্য, সাহিত্যক্ষেত্রে “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে”- তাঁর অস্থির ভ্রমণ ও অন্বেষণ, অতৃপ্তি ও সৌকর্য-সন্ধান তিনি নিজের কথায় অনুকরণীয় ও মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং যা গভীরতম কাব্যরস ও করুণরস সিঞ্চিত।
মধুসূদনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ক্ষ্যাপা সাধকের পরশমণি খোঁজার উন্মত্ততা, দুঃখ, শোক, আনন্দ, বিহ্বলতা, বিদ্রোহ, মানবিকতা, অপরিণামদর্শিতা, মাহাত্ম্য-অন্বেষেণ, পরাজয়ের মধ্যেও বিজয় ও আত্মগরিমা দেখেছেন। সত্যিকার অর্থেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের গ্রিক ট্রাজিক হিরো। সুউচ্চ তাঁর অর্জন এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে জগতের কোলাহল থেকে নিয়তিদৃষ্ট মাইকেলের অপরিণত গমন।
মহাকাব্যে মহাজীবনের অংশবিশেষের অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি দিকের পরিচর্যা থাকে না; কিন্তু জীবনের পরিপূর্ণতার পরিচয় থাকে। কবি বিভিন্ন কৌশলে এই পরিপূর্ণতাকে স্পষ্ট করেন। কবি আপন ভাষার মৌলিক শব্দভা-ার এবং বাক্যের অন্বয়শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করেই তার মধ্যে নতুন ভাবস্পন্দন এনে থাকেন এবং মহাকাব্যে জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা জাগে। মাইকেল মধুসূদন উপমার মাধ্যমে ক্রমপ্রসার এবং অবিরল ব্যঞ্জনার সুযোগ নিয়েছিলেন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের তৃতীয় সর্গের পরতে পরতে। পূর্বকালে সাহিত্যে আমাদের দেশে উপমাগুলো ছিল অনেকটা লঘু এবং মূলত বস্তুগত। যে উপমা ছিল একটি বস্তুর তুলনা করে উপমা নির্মাণের মধ্যযুগীয় রীতি মধুসূদন অনুসরণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু উপমা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি বস্তুর প্রাণ-চৈতন্যের উপমা দিয়েছিলেন।
বাংলা সাহিত্যে নিজের জন্মভূমি, ভাষা, দেশপ্রেমের সূচনা করেছিলেন চর্যাপদেরও অনেক আগের এক বাঙ্গাল কবি। তিনি নিজেকে আড়াল করে শুধু ‘বাঙ্গাল কবি’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন। তখনই কবি আজকের বাংলাদেশকে ‘পুণ্য দেশ’ এবং বাংলা ভাষাকে ‘পুণ্য বাণী’ বলে অবিহিত করেছেন। তার লেখায় দেশ ও নিসর্গকে এভাবে তুলে ধরেছেন-
ঘনরসময়ী গভীরা চক্রিমসুভ গোপজীবিতা করি ভিঃ।
অবগাঢ়া চঃতুণীতে গঙ্গা বঙ্গাল বাণী চঃ॥
তার মানে বঙ্গালদেশ যেমন শোভামান নিসর্গে ভরপুর তেমনি পুণ্য গঙ্গা কবিদের প্রশস্তিতে নন্দিত। পুণ্য বঙ্গাল বাণীতে অভি¯œাত হলে মনে প্রশান্তি ও নির্মল ¯িœগ্ধতা আসে। মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সাগড়দাঁড়িতে মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে তাঁর শৈশবশিক্ষা শুরু হয়েছিল। পরে পিতা রাজনারায়ণ দত্তের কলকাতার খিদিরপুরের বড় রাস্তার পাশে ক্রয় করা এক দোতলা বাড়িতে গিয়ে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ভর্তি হন কলকাতার হিন্দু কলেজে। সেই কলেজে পড়া অবস্থায় তাঁর মধ্যে নব্য বাংলা প্রবেশ করে অন্তরে। মানবমন্ত্রে বিশ^াস, গভীর ইংরেজি সাহিত্যপ্রীতি, দেশীয় আচার-ভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা অনেকটা প্রভাব ফেলেছিল। মধুসূদনের ভেতরে জাতিগত এক পরিবর্তন দেখা দিলো। তিনি খ্রিস্টান হবেন। সেই মতে ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি আর্চডিকন ডিয়াল্ট্রির কাছে গিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে সম্বলহীনভাবে মাদ্রাজ নগরে উপস্থিত হলেন। বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক পদে চাকরি নিলেন। ১৮৪৮-৫৬ সালের মধ্যেই তিনি আপন পা-িত্যের সুনিশ্চিত পরিচয় দিয়েছিলেন শিক্ষামহলে। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতে লাগলেন সেখানে। কবিতা, গীতিকবিতা, সনেট, খ-কাব্য প্রকাশিত হতে লাগল ছদ্মনামে। প্রকাশিত হলো ঠরংরড়হং ড়ভ ঃযব ঢ়ধংঃ এবং ঞযব ঈধঢ়ঃরাব খধফু কবিতা দুটি। পরে ঞযব ঈধঢ়ঃরাব খধফু নামেই প্রথম কবির লেখা প্রথম প্রকাশিত রচনা।
প্রথম দিকে মধুসূদনের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। তাই বছরের মাথায় বিবাহবিচ্ছেদ হয়। সেই ঘরে চার সন্তান। পরে এমিলিয়া আঁরিয়েতা সোফিয়া নামক এক ফরাসি তরুণীকে বিয়ে করেন। তিনি মধুসূদনের সারাজীবনের সঙ্গী ছিলেন। মধুসূদন দত্ত তাঁর সময়ের লেখকদের মতো আড়ষ্ট-কঠিন সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি তার রচনায় স্বতঃস্ফুর্ত গতিচাঞ্চল্যে সমগ্র সাহিত্যে জাতির মুক্তির জন্য উত্তরণের দিগন্ত নির্দেশ করেছেন। তিনি চেয়েছেন ভবিষ্যৎ কবিদের কাছে একটা দৃষ্টান্তমূলক প্রেরণা-উৎস হিসেবে কাজ করুক তার সাহিত্য। তিনি যতটুকু ইউরোপীয় ঢং কাব্যে ব্যবহার করেছেন তা তাঁর নিজস্ব ঢংয়ে। কাব্যের কাহিনি, চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ মূল্যবোধের নবতর অভিক্ষেপে এবং প্রাণ উদ্দামতায় স্পন্দিত ও তরঙ্গিত। তেমনি ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে উদ্ভাসিত গুণাবলির প্রথম আভাস এ কাব্যেই সূচিত হয়েছিল।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা ভাঙা-গড়ার এক অপূর্ব কারিগর ছিলেন। কাব্যে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে তার মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা, প্রতিবাদের ভাষার চেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যেই আলোচিত হয়েছে। তিনি সনেট কবিতা লিখেছেন। যা তার ব্যতিক্রমধর্মী এক অনবদ্য সৃষ্টি। ‘কপোতাক্ষ নদ’ তার বিখ্যাত সনেট কবিতা। এই কবিতায় স্বদেশের প্রতি অপার প্রেম, গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কপোতাক্ষের জল আর মমত্ববোধ মিলেমিশে একাকার হয়েছে। মধুসূদন সুদূর প্রবাসে বসেও যাপিত জীবনে উচ্চারণ করেছেন-
হে বঙ্গ, ভা-ারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি
পর-ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।
মধুসূদনের কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও প্রহসনে দেশপ্রেমের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে বহুবার। প্রতিটি লেখাতেই তিনি পুরনো প্রথা ভেঙে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। ব্যবহার করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মধুসূদন শুধু পয়ারের বৃত্তই ভাঙেননি, ভেঙেছেন অহমিকার প্রাচীর। তার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে- ঈধঢ়ঃরাব খধফু, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য, শর্মিষ্ঠা (নাটক), পদ্মাবতী (নাটক), কৃষ্ণকুমারী (নাটক), একেই কি বলে সভ্যতা (প্রহসন), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (প্রহসন), চতুর্দশপদী কবিতা ইত্যাদি।
তিনি শেষের দিকে চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও বাংলাসাহিত্যকে আধুনিকতায় রূপ দিয়ে গেছেন।