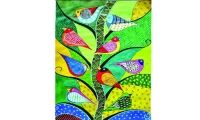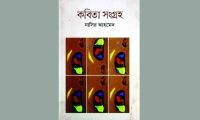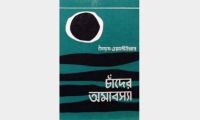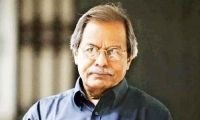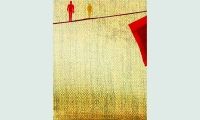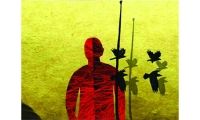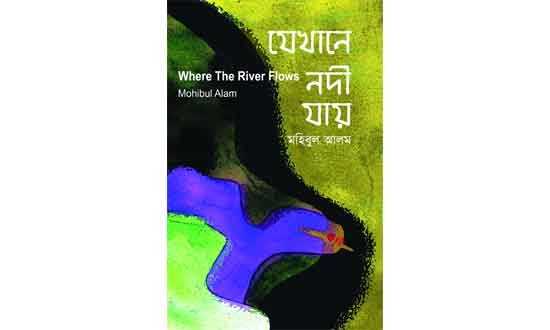
মহিবুল আলমের কবিতায় নদী ও নারী
আনোয়ার মল্লিক
মহিবুল আলম মূলত কথাসাহিত্যিক। আরও নির্দিষ্ট করে বললে তিনি গল্প ও উপন্যাস লেখেন। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েবাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাস জীবন যাপন করছেন। তবে দেশ ছেড়ে তার সুদূরের এই অবস্থান দেশ, দেশের মাটি আর মানুষকে তার ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। কাল বিচারে নব্বইয়ের দশকের লেখক তিনি। নব্বইয়ের দশকে এসে কবিতার ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক, প্রকরণ এবং কাব্যভাষায় ভিন্ন এক অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে। আবার বেশ কিছু প্রতিভাবান লেখক এই দশকে নতুনতর ভাবনা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন।
এবছর একুশে গ্রন্থমেলায়মহিবুল আলমের প্রথম কবিতার বই “যেখানে নদী যায়”প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ করেছে অধনাবাদী চিন্তার লিটল ম্যাগাজিন ‘শালুক’।
বইটির একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে যে কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে, বাংলার পাশাপাশি তার ইংরেজি ভার্সনও জুড়েদেওযা হয়েছে। ফলে অবাঙালি পাঠকদের জন্য এই কাব্যগ্রন্থের রস আস্বাদনে কোনো বাধা হবে না।
‘যেখানে নদী যায়’কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট তিরিশটি কবিতা রয়েছে। এই তিরিশটি কবিতাকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায়অথবা বলা যায় কবি নিজেই এই বিভাজন করে দিয়েছেন। যেমন ‘বিমলা উপখ্যান’ সিরিজে নয়টি কবিতা রয়েছে। এরপরে ভিন্ন ভিন্ন নামে তেরোটি একক কবিতা। বাকি আটটা কবিতার একটা সিরিজ রয়েছে ‘নয়দুয়ারের বারো উঠান’ শিরোনামে।
মহিবুল আলমের ‘যেখানে নদী যায়’কাব্যগ্রন্থে বাংলাদেশের নারীদের জীবন-যন্ত্রণা, তাদের প্রতি অবহেলা, নিষ্পেষণ এবং সর্বোপরি তাদের সংগ্রামের কাহিনীচিত্র গভীর দরদ দিয়ে কবি তুলে এনেছেন। নদী কেন্দ্রিক ভংগুর মানুষের স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্প অংকিত হয়েছে চিত্রকল্প, এবং উপমার অনুপম শৈলীতে। কবিতায় যে নদীর কথা বলা হয়েছে, তা শুধু প্রকৃতির অংশই নয়, নদী এখানে জীবনের বহমানতাকে ধারণ করে প্রতিরোধ, নতুন স্বপ্ন এবং ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে। দুই পারের মানুষের ভাঙা-গড়া, আনন্দ বেদনার সাক্ষী হয়ে এখানে নদী হয়ে উঠেছে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
বিফলা উপাখ্যান সিরিজে বিফলা নামের এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারীর পতিত জীবনের মর্মস্পর্শী বয়ানে রাষ্ট্রের কদর্যতা, ভ-ামি, এবং জীবনের নগ্নতা, নিষ্ঠুরতার হৃদয় বিদারক ভাষ্য নির্মাণ করেছেন কবি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়বিফলা পালাতে গিয়ে পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। কবি বলেন, “কাঁদায় লেপটে থাকা বুক নিয়েসে এক দুপুরে নিজের জমিন কাঁপিয়ে পালাতে গিয়েগোপাটের বেতগাছে জড়িয়েপাক হানাদারের এক এক জোয়ানের কাছে ধরা পড়ে।” (বিফলা উপাখ্যান : এক)। তখন তার বয়স ষোলোর ঘরে; যৌবনের একেবারে সন্ধিক্ষণে। তারপর তার জীবনে নেমে আসে ভয়াল অমানিশা। পাক নরপশুরা তার শরীর খুবলে খায়। দিগি¦দিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়বিফলা। মানসিক ভারসাম্যও লোপ পায়তার। নারীত্বের চরম অপমানে কান্নার বদলে দিঘল হাসির আশ্রয়নেয়সে। এই হাসিই তাকে বাঁচিয়েদেয়। এই হাসি সমাজ ও রাষ্ট্রের বর্বরতাকে যেমন বিদ্রুপ করে তেমনি মানুষের কুৎসিত মুখচ্ছবি আমাদের সামনে নগ্নভাবে উন্মোচন করে দেয়।
বিফলার নারীত্বের প্রতি ঘৃণ্য অপমানের কদর্য চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে : ‘এক হানাদার থেকে আরেক হানাদার, এক ঘর থেকে অন্য ঘর, শরীরে শরীর বদলায়। দেহের পর দেহ। মোকামও বদলায়। শরীরের এই অদল বদল খেলায় একদিন সে নিজ শরীরে মানুষের গন্ধ পায়।’ (বিফলা উপাখ্যান : তিন)। বিফলার স্ফীত পেট তাকে পাক বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়। সে আজাদ হয়ে যায়। যদিও আজাদীর অর্থ বিফলা আজও বোঝে না।
দেশ একদিন স্বাধীন হয়। কিন্তু বিফলার জীবনে সেই স্বাধীনতা কোনো অর্থ বয়ে আনে না। স্বাধীন দেশে বিফলার কোনো ঠাঁই হয় না। একদিন নদীর অপর পাড়ে সে ঘরের খোঁজে যাচ্ছিলো। তারই মতো যুদ্ধে সব হারানো সুবোধ মাঝি নদী পারের জন্য পয়সা চাইলে বিফলা তার পোয়াতি পেট দেখিয়ে শুধু দিঘল হাসে। সুবোধ মাঝি আর পয়সা নেয় না।
“সুবোধ মাঝি বলে ওঠে, ‘বুজি, আর কোনো চিন্তা নাই, আমাগো দেশ স্বাধীন’...!”
“দেশ স্বাধীন...! বিফলা এর মানে বোঝেনি। সেদিনও না।/আজও না।” (বিফলা উপাখ্যান : চার)।
অবশেষে দিবাকর ভৌমিকের পরিত্যক্ত কপাটবিহীন দালান ঘরে তার আশ্রয় জোটে। এই দালানেই একদিন হিম বাতাসে আলোর মুখ দেখে তার আত্মজা। আবারও তার দিঘল হাসি- “মা গো তুই স্বাধীন হ...!” বিফলার স্বগতোক্তি। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ কি বিফলা নিজেও জানে না।
দিবাকর ভৌমিকের সেই ভুতুড়ে, পরিত্যক্ত, কপাট খোলা দালান দেখতে দেখতে বিফলার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যায়। এই ঘরে দিনে রাতে অগণিত মানুষের আনাগোনা হয়। মমিন মেম্বার, লোকমান চৌকিদার, রহমান বয়াতি, রইস মুনশি, সোলাইমান দালাল- এরকম অগনিত শরীর-লোভী তার কাছে আসে-যায় দিনে-রাতে সবসময়। তাদের শঠতা, প্রতারণা আর ছলনায় বিফলা শুধু দিঘল হাসে। এই হাসিই তার সব কথা বলে দেয়; তার বাঁচার মন্ত্র।
‘যেখানে নদী যায়’ গ্রন্থের কবিতাগুলো মুক্তছন্দে লেখা। এবং একটি ভিন্নতর কাব্য প্রকরণে কবিতার শরীর নির্মিত হয়েছে। কবিতার এই স্টাইল কবির একান্ত নিজস্ব। কবিতার বুননে এমন এক স্বরভঙ্গি কবি অনুসরণ করেছেন, কবিতার পাঠ শেষে পাঠক এক মর্মান্তিক সত্যের মুখোমুখি হন। যে সত্য ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে ধসিয়ে দেয়, অর্থহীন করে তোলে।
সমাজের লাঞ্ছিত, ভাগ্য পীড়িত নারীদের জন্য একসময় নির্দিষ্ট এলাকা থাকতো। রিপুর তাড়না মেটানো পুরুষের আনাগোনায় মুখর হতো এসব পাড়া। সেখানে পুরুষের নিলামের জন্য যারা অপেক্ষায় থাকতো তারা নারী। কবি তাদের বর্ননা দিয়েছেন এভাবে : “আধা শিশি আলতা, রঙিন ফিতে, খসখসে একটা সোনালি শাড়ি/আর জিভ বের করা ফুটপাতের একটা লাল লিপস্টিক / মধ্য বিকেলের লেপটানো গাল...। / কিন্তু বর্তমানে এসব পাড়া ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কবি বলেন, পাড়ায়পাড়ায়বুবুরা এখন হিসেবহীন নিলামে ওঠে না, রাজনীতিকরা ওঠে।” (নিলাম)। তিনি এখানে রাজনীতিকদের নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়করিয়াছেন যে সত্যকে রাজনীতির মানুষেরা সবসময় লুকাতে চেয়েছেন।
“সচল শকুন” কবিতায় কবি সমাজের এক কদর্যতার দিকে আমাদের বৃষ্টি ফিরিয়েছেন। যেমন: “শকুন কি তবে পুরুষেরা, নাকি কোনো যুবতীর দিঘল উঠোন?”
কবি নদীর তীরবর্তী মানুষের শত বছর ধরে চলে আসা পুরনো একটি পেশার
বর্ণনা কবিতায় তুলে এনেছেন নিপুণ শিল্প কুশলতায়:
“মধ্যরাতে শিস দেওয়া সাপের মতন শকুন ডাকে, গাং পাড় ধরে যুবতীরা যায়।” (যেখানে নদী যায়)। অথবা, “উঠোনের মাঝখানে পত পত করে ওড়ে যুবতীর সমস্ত শরীর। যুবতী শরীর শুকোয়।/ মধ্যরাতে কুপি নিবে, মহাজন মরে যায়।” (প্রাগুক্ত)।
দীর্ঘদিন ধরে আরিচার কোলঘেঁষে দেহজীবীদের পাড়া ছিলো। এখানকার বাসিন্দাদের জীবন যাপনের চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। “নয় দুয়ার বারো উঠোন” সিরিজের প্রথম কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে:
“ট্রেনের গতি ছিল শকুনের আঁচড়খাওয়া বুকের মতন / শুরুতেই ঝড়উঠতো না। / আরিচার ঠিক পশ্চিমে দিঘল ভাটিতে ধোঁয়া ওঠা সন্ধ্যায়বুবুরা / শরীরে কাপড়পেঁচিয়ে শীতল জলে তিরতির দেহ ভেজাতো।/দীর্ঘ ছায়া ছিল। রূপ ছিল সোনামুখী সোনামুখী সুঁইয়ের মত।” (নয়দুয়ারের বারো উঠোন : এক)।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হতভাগা নারীদের ঠাঁই হতো এই পাড়াতে। সমাজ যাদের গ্রহণ করতো না এই পাড়া তাদের সাদরে বরণ করে নিতো। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি অনুষঙ্গে মিশে যায় এইসব নারীদের করুণ ইতিহাস। এদের জীবন যেন মানুষের জীবন নয়, পশুপাখির জীবন। পানিতে ভেসে থাকা হাঁস সন্ধ্যায় ডাকতে ডাকতে ঘরে ফেরে। এই পাড়ার নারীরাও তেমনিভাবে মানুষকে আহ্বান করে নিজ নিজ ঘরে।
“সারিবাঁধা বুবুদের ঘর, দক্ষিণ দুয়ার, উত্তর দুয়ার, দুয়ারের পর চক/সন্ধ্যা শেষে হাঁসের ডাক- ‘এ্যাঁই প্যাঁক প্যাঁক, এ্যাঁই প্যাঁক প্যাঁক।’ ঘরের বেড়ায়কত কী যে ছাইপাশ-/নাকফুল, কানপাশা, কাঁকুইর চুল ও গলার তাবিজ। /মহাজনের আসরে বুবুদের যাত্রাপালা বসে। শকুনের চোখ চকচক করে ওঠে...।’ (নয় দুয়ারের বারো উঠোন : দুই)।
“নয় দুয়ারের বারো উঠোন” সিরিজে কবি গভীর মমতায় আরিচা পাড়ের এই সব বিশেষ নারী তথা বুবুদের জীবন, তাদের আনন্দ, হাসি-কান্নার উপাখ্যান কবিতায় বয়ান করেছেন। সেই অনাদিকাল থেকে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর জীবন কখনো সুখময়ছিল না। নারী কখনো সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য কাক্সিক্ষত ছিলো না। নারী ছিল প্রজন্ম রক্ষা এবং ভোগের উপলক্ষ মাত্র। সমাজে, রাষ্ট্রে- সর্বত্র নারীর জীবন ছিল ভঙ্গুর, অপাংক্তেয়।
যুগ যুগ ধরে নদীপাড়ের এই সব মানুষেরা নদীকে অবলম্বন করে জীবন টিকিয়ে রেখেছে। এই নদী নারীর জীবনের পাপ, কালিমা জলে ধুয়েবাঁচার প্রেরণা যোগায়। নারী তার অস্তিত্বের জন্য, টিকে থাকার জন্য নদীর পানে চেয়েথাকে। নদীতে ভেসে আসা মহাজনের জন্য নারীর বিনিদ্র রাত কাটে।
পুরুষ তার শরীরের ক্ষুধায় এখানকার বুবুদের সান্নিধ্যে যায়। পুরুষের পঙ্কিলতায় নারী বাঁচে। কিন্তু এই বুবুদের জীবন যেন ভাগাড়ে পরিত্যক্ত পশুর মতো। তাই এদের জীবনের দুঃখ, বেদনা অব্যক্তই থেকে যায়, কেউ তাদের বোঝে না। তবে সমাজের সংবেদনশীল মানুষ তাদের জীবন কাহিনী শুনে ব্যথিত হবে, বিষণœ হবে। কবি বেদনাদীর্ণ উচ্চারণে সেই কথাই যেন বলতে চেয়েছেন:
“তুমি কখনোই বুবুদের ঠোঁট ছুঁয়ো না, কষ্ট পাবে।
দুঃখগুলো অন্তরালে চুইয়ে চুইয়ে শুদ্ধি হবে।
ওরা ঈশ্বরের দেহে ভগবানের দেবী হয়।”
ওরা সীতা, মেরি বা আমিনা সেজে ঈশ্বরের ঘরে বংশ বাড়ায়/ওরা রাবেয়ার রূপ ধরে শকুনের কষ্টে তাকায়। /তুমি কখনোই বুবুদের চোখ ছুঁয়ো না, কষ্ট পাবে। তুমি শুধু পাপী হবে।” (নয়দুয়ারের বারো উঠোন: আট)।
মহিবুল আলমের প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ “যেখানে নদী যায়”। ব্যতিক্রম শৈলীতে এই বইয়ের কবিতাগুলো লেখা হয়েছে। তার কথাসাহিত্যের মতো কবিতার ভাষাও ঝরঝরে। এবং বিষয়বিন্যাস তাৎপর্যপূর্ণ। আশা করি কবিতাগুলো পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।
যখানে নদী যায়। মহিবুল আলম। প্রকাশক : শালুক। প্রচ্ছদ : নাজিব তারেক। পৃষ্ঠা: ৬৪।মূল্য : ২৫০.০০টাকা।