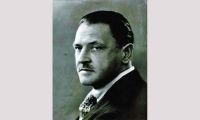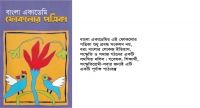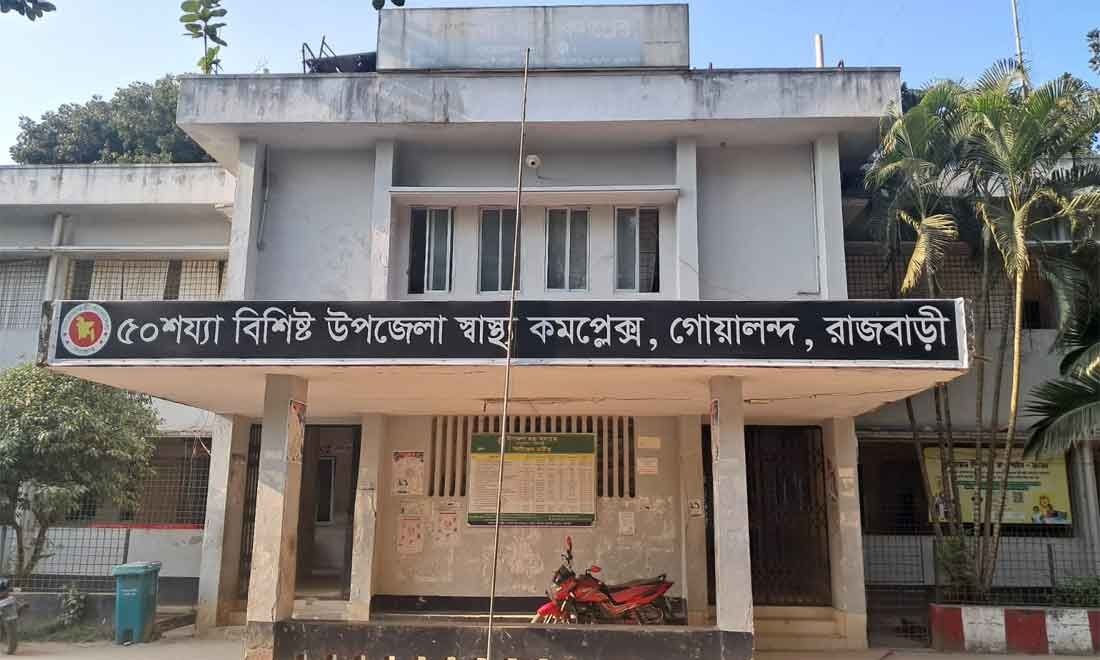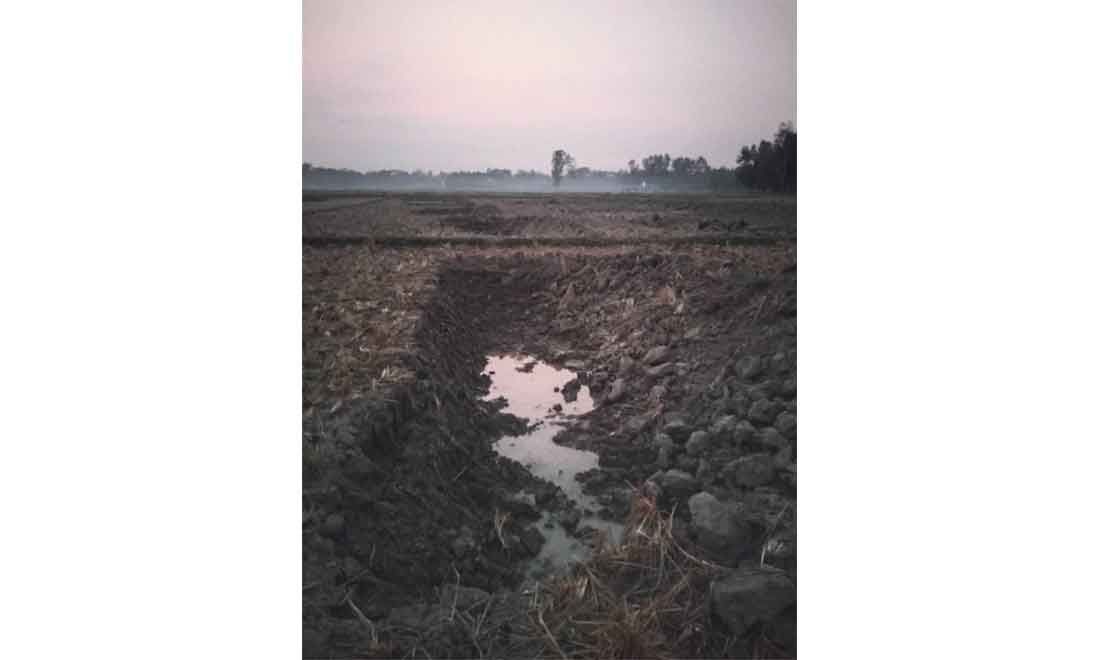অনুবাদকের দায় : বিশ্বস্ততা নাকি সরলতা?
আনিসুজ জামান
সাহিত্যের অনুবাদে প্রত্যেক অনুবাদক এক মৌল প্রশ্নের মুখোমুখি হন: অনুবাদের কাজ কি মূলকে পাঠকের জন্য আরো সহজ ভাষায় তুলে ধরা নাকি মূলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়েই অনুবাদ করা? বিশেষত সংলাপ অনুবাদের সময় এই প্রশ্নটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
অনুবাদ আলাদা কোনো সহজবোধ্য ভার্সন হিসেবে রচিত হয় না। সেই উদ্দেশ্যে অনুবাদ সাহিত্যের জন্ম হয়নি। তাই, বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ পড়া কোনো সহজীকৃত টেক্সট পড়া নয়
সংলাপে ব্যবহৃত প্রবাদ, স্ল্যাং, বক্রোক্তি, লোকাচার ইত্যাদি শুধু ভাষাগত রেজিস্টার নয়, সাহিত্যের নান্দনিক দিকও ফুটিয়ে তোলে। এর মধ্য দিয়ে একটি টেক্সটের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক স্থান ও আবহ প্রভৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব কারণে অনুবাদের উদ্দিষ্ট পাঠকের জন্য সংলাপের ভাষা কখনো কখনো জটিল মনে হতে পারে। এটা ভেবে অনুবাদক কথ্য ভাষাকে “সহজ”করে আরও বোধগম্য করার চেষ্টা করতে পারেন, তাতে মূল রচনার স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জীবন্ত টেক্সট মৃত হয়ে পড়ে। ফুল গাছে থাকলে যে প্রাণটা থাকে, তোলার পর আর তা থাকে না। জীবন্ত ফুল দেখতে হলে পাঠককে ফুলের কাছে যেতে হবে। অনুবাদক যদি পাঠকের সুবিধার জন্য ফুলটা ছিড়ে এনে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন তাহলে তিনি ফুলটা পাবেন কিন্তু প্রাণটা পাবেন না। তাই, আমি মনে করি, অনুবাদকের কাজ মূলকে সহজ করা নয়। মূল তার নিজের ভাষার পাঠকের জন্য যতটা কঠিন বা দুর্বোধ্য ঠিক ততোটাই কঠিন বা দুর্বোধ্য করে উপস্থাপন করা। এই সাহিত্যিক ‘দুর্বোধ্যতার’ মধ্যেই লুকিয়ে থাকে শিল্পরস, লেখকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অনুবাদকের কাজ, ভাল্টার বেনিয়ামিন যেমনটি বলেছিলেন, কেবল অর্থ স্থানান্তর নয়, ভাষার কম্পনটিও পৌঁছে দেওয়া। লেখকের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা।
অনুবাদের কৌশল নিয়ে আলোচনার আগে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা জরুরি: সাহিত্য আসলে কী? সাহিত্য কেবল ঘটনার বিবরণ নয়। একটি কাহিনি কয়েক লাইনে সংক্ষেপ করে প্রকাশ করা সম্ভব, সেটা সাহিত্যের শরীর, কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ হলো রস: বাক্যের সুর, তার সংগীত, নীরবতা, দ্ব্যর্থতা, এবং শব্দে বহন করা সাংস্কৃতিক উপকরণ।
বোর্হেসকে পড়তে বসলে পাঠক সরল, একরৈখিক ও আরামদায়ক গল্প পাবেন না। সেটাই বোর্হেস। বোর্হেসের সাহিত্যে তিনি এমন সব শব্দের মুখোমুখি হবেন যা এসেছে ইতিহাস থেকে, দর্শন থেকে, ধর্মতত্ত্ব থেকে, গণিত থেকে, আরো অনেক কিছু থেকে। প্রকৃত অর্থে বোর্হেসকে পড়তে হলে প্রস্তুতি নিতে হবে: দর্শন অধ্যয়ন করতে হবে, শোপেনহাওয়ার বা স্পিনোজার ইঙ্গিতগুলি ধরতে হবে; গণিত শিখতে হবে, গোলকধাঁধা ও প্যারাডক্সের ধারণা বুঝতে হবে। তার চেয়ে বড়ো কথা বোর্হেসকে বোঝার অখ- ধৈর্য ও আকাক্সক্ষা নিয়ে বসতে হবে।
ভালো পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন, সাহিত্য পড়া মানে শুধু কাহিনী নয়। কোনো কোনো মহৎ টেক্সট আছে যেখানে কাহিনী অপ্রধান বা সেটি আখ্যান-প্রধান না; ভাষা-প্রধান অথবা নির্মিতি-প্রধান। সাহিত্য হলো সেই জালের মতো- রেফারেন্স, শৈলী এবং অনুরণনে গাঁথা, যেটা সক্রিয়, শিক্ষিত এবং পরিশ্রমী পাঠক দাবি করে।
এই কথাগুলো মূল কিংবা অনুবাদের পাঠকের জন্য অভিন্ন কিছু না। পাঠক পাঠকই। একইভাবে টেক্সট টেক্সটই। অনুবাদ আলাদা কোনো সহজবোধ্য ভার্সন হিসেবে রচিত হয় না। সেই উদ্দেশ্যে অনুবাদ সাহিত্যের জন্ম হয়নি। তাই, বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ পড়া কোনো সহজীকৃত টেক্সট পড়া নয়। যখন কোনো পাঠক অন্য ভাষার কোনো লেখককে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি অন্য একটি জগতে প্রবেশ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এই চ্যালেঞ্জ আসে অচেনা শব্দ ও অজানা ইঙ্গিত থেকে। তাই অনুবাদ সাহিত্যের পাঠককে প্রস্তুত থাকতে হয়: শুধু পড়তে নয়, খুঁজে বের করতে, থামতে, প্রশ্ন করতে।
যেমন উদাহরণ হিসেবে, কোনো মেক্সিকান উপন্যাসে তেপিতোর স্ল্যাং বা হালিস্কোর কোনো গ্রামীণ শব্দ কেবল শব্দ নয়: এগুলো হলো সেই ভূমিতে জন্ম নেওয়া গল্পের জগতে প্রবেশের দরজা। যদি মূল পাঠে মেক্সিকান পাঠককে থামতে হয়, ভাবতে হয়, বা জিজ্ঞাসা করতে করতে এগোতে হয়, তবে কেনো বাঙালি পাঠককে অনুবাদ পাঠের সময় একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অনুবাদক কেনো সেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বা জটিতলতা বর্জন করে সহজ করে দেবেন? পাঠকের যে অসুবিধা, সেটাই তো নান্দনিক অভিজ্ঞতার অংশ। সেই অভিজ্ঞতা ও যাত্রা থেকে পাঠককে কেন তিনি বঞ্চিত করবেন?
সমালোচক লরেন্স ভেন্যুতি এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন মূলের foreignization: মূলের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, টেক্সটকে এতটা “ঘরোয়া”(domestication) না করা যাতে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। বরং পাঠককে ভিন্নতার অনুভূতি দেওয়া। ঘরোয়াকরণ-রীতি সবকিছু সমান করে তুলতে চায়, কিন্তু তাতে সাহিত্য ও শিল্পরস শুকিয়ে যায়। ফুলের সেই দেহটা থাকে প্রাণটা থাকে না।
অনুবাদ হওয়া উচিত নয় এমন এক পর্যটক দোভাষীর মতো, যে সবকিছু সরলীকরণ করে ব্যাখ্যা করে দেয়, বরং হওয়া উচিত সেই গাইডের মতো, যে আমাদেরকে পাথর কাঁটার ভেতর দিয়ে ভূদৃশ্য অতিক্রম করতে আহ্বান জানায়।
অনেক প্রখ্যাত অনুবাদক জোর দিয়ে বলেছেন যে, কথ্যভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। মার্কেসের অনুবাদক গ্রেগরি রাবাসা, যিনি “নিঃশঙ্গতার একশ বছর” ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, বলেছিলেন, অনুবাদের সময় সবচেয়ে কঠিন ছিল জনপ্রিয় কণ্ঠগুলো ধরে রাখা, কিন্তু সেখানেই তো ম্যাজিক রিয়ালিজমের চাবিকাঠি ছিল: “চরিত্রগুলির কথ্যভাষা ফ্লাট করে দিলে কুহকিবাস্তবের বুননটি ধ্বংস আর থাকবে না।”
হোসে ওর্তেগাই গাসেত তাঁর The Misery and Splendor of Translation প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, প্রতিটি অনুবাদই এক ধরনের ইউটোপিয়া, কিন্তু অনুবাদক ভাষাকে “নিচে নামিয়ে” মূলকে এমনভাবে নমনীয় করে তুলতে পারেন না যাতে পাঠক চিন্তা না করেই বুঝতে পারে: চিন্তা করাটাই শিল্পের অংশ।
উমবের্তো একো স্মরণ করিয়েছিলেন যে অনুবাদ হলো- “প্রায় একই কথা বলা”। সেই “প্রায়” মানে কিছু খামতি নেওয়া, কিন্তু এটিও নিশ্চিত করা মূলের মৌলস্বর কীভাবে কোথায় সংরক্ষিত হবে। একোর মতে, সেই মৌলস্বর প্রায়শই শব্দে নয়, স্বরে থাকে।
এমনকি বোর্হেসও বলেছেন যে, কখনো কখনো অনুবাদক মূলকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, এজন্য সাহস করে তাকে নিজের ভাষায় উপযুক্ত প্রতিধ্বনি খুঁজে বের করে আনতে হবে, সেটা সেই ভাষার পাঠকদের কাছে কর্কশ শোনালেও। বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জ দ্বিগুণ। কথ্যভাষার কোনো একক মানদ- নেই: ঢাকার নাগরিক ভাষা, পুরাণ ঢাকার ভাষা, গ্রামীণ রূপ, আঞ্চলিক উপভাষা, এমনকি একটি “সাহিত্যিক কথ্য”ভাষাও রয়েছে, যা হুমায়ূন আহমেদের মতো জনপ্রিয় লেখকেরা ইতিমধ্যেই প্রচলন করেছেন। সংলাপ অনুবাদ করার সময় অনুবাদককে সতর্কতার সঙ্গে এসব কথ্যভাষা থেকে একটিকে বেছে নিতে হয় অথবা তাকে একটি একটি কথ্যভাষা তৈরি করে নিতে হয়; যাতে তিনি এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে না পড়েন যেখানে মেক্সিকান চরিত্র পুরান ঢাকার বাসিন্দা হয়ে ওঠে। তাই কৌশল হিসেবে তিনি কথ্যভাষার একটি একটি স্বীকৃত সাহিত্যরূপ তৈরি করতে পারেন- যা মৌখিক ভাষার আবহ তৈরি করে কিন্তু চরিত্রকে সম্পূর্ণ লোকাল বা স্থানীয় করে তোলে না।
তাহলে, একজন বাঙালি পাঠক একটি অদ্ভুত বাক্যের সম্মুখীন হয়ে যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যান মেক্সিকান পাঠকও সেই একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। সেটিই হলো পাঠের অভিন্নতা, পাঠকের মৌল অনুভূতি যা অনুবাদে বিকৃত হয় না।
অনেক বাণিজ্যিক সম্পাদক ও অনুবাদক সরলতাকে পছন্দ করেন: যাতে পাঠক হোঁচট না খান, যাতে সবকিছু প্রথম পাঠেই বুঝতে বোধগম্য হয়। কিন্তু সাহিত্য সবসময় আরামের জন্য রচিত হয় না। যেমন অঁতোয়ান বেরমান উল্লেখ করেছিলেন, অনুবাদকের দায়িত্ব হলো দুর্বোধ্যতাকে মুছে না ফেলা, বরঞ্চ ধরে রাখা। এটাই হলো শিল্পের চিহ্ন।
তাই, সাহিত্যের অনুবাদককে কখনোই “সুখপাঠ্য”তে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তা হলে বলা হবে বোর্হেসকে পড়তে হবে দর্শন বা গণিত ছাড়াই, বা গার্সিয়া মার্কেসকে পড়তে হবে ক্যারিবীয় উপকূলের জনপ্রিয় লোক অনুষঙ্গ ছাড়াই। তখন যা অবশিষ্ট থাকে তা সাহিত্য নয়, কেবল কাহিনি।
তাই জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন: সাহিত্যকে পাঠকের কাছে তাৎক্ষণিক ভোগের পণ্য হিসেবে পৌঁছে দেওয়া অনুবাদকের কাজ নয়। শিল্প-সাহিত্য বোঝার জন্য সময় ও শ্রম দাবি প্রয়োজন, প্রস্তুতি অপরিহার্য। একটি বিদেশি বই পড়া মানে এমন এক ভূখ-ে প্রবেশ করা যেখানে মানুষ ভিন্নভাবে কথা বলে, যেখানে উপমাগুলো অন্য সংস্কৃতি থেকে জন্ম নেওয়া, যেখানে নীরবতা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। তাই এই নতুন জগতে ভ্রমণের জন্য পাঠকের প্রস্তুতি অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষের একজন ভ্রামণিক রোজকার পোশাক পরেই উত্তর মেরুতে চলে যেতে পারেন না, আবার উত্তর মেরুর কেউ এস্কিমোর পোশাক পরে বাংলাদেশে চলে আসতে পারেন না। ভূগল অনুযায়ী ভ্রমণের জন্য ভ্রামণিকের মতো পাঠকেরও প্রস্তুতি, শ্রম ও নিষ্ঠা প্রয়োজন।
কেউ কেউ মনে করেন যে অনুবাদ সাহিত্যে মূলকে “আরও কাছে নিয়ে আসা” উচিত, যাতে তা আরও সহজবোধ্য হয়। কিন্তু সত্য হলো, বিদেশি সাহিত্য কখনোই সহজ নয়। অন্য ভাষার একজন লেখককে পড়া সব সময় স্বভাষা ও স্বদেশি লেখকদের পড়ার চেয়ে দুরূহ কাজ। স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা সবকিছু সহজে বুঝতে পারব না, এবং এক্ষেত্রে বাড়তি আনন্দ যুক্ত হয় দুর্বোধ্য অংশ বোঝার অনুসন্ধানে।
যে পাঠক দর্শনজ্ঞান ছাড়া বোর্হেস পড়বেন, তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু মিস করবেন; যে পাঠক হাইতির ইতিহাস না জেনে কার্পেন্তিয়ের পড়বেন, তিনি ঞযব করহমফড়স ড়ভ ঞযরং ডড়ৎষফ সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন না; যে পাঠক আমেরিকার দক্ষিণের প্রেক্ষাপট না জেনে ফকনারে প্রবেশ করবেন, তাকেও কষ্ট পেতে হবে। কারণ মহত সাহিত্য সব সময় কনটেক্সুয়াল, নেটিভ। মহত সাহিত্যকে বুঝে ওঠার প্রচেষ্টা যাতে অনুবাদে মরে না যায়, সেদিকেও অনুবাদকদের লক্ষ্য রাখতে হবে। ইউলিসিস যদি স্বভাষার পাঠকদের জন্য দুর্বোধ্য হয়, অনূদিত পাঠের পাঠকদের জন্যও দুর্বোধ্য হতে হবে। অনুবাদকের কোনো দায় নেই সেটি সহজ করার, বরঞ্চ দায় আছে যে দুর্বোধ্যতা ইউলিসিসের অনিবার্য অংশ, সেটিকে ধরে রাখার।
তাই আমি অনুবাদ সাহিত্যের পাঠকদের আহ্বান জানাবো: আপনারা ‘পেদ্রো পারামো’ বা ‘কুয়ো’, অথবা ‘এ জগতের রাজত্ব’ এই ধরনের উপন্যাসগুলো যখন বাংলা অনুবাদে পাঠ করবেন তখন অবশ্যই কিছুটা সময় ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বসবেন। এই ধরনের বইগুলো আপনার মনোযোগ ও মনোসংযোগ দাবি করে। মূলের পাঠকদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য।
শিল্প-সাহিত্য সব সময় সহজবোধ্য হয় না। আবিষ্কারের মধ্যেও আনন্দ থাকে। আর সেই কারণেইে আমি কথ্যভাষাকে কথ্যভাষায় অনুবাদ করার পক্ষে- তবে মূলের স্বর বজায় রেখে। শুধু লেখকের প্রতি নয়, সাহিত্যের নান্দনিকতার প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে কিছু দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হলেও সেটা মেনে নিতে হবে। কারণ সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা কাহিনীকে অতিক্রম করে যায়।