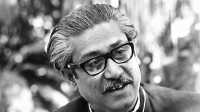মুক্ত আলোচনা
টার্গেট ২০৪১ : মানসম্মত শিক্ষার অপরিহার্যতা
মো. ছোলজার রহমান
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোন প্রকার অঘটন ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। নতুন সরকার গঠন ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণও সমাপ্ত হয়েছে। তাই ভিশন ২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, মেগা প্রকল্প বদ্বীপ পরিকল্পনা এবং টার্গেট ২০৪১ বাস্তবায়নে কোন ছেদ ঘটল না। ২০৪১ বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে। সদিচ্ছা, উদ্যম, দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালায় ইতিবাচক ও যথোপযুক্ত পরিবর্তন এনে বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ ও তদারকির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হলে ২০৪১ সালই বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক হবে, যা দেশটিকে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে পারে। এ দিনটির কামনা ও অপেক্ষা করা অসম্ভব ও অযৌক্তিক কিছু নয়। এজন্য দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, শিষ্টাচার, অপরাধবোধ, নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আইন মেনে চলা ইত্যাদির অভ্যাস গঠনের। এজন্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা, সুশাসন, সুবিচার, সুশিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা, অহিংস নীতি ও কর্মকা-। এসব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে সুদৃঢ়, সুদূরপ্রসারী ও টেকসই ভিত রচনার জন্য নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষার। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত মানদ-।
প্রতি বছর ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে সবার জন্য বই সরবরাহ শিক্ষাগ্রহণকে অনেকাংশে সহজ করে দিয়েছে, এটি সরকারের একটি অন্যতম মহৎ কর্ম ও জাতীয় অগ্রগতি। তাসত্ত্বেও এই দশটি শ্রেণীর ৭টিতে গাইড বইয়ের ব্যবহার ও বাণিজ্য চরম আকার ধারণ করেছে। ৪র্থ থেকে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত তাকালে বোধ হয় এটিই পাওয়া যাবে যে শিক্ষার্থীদের ৭৫-৮০% ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গাইড বই কিনছে ও পড়ছে। বাজারে প্রাপ্যতা, শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশনা ও ইঙ্গিত, অভিভাবকদের আগ্রহ ও সমর্থন, অন্যের দেখে প্রভাবিত হওয়া, শ্রেণীপাঠে ও পরীক্ষায় ব্যবহার, কোচিং শিক্ষকের নির্দেশনা এবং গাইড ব্যবসায়ীদের এলাকাভিত্তিক সিন্ডিকেটের লোভনীয় অফার ইত্যাদির কারণে গাইড বইয়ের ব্যবসা প্রতিবছর হাজার কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হলে এর কোন তথ্য প্রমাণ নাও মিলতে পারে, কিন্তু কেউ যদি অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ১০০ জন শিক্ষার্থীর বাড়িতে বেড়াতে যান এবং আপ্যায়নের এক ফাঁকে শিক্ষার্থী কি কি বই পড়ে তা দেখতে চান তাহলেই এসব বক্তব্যের সত্যতা সরাসরি পাওয়া যাবে।
স্বাধীনতার পূর্ব থেকে ৯০ এর দশক পর্যন্ত দেশে প্রাধান্য ছিল প্রাইভেট পড়ানোর যেখানে সিংহভাগ শিক্ষার্থীকে পড়াত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক এবং অল্প কিছু শিক্ষার্থী পড়ত শিক্ষিত ব্যক্তি ও শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া শিক্ষার্থীদের কাছে। বর্তমানে এ অবস্থা ভিন্নরূপ নিয়ে কোচিং সেন্টারে পরিণত হয়েছে। কোচিং সেন্টারসমূহ শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষা সমাপ্তকারী নিয়ন্ত্রিত এ দুই ধরনের হয়ে থাকে। আবার একজনেই পড়ান ও বহুজনে পড়ান এই দু’ধরনের রয়েছে। শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত কোচিং সমূহে পড়া বুঝিয়ে দেয়াটাই প্রাধান্য পায়। শিট খুব অল্পই দেয়া হয়। শিক্ষা সমাপ্তকারী নিয়ন্ত্রিত কোচিংয়ে শিট প্রদানই মুখ্য, বুঝিয়ে দেয়াটা গৌন। বহুজনে পড়ানো কোচিং সেন্টারে যারা পড়ান তাদের বেশিরভাগই শিক্ষিত বেকার এবং এদের কম অর্থ দিয়ে সন্তষ্ট রেখে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়। এসব পদ্ধতির কোচিংয়ে এখন শিক্ষা সমাপ্তকারীদের কোচিংই সবচেয়ে জমজমাট রূপ লাভ করেছে। অল্প কিছু শিক্ষার্থী এখনও প্রাইভেট পড়াকে ধরে রেখেছে। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান শ্রেণীপাঠ ছুটির পর থেকে প্রতিষ্ঠানেই কোচিং করানোর পদ্ধতি চালু রেখেছে। সবগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে গ্রাম ও শহরের ৮০%-৮৫% শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী পাঠগ্রহণ অনেকাংশেই গৌন হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব কোন নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ না করলে অচিরেই শ্রেণী উপস্থিতি ও শ্রেণীপাঠদান হতাশাজনক জায়গায় নেমে আসবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাও উপরের বর্ণনাসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এদের জন্য বাড়তি কোচিং নির্ভরতা রয়েছে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার জন্য যার একটি হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল ৭ও ৮ আগষ্ট ২০১৮ দৈনিক গ্রামের কাগজ যশোরে এবং এতে ব্যয়ের হিসাবটি ছিল প্রতি বছর দশ হাজার কোটি টাকা। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতেও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া ও শ্রেণী পাঠদানে অংশ নেওয়া গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাসকোর্স ডিগ্রি শ্রেণীতে ক্লাসে উপস্থিত হওয়াটা কোন নিয়মের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। সম্মান ও পাসকোর্স শ্রেণীর বেশিরভাগই হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এদের শ্রেণী পাঠে উপস্থিত হওয়ার আবশ্যকতা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সবার যুক্তিগুলো হচ্ছে-বাড়ি দূরে, চাকুরী করি, গরীব, থাকার জায়গা নেই, ক্লাস হয় না, আজকাল ক্লাস না করলেও চলে, ক্লাস করি আর না করি পাস করলেই হলো, বিবাহিত, বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা আছে, বাড়িতে কাজ করতে হয়, অসুস্থ, বাবা-মা অসুস্থ ইত্যাদি। ভর্তি, ফরম পূরণ, প্রবেশপত্র গ্রহণ, সার্টিফিকেট গ্রহণ ইত্যাদির দিনেও নিজে আসতে পারে না। কলেজসমূহে প্রিলিমিনারি মাস্টার্স বা মাস্টার্স পার্ট-১ শ্রেণীর কোন শিক্ষার্থী দেখতে চাইলে ভর্তি, ফরম পূরণ, ব্যবহারিক পরীক্ষার দিনসমূহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং সে যদি নিজে আসে তবে শিক্ষকগণ দেখতে পাবেন। এ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদেরও যুক্তিসমূহ একই। কলেজসমূহের মাস্টার্স শ্রেণীর অবস্থা আরও একধাপ এগিয়ে। সমাজে ও চাকরিজীবনে অবস্থান কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাদের কলেজে বা ক্লাসে পাওয়াটা অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার।
তাহলে কি কলেজগুলো শিক্ষার্থী শূন্য? প্রতি শ্রেণীর কিছু (৫-১৫) শিক্ষার্থীর বাড়ি নিকটে বা কোন চাকরি না পাওয়ায় এদের একটি অংশ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ক্লাসে হাজির থাকে যেখানে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতি শ্রেণীতে ৫০ থেকে ৬০ জন। ২-৩ জন হাজির হওয়ার কারণেও অনেক ক্লাস গ্রহণ করা হয় না। অন্যান্য লোভনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় ১ম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই অন্যখানে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ৭/৮ মাস ধওে ছোটাছুটি করায় ব্যস্ত থাকে। এতে ৩০/৪০ হাজার শিক্ষার্থীর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যয়কৃত ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা করে পানিতে চলে যায়। এরপরও ভর্তি বাতিল করে মূল নম্বরপত্র নিতে আসলে ভর্তি বাতিলের জন্য পুনরায় হাজার টাকা করে ব্যয় করতে হয়। এসব কারণে অনেক শিক্ষার্থী চলে যাওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ২য় বার ভর্তির জন্য মনোনয়ন করতে ও ভর্তি করতে হয়। ফলে ৬-৭ মাস ব্যয় হয় ভর্তির জন্য অথচ ক্লাস চলমান হয়েছে ৫ মাস আগে থেকেই। দ্বিতীয় দফায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য গমনকারী শিক্ষার্থীদের একটি অংশ যখন ফিরে আসে তখন কলেজসমূহে ইনকোর্স পরীক্ষা, নির্বাচনী পরীক্ষা, ফরম পূরণ ইত্যাদি চলতে থাকে। ফলে একটি বড় অংশের শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় ক্লাসবিহীন অবস্থার মধ্য থেকে। এতে অনেকেই আগ্রহ ও আকর্ষণ হারিয়ে গতানুগতিক ও ক্লাসবিমুখ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীর ১টি বছর নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর তাগিদে বা কোন নিয়মের তোয়াক্কা না করে শূন্য ক্লাসযুক্ত শিক্ষার্থীকেও ফরম পূরণ করতে দেয়া হয়। ১ম বর্ষের অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, প্রাপ্ত সুবিধা ও আনুকূল্য পরবর্তী বর্ষসমূহেও তাদের অনুপ্রেরণা জোগায় এবং তাদের দেখে অন্যরাও ক্লাসবিমুখ হয়ে পড়ে। ডিগ্রি ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ অনার্স ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ মাস্টার্স পার্ট-১ ও মাস্টার্স পার্ট-২ বর্ষসমূহে প্রতি পত্রের ১০০ নম্বরের মধ্যে ২০ নম্বরের চূড়ান্ত পরীক্ষা ক্লাস চলাকালীন ইনকোর্স পরীক্ষা ১৫ নম্বরের এবং শ্রেণী উপস্থিতির জন্য ৫ নম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ নম্বর প্রদান কিছু শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কারণে এবং প্রকৃত উপস্থিতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যাদের শ্রেণী উপস্থিতি ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নেই অথবা কেবল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু পাস নম্বর পায় না তারাও ভাল নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। কিভাবে বা কেন পায় তা আমি জানি না কিন্তু এটুকু জানি যে এ ২০ নম্বরের মধ্যে ফেল করলে ফরম পূরণ বাতিল হয়ে যাবে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। পড়ালেখা না করেও বাকি ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় কিভাবে পাস নম্বর পায় এরূপ প্রশ্ন করা হলে আপনি পূর্ববর্তী ২-৩ বছরের প্রশ্ন সংগ্রহ করে দেখুন প্রশ্নসমূহ এবছর ও বছর এ দু’ভাগে বিভক্ত। ফলে শিক্ষার্থী নিজেই ঠিক করতে পারে সামনের বছর কোনগুলো আসবে। মাঝে মধ্যে ২-১টি পত্রে ভিন্ন হয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার খেটেখুটে ভিন্নরকম প্রশ্ন নির্বাচন করার কারণে। তারপরেও ফেল হওয়াটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। এমনিতেই ইনকোর্স ও শ্রেণী উপস্থিতির ২০ নম্বর অনেকটাই স্থানীয় নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, অধিকারের নম্বর, পৈতৃক নম্বর, কর্তৃপক্ষের নম্বর, চাপের নম্বর, প্রতিষ্ঠানের নম্বর, তদবিরের নম্বর হিসেবে ধরে নেয়া হয় এবং বলতে গেলে শিক্ষার্থীদের নিশ্চিত নম্বর যা থেকে শিক্ষার্থীরা ১৫ থেকে ২০ নম্বরের মধ্যে পেয়ে থাকে (পরীক্ষা দিক বা না দিক, পরীক্ষায় ভালো লিখুক বা খারাপ লিখুক বা না লিখুক, কারও পকেট থেকে তো আর গেল না), তাই পুরো ১০০ নম্বরের মধ্যে পাসের জন্য আরও প্রয়োজন হয় লিখিত ৮০ নম্বরের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ নম্বরের। দু’প্রকারের নম্বর মিলে ৪০ হলে পাস হয়ে যায়। লিখিত ৮০ নম্বরের ১ম প্রশ্নটি কুইজ ধরণের যাতে ১২টি প্রশ্ন থেকে ১০টির জন্য ১০ নম্বর এক শব্দে/এক কথায়/ দু’এক বাক্যে উত্তর প্রদানের জন্য এবং পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিকে কর্তব্যরত শিক্ষকগণ স্বাক্ষর করানো নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ই যে কোনভাবে উত্তর লেখা সম্ভব হয়ে থাকে। আর বাকি থাকল ১০-১৫ নম্বরের। কপালে ভালো কিছু লেখা থাকলে ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত শিক্ষক, গল্পকারী শিক্ষক, বারান্দায় হাওয়া খাওয়ায় ব্যস্ত শিক্ষকও মিলতে পারে। না হলেও খুব একটা সমস্যা নেই-অ্যানড্রয়েড ফোন, কিছু কাগজপত্র ও চোতা পকেটে থাকতেও পারে, টয়লেটেও ২-১টি গাইড বা নোট থাকতেও পারে, এপাশ-ওপাশের চারজনে মিলেমিশে কিছু একটা করতেও পারে। নকল বিভিন্ন রুপ পাওয়ায়, অতি ছোট ফন্টে ফটোকপি করে আনলে শিক্ষকগণ খুঁজে দেখতে আগ্রহী হন না। একথাও শোনা যায় যে কোন কোন শিক্ষক তার চাকুরীকালে কোন নকল দেখতেও পাননি। এতেও না হলে ১৪ দিনের মধ্যে খাতা দেয়ার তড়িঘড়িতে পড়ে না দেখে নম্বর দেয়ার কারণেও অবশিষ্ট ১০টি প্রশ্নে ১ করে পেলেও অসুবিধা হবে না। দোষে গুণে মানুষ, ক্ষমা মহৎ গুণ, পরোপকার উত্তম ধর্ম, ভুল ও অপ্রাসঙ্গিক হলেও নম্বর দেয়া, কিছুটা নম্বর দেয়া ইত্যাদি গুণের কোন কোনটি কারও কারও থাকতে পারে। সকল ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক নম্বর তো নিজের সাবজেক্টের টিকিয়ে থাকা, ভালো ফলাফল ও সুনামের জন্য, প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য, তদবির ভিত্তিক ও বিভাগের শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের ইচ্ছাভিত্তিক হতেই পারে। ব্যস্ত বহিপরীক্ষক যথাসময়ে নাও আসতে পারেন, ২ থেকে ৪ দিনের জন্য হলেও নিজে কোন প্রশ্ন-যাচাই/কাজ না করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতেও পারেন, পরীক্ষাস্থলে না থেকে এদিক ওদিক ঘুরতে/গল্প করতে যেতেই পারেন, বহিপরীক্ষক না থাকলেও বাকি সবাই তো সহকর্মী, খালি নম্বরপত্রে তো আগাম স্বাক্ষর দেয়া যেতেই পারে, টিএ/ডিএ তো পুরো সময়ের পাওয়া যাবে, বাড়তি খামও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মিয়া-বিবি রাজি থাকলে কাজির আপত্তির সুযোগ কোথায়? অনলাইনে নম্বর পোস্টিং দেয় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ও কলেজের শিক্ষক বা অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে অফিস। শিক্ষার্থী কত পেয়েছে বা পরীক্ষায় কেমন পেরেছে তা দেখার সুযোগ ও প্রয়োজন কোথায়? শুধুতো এন্ট্রি দেয়া নম্বরই যাবে। অনলাইনের নম্বর পেলেই তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফলাফল দিয়ে দেয়। রাজশাহী কলেজের ঘটনায় তো বহিপরীক্ষক লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এসব ছোটখাটো বিষয়ে কর্তপাত করার/দৃষ্টি দেয়ার সময় থাকে, সারাদেশ নিয়ে কাজ, এমনিতেই ব্যস্ততা অনেক।
শিক্ষায় গরিব-ধনীর পার্থক্য ঘোচানোর সঠিক উপায়টি আসলে কি হওয়া উচিত? গরিবের বিক্রয়যোগ্য কোন দ্রব্য যেখানে আমরা সহানুভূতি ও সহযোগিতা বিবেচনায় বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করি না সেখানে পরীক্ষায় মূল্যায়নে বেশি নম্বর দিয়ে পুষিয়ে দেয়াটাই কি আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের উপায়?
কয়েকটি বর্ষে মাঠকর্ম রিপোর্ট, টার্মপেপার, প্রজেক্ট পেপার, মাঠ জরিপ ইত্যাদি ছোট আকারের গবেষণা রয়েছে। কিছু একটা লিখলেই অন্তত নম্বর দেয়া যাবে। গ্রাম থেকে এসেছে। এমনিতে কোনদিন আসে না, তবুতো এনেছে, অতসব পদ্ধতি, নিয়মকানুন ঘেটে দেখার দরকার কি, ১ দিনেই ঘরে বসে গবেষণা সেরেছে, তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজারের দরকার কিসে, উনি শুধু স্বাক্ষর দেবেন, স্বাক্ষর না দিলেই বা বাংলাদেশে কে কবে ফেল করেছে। হোক না হোক ৬০-৮০% নম্বর দিলে কার ক্ষতি; ঠিক যেন গ্রাম্য সালিশ অথবা মিলাদ মাহফিল, উপস্থিত থাকলেই তবারক প্রাপ্য। মৌখিক বা গবেষণা রিপোর্ট মূল্যায়ন করে সর্বনিম্ন নম্বর কত সব দেয়া হবে তার প্রতিষ্ঠান ও এলাকাভিত্তিক ধারা বা অভ্যাসও দেখা যায়, আবার গত বছর কাউকে ৭০ এর কম দেয়া হয়নি এবার কত দিয়ে শুরু করা হবে তাও আগেই ঠিক করে নেয়া হয়। ব্যবহারিক, মৌখিক ও ইনকোর্স পরীক্ষায় হাজির না হলে পরীক্ষার্থীকে ফোন করে ডাকতে বা অনুরোধ করতে হয়। ওপাশ থেকে উত্তর আসে (এখন/আজ ও কাল/চাকরিতে ছুটি পাইনি) আসা সম্ভব নয়। কখনও শুন্যখাতায় বহিপরীক্ষকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখতে হয় যদি পরে কোনদিন আসে।
ডিগ্রি/সম্মান/মাস্টার্সের তত্ত্বীয় পরীক্ষাসমূহের দিনে অনেক পরীক্ষার্থীই পথিমধ্যে পড়ার জন্য হাতে একটি গাইড বই নিয়ে আসে। তাই গাইড উচ্চশিক্ষায়ও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াটা কোন কোন পরীক্ষার জন্য সমালোচনার বিষয় হলেও উচ্চশিক্ষায় এর যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, পরীক্ষার্থীরা অন্তত ঐ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকে, তাই নাই মামার থেকে কানা মামাই ভালো বা মন্দের ভালো। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষা না দিয়ে নম্বর পাওয়া, কিছু না লিখেই নম্বর পাওয়া, ভুল উত্তরে নম্বর পাওয়া, অপ্রাসঙ্গিক উত্তরে নম্বর পাওয়া, না পারলেও নম্বর পাওয়া ইত্যাদি অপেক্ষা প্রশ্ন ফাঁসই উত্তম। ইনকোর্স একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা হলেও কিছু কলেজে পরীক্ষার বেশ কয়েক দিন আগে তার প্রশ্ন দিয়ে দেয়া হয় যা সাজেশন নামে পরিচিত। টার্ম পেপার, প্রজেক্ট পেপার, রিসার্চ মনোগ্রাফ ইত্যাদিতে অনেক শিক্ষার্থী এমন কিছু লিখে যা প্রাসঙ্গিক ও নিয়মতান্ত্রিক নয়। বানান ও বাক্য গঠন ধরা হলে নম্বরের চিত্রটি আরও হতাশাজনক হবে।
এলএলবি পাস পরীক্ষার হলের চিত্র চরম হতাশাজনক। নকল হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। বই দেখে লেখার নিয়ম ঘোষণা করা হলেই বরং কক্ষপরিদর্শকরা অনাচার হওয়ার ও দেখার বিরক্তি থেকে মুক্তি পাবেন। অথবা বাড়ি থেকে উত্তর লিখে আনতে বলা হলে বা নিয়ম করা হলে শিক্ষকগণ চোখের সম্মুখে নকলের বাড়াবাড়ি দেখতেন না বা ছাড় দেয়ায় অভ্যস্ত হতেন না। বয়স্ক ব্যক্তি হওয়ায় এবং বিভিন্ন মহলের সমর্থনপুষ্ট সহযোগিতা থাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ মনে হয় এটি এভাবেই দেয়ার নিয়ম। কারো নকল ধরা হলে বা বাঁধা দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের হুমকি ও ভীতির মধ্যে পড়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।
এ লেখাটিতে দেশে বিরাজিত শিক্ষা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কিছু দিক তুলে ধরা হলো। কাউকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক নির্বাচন, নম্বরসর্বস্ব শিক্ষা, আন্ত শিক্ষাবোর্ড পরীক্ষা পরবর্তী প্রতিযোগিতা, শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালায় তয় শ্রেণী থাকা, ঘুষ বা ডোনেশন, প্রভাব বিস্তার, কিছুক্ষেত্রে মেধাকে প্রাধান্য না দেয়া, ছোট ছোট ও সীমিত সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাস, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, অবকাঠামো-আসবাবপত্র-বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদির ঘাটতি, সামাজিক আয়স্তরে তারতম্যের বিস্তৃতি, শ্রেণীপাঠবিহীন বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অনুমতি প্রদান, অভিভাবকের মনোভাব-সমর্থন ও চাওয়া-পাওয়া, মনিটরিং ও তদারকির ব্যবস্থা না থাকা, উচ্চশিক্ষার ভর্তিও জন্য যোগ্যতা জিপিএ-২ চাওয়া, সমন্বিত একটি ভর্তি পরীক্ষা না থাকা, প্রশাসন-পুলিশ-সেনাবাহিনী-বিডিআর কর্তৃক শিক্ষার একটি অংশ দখল করা, শিক্ষকতায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে না পারা, শিক্ষকের পারদর্শিতা ও পদসংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও অনার্স-মাস্টার্স খোলার অনুমতি প্রদান, উচ্চশিক্ষাকে সহজীকরণের নামে বিশেষ ছাড় দেয়ার অনুকূলে উস্কানিমূলক ও অনৈতিক বক্তব্য প্রদান, উচ্চশিক্ষাকে সবার জন্য ও বাধ্যতামূলক করার মতো ভাবনা, ঘরে ঘরে উচ্চশিক্ষিতের সার্টিফিকেট পৌঁছানোর দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা, কোচিং ও গাইড বন্ধকরণের পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহা, ছাত্রাবাসসমূহে মেয়াদোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও বহিরাগতদের বসবাস ও নিয়ন্ত্রণ, ম্যানেজ করে চলার নির্দেশনা, কোন প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংসদ না থাকা এসব কিছুই আলোচনায় চলে আসবে। শিক্ষার্থী ফেল করে নাই, শিক্ষক ফেল করিয়েছেন, ফেল করিয়েছেন কেন-কেহ কি ফেল হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিয়েছে, ফলাফল বিপর্যয়, শিক্ষার্থী না হয় লিখতে পারে নাই-তাই বলে কি ফেল করাবেন, বেছে বেছে আমার ছেলেদেরকেই কম নম্বর দিয়েছে, শিক্ষার্থী ভুল করলেও শিক্ষক ভুল করতে পারেন না, জীবনটা নষ্ট করে দিলেন, পাস করিয়ে দিলে কি ক্ষতি হতো-এগুলো উস্কানিমূলক বক্তব্য। ভিকারুন-নিসা নূন স্কুলে শিক্ষকদের হেনস্থা ও জুলুম করাটাও অনেকটা উস্কানিমূলক ছিল। ইয়াবা ট্যাবলেট আকারে ছোট হলেও তা ধরা সম্ভব হচ্ছে এবং গাইড বড় আকারের হওয়া সত্ত্বেও ধরা পড়ছে না। আবার দেশে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধিতে এসব ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে যথেষ্ঠ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতেও সক্ষম হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যমান নিয়মই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি অর্জনকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। পিছিয়ে পড়া, কম মেধাবী শিক্ষার্থীকে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকেই অনেকটা বিগলিত ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেন এবং যুক্তি হিসেবে গ্রামাঞ্চল, গরিব, অসহায় ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। এ প্রকারের যুক্তি আসলে কম্প্রোমাইজিং ও নিগোসিয়েটিং। কম আয়, সামর্থ্য নেই, সহায় সম্বল নেইÑ তাই তা পুষিয়ে দিতে বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নম্বর। কিছু খাটো খুঁটিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পুরো ঘরটিকে খাটো করে বানানোর পরিকল্পনা না করে বড় খুঁটি দিয়ে উঁচু ঘর এবং ছোট খুঁটি দিয়ে খাটো ঘর তৈরি করাই শ্রেয়, নতুবা বড় খুঁটিসমূহকে খাটো করে রাখা বা বাদ দিতে হবে। নরম বা নমনীয় বস্তুর সাহায্যে কোন কিছুতে ধার তীক্ষè ও শাণিত করা যায় না বরং কঠিন বা শক্ত বস্তু যেমন- বালি, পাথর, লোহা, সিমেন্টের ঢালাই ইত্যাদির প্রয়োজন হয় আর মেধাকে শাণিত করতে প্রয়োজন মেধাবী শিক্ষক ও পাঠগ্রহণ কাজে উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা। শিক্ষাদান কাজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক সুপারিশ, অল্প পারিশ্রমিকে চাকরিতে রাজি ইত্যাদি ধরনের প্রস্তাবকেই বেশি বিবেচনা করা হয়। সমাজের নতুন ও আগামী প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ নিয়মনীতি মানতে শিখে মূলত শিক্ষকদের কাছে, শিথিল নিয়ম নীতিতে বেড়ে উঠলে বা অভ্যস্ত হলে তারা পরবর্তী জীবনে নিয়ম নীতি মেনে চলায় অভ্যস্ত হতে চাইবে না।
শিক্ষায় গরিব-ধনীর পার্থক্য ঘোচানোর সঠিক উপায়টি আসলে কি হওয়া উচিত? গরিবের বিক্রয়যোগ্য কোন দ্রব্য যেখানে আমরা সহানুভূতি ও সহযোগিতা বিবেচনায় বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করি না সেখানে পরীক্ষায় মূল্যায়নে বেশি নম্বর দিয়ে পুষিয়ে দেয়াটাই কি আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের উপায়? যদি মনে করা হয় ক্ষতি কি তাহলে দেখা যাবে ক্ষতি আছে। কারও চাপে/ তদবিরে কোন কম মেধার শিক্ষার্থীকে বেশি নম্বর দেয়া হলে সে কারণে আরও অনেককে বেশি নম্বর দিতে হয়। এভাবে উত্তীর্ণদের একটি অংশ এখন একই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক হিসেবেও নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন। বলা বাহুল্য, বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে কর্মরত শিক্ষকদের একটি বড় অংশ যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক ক্লাসসমূহ সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন নন। নমনীয় পদ্ধতিতে মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা হলে আমাদের অচিরেই বিদেশ থেকে যোগ্য শিক্ষক আমদানি করতে হতে পারে। একজন অল্প মেধার শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ দেয়া হলে তিনি যত বছর পড়ানোর দায়িত্বে থাকবেন তত বছর ধরে সেই স্কুল/এলাকার সব শিক্ষার্থী তার দ্বারা বেশি মেধাবী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।
উন্নত দেশসমূহে শিক্ষায় উন্নততর মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনে চালু করেছে ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ শ্রেণীপাঠদান ও শ্রেণীকার্যক্রমে সফলভাবে দৈনন্দিন অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন। আমরা শ্রেণী কার্যক্রম থেকে দূরে রাখার সকল নমনীয়তা ও সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছি। ৬ বছরে একটি দিনের জন্য ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে পাসের সনদপ্রাপ্তি বিশ্বে কোথাও তো নয় বরং আমাদের দেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও সম্ভবপর নয়।
নতুন বছরের শুরুতে নতুন সরকার, মন্ত্রিসভায় নবীন ও প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যমীগণের সমাগম, পাশাপাশি নতুন শিক্ষামন্ত্রী, ইত্যাদি কারণে পরিবর্তনের পদক্ষেপ কামনা করা যায়। পরিবর্তন কোন দিকে হলে ভালো হবে তা সার্বিক দিক ভাবনায় স্থির করবে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে ২০৪১ সালকে বিবেচনায় আনলে তার জন্য পরিবর্তন-পরিকল্পনা এখন থেকেই করা প্রয়োজন বলে মনে করি।
[লেখক : সহযোগী অধ্যাপক-ভূগোল, সরকারি এমএম কলেজ, যশোর]
দৈনিক সংবাদ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, বৃহস্পতিবার, ৭ এর পাতায় প্রকাশিত
-
বিশ্ব রেড ক্রস দিবস
-
আত্মরক্ষার খালি-হাতের ইতিহাস ও আধুনিক বিস্তার
-
বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর : সমাজ সংস্কারের পথিকৃৎ
-

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস “বিজয় বসন্ত“গ্রন্থের লেখক
-
পয়লা বৈশাখ : বাঙালির সংহতি চেতনার সংস্কৃতি
-

স্মরণ : কমরেড রূপনারায়ণ রায়
-
সাংবাদিক-সাহিত্যিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে কিছু কথা
-
রেসলিং
-
কোটা সমাচার
-
বাজেট ২০২৪-২৫: তথ্যপ্রযুক্তি খাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের যাত্রা শুরু হোক এবার
-
সীমান্ত সড়ক পশ্চাদপদ পার্বত্য অঞ্চলকে উন্নয়নের স্রোতধারায় একীভূত করেছে
-
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১: উন্নত ও সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশের মহাকাশ জয়